জে ডি স্যালিনজারের দ্য ক্যাচার ইন দ্য রাই (১৯৫১) প্রকাশের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং বিতর্কের জন্ম দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্কুলে নিষিদ্ধ (১৯৬১-১৯৮২) থাকলেও বহু স্কুলে বইটি ছিল পাঠ্য। উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের জন্য। কিন্তু কিশোর দ্রোহ, একাকিত্ব ও মনস্তত্ত্বের অকপট দলিল হিসেবে কিশোরকিশোরীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। অশালীন ভাষা, যৌনতা এবং মাদকবিষয়ক বিবরণের জন্য এই বই আদালতের কাঠগড়ায় ওঠে। বিশ্বব্যাপী এখনও বিভিন্ন ভাষায় প্রতিবছর প্রায় আড়াই লাখ কপি বিক্রি হয় । ২০০৫ সালে দ্য টাইমস-এর করা ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ একশ উপন্যাসের তালিকায় ছিল বইটির নাম । এ উপন্যাসের পাঠ যেকোনো পাঠকের জন্য চমৎকার অভিজ্ঞতা ।
দ্য ক্যাচার ইন দ্য রাই – জে ডি সালিঞ্জার
অনুবাদ – রাফায়েত রহমান রাতুল
প্রকাশক – মো: রাজিবুর রহমান, রেনেসাঁ প্রকাশনী
প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২১
The Catcher in the Rye by J.D. Salinger Published by Renaissance.
উৎসর্গ
আমার মাকে
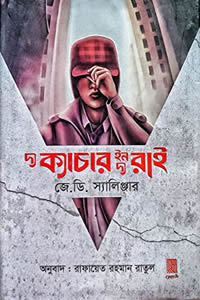
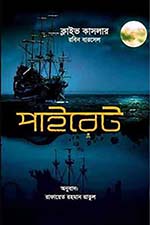

Leave a Reply