স্রষ্টা সত্যজিৎ
সত্যজিতের মধ্যে একটা সংগ্রামী মানুষের পরিচয় আমরা পাই। এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি দমলেন না। বংশী চন্দ্রগুপ্ত আর সুব্রত মিত্রকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। একটা ১৬ মিলিমিটার ক্যামেরা নিয়ে তাঁরা পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করলেন। ওঁরা হিসাব কষে দেখলেন কম করেও কুড়ি হাজার টাকা লাগবে ছবিটা তুলতে। সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ রইল।
১৯৫২ সালে সত্যজিৎ জীবনবীমা কোম্পানি থেকে সাত হাজার টাকা ধার নিলেন। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আরও দু-হাজার টাকা পাওয়া গেল। অপেশাদারদের দিয়ে তিনি শুরু করলেন তাঁর ছবির কাজ। নামি কোনো শিল্পীকে টাকা দেবার সামর্থ্য ছিলনা তখন।
বোড়াল গ্রামে লোকেশনের জায়গা ঠিক হল। একটা জীর্ণ, ভগ্নপ্রায় বাড়িকে বংশী চন্দ্রগুপ্ত খাড়া করলেন হরিহরের বাসা হিসাবে। তাতেই অনেক টাকা বেরিয়ে গেল।
দুর্গার ভূমিকার জন্য একটি মেয়েকে আগেই পাওয়া গিয়েছিল, নাম উমা দাশগুপ্তা, ইস্কুলে পড়ে। মা সর্বজয়ার ভূমিকায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পছন্দ হল সত্যজিতের। ভদ্রমহিলা একটি স্টোরে চাকরি করতেন, সেখানেই সত্যজিৎ তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন। শখের থিয়েটারে করুণা আগেই অভিনয় করেছেন।
মুশকিল হল অপুকে নিয়ে, কাউকেই সত্যজিতের মনে ধরেনা। মনের মতো ছেলের খোঁজে তাঁরা ইস্কুলে হানা দিয়েছিলেন, কাগজেও বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, কিন্তু সত্যজিৎ চান পারফেকশন।
একদিন বিজয়া দেবী তাঁদের লেক অ্যাভিনিউর বাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন, হঠাৎ নজরে পড়ল পাশের বাড়ির ছাদে কয়েকটি বাচ্চা ছেলে খেলা করছে। তাদের মধ্যে একটির দিক থেকে নজর ফেরানো যায় না। বিজয়া ‘পেয়েছি, পেয়েছি’, বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, ছুটে গেলেন সত্যজিতের কাছে, বললেন, ‘অপুকে পেয়েছি।’
‘কোথায়!’ সত্যজিৎও উত্তেজিত।
‘পাশের বাড়ি।’ বিজয়া জবাব দিলেন।
সারা কলকাতা হন্যে হয়ে খুঁজে যে ছেলেকে পাওয়া যায় নি, তাকে পাওয়া গেল পাশের বাড়িতে। ছেলেটির নাম সুবীর ব্যানার্জি।
ইন্দির ঠাকুরুনের ভূমিকার জন্য আশি বছরের চুনীবালা দেবী নির্বাচিত হলেন। তিরিশ বছর আগে তিনি পেশাদারি মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর দক্ষিণা ঠিক হল দৈনিক কুড়ি টাকা।
হরিহরের ভূমিকার জন্য মনোনীত হলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিই তখন একমাত্র পেশাদার অভিনেতা, সিনেমায় অভিনয় করেন। প্রথম শুটিংয়ের দিন তিনি সেলুন থেকে দারুণ এক ছাঁট দিয়ে এলেন। সত্যজিৎ তো হতভম্ব। একজন গেঁয়ো ব্রাহ্মণ, তাঁর চুলে হালফ্যাশনের ছাঁট। সত্যজিৎ সেদিন শুটিং বন্ধ রাখলেন, তাতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হল। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বললেন আগের মতো চুল বড়ো করে তারপর আসতে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এ ব্যাপারে মোটেই অসন্তুষ্ট হননি, বরং তিনি বলে বেড়িয়েছিলেন এতদিনে সত্যিকার একজন পরিচালকের দেখা পেয়েছেন। এর আগে কোনো পরিচালক তাঁকে নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রের জন্য চুল সম্বন্ধে কিছু বলেননি।
.
সত্যজিৎ তখনও চাকরি করেন তাই সপ্তাহে শুধু শনিবার আর রবিবার ছবির শুটিং হচ্ছিল। যা শট নেওয়া হচ্ছিল তা এডিট করাও সম্ভব হচ্ছিল না, এদিকে টাকাও ফুরিয়ে এসেছে। সত্যজিৎকে বাধ্য হয়ে তাঁর লাইব্রেরির বই মায় আর্টের দামি দামি বইও বেচে দিতে হল। স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে যোগাড় করতে হল টাকা। এত করেও চল্লিশ মিনিটের বেশি ছবি করা গেল না, এখনও অনেক বাকি। যেটুকু হয়েছে তা দেখে কেউ টাকা নিয়ে এগিয়ে আসবেন এমন ভরসাও নেই। ছবির কাজ বন্ধ।
সুপ্রভা দেবীই ত্রাণকর্তা হয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর এক পরিচিতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বি. সি. রায়ের খুব আলাপ ছিল। তাঁকে ধরে তিনি ডা. রায়কে ছবির ওই অংশটুকু দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। ডা. রায় কিন্তু মোটেই শিল্পকলা প্রেমিক ছিলেন না, ছবির ব্যাপারেও কোনো জ্ঞান ছিল না। তবু সময় নষ্ট করে ছবিটা তিনি দেখলেন।
ডা. রায়ের প্রথমে ধারণা হয়েছিল ‘পথের পাঁচালী’ গ্রাম্যজীবনের ওপর তথ্যমূলক একটা ছবি। তিনি উপদেশ দিলেন, ‘ওই পরিবারটাকে একটা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও।’
সত্যজিৎ চুপ করে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।
ডা. রায় অবিশ্যি নির্দিষ্ট বিভাগকে বলে দিয়েছিলেন ছবিটা শেষ করার ব্যাপারে একটা চুক্তির খসড়া করার জন্য, তখুনি দশ হাজার টাকা সরকারি অনুদান পাওয়া গেল।
পরে যখন ‘পথের পাঁচালী’ আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছিল, ডা. বিধানচন্দ্র রায় গর্ব করে বলতেন, ‘আমার ছবি’ [মাই ফিলম]। সত্যজিতের তিনি একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সব ছবি দেখতেন। শেষ ছবি দেখেছিলেন ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’।
সত্যজিৎ যেখানে চাকরি করতেন সেই ডি. জে. কীমারের একজন কর্মকর্তা ছবির কিছু অংশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি ছবির কাজের জন্য সত্যজিৎকে লম্বা ছুটি মঞ্জুর করলেন, কিছু আর্থিক সাহায্যও পাইয়ে দিলেন ছবির জন্যে।
‘পথের পাঁচালী’র কাজ যখন চলছে তখন নিউ ইয়র্ক মিউজিয়মের মডার্ন আর্ট বিভাগের মনরো হুইলার এলেন কলকাতায়। তিনি পরের এপ্রিল, ১৯৫৫ সালে, নিউ ইয়র্কে একটা শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজনের ব্যাপারে এসেছিলেন। ছবিটার যেটুকু অংশ এডিট করা হয়েছিল এবং কিছু অসংশোধিত অংশ দেখে সত্যজিৎকে তিনি প্রস্তাব দিলেন ছবিটা ওই প্রদর্শনীর আগেই শেষ করতে যাতে প্রদর্শনীতে ওটা দেখানো যায়।
ওই সময়ের মধ্যে ছবিটা সম্পূর্ণ করা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। রবিশঙ্করকে সত্যজিৎ মাত্র কয়েকটা রিল দেখাতে পেরেছিলেন, যাতে তিনি ছবির সুর সৃষ্টির একটা ভাবনাচিন্তা করতে পারেন। এগারো ঘণ্টার একটানা এক অধিবেশনে পুরো ছবিটার সংগীত রেকর্ড করা হয়েছিল।
ছবিটা যথাসময় শেষ করার জন্য ইউনিটের কেউই দশ দিন বাড়ি যাননি, প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ হয়েছিল, দাড়ি গোঁফ কামাবার পর্যন্ত সময় হয় নি।
আমেরিকায় পাঠাবার আগের মুহূর্ত ছাড়া সম্পূর্ণ সংশোধিত ছবিটা সত্যজিতের কিন্তু দেখার সময় হয়ে ওঠেনি। দুলাল দত্ত যখন আহার নিদ্রা ছেড়ে সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সত্যজিৎ আর অনিল চৌধুরি কলকাতার বড়ো বড়ো দোকানে এমন একটা ট্রাঙ্কের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যার মধ্যে ছবির রিলের গোলাকৃতি টিনের পাত্রগুলো একসঙ্গে ভরা যায়। তারপর আছে শুল্ক বিভাগের ছাড়পত্রের জন্য ছোটাছুটি। এই ছোটাছুটিতে সত্যজিৎ এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে একটু সময় পেলেই ঘুমিয়ে পড়তেন।
সময়কে হারিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত শেষ হল ছবির সব কাজ, সবাই ঘরে গিয়ে সটান আশ্রয় নিলেন বিছানায়। কি ঘুম! কি ঘুম! পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সড়ক উন্নয়নখাতের আর্থিক অনুদানে আমেরিকা পাড়ি দিল ‘পথের পাঁচালী’। ছবির সরকারি নাম হল, ‘সঙ অফ দি লিটল রোড’। সড়ক উন্নয়ন খাতে সরকারি সাহায্য পাওয়া গেছে যে!
১৯৫৫ সালে কলকাতায় ‘পথের পাঁচালী’ প্রথম মুক্তি পেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজক, তারা কিনে নিয়েছেন ছবিটা।
দক্ষিণ কলকাতার বসুশ্রী সিনেমা হলে ‘পথের পাঁচালী’র প্রথম মুক্তির দিনের কথা শুনলে লোকে আজ অবাক হবে। হলে প্রথম দিনের প্রথম শ্রেণিতে দর্শক হয়েছিল মুষ্টিমেয়। ছবির শেষে তারা প্রায় চেয়ার ভেঙে ফেলে আর কি! সত্যজিৎ রায় আর তাঁর ইউনিটের অন্যান্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন দর্শকদের মতামত শোনবার জন্য। তাঁদের তখন কেউ চেনেনা সেটাই সৌভাগ্য।
এই ‘পথের পাঁচালী’ পরে এগারোটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়ে পৃথিবীর অদ্বিতীয় মাস্টারপিস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
বসুশ্রী হলে ছ-সপ্তাহ চলেছিল ছবিটা। তৃতীয় সপ্তাহর পর থেকে চাকা গেল ঘুরে। লোকের মুখে মুখে রটে গেল অসাধারণ ছবি, টিকিটের জন্য লাইন পড়তে লাগল। সাফল্যের মুখেই ছবিটাকে তুলে নিতে হল কারণ আরেকটা ছবির জন্য হল বুক করা ছিল, সেই ছবির প্রযোজক দিন পেছোতে রাজি হলেন না। তবে পরে তিনি সত্যজিতের কাছে এসে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন, বলেছিলেন যে এত ভালো ছবি আগে জানলে তিনি নিজের ছবির রিলিজ পিছিয়ে দিতেন। তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে কথা বলতে বলতে ভাবাবেগে সজল হয়ে উঠেছিল তাঁর দু-চোখ।
আর একটা হাউসে একটানা সাত সপ্তাহ চলল ‘পথের পাঁচালী’, সারা বাংলায় প্রশংসিত হল, তারপর ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে টাকা ঢেলে ছিলেন তার বহুগুণ ফিরে পেলেন। ১৯৬১ সালে ‘পথের পাঁচালী’র আমেরিকার ডিস্ট্রিবিউটর এডোয়ার্ড হ্যারিসনের মুখ থেকেই জানা যায় ওই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ছবির স্বত্ব হিসেবে পঞ্চাশ হাজার ডলার তিনি শোধ করেছিলেন, তা ছাড়া আরও পাওনা ছিল।
বিদেশ থেকে ওই ছবির জন্য যদি টাকা আসে তবে তার একটা অংশ সত্যজিৎ পাবেন এমন একটা কথা ছিল, কিন্তু তিনি শুধু খ্যাতিটাই পেয়েছেন আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার পেয়েছেন লাভের গুড়। ছবিটা শেষ করার দরুন বাকি টাকা এবং ওটা কিনে নেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খরচ হয়েছিল প্রায় দুলক্ষ টাকা। ১৯৬১ সালে শুধুমাত্র আমেরিকা থেকেই ওই ছবি থেকে আয় হয়েছিল ৫০,০০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছ-লক্ষ টাকা। তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য শহর এবং ভারতবর্ষেও প্রচুর উপার্জন হয়েছে এ ছবি থেকে, কিন্তু ছবির স্রষ্টা আর তাঁর ইউনিটের দলকে শুধু সৃষ্টির আনন্দেই তৃপ্ত থাকতে হল।
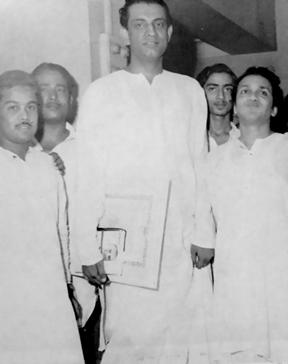
[‘পথের পাঁচালী’ থেকে সত্যজিৎ রায় আট দশ হাজার টাকার বেশি পাননি। আলোচনার সময় মৌখিক চুক্তি হয়েছিল বিদেশি স্বত্বের একটা লভ্যাংশ তিনি পাবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন প্রচার অধিকর্তা যে কারণেই হোক সেই শর্তটি চুক্তির মধ্যে লিখিতভাবে ঢোকাননি, ফলে একটা ন্যায্য টাকার অঙ্ক থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন সত্যজিৎ।]
এমনকি ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক দায়িত্বসম্পন্ন আমলা ফাইলে তাঁর মন্তব্যে লিখেছিলেন, ছবিটা নিতান্তই মামুলি ধরনের মন্থর ছবি, বিষয়বস্তু বাঙালি দুঃস্থ পরিবারের অভাব অনটনের দৈনন্দিন ঘটনা। এ ছবির পেছনে যে টাকা ঢালা হবে তা উঠে আসবে কিনা সন্দেহ।
সরকারি পক্ষ সম্পূর্ণ ছবিটা দেখে সুপারিশ করেছিলেন গ্রামদেশে যেসব উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হচ্ছে তার কিছুটা দেখিয়ে ছবি শেষ করতে। সত্যজিৎ যদি তাঁদের কথা মেনে নিতেন তবে ১৯৫৬ সালে কান ফিলম ফেস্টিভ্যালে ওটার ভাগ্যে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার জুটত না, একটা তথ্যচিত্র হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকত ‘পথের পাঁচালী’। রাষ্ট্রপতির সোনার মেডেল তারও প্রায় একবছর আগে। সে পুরস্কার নিতে কিন্তু সত্যজিৎকে আমন্ত্রণ করা হয়নি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের অধিকর্তা মি. মাথুর গ্রহণ করেছিলেন ওই পুরস্কার।
.
কিছু কিছু সমালোচক বলেছিলেন ‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে জাঁ রোনোয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি সত্যজিৎ। বরং বলা যায় যে দৃশ্যে সর্বজয়া রেগে আগুন হয়ে দুর্গার চুলের মুঠি ধরে এলোপাথারি মারছে, তার মধ্যে খানিকটা রবার্টো রসেলিনির ‘Open City’ আর ‘La voce Humana’ ছবির অভিনেত্রী আনা ম্যাগনানির অভিনয়ের কিছুটা মিল আছে। ১৯৫০ সালে ছবি দুটি সত্যজিৎ দেখেছিলেন। আনার অভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বংশী চন্দ্রগুপ্তকে বলেছিলেন, ‘অসাধারণ অভিনয়।’ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সর্বজয়ার ভূমিকায় দুর্গার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনছিলেন তখন তাঁর মধ্যেও আনার ক্রোধে ফেটে পড়ার চিত্রটা ফুটে উঠেছিল। নিজের সন্তানের সম্বন্ধে এক ক্ষুরধার জিহ্বা মহিলার বিষোদগারে মায়ের রোষ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ওই দৃশ্যে। সত্যজিৎ হয়তো ওই শটটা নেবার সময় আনার কথা মনে রেখেছিলেন।
‘পথের পাঁচালী’র দুটি দৃশ্যের কথা এখানে উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না [অবিশ্যি অনেক দৃশ্যই আছে যা উল্লেখ না করলে রচনা অসমাপ্ত থেকে যায়]। একটি দৃশ্য হল যেখানে কাশবনের ভেতর দিয়ে ভাই-বোন রেলগাড়ি দেখল, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল ওরা। আরেকটি হল প্রথম বর্ষার। পুকুরে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে রবিশঙ্করের সংগীতের মূর্চ্ছনা। বৃষ্টি দেখে আনন্দে আত্মহারা দুর্গা চরকির মতো ঘুরছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। কি সুন্দর সেই দৃশ্য! দুর্গার ভেতর দিয়ে সত্যজিৎ সৃষ্টি করেছেন আনন্দের এক অনাবিল অভিব্যক্তি। কিন্তু ওই বৃষ্টিতে ভিজেই নিউমেনিয়া রোগে মারা গেল দুর্গা, বর্ষা ওদের জীবনে আনন্দের সঙ্গে নিয়ে এল চরম বিষাদ।
দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া-র, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিল,
It is absurd to compare it (Pather Panchali) with any other Indian picture— for even the best of the pictures produced so far have been cluttered with eliche’s. Pather Pancili makes a complete break with the world of make believe… Satyajit Ray has an uncanny eye for the scene and for people.
নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা-য় এক বিদেশিনী লিখেছিলেন, ‘One of the most beautiful and sensitive pictures I have ever seen.’
এডোয়ার্ড হ্যারিসন, যিনি ‘পথের পাঁচালী’কে নিউ ইয়র্কে দেখাবার ভার নিয়েছিলেন, ১৯৬৭ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন সত্যজিতের একজন অন্ধ অনুরাগী। সত্যজিতের সব ছবি আমেরিকায় দেখাবার ভার তিনিই নিয়েছিলেন, এমনকি এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য সুদূর আমেরিকা থেকে তিনি ছুটে ছুটে আসতেন।
বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক রবার্টো রসেলিনি ‘পথের পাঁচালী’ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘রে একজন মহান শিল্পী, তিনি ডস্টয়ভস্কির মতো এমনভাবে তাঁর ছবিতে গল্প বলেন যা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে।’
রোমান পোলানস্কি ১৯৮০ সালে বাঙ্গালোরে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন, ‘ওয়ারশতে আমি যখন ফিলম ইনস্টিটিউটে ছিলাম, তখন ”পথের পাঁচালী’ আমাদের কাছে ছিল টেক্সট বইয়ের মতো।’
স্যার রিচার্ড অ্যাটনবরো বলেছেন, ‘সত্যজিতের যে জিনিসটা তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হল ডিটেলসের দিকে তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি। একমাত্র চ্যাপলিন ছাড়া আর কোনো পরিচালকের সত্যজিতের মতো সিনেমা পরিচালনার ব্যাপারে সব বিষয়ে প্রতিভা আছে কিনা সন্দেহ। দ্য ফ্লোর ইজ টোটালি কন্ট্রোলড বাই হিম।’
১৯৭৪ সালের সংস্করণে নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লিখেছে, বর্তমান যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র পরিচালকদের অন্যতম হলেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিতের অনুপ্রেরণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মিতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
দ্য টাইমস পত্রিকা লিখেছে:
The first work of the young Bengali Artist who has succeeded at one blow in escaping from stylistic and sentimental conventions of film making in his country. It is never easy to translate poetry, and words can only barely convey the beauty and richness of this masterly film.
আর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তো বলেছিলেন, আমরা সত্যজিৎ রায় এবং তাঁর ছবি ‘পথের পাঁচালী’ সম্বন্ধে গর্বিত [We are proud of Satyajit Roy and of his film ‘Pather Panchali’]। জহরলালের শিল্পবোধের তারিফ করতে হয়, তিনি বিধানচন্দ্রের মতো ছবিটাকে গ্রাম্য উন্নয়নমূলক এক তথ্যচিত্র করার উপদেশ দেননি। ছবিটাকে উপভোগ করেছিলেন, তাঁর কোমল হৃদয় আবেগরুদ্ধ হয়েছিল মানবিকতায়।
আমেরিকায় যেদিন ‘পথের পাঁচালী’ প্রথম মুক্তি লাভ করেছিল, সত্যজিৎ হলের লবিতে বসেছিলেন। বিদেশি দর্শকরা ওই ভারতীয় ছবি কিভাবে নেবেন তা নিয়ে মনে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। রাত প্রায় সাড়ে আট। হল থেকে সাদা আর কালো মানুষ বেরিয়ে আসছেন, তাঁদের চোখে জল। কেউ কেউ আবার সত্যজিতের দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন এর আগে কোনো ছবি এমনভাবে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করেনি।
ছবি সার্থক, সত্যজিৎ নিশ্চিন্ত হলেন।
.
‘পথের পাঁচালী’ সফল, সত্যজিৎ ছবির কাছে আত্মনিয়োগ করার জন্য অমন ভালো চাকরি ছেড়ে দিলেন। নিশ্চিত নিশ্চিন্ততা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অনিশ্চয়তার সমুদ্রে। এদিকে যখন অপুর জন্মের শুটিং চলছিল, বংশী চন্দ্রগুপ্ত খড় আর বাঁশ দিয়ে একটা আঁতুড়ঘর খাড়া করেছেন, ঠিক তখন বিজয়ার কোলে এল সন্দীপ। জন্মের সময় বাবা যেমন ছোট্টটি ছিল ঠিক তেমন। উপেন্দ্রকিশোরের প্রপৌত্র, রায় বংশের প্রতিভা নিয়েই যেন ছোট্ট ছেলেটির জন্ম। দায়িত্ব বেড়ে গেল তবু সত্যজিৎ তাঁর লক্ষ্যে অবিচল রইলেন।
‘পথের পাঁচালী’র সাফল্যের পর জর্জেস সাদুলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন, ‘ইউরোপ ও আমেরিকার চলচ্চিত্র ও বাংলাদেশের (পশ্চিমবঙ্গ) সাহিত্য আমার ছবির অনুপ্রেরণা। ফ্লেহার্টি ও ডনস্কয়ির মতো চলচ্চিত্র চিন্তাবিদদের কাছে আমি ঋণী। আমার মতে ছবির স্টাইল হওয়া উচিত তার বিষয়বস্তু অনুসারে। ”পথের পাঁচালী” যদি ব্যবসায়িক সফলতা না পেত, তবু এটা প্রমাণিত হয়েছিল দর্শক আমাকে বিশ্বাস করতে পারে। আমি ”অপরাজিত” করতে পারি।
‘আমি নিজেই ”সিনারিও” লিখেছি, উপন্যাস বা ছোটো গল্পের ভাব নিয়ে ছবি করেছি। আমি থিয়োরি পাগল ছিলাম, হাতে-কলমে কাজ করে অনেক কিছু শিখেছি। ছবির বিষয়বস্তু আমার নিজস্ব স্টাইল গড়ে দিয়েছে। নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি, এ দেশের মানুষের মন্থর জীবনযাত্রা, তাদের আচরণ, আমার স্টাইলের মূলে এ সবই আছে। হলিউডি কায়দায় আমি ক্যামেরা ঘোরাই না। স্টুডিয়োর বাইরে স্বাভাবিক আলো, সহজ সজীব পরিবেশ জীবনের সঙ্গে ছবিকে যুক্ত করে। স্টুডিয়োর ফ্লোরে এ জিনিস পাওয়া যায় না।’
সত্যজিতের সব ছবিতেই আবহ সংগীত একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। ‘পথের পাঁচালী’তে রবিশঙ্করের অনবদ্য সংগীতের মূর্চ্ছনা ভোলা যায় না। সংগীত সম্বন্ধে সত্যজিতের নিজেরও খুব ভালো জ্ঞান, এ নিয়ে অনেক পড়াশোনাও করেছেন। তিনি বলেন, ‘পাশ্চাত্য সংগীতের কাছে আমার অজস্র ঋণ। সিনেমার মতো সংগীতও শিল্পগতভাবে সময়ের পরিধিতে বাঁধা। ছবি সময়ের অনুশাসন মেনে একটু একটু করে নিজেকে উন্মোচিত করে।’
সংগীতে তাঁর অনুরাগ সম্বন্ধে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, ‘আমি যখন স্কুলে পড়ি আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে পেয়ে গেলাম বেটোফেনের একটা রেকর্ড। এই মহান শিল্পীর সংগীত শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বেটোফেন সম্পর্কে যেখানে যত লেখা পেলাম সব পড়ে ফেললাম। কলেজে ঢোকার আগে থেকে আমি পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের রেকর্ড সংগ্রহ করতে শুরু করি। আমার ছবিতে ”সিম্ফনি” বা ”সোনাটা”র যথেষ্ট প্রভাব আছে। ”চারুলতা”র জন্য আমি অবিরাম ভেবেছি মোৎসার্টের কথা।’
রবিশঙ্কর বলেছেন, ‘সত্যজিৎ তাঁকে ”পথের পাঁচালী”র ছবির রাশ প্রিন্ট দেখিয়েছিলেন। তাই দেখে তিনি ভাবাবেগে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে স্নায়ুতে তখনই যেন বিষণ্ণ সংগীতের অনুরণন অনুভব করেছিলেন। মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে তিনি গোটা ছবির নেপথ্য সংগীতের মানস লিপি তৈরি করে ফেলেছিলেন।’
নিউ ইয়র্ক শহরে ‘পথের পাঁচালী’ চলেছিল দীর্ঘ সাত মাস পরে। মার্কিন মুলুকে ফ্রান্সের রবার্ট ব্রেসো, কার্ল ড্রিয়ার কিংবা আরমানো ওলমিও জীবনে এমন সুযোগ পাননি।
শিল্পের মাধ্যমে একটা জাতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পের মাধ্যমে জানা যায় কাল ও সমকালের মহত্ত্ব। ‘পথের পাঁচালী’ তাই বোধ হয় একটা মহৎ সৃষ্টি। সবচেয়ে আশ্চর্য, তার আগে সত্যজিৎ আর কোনো ছবি করেন নি। ছবিটি শুধু একটা পরিবারের কাহিনি নয়, গ্রামীণ দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, হতাশা, আশা, আনন্দ সবকিছু একাত্ম হয়ে আছে এই ছবির সঙ্গে।
রবার্ট স্টিল রেনোয়া ‘রিভার’ ছবির ব্যাপারে ১৯৪৯ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ১৯৫৬ সালে রবিবারের এক সকালে বোম্বেতে ‘পথের পাঁচালী’ দেখে তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল এমন একটা ছবি দেখলেন যাকে নির্দ্বিধায় মহৎ ছবি বলা যায়। এই প্রথম একটা ভারতীয় ছবি তিনি দেখলেন যা বিরক্তিহীন, বিভ্রান্তিহীন ও ক্লান্তিহীন।
আমেরিকায় শ্রীমতী ফ্লেহার্টিকে তিনি চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন যেন ফ্লেহার্টি ফিলম সেমিনারে ‘পথের পাঁচালী’ দেখাবার ব্যবস্থা করা হয় এবং সম্ভব হলে ছবির পরিচালককেও যেন ওই উৎসবে আমন্ত্রণ করা হয়।
পরের সেমিনারে মার্কিন সরকারের ভ্রমণ-সংস্থার সহযোগিতায় সত্যজিৎ ‘পথের পাঁচালী’ নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দিলেন। এডোয়ার্ড হ্যারিসন মার্কিন মুলুকে ছবিটা দেখাবার ভার নিলেন। হ্যারিসনের এত ভালো লেগেছিল যে অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও ‘পথের পাঁচালী’ নিয়ে তিনি ব্যস্ত থেকেছেন, কষ্ট স্বীকার করেছেন। তিনি উদ্যোগ না নিলে ছবিটা বোধ হয় সারা আমেরিকায় প্রদর্শিত হতই না।
যাহোক, ‘পথের পাঁচালী’ ফিফথ অ্যাভেন্যুর সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছিল একটানা সাত মাস চলে। ওখানকার নিন্দুক সমালোচকরা ছবিটা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে ছাড়েননি। একজন লিখেছিলেন, ‘এটা যে সত্যজিতের প্রথম ছবি তা দেখেই বোঝা যায়। এত ঢিলেঢালা গাঁথুনি যে হলিউডের রাফ কাটও এর চেয়ে ভালো।’
এই নিন্দায় সত্যজিতের কোনো ক্ষতি হয়নি বরং তিনি বিখ্যাত হয়েছেন, পরিচিত হয়েছেন। তাঁকে সমর্থন করে অন্যান্য সমালোচকরা কলম ধরেছেন। নিউ ইয়র্কে ‘পথের পাঁচালী’র বিপুল সাফল্যে আমেরিকার কিছু কিছু চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বোস্টনের ভায়োলা বারলিন তাঁর হলের ইংলিশ কমেডির চেন বাদ দিয়ে ‘পথের পাঁচালী’কে সুযোগ দিয়েছিলেন।
পরিচালক জর্জ স্টোনি সত্যজিতের একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। শুধুমাত্র সত্যজিতের ছবি সম্বল করে তিনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ‘ফিলম এসথেটিক্স’-এর ক্লাশ নিয়েছেন।
স্ট্যানলি কাউফম্যান একটা নামি পত্রিকার সাংবাদিক। ‘পথের পাঁচালী’র সমালোচনা তিনি করেছিলেন মাত্র চোদ্দো লাইনের মধ্যে। তিনি লিখেছিলেন, ‘ ”পথের পাঁচালী”কে একটু বেশি প্রশংসা করা হচ্ছে। গল্পটা সহজ— প্রায় বস্তাপচা।’
তিনিই পরে ‘অপরাজিত’র সমালোচনা করে বলেছিলেন, ‘ ”অপরাজিত” দেখার পর মনে হচ্ছে ”পথের পাঁচালী” নিঃসন্দেহে ভালো ছবি। রায় ন্যাশনাল ফিলম এপিকের কায়দায় যে ছবি করে যাচ্ছেন তা গোর্কি ট্রিলজির সঙ্গে তুলনীয়। ফ্লেহার্টির ”নানুক” ও ”মোআনা”র সঙ্গেও তুলনা চলতে পারে। রায়ের শিল্প সততা মহান পর্যায়ের। স্বীকার করতে বাধা নেই, এই ছবির মাধ্যমে রায় সমকালীন পরিচালকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।’
চলচ্চিত্র পরিচালক পল গ্রিম বলেন, ‘ ”পথের পাঁচালী”র আগে কোনো ভারতীয় ছবি পশ্চিমে এত অভিনন্দিত হয় নি। ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র শিল্প হলিউড থেকে অনেক বছর পিছিয়ে আছে, তাই সত্যজিতের আন্তর্জাতিক সম্মানের জন্য ভারতবর্ষ প্রস্তুত ছিল না। সত্যজিৎ তাঁর গভীর মানবিকতা ও সততা নিয়ে পশ্চিমের একঘেঁয়ে আর শস্তা ভাবপ্রবণ ছবিকে ম্লান করে দিয়েছেন। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, শ্রী রায় ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নতুন যুগের স্রষ্টা। ভারতীয় মামুলি ছবিতে শিল্পকর্ম বড়ো কথা নয়, সেখানে বিচার্য হল জনপ্রিয় তারকা। সত্যজিৎ সেই ট্র্যাডিশন ভেঙে দিয়েছেন, শুধু ভারতবর্ষের নয়, চলচ্চিত্রের অনেক বাঘা বাঘা সমালোচকই মনে করেন সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে নতুন যুগের স্রষ্টা।’
.
‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি পেয়েছিল অনেক বাধাবিঘ্ন ও আর্থিক সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে। ওটা থেকে সত্যজিৎ খ্যাতি ছাড়া আর কিছু পাননি। তবে ওই খ্যাতি তাঁকে ১৯৫৬ সালে অপুর দ্বিতীয় ছবি ‘অপরাজিত’-য় হাত দিতে ভরসা যুগিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে তিনি করলেন ‘অপুর সংসার’— অপুর ট্রিলজি।
সাহিত্যে ট্রিলজি নতুন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু চলচ্চিত্রে মাত্র তিনটি ট্রিলজি সৃষ্টি হয়েছে— করেছেন পৃথিবীর তিনজন বিখ্যাত পরিচালক। তার মধ্যে আবার একটি অসমাপ্ত রেখে পরিচালক মারা গেছেন।
রাশিয়ায় দুটি ট্রিলজি তৈরি হয়েছে। ডনস্কয়ের ম্যাকসিম গোর্কির জীবন কাহিনিকে ভিত্তি করে তোলা একটি আর অন্যটি আইজেনস্টাইনের ‘আইভান দ্য টেরিবল’-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে। তৃতীয় অধ্যায় অসমাপ্ত রেখে পরিচালক মারা গিয়েছিলেন। আর তৃতীয় ট্রিলজি হল সত্যজিতের, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ কাহিনি নিয়ে। অপু ট্রিলজির প্রথম অধ্যায় হল সত্যজিতের প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’।
অপুর ট্রিলজির সঙ্গে একমাত্র ডনস্কয়ের গোর্কি ট্রিলজির তুলনা হতে পারে। কিন্তু গোর্কির শেষ খণ্ড প্রথম দুই খণ্ডের মতো উচ্চমানের নয়, সেদিক দিয়ে অপুর ট্রিলজি শ্রেষ্ঠ— এ কথা বলেছেন প্যাট্রিসিয়া বেকার। পুরোটাই যেন একটা লিরিকের মতো, মিষ্ট একটি কবিতা।

ট্রিলজির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আত্মজীবনীমূলক ঘটনাস্রোতে জীবনের এক গভীরতায় পৌঁছানো, সত্যজিৎ রায়ের ট্রিলজির তিনটি ছবিই ভারতীয় সামাজিক চলচ্চিত্রে এক অসামান্য অবদান— এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।
ড্যানিয়েল ট্যাবলট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সর্বজনস্বীকৃত চিত্রবোদ্ধা। তিনি লিখেছিলেন, ‘ ”অপুর সংসার”-কে মাস্টারপিস বললে কোনোরকম অত্যুক্তি হয় না। ”বাইসাইকেল থিফ”-এর পর অন্য কোনো ছবি আমাকে এত নাড়া দেয়নি। নতুন যুগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ মানবতাবাদী, বাস্তববাদী ও রোমান্টিক। সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ ঘটনা দিয়ে যেভাবে তিনি বোঝাতে পারেন তা খুব কম পরিচালকই পারেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্রীয় ভঙ্গীতে তাঁর ধারণা এগিয়ে দেন না, এগিয়ে দেন অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে, যার মধ্যে দর্শক গভীর সত্য আবিষ্কার করেন।’
রেনোয়া ও ডি সিকার মতো সত্যজিৎ জীবনকে দেখেন, সে জীবন খারাপই হোক আর ভালোই হোক, এ মন্তব্য রবার্ট স্টিলের। তিনি আরও বলেছেন, ‘আমরা সত্যজিৎকে রেনোয়া, ডি সিকা, ড্রিয়ার, ডভঝেনকোর সঙ্গে একাসনে বসিয়েছি। হলিউডের চোখ ধাঁধানো আলো সত্যজিতের কাছে কানা হয়ে যাবে একদিন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।’
.
‘অপরাজিত’ অপুর বালক বয়স থেকে কৈশোরে উপনীত হবার ছবি। গঙ্গার দৃশ্য দিয়ে ছবির শুরু। এই ছবিটা করার সময় সত্যজিৎকে বিভূতিভূষণের আসল কাহিনির কিছু ঘটনা ও চরিত্রের অদল বদল করতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, সিনেমার জন্য উপন্যাস বা কাহিনি লেখা হয় না। তা যদি হত তবে বই না হয়ে সেগুলো চিত্রনাট্য হয়ে দাঁড়াত, আর তা যদি ভালো চিত্রনাট্য হত তবে সাহিত্য হিসাবে হয়তো তার মূল্যবোধ কমে যেত। ওই ছবিতে বিধবা মা এবং কিশোর ছেলের গভীর সম্পর্কের ওপরেই তিনি জোর দিয়েছিলেন বেশি, যার ফলে আমাদের মনের অন্তঃস্থলে তা গিয়ে স্পর্শ করে। মা ও ছেলের ভালোবাসার এক শাশ্বত কাহিনি ‘অপরাজিত’।
অপরাজিতর শুরুতে বালক অপুর বয়স দশ, সর্বজয়ার বুকের সবটাই জুড়ে রয়েছে সে। হরিহর গঙ্গার ঘাটে ধর্ম কাহিনি পাঠ করে শোনায়, ভদ্র শ্রোতাদের দানে তার দিন চলে যায়।
‘পথের পাঁচালী’ ছবির সবটাই তোলা হয়েছিল স্টুডিয়োর বাইরে, স্বাভাবিক আলোয়, কিন্তু ‘অপরাজিত’-তে সত্যজিৎ কাশীর সেটগুলো স্টুডিয়োতে বানিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করলেন। দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বনাথের মন্দির, এসব ছাড়া বাকি প্রায় সব দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছিল স্টুডিয়োর ভেতর। যেমন হরিহর একটা গলি দিয়ে বাড়ি ফিরছে, এটা লোকেশন শট অর্থাৎ স্বাভাবিক বহির্দৃশ্য, আর যখন সে বাড়ি ঢুকছে সেটা স্টুডিয়োর ভেতর ক্যামেরার কারসাজিতে তোলা, কিন্তু দুটো শটের মধ্যে তফাৎ বোঝার উপায় নেই।
অপুর চোখ দিয়ে সত্যজিৎ আমাদের বারাণসী শহর দেখিয়েছেন। গঙ্গার ঘাটে পালোয়ান মুগুর ভাঁজছে, সরু গলিতে ছোটো ছেলেদের লুকোচুরি খেলা, হরিহর একদল বিধবা মহিলার সামনে বসে নিবিষ্ট মনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছে আর সেটা দূর থেকে দেখছে অপু, এমন সব ছোটো ছোটো শটের ভেতর দিয়ে সত্যজিৎ আমাদের বারাণসী দর্শন করিয়েছেন।

হরিহরের মৃত্যুর পর ওপরতলার প্রতিবেশী যে লোভী হয়ে উঠবে তার ইঙ্গিত কিন্তু সত্যজিৎ প্রথমেই দিয়েছেন, যখন সেই প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রথম দৃশ্যে সর্বজয়া ত্রস্তে ঘোমটা টেনে আড়ালে চলে যায়। হরিহরের মৃত্যুর পর নিঃশব্দে লোকটি যখন পেছন থেকে এগিয়ে আসে, সর্বজয়া টের পেয়ে প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যায়, তারপরই নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য হাতে তুলে নেয় তরকারি কাটার বঁটি— মেয়েদের আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র।
হরিহরের মৃত্যুদৃশ্যের অন্তিম মুহূর্তে বাবার মুখে পবিত্র গঙ্গার জল দেবার জন্য বালক অপুর গঙ্গাজল নিয়ে আসা, হরিহরের শেষনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক পাখির আকাশে ওড়া, এ সবই কুশলী শিল্পীর মতো শটে ধরেছেন সত্যজিৎ।
হরিহরের মৃত্যুর পর দেশে ফিরে আসার পর অপুর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। বাবার জীবিকায় ওর মন নেই, ও চায় লেখাপড়া করতে। পিনাকি সেনগুপ্তর জায়গা নিল স্মরণ ঘোষাল, এখন সে আর বালক নয়, কিশোর। ইস্কুলে হেডমাস্টার মশায়ের সুনজরে পড়ল অপু, কিন্তু এই লেখাপড়াই আস্তে আস্তে ওকে সরিয়ে নিতে লাগল ওর মায়ের কাছ থেকে। তারপর বৃত্তি পেয়ে কলকাতায় কলেজে পড়তে গেল অপু, দূরত্বটা আরও বেড়ে গেল। সর্বজয়ার একাকিত্ব বোধটা করুণা ব্যানার্জি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। ওই ছবি জুড়ে আছেন তিনি।
ছুটিতে অপু এসেছে, ওর চলে যাবার আগের রাত্রে সর্বজয়ার সঙ্গে ওর সেই দৃশ্য বড়োই হৃদয়স্পর্শী। সর্বজয়া বলছে, ‘তুই যখন চাকরি পাবি আমি তোর কাছে গিয়ে থাকব। তা কি হবে? আমার কেমন যেন মনে হয় আমার যদি খুব অসুখ করে? জানিস সন্ধের দিকে আমার শরীরটা ভালো থাকে না, খিদে হয় না।’
সত্যি সর্বজয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে অপু পড়া ছেড়ে মার দেখাশোনা করতে আসবে কিনা এ প্রশ্নের জবাব না পেয়ে সর্বজয়া বলছেন, ‘আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন?’
কিন্তু অপু ঘুমিয়ে পড়েছে, মার ব্যাকুল কথা তার কানে যায়নি। মনে গাঁথা হয়ে থাকার মতো একটি দৃশ্য।
সর্বজয়ার মৃত্যুশয্যায় শেষ মুহূর্তে অপুকে এনে মা ও ছেলের এক করুণ দৃশ্যের নাটকীয়তার ধার দিয়েও সত্যজিৎ যাননি। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে অপু ট্রেন থেকে নেমে যখন হেঁটে আসছে তখন সে খবর শুনল, সব শেষ। এখানেই সত্যজিতের কৃতিত্ব। তিনি বাঁধাধরা রাস্তায় চলেন না, নতুন ভাবনা চিন্তার ইঙ্গিত থাকে তাঁর ছবিতে।
১৯৫৭ সালে ভেনিসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বাঘা বাঘা পরিচালকরা যোগ দিয়েছিলেন প্রতিযোগিতায়। জাপানের তাসাকা [‘উকি ওয়ারেসু’ খ্যাত] এবং কুরোসাওয়া [‘রসোমন’ খ্যাত]; জিনেম্যান [Zinnemann], ইতালির ভিসকন্তি এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আরও অনেকে এসেছিলেন। প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ‘গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক’ পেলেন সত্যজিৎ রায়, তাঁর ‘অপরাজিত’ ছবির জন্যে।
১৯৫৯ সালে লন্ডন ফিলম ফেস্টিভ্যাল এক স্মরণীয় ঘটনা। অনেক ভালো ভালো ছবি ওই উৎসবে এসেছিল। কাম্যুর ‘অরফিউ নেগ্রো’, বার্গম্যানের ‘ব্রিংক অফ লাইফ’, ডেনিস স্যান্ডার্সের ‘ক্লাইঙ অ্যান্ড পানিশমেন্ট,’ ডনস্কয়ের ‘অ্যাট এ হাই প্রাইস’ ইত্যাদি, কিন্তু সব ছবিকে ম্লান করে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল ‘অপুর সংসার’। সত্যজিতের জয় জয়কার।

অনেক সমালোচক বলেন:
‘পথের পাঁচালী’ আর ‘অপুর সংসার’-এর যে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি সে তুলনায় ‘অপরাজিত’ নিষ্প্রভ। তবে অপু-ত্রয়ী একত্রে যে একটি মহান সৃষ্টি সে বিষয়ে সমালোচকদের মতভেদ নেই। এই ত্রয়ী চিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের মহান উপন্যাসগুলির। ডি থিলহেলম মাইস্টুর ‘লস্ট ইলিউশনস’ গ্রন্থে অনেকটা যেন অপুর জীবন খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেও নায়কের ভবঘুরে জীবন বিচিত্র ভাঙাগড়ার মধ্যে গড়ে উঠেছে। রঁমা রঁল্যা এবং গোর্কির মধ্যেও জীবনের এমন ছবি দেখা যায়। তবে সত্যজিতের ছবির সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্য শুধু বাহ্যিক— এ কথা বলেছেন মিকেল সেমেঁৎ।

‘অপুর সংসার’ ছবিতে নব বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর অনুরাগের চিত্র সত্যজিৎ দীর্ঘ সংলাপ কিংবা পল্লবিত কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেননি। অপর্ণার রূপে অপুর মুগ্ধ দৃষ্টি, নববধূর অবগুণ্ঠিত মস্তকের ঈষৎ সঞ্চালন, সলজ্জ মিষ্টি হাসি, চটুল কটাক্ষ, এ সবের ভেতর দিয়ে প্রেম যে কিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দক্ষ শিল্পীর মতো তা ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ। এ যেন কাব্যের সুষমায় স্নিগ্ধ— যেন শিল্পী তুলির কয়েকটা আঁচড়ে জীবন্ত করে তুলেছেন কয়েকটা মুহূর্ত। ‘গরিব স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে পারবে তো?’ নতুন বইয়ের খুব ছোট্ট, ‘হ্যাঁ,’ কিন্তু তার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক গভীর প্রেমের ব্যাপ্তি— সত্যজিতের প্রতিটি দৃশ্য গ্রহণের মধ্যে ফুটে ওঠে নতুন নতুন শিল্পভাবনা। স্বামীর ঘর করতে এসে অপর্ণা হতশ্রী ভাঙা-বাড়ির চার দেওয়ালে চোখ বুলোচ্ছে— এক শব্দহীন পরিবেশের ভেতর দিয়ে সমস্ত ঘটনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তারপরই অপর্ণা জানালা দিয়ে ধোঁয়াচ্ছন্ন রেলইয়ার্ডের দিকে চোখ ফেরানো— এইরকম টুকরো টুকরো অনেক দৃশ্যের ভেতর দিয়ে সত্যজিৎ ধরে রেখেছেন এক চিন্তাশীল মনের অতলস্পর্শী গভীরতা।
রবার্ট হকিন্স বলেছেন, ‘ ”অপুর সংসার” প্রমাণ করেছে সত্যজিৎ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অন্যতম। এ ছবি বিশ্বমানবতা ও সৌন্দর্যের ছবি।’
শর্মিলা ঠাকুরের বয়স তখন মাত্র চোদ্দো। অপর্ণার ভূমিকায় কি সংযত, কি অনবদ্য অভিনয়ই না তিনি করেছিলেন। ওটাই তাঁর প্রথম ছবি এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সত্যজিতের তিনি আবিষ্কার।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ‘পথের পাঁচালী’-র অপু বা সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করেছিলেন সত্যজিৎ জায়া বিজয়া রায়, আর ‘অপরাজিত’-র বালক অপুকে সত্যজিৎ আবিষ্কার করেছিলেন বালীগঞ্জ স্টেশনে। পিনাকী সেনগুপ্ত তখন সুরেন ঠাকুর রোডে থাকে আর পড়ে জগবন্ধু স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে ডায়মন্ডহারবারের লাইনে ধামুরায় পিকনিক সেরে ফিরছিল। সত্যজিৎ ফিরছিলেন মল্লিকপুর [এখন যেটা সুভাষগ্রাম] স্টেশন থেকে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ইউনিটের লোকজন। লোকেশনের খোঁজে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। এক ঝাঁক ছেলের মধ্যে বালীগঞ্জ স্টেশনে পিনাকীকে দেখে সত্যজিতের চোখে লেগে গেল ‘অপরাজিত’-র বালক অপুর ভূমিকার জন্যে। চোখ তো নয়, ক্যামেরা আই।
পিনাকী সেনগুপ্ত ‘জলসাঘর’ ছবিতেও ছবি বিশ্বাসের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
‘অপরাজিত’-র আর এক অপু, অর্থাৎ আরেকটু বেশি বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্মরণকুমার ঘোষাল। স্মরণের মা অমিতা ঘোষালের সঙ্গে সত্যজিতের আগেই পরিচয় ছিল, দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল। বড়ো অপুর ভূমিকায় স্মরণকে নেবার কথা তখনই মনে হয়েছিল তাঁর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বয়স কিছু কম থাকলে তাঁকেই ওই চরিত্রে আমরা দেখতে পেতাম।
‘পথের পাঁচালী’র দুর্গার ভূমিকায় ছিল উমা দাশগুপ্তা। ওই ছবির সহকারী পরিচালক ছিলেন আশীষ বর্মণ। তিনি স্কুলে স্কুলে মেয়ে খুঁজছিলেন ওই ভূমিকার জন্য। কমলা গার্লস স্কুলের সামনে উমাকে দেখে তাঁর চোখে লেগে গেল। সিনেমায় নামবে বলে খুব সেজে এসেছিল। বিজয়া দেবীই চুল টেনে বেঁধে, গাছ কোমর করে শাড়ি পরিয়ে দুর্গার মতন করে সাজিয়েছিলেন। শর্মিলা ঠাকুরকেও বিজয়া দেবী সাজিয়ে ছিলেন। কোঁকড়া ঝাকড়া অবাধ্য চুল টেনে বেঁধে চেহারাই বদলে দিয়েছিল।
‘পথের পাঁচালী’-র সাত বছরের সেই অপুর বয়স আজ চুয়াল্লিশ, কুদঘাট পুলিশ ওয়ারলেসের হেড কোয়ার্টার্সের পাশে নিজেদের বাড়িতে ১৯৫৯ থেকে আছেন সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ‘পথের পাঁচালী’-র অপু। বেঁটেখাটো চেহারা অপুর সঙ্গে এখন আর কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সত্যজিৎ রায় ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ছবি করার সময় সুবীর তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সত্যজিৎ চিনতে পারেননি। দমদমে কেন্দ্রীয় সরকারের এক অধিগ্রহণ সংস্থায় টেকনিক্যাল অপারেটরের কাজ করেন সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়।
‘অপরাজিত’-র বালক অপু পিনাকী সেনগুপ্তর দাদু বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন আসামের সিভিল সার্জন, বাবা বিনয় সেনগুপ্ত ইঞ্জিনীয়র। অকৃতদার। [১১ জুন ১৯৮৮ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে বালিগঞ্জে সুরেন ঠাকুর রোডের বাড়িতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অকালে পরলোকগমন করেছেন পিনাকী সেনগুপ্ত।]
‘অপরাজিত’-র কিশোর অপু স্মরণকুমার ঘোষালের বয়স এখন আটচল্লিশ। তিনিও আর ছিপছিপে কিশোরটি নেই। চুল পাতলা হয়ে পাক ধরতে শুরু করেছে, শরীরও ঈষৎ মেদবহুল। পার্ক সার্কাসের মেহের আলি রোডে কম্প্যুটারচালিত রিপ্রোগ্রাফির ব্যবসা। তাছাড়া ওড়িশার সিমলিপালে চায়না ক্লের খনি আছে, ওখানেই বেশিরভাগ সময় কাটান। অন্যতম হবি হল শিকার। মেহের আলি রোডের বাড়ির ভেতরের একটা ঘরের দেয়ালে সারি সারি বন্দুক টাঙানো। সিকিমে বিয়ে করেছেন, দুই মেয়ে। শিকার ছাড়াও নিজস্ব লাইব্রেরি করা, গানের সংগ্রহ, প্রাচীন চীনা ছবি, তিব্বতী তংখা ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনার বাতিক আছে।
আর ‘অপুর সংসার’-এর অপুর পরিচয় আলাদা করে দেবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্বপ্রতিভায় উদ্ভাসিত।
.
১৯৫৭ সালে ‘পরশপাথর’, ১৯৫৮ সালে ‘জলসাঘর’, ১৯৬০ সালে ‘দেবী’, ১৯৬১ সালে ‘তিনকন্যা’, ১৯৬২ সালে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ও ‘অভিযান’, ১৯৬৩-তে ‘মহানগর’, ১৯৬৪-তে ‘চারুলতা’ তারপর আরও— সত্যজিতের জয়যাত্রা অব্যাহত।
রবার্ট স্টিল বলেন সত্যজিৎ শুরুই করেছেন মাস্টারপিস দিয়ে। অপু না পাওয়া গেলে ‘দেবী’-কে সেই সম্মান দেওয়া হত, সেটাও না পেলে ‘দুই কন্যা’ ‘পোস্টমাস্টার’কে মাস্টারপিস বলা যেত।
কিন্তু ‘মহানগর’? ‘চারুলতা’? কোনটা বাদ দেওয়া যায়? ‘চারুলতা’র গভীরতা মর্ম স্পর্শ করে। চরিত্রচিত্রণ কি অসামান্য! সমৃদ্ধ! প্রতিটি দৃশ্যে সত্যজিৎ যেন এক আশ্চর্য কোমলতা উপহার দিয়েছেন। সূর্যের আলোর মতো পরিচ্ছন্ন এক ছবি।
‘মহানগর’ অপূর্ব মননশীল ছবি, যার মধ্যে একটা সর্বজনীন আবেদন আছে। মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতা, সুখ-দুঃখ-বিষাদ সবকিছু যেন নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে এই ছবির মধ্যে। ‘মহানগর’ আর ‘চারুলতা’ পর পর দু-বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান এনে দিয়েছে সত্যজিৎকে। একজন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক বলেছিলেন, ‘মহানগরের মতো ছবি তোলার জন্য আমি সারাজীবন অপেক্ষা করতে রাজি।’ অবশ্যই তিনি এ দেশের মানুষ নন।
রবার্ট স্টিল আরও বলেছেন, ‘আঁদ্রে জিদের সিম্ফনি ”প্যাসটোরালের” সঙ্গে ”দেবী”, চেকভের ”চেরি অর্কাড”-এর সঙ্গে ”জলসাঘর” ”দুই কন্যা” ও ”মহানগর”-এর সঙ্গে ইতালিয়ান নিওরিয়ালিস্ট ছবি নিঃসন্দেহে একাসনে ফেলা যায়।’
ফিলিপ স্ট্রিক বলেন, ‘ভিস্যুয়াল টেকনিকের দিক থেকে ”দেবী” সত্যজিতের সবচেয়ে প্রাঞ্জল, সরল ছবি। ছবিটার মধ্যে যে দীর্ঘ নীরবতা, আবেগের গভীরতা, চরিত্রের যে আশ্চর্য রূপায়ন আছে, তাতে ওই ছবিকে একক শিল্প বললে অত্যুক্তি করা হবে না।’
এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁর পূর্ণযৌবনা বধূমাতাকে দেবী সাজালেন। দেবীর তরুণ স্বামীর এটা পছন্দ নয়; সে স্ত্রীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বধূটিও তাই চায় কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করতে না পারার ফলে তার জীবনে নেমে আসে দারুণ ট্র্যাজেডি। গভীর নাটকীয় সংঘাতের ভেতর দিয়ে সত্যজিৎ প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্ধ বিশ্বাসের করুণ পরিণতির কাহিনি।
‘দেবী’ সত্যজিতের ষষ্ঠ ছবি। ভারতের সেন্সর বিভাগ ছবিটাকে মুক্তি দিতে গড়িমসি করেছিল, তাদের মনে হয়েছিল হিন্দুধর্মকে বিকৃত করা হয়েছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু হস্তক্ষেপ না করলে ছবিটা বোধ হয় বিদেশে মুক্তি পেতনা।
‘দেবী’ ছবিতে তরুণ দম্পতির ভালোবাসা, পরস্পরের সঙ্গসুখ কামনার দৃশ্য সত্যজিৎ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দর্শকের কথা ভেবে মশারির আড়ালে শুধু তাদের একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া আর এগুতে সাহস করেন নি। তা যদি করতেন তবে সামনের সারির দর্শকরা বেড়ালের ডাক ডেকে উঠত এটাই তিনি চিন্তা করেছিলেন। সত্যজিতের হিসেবে ভুল হয়নি, এমনিতেই ‘দেবী’ হিন্দুধর্মের বিশ্বাসে আঘাত বলে রব উঠেছিল, তার ওপর ক্লোজ আপে যদি ওই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি সত্যজিৎ ধরতেন তবে আর রক্ষে ছিল না, দেবীকে নিয়ে ব্যাভিচার দেখিয়েছেন এই অপরাধে কেউ তাঁকে আদালতে টেনে নিয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। অথচ হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে কত যে ছবি হচ্ছে, উদ্ভট সব ছবি, শ্রদ্ধার বদলে বিরক্তিকর, ভক্তি উদ্রেকের বদলে অবাস্তবতা আর হাস্যকর ব্যাপার মনকে পীড়া দেয়, কই তা নিয়ে তো হইচই হয় না।
‘দেবী’র নায়িকা তো একজন রক্তমাংসের মানুষ, এক তরুণী বধূকে নিয়ে কাহিনি। আমাদের অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারে এ এক কুঠারাঘাত। শ্বশুরমশাই স্বপ্নে দেখলেন তাঁর পুত্রবধূ স্বয়ং মা কালীর অবতার, তিনি সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করলেন। এর ভেতর দিয়ে সত্যজিৎ রূঢ় বাস্তবকেই তো সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, কোনো দেব-দেবী নিয়ে তিনি তো ব্যঙ্গ করেননি। তাছাড়া প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে ওই ছবি, দোষ যদি দিতে হয় তবে তাঁকেই সবার আগে দেয়া উচিত, কেন তিনি অমন গল্প লিখলেন! ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ওই ছবি মুক্তির ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। জহরলালের উদার দৃষ্টিভঙ্গি সত্যজিৎকে একাধিকবার অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা করেছে এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। তাঁর হস্তক্ষেপেই ‘পথের পাঁচালী’ বিদেশে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছিল।

সাধারণ বিষয় নিয়ে অসাধারণ ছবি করাই হল সত্যজিতের বৈশিষ্ট্য। কোনো বিকৃত মানসিকতা বা বিচ্ছিন্নতা না এনেও ছবি কত সুন্দর আর গভীর করা যায় তার জ্বলন্ত নিদর্শন হল ‘নায়ক’। যুগের যন্ত্রণা আছে এ ছবিতে কিন্তু কোনো চটুল রস নেই। ‘নায়ক’ ছবিতে আপাতদৃষ্টিতে সফল এক মানুষের জীবনযন্ত্রণার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ অসাধারণ দক্ষতায়।

ট্রেনে সহযাত্রী ও সহযাত্রিণীদের চরিত্রের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে সমাজের বিভিন্ন দিক, যেখানে এক শিল্পপতি স্ত্রীকে নিয়ে বাজি ধরতেও লজ্জা পায় না। জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতার খ্যাতি ও সচ্ছলতার অন্তরালে যে অসহনীয় একাকিত্ব, সূক্ষ্ম শিল্প নিষ্ঠায় আর নিটোল ঘটনাবিন্যাসে তা জীবন্ত করে তুলেছেন পরিচালক। নায়ক নিঃসঙ্গ, অনেকের মধ্যেও সে একা, প্রাচুর্যের মধ্যেও সে দীনহীন।
নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমারের অভিনয় এতই বাস্তব ও স্বাভাবিক যে মনেই হয় না অভিনয় দেখছি। এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।
‘নায়ক’ ইনডোর শুটিংয়ের সময় একদিন স্টুডিয়োতে সত্যজিৎ, তাঁর ইউনিট এবং অন্যান্য শিল্পীরা অপেক্ষা করছেন। কাজ শুরু করা যাচ্ছে না কারণ নায়কের দেখা নেই। সত্যজিৎ আবার খুব সময়নিষ্ঠ, সবকিছুতেই ডিসিপ্লিন মেনে চলেন। উত্তমের ব্যবহারে মনে মনে তিনি বিরক্ত হলেন, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করলেন না।
সেদিনের শুটিং ছিল নায়ক টাকার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, এই ব্যাপারটা।
উত্তমকুমার কোনোদিন দেরি করেন নি, সেদিনই ব্যতিক্রম। বারোটার সময় ওঁর ফোন এল, ‘আটকা পড়ে গেছেন, একটু দেরি হবে।’ যাক, আসছেন তবে। সত্যজিৎ সবাইকে দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে বললেন।
কিন্তু তবু উত্তমের দেখা নেই। সে এক অসহনীয় অবস্থা। সত্যজিৎ স্টুডিয়োর বাইরে একটা লোহার চেয়ারে বসে শিস দিচ্ছেন, ঠিক শিস নয়, রবীন্দ্রনাথের ‘ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু’ গানটা শিস দিয়ে গাইছেন। সত্যজিৎ চমৎকার শিস দিতে পারেন, এমনকি পাখির ডাক পর্যন্ত অবিকল তুলতে পারেন শিসে।
এমন সময় নায়ক এলেন। এসেই সত্যজিতের কাছে গিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বললেন, ‘মানিকদা—’
সত্যজিৎ তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, ‘এই যে গুরু—’
উত্তম তখন ওই নামে জনপ্রিয়।
‘লিখে দিন,’ উত্তম একটুও না দমে বললেন।
‘কি লিখে দেব?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন সত্যজিৎ।
‘লিখে দিন সত্যজিৎ রায় উত্তমকুমারকে গুরু বলেছে, তারপর নিচে নাম সই করে দিন,’ বেশ সপ্রতিভভাবে বললেন উত্তম।
হা হা হা করে হেসে উঠলেন সত্যজিৎ, সব বিরক্তি হালকা মেঘের মতো উড়ে গেল।
.
সত্যজিতের জন্ম এমন এক পরিবারে যেখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটা বংশগত ঘটনা। শিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ তাই স্বতঃস্ফূর্ত। ছোটোবেলা থেকেই শিল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। চলচ্চিত্রের প্রতিও সেটা কম ছিল না, বরং বলা যায় একটা গভীর আসক্তি ছিল। চলচ্চিত্র বিষয়ে বহু তথ্য যেমন তিনি পড়েছেন, সংগ্রহ করেছেন, গভীর মনোযোগের সঙ্গে হলিউডের বহু ছবিও তেমন দেখছেন— এক একটা ছবি একাধিকবার। জন ফোর্ড, উইলিয়াম ওয়াইলার, ফ্রাঙ্ক কাপরা, জন হাস্টন, বিলি ওয়াইলডার প্রভৃতির ছবি অনেকবার তিনি দেখেছেন।
জাঁ রেনোয়ার ‘দ্য সাউদার্নার’, রবার্ট ফ্লেহার্টির ‘নানুক অফ দ্য নর্থ’ এবং চ্যাপলিনের প্রায় সমস্ত ছবিই তাঁকে যুগিয়েছিল অনুপ্রেরণা। তা বলে তাঁর সৃষ্টিকর্মে ওই চিত্র পরিচালকদের প্রভাব পড়েছে এ কথা বলা সঙ্গত হবে না, কেননা সত্যজিৎ নিজের সৃষ্টিতেই বিভোর, আপন প্রতিভায় উদ্ভাসিত, তিনি গ্রহণ করেন না, সৃষ্টি করেন।

‘অভিযান’ সম্বন্ধে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন সত্যজিতের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাত পরিচালকের অমন একটা বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করা উচিত হয়নি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে মানবিক মূল্যবোধের গভীরতার রসে ছবিটি নিংড়ানো। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তার সাফল্য নির্ভর করছে তার শিল্পগত ব্যবহারের উপর। এই শিল্পকর্মের ব্যাপারটা সত্যজিৎ খুব ভালোভাবেই বোঝেন, তাই বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই।
‘অভিযান’-এর নায়ক নরসিং। সে একজন রাজপুত, সামাজিক বিচারে তার স্থান উঁচুতে, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে নামতে নামতে সে ট্যাক্সি ড্রাইভারে এসে দাঁড়িয়েছে। তার নতুন বন্ধু হল জোসেফ, এক হরিজনের নাতি। হরিজন থেকে সে খ্রিস্টান হয়েছে। এখানেও তথাকথিত সামাজিক বৈষম্যের সূক্ষ্ম হুল ফোটানো।
নরসিংয়ের অনুভূতি আর আবেগ গভীরতায় পৌঁছে দিয়েছেন সত্যজিৎ। তার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব— সোজাপথে চলার বাসনা আবার চোরাগলি দিয়ে আসা কাঁচা পয়সার লোভ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই ছবিতে। সত্যজিৎ বলতে চেয়েছেন এই পাপ আর দুষ্ট ক্ষতে ভরা সমাজের মধ্যেও ভালো থাকা যায়, সুস্থ জীবনযাপন করা অসম্ভব নয়, শুধু মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকা চাই। সত্যজিৎ মানবতাবাদী তাই নরসিংয়ের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে গুলাবীর সঙ্গে তার স্থায়ী জীবনের একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন।
ছবির আলোকসম্পাত, ফোটোগ্রাফি, অভিনয় সব কিছু পরিচ্ছন্ন। আজকের জরাগ্রস্থ সমাজের বিরুদ্ধে নরসিংহ যেন এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ।
শিল্পের মাধ্যমে সময় ও সমকালের দোষ-গুণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একজন শিল্পী একজন স্রষ্টা। সত্যজিৎ শুধু মহৎ শিল্পী নন একজন মহৎ স্রষ্টা। বিদেশে কেউ কেউ বলেছেন সত্যজিৎ নাকি আদিম শিল্পী। তাই যদি হয় তবে এস্কিমোদের নিয়ে তোলা বিখ্যাত ছবি ‘নানুক অফ দ্য নর্থ’-এর স্রষ্টা রবার্ট ফ্লেহার্টিও আদিম শিল্পী। এ কথা কিন্তু কেউ স্বীকার করেন না।
সত্যজিৎকে কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না। যে আর্থিক অসুবিধের মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে [প্রয়োজনে স্ত্রীর গয়না বেচে], তাঁর বিষয়বস্তুর ওপর যেভাবে সরকারি বিষনজর পড়ে, স্বদেশি পত্রপত্রিকা এমনকি এ দেশেরই বিখ্যাত পরিচালকরা যেভাবে তাঁকে আঘাত করতে চেষ্টা করেছেন, তা কোটি কোটি টাকায় তৈরি বিদেশি ছবির পরিচালকরা চিন্তাও করতে পারবেন না। তাঁদের পেছনে থাকে অর্থ ও ক্ষমতা, ছবি তোলার আধুনিক সাজসরঞ্জাম, যার কিছুই নেই সত্যজিতের অথচ তাঁর তোলা ছবি নিয়ে সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। ‘পথের পাঁচালী’ যে মুভি ক্যামেরা দিয়ে তোলা হয়েছে, হলিউডের কোনো তৃতীয় শ্রেণির পরিচালকও সেই ক্যামেরা ছোঁবেন কিনা সন্দেহ। এমনকি যে দৈন্যদশার মধ্যে সত্যজিৎকে কাজ করতে হয়েছে তা বোম্বের পরিচালকদের কাছেও দুঃস্বপ্ন।
এ কথা মিথ্যে নয় যে এই ভারতবর্ষেই কিছু লোক আছেন, যাঁরা সত্যজিৎকে হেয় করার জন্য মুখিয়ে আছেন। আসলে এটা কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে ঈর্ষা থেকে। পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ একজন, এটা কেন যে তাঁরা বুঝতে চাননা সেটাই আশ্চর্য। হয় সত্যজিৎ আমাদের চিন্তাধারা থেকে অনেক বছর এগিয়ে আছেন, নয় যে মানসিকতা দিয়ে সত্যজিতের ছবির মর্ম গ্রহণ করা উচিত তা আমাদের নেই। আমাদের এই ভারতবর্ষে সত্যজিতের আগে এ দেশের সংস্কৃতি আর মূল্যবোধ নিয়ে আর কোনো ছবি হয় নি।
‘দেবী’তে তিনি কুসংস্কারে আঘাত করেছিলেন। তাই অনেকেই বলেছিলেন যেহেতু তিনি ব্রাহ্ম, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেই। লোকসভায় এমন প্রস্তাবও উঠেছিল যেন ওই ছবি বাইরে না যায়। আগেই বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী জহরলাল হস্তক্ষেপ না করলে ওটা হয়তো কোনোদিনই বাইরের আলো দেখতে পেত না।
পাশ্চাত্য দর্শনের চোখে সত্যজিতের ছবি খানিকটা মন্থর মনে হলেও অপু-ত্রয়ী তাঁদের মন কেড়েছিল, কবিতার মতো সুরেলা মনে হয়েছিল। ‘চারুলতা’-র শিল্পসৌন্দর্য তাঁদের ভালো লেগেছিল। কিন্তু তবু বলা হয়েছিল একটু ধীরগতি সম্পন্ন। তবে, সবাই কিন্তু স্বীকার করেছেন ছবির মূল সুর জীবনকে ছুঁয়ে গেছে।
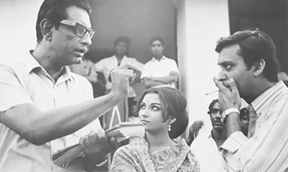
‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ তার এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ। এখানে উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের একটা চিত্র, জীবনযন্ত্রণা, সবকিছু ফুটে উঠেছে। জন রাসেল বলেছেন, ‘অনেকে বলেন সত্যজিৎ অপু-ত্রয়ীর মতো ভালো ছবি আর করেননি। আমি তা বিশ্বাস করি না। ”অরণ্যের দিনরাত্রি” আমাকে সে কথা বিশ্বাস করতে দেয় না।’
সত্যজিৎ নিজেই চিত্রনাট্য লেখেন, সংগীত সৃষ্টি করেন। প্রয়োজনে ক্যামেরার শাটার পর্যন্ত টেপেন। জাঁ রেনোয়া এমনিতেই তাঁকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পিতৃতুল্য বলেন নি। তিনি তাঁকে গদার ও আন্তোনিওনির সমমর্যাদা দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি।
এ কথা এখন কড়া সমালোচকরাও স্বীকার করেন যে, অপু ট্রিলজিতে খুব সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে যে এপিক সৃষ্টি সত্যজিৎ করেছেন, চলচ্চিত্রে তা দুর্লভ।
সত্যজিতের সব ছবিতেই প্রতীকী ব্যবহার লক্ষ্য না করে পারা যায় না। ছোটো ছোটো কিছু ঘটনা, কিছু কথাকে বিলম্বিত লয়ের মধ্যে ফেলে তিনি নিপুণভাবে কাহিনির পরিবেশ ও মেজাজ গড়ে তোলেন।
বৃষ্টি, পুকুর, নদী সত্যজিতের ছবিতে যেন একটা অপরিহার্য বিষয়। নদী আপন খুশিতে বয়ে চলেছে, তা যেন গতিময় জীবনের প্রতীক, মানবসত্তার নির্মল প্রকাশ। ছোটো অপু যখন দুর্গার চুরি করা মালাটিকে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দেয় আর দুপাশের পানা এসে সেটাকে ঢেকে ফেলে, আমরা যেন অপুর সঙ্গেই একটা নিশ্চিন্ততা বোধ করি। যাক, ওটা আর জানাজানি হল না।
বড়ো অপু তার বন্ধুর সঙ্গে এক গ্রামে গেছে বিবাহ অনুষ্ঠানে। নদীতে নৌকো ভেসে যাচ্ছে, আর নদীর পারে মনের আনন্দে কবিতা আবৃত্তি করছে অপু। যেন জীবনের জয়গান মূর্ত হয়ে উঠেছে বীণার ঝংকারে।
সত্যজিৎ একটি ছবি তোলার আগে অনেক ভাবনাচিন্তা করেন। অপর্ণার ভাই মুরারী যখন এসে দুঃসংবাদটা দিল তখন অপুর কি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত তা নিয়ে কয়েকদিনই তিনি চিন্তা করেছিলেন। বিহ্বল হয়ে যাওয়া, কান্নায় ভেঙে পড়া কিংবা মাথায় বাজ পড়ার মতো কিছু তাঁর মনে ধরল না। অপুর মনের সমস্ত আবেগ তিনি মুক্তি দিলেন একটা ঘুষির ভেতর দিয়ে।
এ নিয়ে কম বাদানুবাদ হয়নি। আসল বইয়ে এ ঘটনা নেই। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের চিত্র সমালোচক লিখেছিলেন সমস্ত ব্যাপারটা অনেকের কাছেই একটা রূঢ় আঘাতের মতো লাগবে, কারণ লেখক অপুর চরিত্রকে যেভাবে খাড়া করতে চেয়েছেন এটা তার ঠিক বিপরীত। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, সত্যজিৎ বিভূতিভূষণের মূল কাহিনি থেকে আরও কিছু কিছু জায়গায় ঘুরে সরে গেছেন এবং তাতে ছবির উৎকর্ষতা কমেনি বরং বেড়েছে।
আসলে আমরা ভারতীয়রা গান্ধীজির অহিংস-নীতির উপাসক বলেই বোধ হয় অপুর অমন হিংসাত্মক হয়ে ওঠার ব্যাপারটাকে পুরোপুরি মানতে পারি নি। আগেই বলেছি, সত্যজিতের চিন্তাধারা আমাদের সময় পেরিয়ে— সময়কে পেছনে ফেলে অনেক এগিয়ে আছেন তিনি, তাই আমাদের পক্ষে তাঁর ছবির শিল্পকর্ম বুঝে ওঠা কঠিন।
সেই কারণেই ভারতীয় পত্রপত্রিকা সত্যজিতের ছবি সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই সহনশীল না হলেও বিদেশে তাঁর ছবির ভালো সমালোচনা হয়েছে।
‘অপরাজিত’ ছবিতেও আসল কাহিনি থেকে তিনি কিছুটা সরে এসেছেন এবং এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। ফরাসি দেশের জাঁ হেরম্যান কিন্তু তখন সত্যজিতের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন, যার ফলে রবীন্দ্রনাথের কাহিনিতেও প্রয়োজনমতো হেরফের করতে সাহসী হয়েছিলেন সত্যজিৎ।
হেরম্যান বলেছিলেন চলচ্চিত্রে একটা আলাদা স্টাইল আছে, তাই কাহিনির সঙ্গে হুবহু মিল রেখে ছবি তোলা কিংবা বিশ্বস্ততা বজায় রাখা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের ধারাই আলাদা, চলচ্চিত্র সাহিত্যকে অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ করে সৃষ্টি হতে পারে না, শুধু দেখতে হবে লেখকের বক্তব্যের মূল সুরটা বজায় আছে কিনা।
‘পরশ পাথর’ গল্পটি মাত্র দশ পাতার। পরশুরাম (রাজশেখর বসু) তখনও বেঁচে। সত্যজিৎ চিত্রনাট্য লিখে তাঁকে দেখিয়েছিলেন, মূল কাহিনি অদলবদলের যে স্বাধীনতা তিনি নিয়েছিলেন, পরশুরাম তাতে মোটেই আপত্তি করেননি। তেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রর ‘কাপুরুষ’, নরেন্দ্র মিত্রর ‘মহানগর’ এবং শঙ্করের ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিতেও প্রয়োজনমতো পরিবর্তনের দরকার হয়ে পড়েছিল এবং লেখকদের তাতে অসম্মতি ছিল না। একটা ভালো গল্প বা উপন্যাস যতই সুখপাঠ্য হোক না কেন, তাকে চিত্রায়িত করার অনেক অসুবিধে, সেখানেই পরিচালকের কৃতিত্ব। কাহিনিকে ছবির উপযোগী সুষম করে তুলতে যিনি না পারেন তিনি আর যাই হোন, ভালো চিত্র পরিচালক নিশ্চয়ই নন।
শঙ্করের ‘সীমাবদ্ধ’-র মূল কাহিনি থেকে অনেক সরে এসেছেন সত্যজিৎ, কিন্তু তাতে মৌলিক রসের হানি হয়নি বরং রসোত্তীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রপতির সুবর্ণ পদক লাভ করেছিল ওই ছবি।
‘সমাপ্তি’ ছবিটির চমৎকার সমাপ্তি মনে দাগ না কেটে পারে না। গার্ডিয়ান পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, চেকভের মিলনাত্মক কাহিনির মতোই সমৃদ্ধ একটা ছবি।
লন্ডন টাইমস আরেক ধাপ এগিয়ে লিখেছিল, সত্যজিৎ রায় এমন একজন পরিচালক যাঁর হেলাফেলার ছবিও অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতার তথাকথিত মাস্টারপিসের চাইতে বসে দেখবার মতো।
‘মণিহারা’কে ছেঁটে ‘পোস্টমাস্টার’ আর ‘সমাপ্তি’ একসঙ্গে ‘দুই কন্যা’ নাম নিয়ে বিদেশের বাজারে ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানী আর মধ্যপ্রাচ্যে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ফিলম ফেস্টিভ্যালে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল ‘দুই কন্যা’।
একজন ইংরেজ সমালোচক লিখলেন, এটা রায়ের সপ্তম ছবি এবং এখন আর কারও মনে সন্দেহ থাকতে পারে না যে, তাঁর প্রতিভা সহজে ক্লান্ত হয়ে যাবার নয়।
নিজের ছবি শুরু করার অনেক আগেই বিদেশি ছবি ছাড়াও প্রচুর ভারতীয় ছবি সত্যজিৎ দেখেছিলেন। নীতিন বসুর ‘ধরতি মাতা’ তাঁর ভালো লেগেছিল। প্রথম যে ছবিতে তিনি সমসাময়িক ভাবনা খুঁজে পেয়েছিলেন তা হল বিমল রায়ের ‘উদয়ের পথে’। প্রথম যে ভারতীয় ছবি তাঁর মন নাড়া দিয়েছিল, তা হল ‘দো বিঘা জমিন’। যোগীন দাসের ‘রামশাস্ত্রী’ও তাঁর ভালো লেগেছিল।
সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে ছবি করার চাইতে গল্পের মধ্যে মানবিক বোধটাই সত্যজিৎকে আকৃষ্ট করে বেশি। কিন্তু গল্পের মধ্যে এই গুণ শাশ্বতভাবেই নিহিত থাকে, যেমন ‘অপু’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘চারুলতা’, আবার কিছু কাহিনিতে এই গুণ প্রতিফলিত হয় অতীতে, যেমন ‘জলসাঘর’।
.
সত্যজিতের প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’, ওই ছবিই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, অন্ধকার থেকে নিয়ে গিয়েছিল আলোর রাজ্যে, বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন তিনি। চলচ্চিত্র জগতে এখন তিনি এক প্রবাদ পুরুষ। অথচ এই প্রথম ছবি রূপায়িত করতে কি ক্লেশই না তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে, কি আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে কেটেছে প্রতিটি দিন। একটা প্রশ্ন মনে জাগে, যদি সত্যজিতের তখন প্রচুর টাকা থাকত কিংবা ধনী প্রযোজক পেতেন এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি কাজে লাগাতে পারতেন, তবে কি ছবিটা আরও ভালো হত? মনে হয় না, কেননা অভাব আর দুঃখবোধের ভেতর দিয়েই গড়ে ওঠে মহৎ শিল্প। প্রাচুর্যই যদি প্রধান হাতিয়ার হত তবে হলিউডের অধিকাংশ ছবিই তো মহৎ শিল্পের পর্যায়ে পড়ত। কিন্তু তা তো হয়নি। অপ্রতুলতা মানুষকে সংগ্রামী করে তোলে, প্রকাশ করে তার লড়াকু মনোভাব— সেটাই বোধ হয় সত্যজিৎকে এনে দিয়েছিল অনমনীয় দৃঢ়তা, ঘটিয়েছিল তাঁর প্রতিভার বিকাশ।
আর্ট ফিলম পাবলিকেশনস সত্যজিৎ সম্বন্ধে লিখেছিল:
রায় নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেন এবং মিতব্যয়ী পরিচালকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। একটা কিংবা দুটো শটে, একটি অথবা দুটি সংলাপে যে কোনো ঘটনাকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁর আছে। ‘পথের পাঁচালী’ কালের সীমা উত্তীর্ণ হওয়া একটি আন্তর্জাতিক ছবি। এই গল্প ও চরিত্র পৃথিবীর যেকোনো মাটিতেই সম্ভব। গোর্কি ট্রিলজির চাইতেও রায় অনেক ঊর্ধ্বে। পৃথিবীর মাস্টারপিস ছবির তালিকায় অপু থাকবে। যেখানে দুর্গা মারা গেল, শুধু ঠোঁট নেড়ে যে নিঃশব্দ কান্না, রবিশঙ্করের সুরের মূর্চ্ছনায় যে ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে, তা বোধ হয় চিরকালের জন্য শাশ্বত হয়ে থাকবে।
এই ছবি করার সময় কত ঘটনাই ঘটেছে। ‘পথের পাঁচালী’ হল চুনিবালার আর ‘অপরাজিত’ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। করুণার আশ্চর্য অভিনয় পৃথিবীর যে কোনো অভিনেত্রীর কাছে শ্লাঘার বস্তু।
আশি বছরের চুনিবালা দেবী উত্তর কলকাতার এক নিষিদ্ধ পল্লিতে বাস করতেন। বয়সকালে কিছু ছবিতে তিনি কাজ করেছিলেন, কিন্তু তেমন নাম করেননি, সুস্থ সরল জীবন তাঁর কপালে জোটে নি। সত্যজিৎ আর অনিল চৌধুরি অনেক খুঁজে তাঁর বাড়ি বার করলেন। কড়া নাড়তে চুনিবালাই দরজা খুলে তাঁদের ভেতরে আহ্বান জানালেন। লোলচর্ম, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া ওই বৃদ্ধাকে দেখামাত্র সত্যজিতের মনে হল তিনি ইন্দির ঠাকরুনকে খুঁজে পেয়েছেন।
চুনিবালা তাঁদের ঘরে বসিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, বললেন তাঁর মেয়ে, পেশাদার অভিনেত্রী। ভদ্রলোকদের চা দিয়ে আপ্যায়িত করে চুনিবালা ওই বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁদের আলাপ করিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন বাবুরা সেই ব্যাপারেই এসেছেন।
সত্যজিৎ তাড়াতাড়ি তাঁর ভুল ভেঙে দিলেন, বললেন একটা ছবির জন্য চুনিবালার কাছেই তাঁরা এসেছেন, অন্য মেয়েদের দরকার নেই। চুনিবালা সব শুনে তো আহ্লাদে আটখানা। বয়সকালে যে সব নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন তার পুরোনো হ্যান্ডবিল এনে দেখালেন।
চুনিবালাকে খুব ছোটো করে চুল কাটতে বলা হল। তাঁকে নিয়ে কয়েকটা শট নেবার পর বন্ধ করতে হল কাজ, টাকা যা যোগাড় হয়েছিল ফুরিয়ে গেছে। আট মাস পর সরকারি অনুদানের প্রথম কিস্তি হাতে আসার পর আবার নতুন উদ্যমে শুরু হল শুটিং। চুনিবালাকে ট্যাক্সি করে খুব ভোরে নিয়ে আসতে হত যাতে বেলা বেলা ফিরে ঘরের কাজকর্ম করতে পারেন।
অনিল চৌধুরি তাঁকে আনতে এসে আঁতকে উঠলেন। ওই আট মাসে তাঁর চুল অনেক বড়ো হয়ে গেছে, আগের তোলা ছবির সঙ্গে একেবারেই বেমানান। অত সকালে নাপিত পাওয়া যাবে কোথায়! চৌধুরি আর কি করেন, চুনিবালাকে সোজা বোড়ালে যেখানে শুটিং হচ্ছিল সেখানে নিয়ে হাজির করলেন। সম্পাদকের সহকারী শান্তি চ্যাটার্জি শেষপর্যন্ত ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তাঁর একটা অভ্যেস ছিল সবসময় সূঁচ সুতো আর একটা ক্ষুর সঙ্গে রাখা, বলা যায় না কখন কি কাজে লাগে। ওই ক্ষুর দিয়ে তিনি চুনিবালার চুলে কদমছাঁট দিলেন, সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।
ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর দৃশ্যে সত্যজিৎ কোনো ডামির সাহায্য নেননি। চুনিবালার বয়স তখন একাশি, তাঁর পক্ষে হুমড়ি খেয়ে পড়াটাই বিপজ্জনক ব্যাপার, কিন্তু সত্যজিৎ কোনোরকম কৃত্রিমতার আশ্রয় নিলেন না। চুনিবালাকে দিয়েই ওই দৃশ্য করালেন। তিনি পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাঁর মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন। ততক্ষণে অবশ্য শট নেয়া হয়ে গেছে। সত্যজিতের কোমল মনের এটা একটা উদাহরণ।
পরের দিনের শুটিং নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত। ইন্দিরার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অতি বৃদ্ধা চুনিবালা শ্মশানের দিকে এক পা বাড়িয়েই আছেন, তাঁকে কি করে দৃশ্যটার কথা বলা যায়! কেউই মুখ খুলতে চান না। একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন তাঁকে বলা হল, তিনি তো হেসেই অস্থির, বললেন, ‘আমি তো অভিনয় করছি, তোমাদের এত কিন্তু কিন্তু কেন?’
১৯৫৮-র সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ‘পথের পাঁচালী’ নিউ ইয়র্কে মুক্তিলাভ করার পর ওখানকার বিখ্যাত পত্রিকা নিউ ইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউন উচ্ছ্বাসভরে মন্তব্য করেছিল, ‘চুনিবালা দেবী ইজ ফ্যান্টাস্টিক্যালি রিয়্যালিস্টিক অ্যান্ড এফেকটিভ অ্যাজ দ্য এজিং ক্রোন।’ তার কয়েক মাস আগে ফিলমস অ্যান্ড ফিলমিং পত্রিকায় বলা হয়েছিল, ‘এ ফ্যান্টাস্টিক ওল্ড অ্যাকট্রেস।’ [নিউ ইয়র্কে প্রকাশ্যে মুক্তিলাভের আগে ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে ওখানে একটা শিল্প প্রদর্শনীতে ছবিটা পাঠাবার তোড়জোড়ের কথা আগেই বলা হয়েছে]।
‘পথের পাঁচালী’র শুটিং যখন চলছিল, ছবি তোলার ব্যাপারে যাঁরা পেশাদার তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে কম হাসাহাসি হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভস্মে ঘি ঢেলেছেন এ কথা প্রকাশ্যেই বলা হয়েছিল। কান ফেস্টিভ্যালে ছবিটা যে প্রদর্শনীর জন্য যেতে পেরেছিল সেটা সত্যজিতের পরম সৌভাগ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি, গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকেও কোনো উৎসাহ ছিল না। ওটাকে কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠাবার জন্য কত যে কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিল সেও এক ইতিহাস। ব্রিটিশ ফিলম ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর জেমস কুইন ছিলেন ওই উৎসবের বিচারকমণ্ডলীর একজন জুরি। কুইন লন্ডনে ওই ছবিটা দেখেছিলেন, সত্যজিৎই এক কপি প্রিন্ট তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ছবিটা দেখে কুইনের এত ভালো লেগেছিল যে, তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মেছিল ওটার পুরস্কার পাওয়া উচিত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে এই জেমস কুইনের সঙ্গেই বার্লিনে ফিলম ফেস্টিভ্যালে সত্যজিৎ বিচারকের আসন অলংকৃত করেছিলেন। কুইন গুণী মানুষ ছিলেন, ছবিটাকে যাতে কান উৎসবে পাঠানো হয় তার জন্য দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাতেই বোধ হয় কর্তৃপক্ষদের টনক নড়েছিল।
এমনকি কান উৎসবে ছবিটা পুরস্কার পাবার পরেও বিদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ওটা প্রদর্শনীর ব্যাপারে সরকার পক্ষ থেকে গড়িমসির অন্ত ছিল না। বোম্বেতে এমন কানাঘুসোও শোনা গিয়েছিল যে, ছবিটাকে এবার শিকেয় তুলে রাখা হবে। শেষপর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর হস্তক্ষেপে বিদেশ দপ্তর ভারতীয় সমস্ত দূতাবাসে নির্দেশ পাঠিয়েছিল ‘পথের পাঁচালী’র ছবির প্রিন্ট যোগাড় করে তা যেন দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়।
দেশের সম্মান যেখানে জড়িত সেখানেও রাজনীতি। এটা নিশ্চয়ই সত্যজিতের সৌভাগ্য যে শেষপর্যন্ত ছবিটা বাইরে যেতে পেরেছিল এবং ভারত নামক দেশে জন্মগ্রহণ করেও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালকের মর্যাদা তিনি পেয়েছেন।
কান ফিলম ফেস্টিভ্যালে ছবিটা যদি না যেত তবে চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিতের বোধ হয় দ্বিতীয় ছবি করা হয়ে উঠত না, এক বিরাট প্রতিভার ঘটত অপমৃত্যু, আমরা বঞ্চিত হতাম মহৎ সৃষ্টি থেকে।
ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া থেকে শুরু করে বিশ্বের কত দেশ তাঁকে সম্মান দিয়ে নিজেদের সম্মানিত মনে করেছে আর আমাদের ভারতবর্ষ। সম্মান দেখাবার চাইতে তাঁকে হেয় করার চেষ্টাই হয়েছে বেশি। এই পশ্চিমবাংলার সমালোচকরাই কি ছেড়ে কথা বলেছেন। দু-শো বছর ইংরেজদের দাসত্ব আমাদের মনে যে বিদ্বেষ আর সঙ্কীর্ণতার বীজ রোপণ করেছে, হাজার বছরেও কি তা নির্মূল হবে।
রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার না পেলে স্বদেশে বোধ হয় অনাদৃতই থেকে যেতেন। তাঁর বিরুদ্ধেও অপপ্রচার কম হয় নি।
একটা ঘটনা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ‘পথের পাঁচালী’ শুটিং-এর সময় [সরকারি অনুদানের আগের ঘটনা] এমন এক সময় এসেছিল যখন ইউনিটের সবাইকে খাওয়াবার জন্য দু-শো টাকা পর্যন্ত নেই। বিজয়া দেবী তখন সন্তানসম্ভবা। অনিল চৌধুরির উপর ভার ছিল ইউনিটের তদারকি করার। তিনি নিরুপায় হয়ে বিজয়া দেবীর শরণাপন্ন হলেন। বিজয়া দেবী তাঁর হাতের বালা খুলে দিলেন, তাই বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করা হল। ঘরের বউ গয়না বন্ধক দিয়েছে জানতে পারলে সুপ্রভা দেবী রাগ করবেন তাই ব্যাপারটা তাঁর কাছে গোপন রাখা হল। এমনকি একটি ঘরোয়া সামাজিক উৎসবে অন্য এক ভদ্রমহিলার সোনার বালা জমা দিয়ে বন্ধকীর দোকান থেকে বিজয়ার বালা জোড়া ধার করে আনা হল যাতে সুপ্রভা দেবী আসল ব্যাপারটা জানতে না পারেন।
১৯৫৮ সালে নিউ ইয়র্কে ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি প্রসঙ্গে সত্যজিৎ এক অনুষ্ঠানে ওই মজার ঘটনা বলেছিলেন। পরদিন একটা সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল ওই ঘটনা। মার কাছে গোপন করার জন্য সত্যজিৎ কাগজের কাটিংটা স্ত্রীর কাছে পাঠাবার সময় শুধু ওই বিশেষ অংশটুকু কালি লেপে পাঠিয়েছিলেন। সুপ্রভা দেবী কালি লেপা কাগজের কাটিংটা দেখেই হাসতে শুরু করলেন। পরে বিজয়াকে বললেন, গোড়া থেকেই ব্যাপারটা তিনি টের পেয়েছিলেন কিন্তু চুপ করে থাকাই উচিত মনে করেছিলেন। সত্যজিৎ যাঁর চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিলেন তিনি যে স্বয়ং তাঁর গর্ভধারিণী এটা তাঁর খেয়াল করা উচিত ছিল।
‘অপরাজিত’ কিন্তু কলকাতায় মুক্তিলাভের পর সাফল্য পায়নি। সত্যজিৎ আশা করেছিলেন ‘পথের পাঁচালী’র পর ওই ছবিটা পশ্চিমবঙ্গবাসী সাদরে গ্রহণ করবে। তাঁর আশাভঙ্গ হল। জাতীয় পুরস্কারের জন্যেও ছবিটাকে মনোনীত করলেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিরূপ সমালোচনা এবং প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হল সত্যজিৎকে।
তবে ভেনিস ফিলম ফেস্টিভ্যালে ‘অপরাজিত’ কিন্তু আমন্ত্রণ পেল। ‘পথের পাঁচালী’ কান উৎসবে যে শোরগোল ফেলেছিল তারই সুবাদে ওই আমন্ত্রণ।
১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে জুরিদের নির্বাচনে ‘অপরাজিত’ লাভ করল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার— গোল্ডেন লায়ন। বিখ্যাত চিত্র পরিচালকদের ছবি ওই উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল, সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ‘অপরাজিত’ জুরিদের বিচারে সর্বোত্তম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটিকে আঞ্চলিক পুরস্কারের জন্য পর্যন্ত বিবেচনা করেন নি, জাতীয় পুরস্কার তো দূরের কথা। এই তো আমাদের জাতীয় চরিত্র।
সত্যজিৎ যেদিন ভেনিস উৎসবে যাত্রা করেছিলেন আর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে যেদিন তিনি দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন, তার মধ্যে ‘পথের পাঁচালী’ আর ‘অপরাজিত’ ডেভিড সেলজনিক গোল্ডেন লরেল পুরস্কার লাভ করেছে। দমদম বিমানবন্দরে প্রচুর লোক জমায়েত হয়েছিল, সত্যজিৎকে তাঁরা বীরোচিত সংবর্ধনা দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর। এই প্রথম বোধ হয় দেশের জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পেলেন সত্যজিৎ। দেশবাসীর এই উষ্ণ সংবর্ধনায় নিশ্চয়ই তাঁর মন আবেগে মথিত হয়ে উঠেছিল।
১৯৬০ সালে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান দেওয়া হল সত্যজিৎকে— আমেরিকায় সেই প্রথম সম্মান। সত্যজিতের একক ছবির প্রদর্শনীও সেই প্রথম। অপু ট্রিলজি ছাড়াও সেই প্রদর্শনীতে ছিল ‘জলসাঘর’ আর ‘দেবী’। এর আগে ১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক এবং ১৯৫৯ সালে মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সংগীতের জন্য রৌপ্য পদক পেয়েছিল ‘জলসাঘর’। ‘দেবী’ অবিশ্যি ১৯৬০ সালে শ্রেষ্ঠ ছবি বিবেচিত হয়ে পেয়েছিল রাষ্ট্রপতির সুবর্ণ পদক।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, পণ্ডিত রবিশঙ্কর অপু-ত্রয়ী এবং ‘পরশপাথর’, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ‘জলসাঘর’ আর আলি আকবর খাঁ ‘দেবী’ ছবির সংগীত সৃষ্টি করেছিলেন। রবিশঙ্কর, বিলায়েৎ খাঁ এবং আলি আকবর— তিন কীর্তিমান সংগীত সাধক, ভাবতেও শিহরণ জাগে।
পরবর্তীকালে অবিশ্যি সত্যজিৎ নিজেই তাঁর ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন, এমনকি সুর সৃষ্টি পর্যন্ত করেছেন।
.
১৯৬৬ সালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়েছিল ‘নায়ক’। ওখানে কেউ কেউ ছবিটার বিরূপ সমালোচনা করলেও ওটা কিন্তু ওই উৎসবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল, আর চলচ্চিত্র জগতে তাঁর উৎকর্ষ শিল্পবোধের জন্যে সত্যজিৎকে সম্মানিত করা হয়েছিল বিশেষ পুরস্কারে।
‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ বোধ হয় সত্যজিতের একমাত্র ছবি যেখানে কোনো স্টুডিয়ো সেট বানাতে হয় নি। দাজিলিং-এর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে শুধু আউটডোর শুটিং। নাক উঁচু এক বাঙালি পরিবারের কর্তা, যাঁর হুকুমই হল শেষ কথা, তাঁরই ছোটো মেয়ের বিদ্রোহী মনোভাব, বাবার মনোনীত, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করে এক সাধারণ যুবককে তার ভালো লাগা, বড়ো মেয়ের দাম্পত্য জীবনের ভুল বোঝাবুঝি, ওই সমাজের মেকি আড়ম্বর, যন্ত্রণা, সবকিছু প্রকাশ পেয়েছে এই ছবিতে।
‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ সত্যাজিতের প্রথম রঙিন ছবি এবং প্রথম স্বরচিত কাহিনির ছবি, দ্বিতীয় স্বরচিত কাহিনির ছবি হল ‘নায়ক’। তারপর ফেলুদার কাহিনি তো আছেই।
‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র সিনারিও লিখতে দার্জিলিং গিয়েছিলেন সত্যজিৎ, মাত্র দশদিন লেগেছিল শেষ করতে। সেই সিনারিওদের সঙ্গে ছিল দার্জিলিং শহরের একটা মানচিত্র, তার মধ্যে সতেরোটি জায়গা ক্ষুদে বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত, প্রত্যেকটি বৃত্ত এক একটি লোকেশনের জায়গা নির্দেশ করছে। তাছাড়া প্রধান লোকেশনের জায়গাগুলির জন্যে ছিল আরও কয়েকটি নকশা।

দিনের কোন সময় কোন শটটা নেওয়া হবে তার উল্লেখ ছিল সিনারিওতে, আলোর সঠিক প্রভাব যাতে পাওয়া যায় তার জন্যে হিসেব করে ভাগ করা হয়েছিল সময়।
পরিবারের কর্তা ইন্দ্রনাথ চৌধুরির ভূমিকায় ছিলেন ছবি বিশ্বাস, তাঁর স্ত্রী লাবণ্যর ভূমিকায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথের শ্যালক জগদীশের ভূমিকায় পাহাড়ি সান্যাল, ইন্দ্রনাথের ছেলের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর স্বভাব মেয়েদের পেছনে ঘোরা। দার্জিলিং-এর দুজন কলেজের মেয়েকে পেয়ে গেলেন সত্যজিৎ— বিদ্যা সিং আর নীলিমা রায় চৌধুরি।
দুজনেরই পরনে কালো ড্রেনপাইপ স্ল্যাকস আর গায়ে হাতে বোনা কার্ডিগান বিদ্যারটা গাঢ় হলদে আর নীলিমার ফ্যাকাশে লাল। অনিল চট্টোপাধ্যায় কলকাতার নামি দর্জির দোকান থেকে যে রঙের স্যুট বানিয়ে এনেছিলেন ওদের পোশাকের পাশে তা ম্যাড়মাড়ে দেখাচ্ছিল ফলে তাড়াতাড়ি ম্যালের এক দোকানে তাঁর জন্যও ড্রেন পাইপ স্ল্যাকস অর্ডার দেওয়া হল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওটা বানিয়ে দিয়েছিল দোকানদার।
ইন্দ্রনাথের জামাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সুব্রত সেন, তিনি তখন কলকাতা কর্পোরেশনের একজন বামপন্থী কাউন্সিলর। তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় ছিলেন অনুভা গুপ্তা।
নায়কের ভূমিকার জন্যে একেবারে নতুন একজনকে নেবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন সত্যজিৎ, নাম অরুণ মুখার্জি। তবে সিনেমায় না নামলেও শম্ভু মিত্রর গ্রুপের হয়ে তিনি কয়েকটি নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সত্যজিৎ কিন্তু তাঁর অভিনয় না দেখেই তাঁকে ওই চরিত্রের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সত্যজিতের একটা বৈশিষ্ট্যই হল কোনো চরিত্রের জন্য কাউকে নির্বাচিত করার সময় তাঁর অভিনয় ক্ষমতার চাইতে তাঁর চেহারার ওপরই গুরুত্ব দেন বেশি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে, মুখের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করেন। বেশ চটপটে, সুশ্রী, বুদ্ধিমান একজন মানুষই তাঁর পছন্দ। কিভাবে চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে হবে তার জন্য নির্দেশ দেবার বদলে যারা অভিনয় করেন তাদের তিনি নিজেদের মতো চরিত্রটা প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেন, উৎসাহ যোগান।
এন. বিশ্বনাথন ছোটো মেয়ে মনীষার পাণিপ্রার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। মনীষার চরিত্রের জন্য খুঁজে বার করা হয়েছিল আনকোরা নতুন একটি মেয়েকে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী, অলকানন্দা রায়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়র, সিনেমা টিনেমা করার ব্যাপারে ঘোর বিরোধী। তাঁর সম্মতি আদায় করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, তবে এ ব্যাপারে অলকার মায়ের সাহায্য না পেলে হয়তো অন্য মেয়ের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হত ইউনিটের সবাইকে।
একেবারে নতুন মুখ নিয়ে ছবি তোলার ব্যাপারে সত্যজিতের মতো সাহস আর বাহাদুরি বোধ হয় দ্বিতীয় কারও নেই, শুধু তাই নয়, তার অনেকগুলোই আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়ে সারা বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করেছে।

‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবি তোলার সময় তাৎক্ষণিক বেশ কিছু দৃশ্য ছবিতে ঢুকে গেছে। যেমন একদিন জলপাহাড় রোডে একটা দৃশ্য তুলে যখন ফিরে আসছেন, সত্যজিতের নজরে পড়ল দূরে লম্বা এক গাধার মিছিল নিয়ে চলেছে কয়েকজন তিব্বতী যাযাবর। গাধাদের গলায় আবার নানারকম ঘণ্টা, বিচিত্র ধ্বনি হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সত্যজিৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন গাধার মিছিলটাকে দৃশ্যে ঢোকাতে হবে। তিব্বতীদের অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এমনকি কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে গাধার মিছিলকে ফিরিয়ে ক্যামেরার সামনে আনা হয়েছিল।
ব্যানার্জি যখন মনীষার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করার চেষ্টা করছে সেইসময় ব্যাকগ্রাউন্ডে চমৎকারভাবে গাধার মিছিলের দৃশ্যটাকে কাজে লাগানো হয়েছিল।
কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন কুয়াশায় ঢাকা, মানুষেরও মনও তেমন কুয়াশাচ্ছন্ন, জটিলতায় ভরা, এটাই বোধ হয় দেখাতে চেয়েছিলেন সত্যজিৎ। তারপর একসময় কুয়াশা সরে গিয়ে সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা। মানুষের জীবনের জটিলতাও এমনি করে একদিন কেটে যায়, কেটে যায় তাদের মনের গ্লানির কুয়াশা।
.
‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র পর অসমাপ্ত ‘অভিযান’ শেষ করলেন সত্যজিৎ। তারপর এল সেই অভিশপ্ত দিন, একুশে অক্টোবর ১৯৬২, ইন্দোচীন সীমান্ত সংঘর্ষ। সে সময় একটা গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কেটেছে ভারতবাসীর। চীনা সৈন্যের অনুপ্রবেশ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বইকি। সত্যজিৎও সেইসময় কি হয় ভাবনা থেকে দূরে থাকতে পারেন নি।
যা হোক শেষপর্যন্ত শান্তি ফিরে এল, সত্যজিৎ ‘মহানগর’-এর কাজ শুরু করলেন। মাধবী মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হলেন নায়িকার ভূমিকায় আর অনিল চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বামী।
ওই ছবিতে এডিথ নামে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের ভূমিকা১ ছিল। তার চাকরি চলে যাবে। মালিক তার সম্বন্ধে অশালীন মন্তব্য করায় নায়িকা আরতি প্রতিবাদে চাকরি ছেড়ে দেবে। ছবিটা মুক্তি পাবার আগেই কয়েকজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক শুধুমাত্র বিদ্বেষের বশে অভিযোগ করলেন ওই ছবিতে তাঁদের সেন্টিমেন্টে আঘাত করা হয়েছে। বোম্বেতে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিলম সেন্সরের কাছে নালিশ পর্যন্ত গেল, ফলে ছবিটা মুক্তি পাবার ছাড়পত্র গেল আটকে। শুধু তাই নয়, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের প্রতিনিধি ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি ছবিটা না দেখেই রাজ্যসভায় ঝড় তুললেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে সত্যজিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত পাঠানো হয়েছিল। ওই অভিযোগ সত্যি না মিথ্যে তা বিচার করে দেখার ভার পড়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর ওপর। সত্যজিতের শিল্পকর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তিনি অসঙ্গত কিছু করতে পারেন এটা ইন্দিরার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। নেহরুর নির্দেশেই শেষপর্যন্ত ছাড় পেয়েছিল ‘মহানগর’ এবং ১৯৬৪ সালে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছিলেন সত্যজিৎ ওই ‘মহানগর’ ছবির জন্যই।
সত্যজিৎকে এ নিয়ে কতবার যে অপদস্থ করার চেষ্টা হয়েছে তার শেষ নেই। দার্জিলিং-এ ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র শুটিংয়ের সময় একবার প্রায় ঘেরাও হয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর ইউনিট। কারণটা আর কিছু নয়, আঞ্চলিক সংকীর্ণতা, বাঙালিদের প্রতি ওখানকার পাহাড়ি মানুষদের বিদ্বেষ।
১৯৬৩-র জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োতে মহানগরের শুটিং শুরু হবার আগে (১৯৬২-র ডিসেম্বর) প্রধানমন্ত্রী জহরলালের সঙ্গে সত্যজিতের একটা আলোচনা হয়েছিল। ১৯৬২-র অক্টোবরে সীমান্ত সংঘর্ষ উপলক্ষ্য করে চীনের আগ্রাসী ভূমিকা নেহরুকে ভাবিয়ে তুলেছিল। দেশ রক্ষায় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চলচ্চিত্রকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়েই ওই আলোচনা।
শ্রী গোপাল রেড্ডি তখন বেতার ও তথ্যমন্ত্রী। সত্যজিৎকে শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি চিনতেন, স্নেহ করতেন। সত্যজিৎকে তিনি মানবতাবোধের উপর ভিত্তি করে দেশাত্মবোধক একটি তথ্যচিত্র তৈরি করার জন্য অনুরোধ করলেন। সত্যজিৎ এবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন। তিনি নিজেই প্রস্তাব দিলেন নেহরু ওই ছবিতে থাকবেন এবং ছবির বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

১৯৬২-র বড়দিনের সময় নেহরু শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, তিনি সত্যজিৎকে পঁচিশ কিংবা ছাব্বিশ ডিসেম্বরের যে কোনোদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠালেন। ইন্দিরা গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন ওই সভায়। তিনি তখনও নেহরুর কন্যা ইন্দু, রাজনীতিতে প্রকাশ্যে অভিষেক হয় নি।
সুন্দর পরিবেশে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শেষপর্যন্ত ছবিটা হল না। দ্রুত ঘটে গেল পট পরিবর্তন। ইন্দিরা গান্ধী আবার সত্যজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, কিন্তু তা নেহরুর ভস্মাধার গঙ্গায় বিসর্জনের ছবি তোলার জন্য।
জহরলালের সঙ্গে আলোচনার দশদিন পরেই ‘মহানগর’ শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন সত্যজিৎ। ওটার পরেই নেহরুর ছবিটা ধরবেন এই ছিল পরিকল্পনা। বড়ো বড়ো হোটেল রেস্তোরাঁয় পেশাদার গাইয়ে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তরুণী, ভিকি রেডউডকে এডিথের ভূমিকার জন্য মনোনীত করা হল।
.
‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ থেকেই ছবিতে সংগীত সৃষ্টি ও সংগীত পরিচালনার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ। তার আগে অবিশ্যি ‘তিনকন্যা’-তেও সংগীত পরিচালনা তিনিই করেছিলেন, তবে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ থেকে পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবিতে তিনি হাত দিলেন।
স্ত্রী বিজয়া এ ব্যাপারে তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। ছোটোবেলা যখন মামাবাড়িতে ছিলেন সত্যজিৎ, আর বাবার মৃত্যুর পর বিজয়া দেবীর চার বোন সেই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন, তখন থেকেই দুজনের সংগীতের প্রতি সহমত গড়ে উঠেছিল।
সত্যজিতের সংগীত সৃষ্টিও উল্লেখ করার মতো ঘটনা। প্রথমে শিস দিয়ে সুরটা তিনি সৃষ্টি করেন, তারপর পিয়ানোতে তোলেন। চলচ্চিত্রে লোকসংগীত কিংবা পল্লিগীতির ব্যবহারও পছন্দ করেন তিনি।
ছবি তৈরির শুরুতেই সংগীতের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটা ধারণা হয়ে যায়। এমনকি সিনারিও লেখার সময়ও ওটা এসে যায়। পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব তাকে ঋণী করেছে এ কথা মুক্ত কণ্ঠে তিনি স্বীকার করেন। একটা কথা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, সত্যজিতের কিছু ছবি নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার একমাত্র কারণ হল, একবার সেসব ছবি দেখে তাদের বিচার বা মূল্যায়ন করা সহজ নয়, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ তেমন একটা ছবি। অনেকে ছবিটা প্রথমবার দেখে কিছুই বোঝেননি আবার দেখেছেন। এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ী’ ছবিটা এই অধম তিনবার দেখার পর তবে তার গভীরতা সামান্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, সত্যজিৎ আমাদের সময় থেকে অনেক এগিয়ে, তাই এই অসুবিধে।
‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ কিন্তু ব্যবসায়িক সাফল্যের মুখ দেখেনি। তবে তার জন্য প্রযোজকরাও অনেকাংশে দায়ী। মুনাফা লুটবার তাড়াহুড়োয় সত্যজিতের সঙ্গে পরামর্শ না করেই এমন কিছু কাণ্ড তাঁরা করেছিলেন, যা ছবিটার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওই ভদ্রলোকরা স্বর্ণ ডিম্বের লোভে হাঁসটিকেই বধ করেছিলেন।
‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ‘অভিযান’-এর বাকি কাজটুকু শেষ করার জন্য সত্যজিৎ উঠে পড়ে লেগেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে মাইল কুড়ি দূরে দুবরাজপুরে আউটডোরে শুটিং হয়েছিল। ওখানকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা আর প্রাকৃতিক দৃশ্য মুগ্ধ করেছিল সত্যজিতকে। ও শিলাখণ্ডগুলো প্রায় এক মাইল বর্গক্ষেত্র জুড়ে এমনভাবে ছড়ানো যেন মনে হয় ওগুলো মাটি ফুঁড়ে ওঠেনি, কেউ আকাশ থেকে ফেলেছে।
এ বিষয়ে একটা প্রবাদ ওখানকার লোকের মুখে শোনা যায়। লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণের পুত্র মেঘনাদের শক্তিশেল অস্ত্রে লক্ষ্মণ অচৈতন্য হয়ে পড়লে হনুমানের উপর আদেশ হয়েছিল বিশল্যকরণী গাছের শেকড় নিয়ে আসবার। কিন্তু হনুমান সেই গাছ চিনতে না পেরে যেখানে ওই গাছ জন্মায় সেই গোটা পাহাড়টাকেই উপড়ে আকাশপথে ফিরছিলেন। পাহাড়টা খুব ভারী ছিল তাই তিনি কিছুটা ফেলে ভার হালকা করেছিলেন। সেগুলোই হল ওই শিলাখণ্ড, ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, ঠিক মনে হয় যেন ওপর থেকে পড়েছে।
‘অভিযান’-এ গুলাবী চরিত্রের জন্য বোম্বের ওয়াহিদা রেহমানের কথা ভেবেছিলেন সত্যজিৎ। একটা ছবিতে তাঁকে দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল ওই ভূমিকার জন্য ওয়াহিদাই উপযুক্ত। সে সময় ওয়াহিদা রেহমান এক একটা ছবির জন্য পাচ্ছিলেন প্রায় আড়াই লাখ টাকা, সত্যজিতের একটা সম্পূর্ণ ছবির বাজেটই সে সময় ওই টাকা [কাঞ্চনজঙ্ঘাকে বাদ দিয়ে]। তবু ওয়াহিদাকে একটি চিঠি লেখা হল। অনিল চৌধুরি আর দুর্গাদাস মিত্র বোম্বে গিয়ে ওয়াহিদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললেন। তাঁদের অবাক করে ওয়াহিদা বললেন, ‘মি. রে তাঁকে যাই দিননা কেন, তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করবেন, সত্যজিতের পরিচালনায় ছবি করতে তিনি নিজেই ইচ্ছুক।’
১৯৬২-র মার্চের গোড়ার দিকে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র রঙিন ছবির প্রিন্ট দেখবার জন্য সত্যজিৎ যখন বোম্বাই গিয়েছিলেন, ওয়াহিদার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি ওয়াহিদাকে দৈনিক পাঁচ হাজার টাকার প্রস্তাব দিলেন, সেটাই তখন বম্বেতে তাঁর দৈনিক পারিশ্রমিক ছিল। সত্যজিৎ হিসেব করে দেখেছিলেন ওই ছবির জন্য ওয়াহিদাকে দিন দশেকের বেশি দরকার হবে না। সম্পূর্ণ ছবিটা তুলতে কিন্তু পঞ্চান্ন দিন লেগেছিল, ওই সময় পর্যন্ত ওটাই সত্যজিতের দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড়ো ছবি— চল্লিশ হাজার থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার ফুট শট নেওয়া হয়েছিল।
ওয়াহিদা রেহমান দশদিনের শুটিং-এ সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে তারকাজনিত কোনো উন্নাসিকতা ছিল না; সেটের বাইরে প্রসাধন ছাড়াই বেরুতেন।
যে দৃশ্যে গুলাবী নরসিংয়ের ঘরে এসেছে [তার আগের রাত্রে দুজনের মধ্যে ভালোবাসার মিলন হয়েছে], শক্ত মানুষটাকে শেষপর্যন্ত সে জয় করেছে, তার হাসিখুশি ভাব, নরসিংকে একটু উসকে দেওয়া, টুকরো টুকরো লোকসংগীত, একটুখানি নাচা, বিছানার চাদর ঝাড়তে ঝাড়তে ঠাকুরমার কথার ভেতর দিয়ে অতীতে ফিরে যাওয়া, অদ্ভুত নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন ওয়াহিদা রেহমান। গুলাবীর মনের ঘন ঘন পরিবর্তন এক স্মরণীয় অভিনয়। সত্যজিৎ সঙ্গত কারণেই এই ভূমিকায় অপেশাদার কাউকে নেবার ঝুঁকি নেননি।

১৯৬২-র ১১ জুন সত্যজিৎ ‘অভিযান’-এর এডিটিংয়ের কাজে অনেকটা এগিয়েছেন, নরসিং জোসেফের বোন নীলিমাকে ইস্কুলে পৌঁছে দিচ্ছে, এতটা হয়েছে। বিকেল চারটের সময় একজন ছুটে এসে খবর দিল ছবি বিশ্বাস মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সত্যজিৎ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই তো মাত্র কিছুদিন আগে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’য় ছবি বিশ্বাস ইন্দ্রনাথ রায় চৌধুরির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তার আগে ‘জলসাঘর’ আর ‘দেবী’-তেও তিনি সত্যজিতের ছবিতে ছিলেন। সব কাজ সেদিনের মতো বন্ধ করে দিলেন সত্যজিৎ।
‘অভিযান’ বক্স অফিস হিট করেছিল, কিন্তু তাতেও সত্যজিতের রক্ষে নেই। বুদ্ধিজীবীরা মন্তব্য করেছিলেন সত্যজিৎ তাঁর প্রতিভা থেকে সরে গিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছবি শুরু করেছেন।
এখানে একটা কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সত্যজিতের বেশ কিছু ছবিতে আয়নার ব্যবহার লক্ষণীয়। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’য়, ‘পথের পাঁচালী’তে, তবে সবচেয়ে প্রতীকি ব্যবহার মনে হয় ‘অভিযান’-এর প্রথম দৃশ্যে। গাড়ির ভাঙা আয়নায় ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে নরসিং-এর মুখ— তার মোহভঙ্গ, মানসিক বিপর্যয় যেন ভাঙা আয়নার ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।
তারপর ‘মহানগর’। ওই ছবি মুক্তি পাবার পর বাঙালিরাই সত্যজিৎকে কটূক্তি করতে ছাড়েননি। কাগজে কাগজেও বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। যেন, সত্যজিৎ যে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে, এটাই তাঁর অপরাধ। শোনা যায় জাতীয় পুরস্কারের জন্য ছবিটাকে যখন পাঠানো হয়েছিল, ওটা যাতে বিচারকদের সামনে ঠিকমত প্রদর্শিত না হয় তার জন্য প্রভাবশালী কিছু মানুষ অপচেষ্টা করেছিলেন।
যাহোক ১৯৬৪ সালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ওই ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছিলেন সত্যজিৎ। নিন্দুকের মুখে চুন-কালি পড়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ‘মহানগর’ সত্যজিতের প্রথম ছবি যা রাশিয়ায় মুক্তি লাভ করেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মস্কোয় পরবর্তী আন্তর্জাতিক ফিলম ফেস্টিভ্যালে তিনি বিচারকমণ্ডলীর সদস্য বা ‘জুরি’ নির্বাচিত হয়েছিলেন।
‘চিড়িয়াখানা’ কিন্তু সত্যজিতের নিজের নির্বাচিত কাহিনির ছবি নয়। বাংলা চলচ্চিত্রের তখন খুব দুর্দশা চলছে, হিন্দি ছবি আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলছে চলচ্চিত্র শিল্প। তাঁর সহকারীদের অনুরোধেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের একটি কাহিনি অবলম্বনে ওই ছবি তদারক করতে সম্মত হয়েছিলেন সত্যজিৎ। সহকারীদের সাহায্য করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যোমকেশের ভূমিকায় উত্তমকুমার অভিনয় করেছিলেন, তা সত্ত্বেও যাঁরা ওই ছবির পেছনে টাকা যোগাচ্ছিলেন, তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন সত্যজিৎকেই ওই ছবির পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। শেষপর্যন্ত তাঁকেই ছবিটা শেষ করতে হয়েছিল, যদিও ওটাকে তিনি নিজস্ব চিন্তাধারার বাইরে বলে মনে করেন। স্রষ্টার গভীর অনুভূতি বা আবেগ ছাড়া সৃষ্টি মহৎ হতে পারে না। সত্যজিৎ নিজের নির্বাচিত কাহিনি বা বিষয় নিয়ে যখন ছবি তোলেন তখন তার মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে যান, উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন সৃষ্টির আনন্দ, অপরের মর্জিমত ছবি করায় তিনি অনুপ্রেরণা পান না।
‘চিড়িয়াখানা’ গোয়েন্দা কাহিনির ওপর তোলা ছবি। সমাপ্তির মুখে উত্তমকুমার হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ফলে তিনমাসের জন্য শুটিং বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে ছবিটা কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছিল।
গোয়েন্দা ছবি হিসাবে ‘চিড়িয়াখানা’ দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিল। গোয়েন্দা কাহিনিতে যেমন সাসপেন্স বা উত্তেজনা থাকে তারও অভাব নেই। সত্যজিৎ কিন্তু ছবিটা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে পাঠাতে আগ্রহী হননি, তাঁর মনে হয়েছিল রহস্য কাহিনির যে মূল সূত্র, সেটা ‘চিড়িয়াখানা’য় অনেকটা শব্দের অর্থের মধ্যে নিহিত, যেটা অনুবাদযোগ্য নয়, ফলে বিদেশি দর্শক ছবিটা ভালোভাবে নাও নিতে পারেন।
‘চিড়িয়াখানা’ নভেম্বরের গোড়া পর্যন্ত ভালো চলেছিল। তারপরই কলকাতা আর পশ্চিমবাংলায় নেমে এসেছিল ঘোর রাজনৈতিক অরাজকতা, দুঃস্বপ্নের রাত। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর ডিসেম্বরের কথা মনে করলে এখনও গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, কি অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে দিনগুলি। বেশির ভাগ সিনেমা হলেই রাতেই প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সন্ধের পর মানুষ পথে বেরুতে সাহস করত না। খুনোখুনির রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গ তখন উত্তাল। সেই প্রথম কংগ্রেস সরকারকে হঠিয়ে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার। এই ডামাডোলে ‘চিড়িয়াখানা’কে উঠিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।
‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ছবিতে টাকার মুখ দেখেছিলেন সত্যজিৎ, একটানা সাড়ে আট মাস চলেছিল— বাংলা ছবির এটা একটা রেকর্ড।
‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ করার আগে ‘পথের পাঁচালী’র মতো আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন সত্যজিৎ। চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে সবকিছু তৈরি শুধু ছবি আরম্ভ করলেই হয়, কিন্তু চার লাখ টাকা দরকার। ফিলম ফাইনান্স কর্পোরেশন থেকে টাকা পাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। সত্যজিতের পরিকল্পনা ছিল ১৯৬৭-র নভেম্বর থেকে শুটিং শুরু করবেন। কিন্তু কোনদিক থেকে আলোর পথ দেখতে পেলেন না তিনি। বছর কয়েক আগে হিন্দি ছবির একজন বিখ্যাত অভিনেতা-প্রযোজক তাঁকে বলেছিলেন যে কোনো ছবিই তিনি করুন না কেন, যা টাকা লাগে কুছ পরোয়া নেই, তিনি দেবেন। এমনকি কোনো শর্ত থাকবে না, তাও বলেছিলেন। এ যেন প্রায় ব্ল্যাঙ্ক চেক দেবার প্রতিশ্রুতি।
অগত্যা বোম্বে গেলেন সত্যজিৎ, তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। সেই অভিনেতা-প্রযোজক টাকার ব্যাপারে গররাজি হলেন না কিন্তু একটা শর্ত জুড়ে দিলেন। বোম্বের এক অভিনেতা, তাঁর ভাই আর বাবাকে গুপী গাইনে তিনটি প্রধান চরিত্রে সুযোগ দিতে হবে। সত্যজিৎ সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলেন সেই প্রস্তাব। রবি ঘোষকে বাঘার চরিত্রে আর তপেন চট্টোপাধ্যায়কে গুপীর ভূমিকায় তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলেন, অর্থের জন্য সংকল্প থেকে সরে আসার মানুষ ছিলেন না তিনি। ওই আর্থিক সংকটের মুখে অমন লোভনীয় প্রস্তাব ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতো বুকের পাটা কজন পরিচালকের আছে জানিনা। এ ধরনের নানান ঘটনা থেকে সত্যজিতের চরিত্র আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, নিজের আদর্শের সঙ্গে আপোস করার মতো হীনবল মানুষ তিনি নন।

আশ্চর্যভাবে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের বড়দিনের আগের দিন চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং পরিবেশক শ্রীনেপাল দত্ত সত্যজিতের সঙ্গে দেখা করলেন। ছবির মোট বাজেট চার লাখের অর্ধেক টাকা তিনি দেবেন এই প্রস্তাব তিনি দিলেন, এ কথাও বললেন যে, তাঁর পরিচিত আরেকজন বাকি দু-লাখ টাকা দিতে রাজি আছেন। আসলে নেপাল দত্ত তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়সের তরুণী পুত্রবধূ পূর্ণিমার প্রভাবেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পূর্ণিমা ছিলেন সত্যজিতের একজন গুণমুগ্ধা।
১৯৬২ সালে ‘অভিযান’-এর শেষদিকের কয়েকটি দৃশ্য তুলবার জন্য সত্যজিৎ যখন রাজস্থানে গিয়েছিলেন, তখন ভেবেছিলেন গুপী গাইনের কিছু কিছু ঘটনাবহুল শটের পক্ষে ওখানকার লোকেশন চমৎকার হবে। জয়সলমীরই সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল।
‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ আমাদের দেশে প্রথম ফ্যান্টাসি ছবি বললে বোধ হয় ভুল হবে না। দারুণ হইচই ফেলেছিল ছবিটা এবং চলেছিল একটানা প্রায় সাড়ে আট মাস। শুধুমাত্র সংগীত পরিচালনায় সত্যজিৎ যে কত বড়ো, তার প্রমাণ ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’। উনিশটি গান আছে এই ছবিতে, রচনা, সুর ও সংগীত পরিচালনা সব কৃতিত্ব ওই একটি মানুষের।
পিতামহ উপেন্দ্রকিশোরের লেখা এই মজার কাহিনি নিয়ে একটা ছবি করার কথা কিছুদিন থেকেই সত্যজিতের মাথায় ঘুরছিল। রাজস্থানের জয়সলমিরে হল্লার দৃশ্য তোলা হয়েছিল। ‘সোনার কেল্লা’-তেও এই জয়সলমীর ছিল। আসল কাহিনিতে আছে অশ্ববাহিনী, কিন্তু রাজস্থানে ঘোড়া কোথায়? তাই জোগাড় করা হল উট, একটা দুটো নয়, হাজার উট, তাদের চালক, জাজিম-ঝালর। তাছাড়া হাজার সৈন্যের সাজপোশাক, মাথার পাগড়ি, পায়ের নাগরা, ঢাল, তলোয়ার, বল্লম— সে এক এলাহি কাণ্ড।
সত্যজিৎ ফাঁকির সঙ্গে আপোস করেন না, সবকিছু নিখুঁত হওয়া চাই। তবু কিন্তু কম খরচের মধ্যে তিনি ছবি করেন বলে তাঁর সুনাম আছে। সারা দুনিয়ার লোক জানে যে সত্যজিৎ মিতব্যয়ী পরিচালক।
কোনোদিন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াননি এমনদের দিয়ে তিনি ছবি করিয়েছেন আর ভাবীকালে তাঁরাই বিখ্যাত চিত্রতারকা হয়েছেন। শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সৌমিত্রকে ছায়াছবিতে তিনিই প্রথম এনেছিলেন। তুলসী চক্রবতীকে সবাই ভাঁড়ের ভূমিকাতেই দেখতেই অভ্যস্ত ছিল, ‘পরশপাথরে’ তাঁকে দিয়ে কি অনবদ্য অভিনয়ই না তিনি করিয়ে নিয়েছেন। সত্যজিৎ সবাইকে সুযোগ দেন, তাদের প্রতিভা মেলে ধরতে সাহায্য করেন, এ ব্যাপারে তাঁর কোনো সংস্কার নেই। সৌমিত্রকে সত্যজিৎ ‘অপুর সংসার’-এর জন্য মনোনীত না করলে তিনি হয়তো মঞ্চ অভিনেতা হয়েই থাকতেন, কোনোদিন স্টার হবার সুযোগ পেতেন না।
রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত এঁরা সবাই সত্যজিতের ছবিতেই তাঁদের নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন। রবি ঘোষ ‘অভিযান’-এ নামার আগে একটা মাত্র ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। সত্যজিতের পরিচালনায় তিনি এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে নিজের দৃশ্য ছাড়াও অন্য দৃশ্যে এসে সত্যজিতের কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখতেন।
জহর রায় সত্যজিৎকে ‘আপনি’ করে বলতেন, সত্যজিৎ একদিন মৃদু আপত্তি করে বলেছিলেন, ‘আপনি age-এ বড়ো, আমাকে আপনি করে বলবেন না।’ জহর রায় স্বভাবসুলভ কৌতুকে জবাব দিয়েছিলেন, ‘আমি age-য়ে বড়ো আপনি ইমেজে বড়ো।’
করুণা ব্যানার্জী, তপেন চট্টোপাধ্যায়, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি সত্যজিতের আবিষ্কার।
১৯৬৬ সালে ‘নায়ক-এর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আসার মুখেই একটা ছবি করার কথা সত্যজিতের মনে হয়েছিল। ছোটোদের জন্য গল্পটা তিনি লিখেছিলেন, বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনি বা ফ্যান্টাসি বলা যেতে পারে। ভিনগ্রহ থেকে একটা মহাকাশযান ভুল করে পৃথিবীতে নেমেছে। সেই মহাকাশযানের আরোহীর কাছে অদ্ভুত একটা কাচ আছে যা দিয়ে আশ্চর্য সব জিনিস দেখা যায়। সত্যজিৎ নানান ঘটনার ভেতর দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন ভিনগ্রহবাসী সেই লোকটি দানব বা তেমন কিছু নয়, পৃথিবীর মানুষের সে মঙ্গলই চায়।
১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক তরুণ প্রযোজক২ ভারতে এসে সত্যজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সত্যজিৎ যে ভিনগ্রহ নিয়ে একটা ছবি করার পরিকল্পনা করছেন সেটা তাঁর কানে গিয়েছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞানভিত্তিক লেখক আর্থার ক্লার্কের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক আছে, সত্যজিৎ আবার ক্লার্কের রচনা সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল।
বিদেশি প্রযোজক জানালেন ‘ভিনদেশী’র [The Alien] একটা আন্তর্জাতিক বাজার পাওয়া যাবে। সে সময় বাংলা চলচ্চিত্রের ঘোর সংকট চলছিল তাই সত্যজিৎ সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি হিসেব করে দেখলেন ওই ছবির একমাত্র টেকনিক্যাল খুঁটিনাটির জন্যই তাঁর একটা ছবিতে যা খরচ পড়ে তার চাইতে লাখ দুয়েকের মতো বেশি পড়বে। সেই প্রযোজক তাঁকে নিউ ইয়র্ক, হলিউড এমনকি লন্ডনেও নিয়ে গেলেন। বিলাসবহুল হোটেলে এই প্রথম থাকলেন সত্যজিৎ।
তিন সপ্তাহ ঝটিকা সফরের পর স্থির হল কলম্বিয়ার কিছু ধনী ব্যবসায়ী তাঁর ‘ভিনদেশী’ চিত্রায়িত করার জন্য টাকা যোগাবেন। এটাও ঠিক হল যে, পুরো ছবিটাই শান্তিনিকেতনে তোলা হবে, আকাশযান থেকে শুরু করে সেটের সবকিছু ভারতের স্টুডিয়োতেই তৈরি হবে। ছবি হবে রঙিন।
সত্যজিতের সামনে এক বিরাট সুযোগ। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, অপ্রিয় জটিলতা ছবির কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে প্রথম শুটিং হবার কথা ছিল, সেটা পিছিয়ে দিন ঠিক হল ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে। তারপর আবার জটিলতা, ছবি আরম্ভই করা গেল না।
যখন ওই ব্যাপারে কথাবার্তা চলছিল, সত্যজিৎ চিত্রনাট্য আরও মেজে ঘষে সংলাপের অনেক অদলবদল করেছিলেন। ওই কাহিনিতে সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল তা হল অন্যান্য বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনির মতো ওকে ভিনগ্রহবাসীকে পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক হিসাবে চিত্রিত করা হয়নি। সে ছিল নিরস্ত্র, একটা আশ্চর্য মানসিক শক্তিই তার প্রধান অস্ত্র। নানারকম অদ্ভুত ঘটনার ভেতর দিয়ে কাহিনির পরিসমাপ্তি, একটা চমৎকার ফ্যান্টাসি ছবির পক্ষে দারুণ উপযোগী।
ভিনগ্রহবাসীর চেহারা কেমন হবে তার একটা স্কেচ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ, এমনকি সংগীত সৃষ্টিও হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন রঙের ভেতর দিয়ে পৃথিবীর মানুষের ভেতরটা বা আসল চেহারা স্বচ্ছ হয়ে উঠবে ভিনগ্রহবাসীর কাছে। আমাদের দুর্ভাগ্য ওই পরিকল্পনা বাক্সবন্দী হয়েই রইল।
‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ জীবন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার আরেকটি ছবি। শহরের কয়েকজন যুবক মনের ক্লান্তি দূর করতে অরণ্যে এল, তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি আর মানসিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে বোধ হয় গোটা সমাজের একটা চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন পরিচালক। তরুণী বিধবার অপূর্ব জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষা করুণার উদ্রেক করে।
সত্যজিৎ রায় জীবনসমীক্ষার মাধ্যমে যেন বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে, অরণ্যের আবেষ্টনেও মানুষের যন্ত্রণার মুক্তি নেই। কামনা বাসনা মানুষকে সবসময় যেন আদিম অরণ্যেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই কলকাতার খেলোয়াড় হরি সুযোগ পেয়েই আদিবাসী তরুণী দুলির সঙ্গে মিলিত হয়। স্বামীহারা তরুণী জয়া এক-গা গয়না পরে অপরিচিত যুবকের সামনে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। তবু ছবিটার বলগা ধরে রেখেছেন সত্যজিৎ, আলগা হতে দেননি, তাই শালীনতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি— এটাই সত্যজিতের ছবির মহৎ গুণ।
‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ কলকাতার সমসাময়িক কালের অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার ছবি। যুগের যন্ত্রণা যেন ক্যানভাসে এঁকে সবার সামনে তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আলোড়ন সত্ত্বেও যে শিল্পের জন্ম, তা হল স্বতঃস্ফূর্ত। সত্যজিতের ছবি সম্বন্ধেও সেই মন্তব্য প্রযোজ্য।
ভারতে সত্যজিতের ছবি সম্বন্ধে একটা প্রধান সমালোচনার বিষয় হল তাঁর ছবিতে সমসাময়িক কালের প্রতিফলন নেই। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অবস্থা তিনি যেন সযত্নে এড়িয়ে চলেন। অস্বীকার করা যায় না, ১৯৭০ পর্যন্ত সত্যজিৎ রাজনীতি থেকে দূরে সরে থেকেছেন। ১৯৬৪ সালের গোড়া থেকেই পশ্চিমবাংলা রাজনৈতিক টালবাহানার শিকার হয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র ১৯৬৯ সাল থেকেই বাম আর ডান এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে খুনোখুনি রাজনীতির আসল সূচনা। এটা এখন পশ্চিমবাংলায় দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ সত্যজিতের ১৯৭০ সালের তোলা ছবি, অর্থাৎ দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন তুঙ্গে। সমসাময়িক কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে গেছেন সত্যজিৎ। কলকাতার রাজপথে নগ্ন হিংস্রতার চিত্র তুলে ধরেছেন।
রাজনৈতিক হত্যা কলকাতার রাজপথে যখন দৈনন্দিন ঘটনা তখনকার ছবি হল ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’। মাত্র তিন চারদিনের ঘটনা নিয়ে ছবি, তারই মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতা, পারিবারিক জীবনে তার প্রতিক্রিয়া এবং বেকার সমস্যার ভয়াবহতা আমাদের স্পর্শ করে। বাঙালি যুবকদের বর্তমান সংকট বাবার মৃত্যুর ভেতর দিয়ে দুই ভাইয়ের আচরণে ফুটে উঠেছে। একটা বিশাল শোভাযাত্রা ওই ছবিতে দেখানো হয়েছে, ওটা কিন্তু সত্যিকার রাজনৈতিক শোভাযাত্রা, খুব উঁচু এক বাড়ির ছাদ থেকে তুলেছিলেন সত্যজিৎ।
ছবির এক দৃশ্যে নায়ক চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছে। তাকে প্রশ্ন করা হল, ‘গত দশকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি?’ নায়ক সিদ্ধার্থ জবাব দেয়, ‘ভিয়েতনামের যুদ্ধ।’ তাকে শেষ প্রশ্ন করা হল, ‘তুমি কি কমিউনিস্ট?’
ছোটো ভাই টুনু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বীতস্পৃহ হয়ে নকশালপন্থী হয়ে ওঠে, যারা বিশ্বাস করে রক্তাক্ত আন্দোলনই সত্যিকার মুক্তির পথ। সত্যজিতের অনেক ছবির মতোই এখানেও এক মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। সিদ্ধার্থ শেষপর্যন্ত কম মাইনের একটা চাকরি বেছে নেয় কারণ তাতে স্বাধীনতা আছে। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’-কে এককথায় সমসাময়িক রাজনৈতিক কোন্দল ও অস্থিরতার এক নিখুঁত ছবি বলা যায়।
‘প্রতিদ্বন্দ্বী’তে আমরা সত্যজিতের অসামান্য পরিমিতি বোধের পরিচয় পাই, দেখা পাই তাঁর অনন্য শিল্পকর্মের। একটি পরিচিত পাখির ডাককে সত্যজিৎ চমৎকার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছেন।
সত্যজিতের ছবি বক্স অফিস হিট করে না বলে একটা দুর্নাম আছে। তার একটাই কিন্তু কারণ, সাধারণ মানুষ যে উদ্দাম, হুল্লোড়, নাচ-গান, বোম্বে মার্কা মারদাঙ্গা ছবি পছন্দ করে, সত্যজিতের ছবিতে তার দেখা পাওয়া যাবে না। তাঁর ছবি রিয়েলিস্টিক, বাস্তববাদী। মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি সেখানে ফুটে উঠেছে। আসলে আমাদের রুচিরই অধঃপতন ঘটেছে নইলে বাজারে ‘পথের পাঁচালী’র লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ের যা না বিক্রি তার চাইতে সস্তায় বাজিমাত করা যেসব বই বেরুচ্ছে তার বিক্রি অনেক বেশি কেন? সেসব বই কেনার জন্য লাইন পড়ে যায়। মুসোলিনি একবার বলেছিলেন, ‘ভালো বই আলমারিতে ধুলোয় মলিন হয় আর বাজে বই নিয়ে পাঠকের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।’ কথাটা কিন্তু খাঁটি।
তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, দেশ থেকে বিদেশে সত্যজিতের ছবি মর্যাদা পেয়েছে বেশি, টাকাও এনেছে যথেষ্ট। অনেক সমালোচক বলেন, ‘সত্যজিতের ছবি বড়ো ধীরগতি, বিরক্তিজনক।’ ‘পথের পাঁচালী’ সম্বন্ধেও আমেরিকার কিছু সমালোচক প্রথমে সেই কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই ছবিই দীর্ঘ সাত মাস ধরে চলে মার্কিন মুলুকে হইচই ফেলেছিল। পল গ্রিম তো বলেই ছিলেন, ‘সত্যজিৎ আমেরিকায় যতটা, ভারতবর্ষে অতটা বিখ্যাত নন।’
‘সীমাবদ্ধ’-এ সত্যজিৎ উচ্চবেতনভোগী বিজনেস এগজিকিউটিভদের জীবনের সীমাবদ্ধতারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সোপানগুলি পেরিয়ে এসে নায়কের মনে হল সে যেন ক্লান্ত, নিঃশেষিত।
জীবনে কখনো অভিনয় করেননি এমন সব মানুষকে দিয়ে অসাধারণ অভিনয়ে করিয়ে নেবার দায়িত্ব বোধ হয় একমাত্র সত্যজিতেরই, একবার দু-বার নয়, বেশ কয়েকবারই এটা প্রমাণ হয়েছে।
সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁর নিজেরই কি কোনো অভিজ্ঞতা ছিল? কাজ করতে নেমে অনভিজ্ঞতার দরুণ কত সমস্যা আর অসুবিধের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে, কিন্তু উদ্যমী পুরুষের ভাগ্য সহায়, শেষপর্যন্ত তাঁর দুর্দম মনোবলই জয় হয়েছে, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন সাফল্যের মালা।
‘জনঅরণ্য’-এ সত্যজিৎ আঙুল দিয়ে সমাজের পঙ্কিলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি ছাত্রের ভবিষ্যৎ যেখানে নির্ভর করছে, সেখানে পরীক্ষার খাতা কিভাবে দেখা হয়, কিভাবে একটি বুদ্ধিদীপ্ত তরুণের আশা-আকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, তার নগ্ন চিত্র আমাদের দেখিয়েছেন পরিচালক। ব্যবসা করতে গিয়ে সেই আদর্শবাদী তরুণটি কি দেখল? সৎ পথে জীবিকা অর্জন করা যায় না, ভালো জিনিস সরবরাহ করলেও অর্ডার পাওয়া যায় না, যদি না যে অফিসারের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত তার বিকৃত রুচির মদত দেওয়া যায়। তাই করতে গিয়েও ছেলেটি দেখা গেল বন্ধুর বোনের, সমাজ যাকে নামিয়ে এনেছে অন্ধকার জগতে। সত্যজিতের এ ছবি যেন সমাজের প্রতি কশাঘাত, কালো মানুষদের চিনিয়ে দেওয়া।
‘মহানগর’ বোধ হয় সত্যজিতের প্রথম ছবি যেখানে মধ্যবিত্ত সমাজের সমসাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে। ‘মহানগর’-কে শুধু কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি বললে ভুল হবে, সারা ভারতের সব মহানগরেই এই একই চিত্র, একই সংকট— শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে বেকার সমস্যাজনিত অসহায় অবস্থা। পরিবারের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের যে আমূল পরিবর্তন ঘটছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই ছবিতে। রক্ষণশীল শ্বশুর পুত্রবধূর চাকরি করার প্রবল বিরোধিতা করেন, আবার সেই মেয়েই যখন উপার্জনের টাকায় শ্বশুরের জন্য জিনিস কিনে আনে, তখন তাঁর মনের পরিবর্তন হয়। শাশুড়ি পুত্রবধূর আপিসের ভাত বেড়ে নেন। স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক, কিন্তু সেও আপিসযাত্রিনী স্ত্রীর ঠোঁটে লিপস্টিকের প্রলেপ দেখে বিরক্ত হয়, রেস্তোরাঁয় একজনের সঙ্গে স্ত্রীকে হাসি গল্প করতে দেখে ঈর্ষায় ভোগে। মধ্যবিত্ত জীবনের যে অস্থিরতা, সমস্যা, সত্যজিৎ দেখিয়েছেন, তা সর্বভারতীয় সমস্যা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
সমস্যা জর্জরিত মধ্যবিত্ত সমাজের সহস্র জটিলতা সত্ত্বেও সত্যজিৎ ছবিকে হতাশায় শেষ করেননি, চাকুরিহীন স্বামী-স্ত্রী হাত ধরাধরি করে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছে, তার ভেতর দিয়ে আশাবাদী রূপটা ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণ শিল্পীর দক্ষতায়। সত্যজিৎ যে চলচ্চিত্রের কবি।
‘মহানগর’ নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় ই. এম. ফরস্টারের ‘এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া’ ছবি করার পরিকল্পনা মাথায় এসেছিল সত্যজিতের। এমনকি মিসেস মূরের ভূমিকায় ডেম সিবিল থর্নডাইকের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। সে বছর গরমের সময় সত্যজিৎ লন্ডনে গিয়েছিলেন, ইচ্ছে ছিল ফরস্টারের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু সত্যজিৎ যখন ওখানে পৌঁছুলেন, ফরস্টার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ফলে আর কথাবার্তা হল না। ১৯৬৫ সালের শরৎকালের গোড়ার দিকে কেম্ব্রিজে শেষপর্যন্ত যখন তাঁদের দেখা হল, ফরস্টারের শরীরের ভঙ্গুর অবস্থা দেখে ও নিয়ে আলোচনা করতে সত্যজিতের মন আর চাইল না। ফরস্টার যে তাঁর বই নিয়ে ছবি করার ঘোর বিরোধী তা সত্যজিতের কিন্তু জানা ছিল।
সেই ছবিই ডেভিড লীন করলেন প্রায় দু-দশক পরে, ভিক্টর ব্যানার্জি সেই ছবিতে ডা. আজিজের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি কুড়িয়েছেন। ‘ঘরে বাইরে’ ছবিতেও তাঁর অভিনয় মনে রাখার মতো। সত্যজিৎ তাঁকে দিয়ে কি অভিনয়টাই না করিয়ে নিয়েছেন।
সত্যজিৎ রায়ের ছবির আলোচনা এ বইয়ের বিষয়বস্তু নয়, স্রষ্টা সত্যজিৎই আসল উপজীব্য, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই তাঁর ছবির কথা আপনা থেকে এসে যায়, ঘুরে ফিরে একই ছবির পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটাও এড়ানো যায় না, কারণ সীমা বেঁধে কিংবা নির্দিষ্ট এলাকায় ধরে রাখা যায় না তাঁর চিত্র কথা। সত্যজিতের অন্তর্দৃষ্টি গভীর, ব্যাপক, তাই তাঁর সৃষ্টির গভীরতায় ডুব দিয়ে কিছু মণিমাণিক্য আহরণ করতে গেলে তা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়বেই। সেই কারণেই তাঁর চিত্র সম্বন্ধে একই কথা ঘুরে ফিরে এসেছে, এক জায়গায় তাকে ধরে রাখা সম্ভব হয় নি।
‘পরশপাথর’ আর্থিক সফলতার মুখ দেখেনি, কিন্তু সত্যজিৎ ওই ছবিতে তুলসী চক্রবর্তীকে দিয়ে যে অসামান্য অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন সেটা বোধ হয় তাঁর পক্ষেই সম্ভব। পরেশ দত্ত স্বপ্ন দেখছে ইংরেজ নামি পুরুষদের মতো তাঁর ব্রোঞ্জের মূর্তিও পাথরের বেদির ওপর স্থাপিত হয়েছে। ব্যঙ্গাত্মক, সূক্ষ্ম, হুলের রসে সম্পৃক্ত এই ছবি সাধারণ দর্শকের কাছে হয়তো দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে সূক্ষ্ম রস গ্রহণ করার মতো মানসিকতা আমাদের নেই।
‘চারুলতা’ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবে এটা বিদেশের অনেকেই আশা করেছিলেন। ইংলন্ডের সানডে টাইমস-এর পিটার গ্রেহাম আশা করেছিলেন ‘চারুলতা’ শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। তবে ছবিটা সত্যজিৎকে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান দিয়েছিল। ‘চারুলতা’ নিঃসন্দেহে সত্যজিতের একটি শ্রেষ্ঠ ছবি— এখানে আমরা দেখতে পাই জীবনের প্রতিচ্ছায়া।
‘চারুলতা’র প্রথম চিত্রনাট্য অনেক আগেই, ১৯৫৮ সালে লিখেছিলেন সত্যজিৎ, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী বিশেষ করে চারুলতার ভূমিকায় মনের মতো কাউকে না পাওয়ায় তিনি আর ওটা নিয়ে এগোননি। সত্যজিতের জীবনে এমন ঘটনা একাধিকবারই ঘটেছে। একটা ছবি তৈরি করার পরিকল্পনার পর বেশ কয়েক বছর পরে তিনি সেই ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। ১৯৬১-র মে মাসে ‘তিন কন্যা’ মুক্তির পরই তিনি ‘মহানগর’-এ হাত দেবেন ঠিক করেছিলেন। সেখানেও নায়িকার ভূমিকায় মনোমত কাউকে না পাওয়ায় দু-বছর ওটা তিনি ফেলে রেখেছিলেন আর শেষ করেছিলেন দুটো ছবির কাজ— ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ আর ‘অভিযান’।
‘মহানগর’-এর নায়িকা আরতির ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায়কে সত্যজিতের খুব পছন্দ হয়েছিল, ‘চারুলতা’-তেও তিনি তাঁকেই নির্বাচিত করেছিলেন। মাধবী সত্যজিতের বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিলেন, চরিত্র দুটিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলে।
‘চারুলতা’ সম্বন্ধে পিটার গ্রেহাম আর এরিক শার্টার বলেছেন, ‘বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের কোলাহল, ধর্ম ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে হঠাৎ ভারতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ধীর, স্থির, শান্ত সেই স্বর অথচ অর্থপূর্ণ।’
‘আমরা কয়েকটি ঈপ্সিত, শান্ত মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছি। রমণীর নগ্নতা এখানে দেখবার চেষ্টা হয়নি। নিবিড় আলিঙ্গনের দৃশ্য বড়ো করে দেখাবার প্রচেষ্টাও হয়নি। তার বদলে আমরা পেলাম একটি জীবনের প্রতিরূপ। সেই জাতির রুচি-স্নিগ্ধ নম্রতা ও শোভনতাবোধের ছবি।’
সত্যজিতের সব ছবি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। ‘অশনি সঙ্কেত’, ‘শতরঞ্জ কি খিলাড়ী’ কোনোটাই তা বলে বাদ দেওয়া যায় না।
‘অশনি সংকেত’ সত্যজিতের পরবর্তীকালের নিশ্চয়ই একটি শ্রেষ্ঠ ছবি। গ্রাম্যজীবনের সরলতার দৃশ্য ‘পথের পাঁচালী’র মতো এখানেও ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে। অনেকটা ‘পথের পাঁচালী’র ধরনের ছবি বললেও বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।
মানবতাবোধ গল্পের প্রতি সত্যজিতের দুর্বলতার কথা এখন আর অজানা নেই। ‘পথের পাঁচালী’র লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি কাহিনি নিয়ে এই ছবি করেছেন সত্যজিৎ। সুন্দর, সরল গ্রাম্য পরিবেশে কেমন করে দুর্ভিক্ষের কালো মেঘ এসে এক ফুৎকারে মানুষের জীবনে ওলোটপালোট করে দিল, খিদের তাড়নায় সৎ মানুষগুলো লুঠেরা হয়ে উঠল, ঘরের বউ নিজের দেহ বিকিয়ে দিল, তাই নিয়েই এই ছবি— বিয়াল্লিশের মন্বন্তরের বাস্তব কাহিনির চিত্ররূপ। ছবির শেষে ভুখা মিছিল জানিয়ে দিচ্ছে তাদের পেছন পেছন আসছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।
ছবির মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো চটুল কথা আর হাসি একটা রিলিফ। গঙ্গাচরণকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল সিঙ্গাপুর কোথায়, গম্ভীরমুখে সে জবাব দিল মেদিনীপুরের কাছে টাছে হবে। আমরা তার অজ্ঞতায় হাসলেও তাকে করুণা করি না, গ্রাম্যজীবনের সরলতার মতোই এটা মেনে নিই।
সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় কি ভুলবার! ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ অতিথিকে গঙ্গাচরণের বউ যখন হাঁড়ি উজাড় করে খাওয়াচ্ছে, আর সে সত্যিকার উপোসী মানুষের মতোই গোগ্রাসে খাচ্ছে, একবারও কি মনে হয়েছে আমরা অভিনয় দেখছি। ‘অশনি সংকেত’ সত্যজিৎ রায়কে দেশ-বিদেশ থেকে মিছিমিছিই সোনা এনে দেয়নি।
‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ী’তে প্রত্যেকের অভিনয় মনে রাখার মতো। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের গজল, ‘যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী, তব হাম আদমপর কেয়াগুজরী’— গুণ্ডার সর্দার আমজাদ খানকে দিয়ে কি অভিনয়টাই না করিয়েছেন সত্যজিৎ। যে সৃষ্টি করে বিভীষিকা তাকে দিয়ে করুণ রসের চরিত্র, বাহবা দিতে হয়।
আরমীজজ বেগমের ঘরে পরপুরুষের প্রবেশের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মীরবেশী সঞ্জীবকুমারের প্রাণখোলা হাসি, সে কি ভুলবার!
‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ী’ প্রেমচন্দের একটি দশ পাতার গল্প অবলম্বনে তোলা। দুই বিলাসী ওমরাহ মির্জা আর মীর দাবা খেলায় এতই মত্ত যে বেগমদের দিকে ফিরে তাকাবার পর্যন্ত ফুরসৎ তাঁদের নেই, লখনউয়ের নবাব ওয়াজেদ আলি কোম্পানির রাজনৈতিক দাবার চালে মাত হতে চলেছেন সেদিকেও হুঁশ নেই তাঁদের। আসলে দাবা খেলাটা এখানে প্রতীক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেমন করে রাজনৈতিক দাবার চালে এক এক করে দেশীয় রাজ্য কুক্ষিগত করছে, আর ভারতের মানুষ প্রায় বিনা যুদ্ধে, বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিচ্ছে তাই হল ছবির মর্মার্থ। ওমরাহ দুজন অলস, নিষ্কর্মা, যেন ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি।
জেনারেল আউট্রামের ভূমিকায় রিচার্ড অ্যাটেনবরোর অভিনয় সংযত এবং চরিত্রোপযোগী। একমাত্র যা খারাপ লাগে তা হল তাঁর ইংরেজি কথাবার্তার হিন্দি ডাবিং, ওটা খুব ডিসটার্ব করেছে চরিত্রকে।

সৈয়দ জাফরি, শাবানা আজমি প্রত্যেকের অভিনয় সংযত ও সুন্দর। মীর্জার বেগম, এমনকি শাবানার খাস নোকরানি আর ওই বালকটির পর্যন্ত অভিনয়ে খুঁত নেই।
সঞ্জীবকুমারের সেই কৌতুক হাসির কথা আগেই বলা হয়েছে। অনবদ্য অভিনয়।
সত্যজিতের এটা প্রথম ঐতিহাসিক ছবি। সেই আমলের পোশাক, আসবাবপত্র, আদবকায়দা, নিখুঁতভাবে তিনি দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ছবিটার মধ্যে ব্যঙ্গ আর কৌতুকের সঙ্গে করুণ রসের যে মিশ্রণ তা আমাদের অভিভূত করে। ছবি শেষ হবার পর বুকের ভেতর থেকে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। নিদারুণ ঐতিহাসিক সত্য আমাদের বিষণ্ণ করে।
‘সোনার কেল্লা’, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’, সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত গোয়েন্দা ফেলুদার কাহিনি নিয়ে ছবি। এগুলোকে এন্টারটেনিং পিকচার বলাই বোধ হয় ভালো। তবে ছবি দুটোর ট্রিটমেন্ট এত সুন্দর যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে দেখতে হয়। যেমন দৃশ্য তেমন সাসপেন্স। দৃশ্যের ব্যাপারে সত্যজিতের তুলনা নেই। ‘সোনার কেল্লা’-র নৈসর্গিক দৃশ্য আমাদের মনে গাঁথা হয়ে থাকে। ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ কাশী শহরটাকেই যেন ছবির পর্দায় তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ। সেই সরু গলি, কাশীর বিখ্যাত ষাঁড়, দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশাল গঙ্গা— পুণ্যার্থীদের কাশী দর্শন হয়ে যায়। আর বজরায় চেপে মগনলাল মেঘরাজের ঘাটে আসা মনে রাখার মতো। জটায়ুর দু-পাশে ছোরা বেঁধার দৃশ্য শিহরণ জাগায়। আট বছরের রিকুর সঙ্গে ফেলুর হেঁয়ালিতে কথা বেশ মজার। হেঁয়ালি সত্যজিৎ রায়ের খুব প্রিয়, ফেলুদা ছাড়া অন্য কাহিনিতেও সুযোগ পেলে নানারকম ধাঁধা বা হেঁয়ালি ঢুকিয়ে দিয়েছেন।
‘সোনার কেল্লা’ এবং ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ দুটো ছবিই দর্শক টেনেছে এবং দুটোই দেশ-বিদেশ থেকে শিরোপা এনে দিয়েছে সত্যজিৎকে।
ফেলুদার ছবিতেই জটায়ু রূপে সন্তোষ দত্তকে আমরা পেয়েছি, এই ছবিই তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে। জটায়ু ছাড়া ফেলুদার কাহিনি বা ছবি ভাবাই যায় না। সত্যজিৎ রায় রহস্যধর্মী কাহিনিতে যেমন মুনসিয়ানা দেখান, গরম কেকের মতো বিক্রি হয় তাঁর বই, তেমন ছবিতেও তিনি উপহার দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব স্টাইল, উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি বেঁধে রাখেন দর্শককে।
‘হীরক রাজার দেশে’ ছবিটা গুপী গাইনেরই শেষাংশ বলা চলে, সত্যজিৎ নিজেই কাহিনি লিখেছেন। শুণ্ডী আর হল্লার রাজার দুই মেয়েকে বিয়ে করেছে গুপী আর বাঘা। হীরক রাজার আমন্ত্রণে সে রাজ্যে যাবার পরই শুরু হল যত সব আজব কাণ্ডকারখানা। শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি বিবেচিত হয়ে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছিল এই ছবি। ছোটো বড়ো সবার সমানভাবে উপভোগ করার মতো একখানা ছবি।
‘ঘরে বাইরে’ সত্যজিতের বহুদিনের বাসনার ছবি। এই ছবিতে ভিক্টর ব্যানার্জিকে দিয়ে বিপরীতধর্মী চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ওই ভূমিকাটা দিয়ে ভিক্টরকে তিনি সন্দীপের ভূমিকা দিতে পারতেন। অন্য যে কোনো পরিচালক তাই করতেন। কিন্তু সত্যজিৎ বাঁধা ছক ধরে চলেন না, তিনি সবসময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে মেতে আছেন, নতুন সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে, ‘ঘরে বাইরে’র প্রথম চিত্রনাট্য সত্যজিৎ রচনা করেছিলেন সেই যখন ডি. জে কীমারে চাকরি করতেন তখন।
বনেদি পরিবারের তরুণ, উদারপন্থী জমিদার নিখিলেশ তাঁদের বংশের চিরকালের প্রথা ভেঙে স্ত্রী বিমলাকে ইংরেজি লেখাপড়ায়, গানে আধুনিকা করে তুলল। তারপর যেভাবে তারা সংস্কারের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল সে দৃশ্য অমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করা সত্যজিতের পক্ষেই সম্ভব। একটার পর একটা বন্ধ দরজা খুলে যাচ্ছে আর উদ্ভাসিত মুখে বেরিয়ে আসছে তরুণ দম্পতি। চমৎকার প্রতীকীর ভেতর দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ওই ঘটনা। শুধু বাঙ্ময় নয় ব্যঞ্জনাময়। বন্দি বিহঙ্গ ডানা মেলে আকাশে উড়ল, কিন্তু সেই স্বাধীনতার সংযম না থাকলে ডানা ভেঙে তার যে পতন ঘটতে পারে সে আভাসও আমরা পেয়েছি।
সন্দীপের চরিত্র জটিল। সে প্রথমে সৎ একজন দেশপ্রেমিক হিসাবেই কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু পরে সে নীতিভ্রষ্ট হল, তার চরিত্রহানি ঘটল। সে হয়ে উঠল স্বার্থপর, লোভী, একজন আত্মকেন্দ্রিক পুরুষ। যে বন্ধু সরল বিশ্বাসে তাকে ঘরে স্থান দিল তার স্ত্রীর প্রতিই সে হয়ে উঠল কামাতুর। বিদেশি দ্রব্য বর্জন করার জন্য সে সভা-সমিতি করেছে, উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছে অথচ বিদেশি সিগারেট ছাড়া তার চলে না। নিজের রাজনৈতিক জীবনের ফায়দা তুলতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সে অবিশ্বাস আর সুন্দরের মধ্যে বীজ রোপণ করল যার ফলে হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। [আজকাল রাজনৈতিক নেতাদের কাছে অবিশ্যি এসব কিছু নতুন নয়]।
ভিক্টর ব্যানার্জি যেমন নিখিলেশের শান্ত, সংযত চরিত্র অসামান্য নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও সন্দীপের চরিত্রকে তেমন যথার্থ রূপ দান করেছেন যদিও তাঁকে ওই ছবির ভিলেন বলেই মনে হয়েছে, দর্শকের সহানুভূতি আদায় করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।
সন্দীপের চেহারা, তেজস্বিয়তা আর বাগ্মিতায় বিমলা তার প্রতি আকৃষ্ট হল, নিজের সংযম হারিয়ে ফেলল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সন্দীপের আসল লোভী চরিত্র তার কাছে যখন পরিস্ফুট হয়ে উঠল, সে ফিরে এল নিখিলেশের কাছে। কিন্তু সন্দীপ যে আগুন জ্বালিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তার পরিণাম যে ভয়ঙ্কর।
১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে দামাসকাস চলচ্চিত্র উৎসবে ‘ঘরে বাইরে’ স্বর্ণপদক পেয়েছে, সত্যজিতের টুপিতে যুক্ত হয়েছে আরও একটি পালক। ১৯৯১-৯২ সালে ‘আগন্তুক’ আন্তর্জাতিক [ফ্রিপেসি] ও জাতীয় [স্বর্ণকমল] পুরস্কার পেয়েছে।
সত্যজিতের ছবি বিদেশে প্রদর্শনীর আগে জাপানই চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে এশিয়া মহাদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ‘রুকি ওয়ারেসু’-র পরিচালক তাসাকা; ‘রসোমন’, ‘সেভেন সামুরাই’, ‘রেড বীয়ার্ড’ ইত্যাদির পরিচালক কুরোসাওয়া এবং আরও কিছু পরিচালক সারা পৃথিবীতে শোরগোল ফেলেছিলেন। ভারতবর্ষ তখন অনেক পিছিয়ে। যদিও সংখ্যার দিক থেকে ভারতের স্থান বোধ হয় ছিল আমেরিকার পরেই কিন্তু গুণগত বিচারে ভারতের কোনো স্থান ছিল না।
চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সত্যজিতের যে ঔৎসুক্য, তার প্রথম সূত্রপাত বোধ হয় চেকভের ‘আইভান দ্য টেরিবল’ থেকে। উত্তর কলকাতার একটা সিনেমা হলে ছবিটা তিনি দেখেছিলেন, তখন তিনি তরুণ। রবিবার মর্নিং শোতে ছবিটা দেখেছিলেন, সারাদিন তার রেশ ছিল তাঁর মনে। একটা প্রচণ্ড বিষণ্ণতা তাঁকে আপ্লুত করেছিল। প্রকোফিয়েভের সংগীতও আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।
যুদ্ধের শেষে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বই তাঁর হাতে এসেছিল। ইংরেজি ছবি ‘এ ঘোষ্ট গোজ ওয়েষ্ট’-এর চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্যের সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম পরিচয়, তখন থেকেই অবসর সময়ে চিত্রনাট্য লেখার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল।
‘পথের পাঁচালী’ প্রথম যেদিন শুটিং হয়েছিল, সেটা ছিল অক্টোবর। পুজোর মাস, খুব সম্ভব সেদিন ছিল কালীপুজো। ট্যাক্সি করে গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ঢাকের বাদ্যি কানে আসছিল। ইউনিটে মোট ছিলেন আটজন, একমাত্র বংশী চন্দ্রগুপ্তর ছবির ব্যাপারে কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটা পুরোনো বহু ব্যবহৃত ‘ওয়াল’ ক্যামেরা, একমাত্র ওটাই সেদিন ভাড়া পাওয়া গিয়েছিল। সঙ্গে কোনো শব্দযন্ত্র ছিল না, অবিশ্যি সেদিন যে শটটা নেবার কথা তাতে কোনো সংলাপ ছিল না।
সত্যজিতের একটা গুণ, ছবি তোলার সময় প্রতি শটের সিকোয়েন্স বা ক্রমানুযায়ী স্কেচ তিনি করে নেন। একটা খেরো পাতার মতো খাতায় সংক্ষিপ্ত ডায়ালগ, যারা ছবিতে অংশ নিচ্ছেন তাদের একটা রাফ স্কেচ, তাদের পোশাক, কোন শটের পর কোন শট নেওয়া হবে ইত্যাদি পর পর তৈরি থাকে, অর্থাৎ সময়ের বিন্দুমাত্র অপব্যয় না করে যাতে সুষ্ঠুভাবে শট নেওয়া যায় তার নিখুঁত পরিকল্পনা। সত্যজিৎ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘আমি আর্টিস্ট, কোনো জিনিসের মানসিক রেখাচিত্র আঁকার তাৎক্ষণিক প্রবণতা আমার আছে।’
সেদিনের দৃশ্য ছিল দুর্গা আর অপু গ্রাম ছাড়িয়ে একটা কাশবনে এসে পড়বে। ওদের দুজনের আগে ঝগড়া হয়েছিল, কিন্তু এমন সুন্দর সাদা কাশের বন দেখে ওদের ভাব হয়ে যাবে, তারপর ওরা প্রথম রেলগাড়ি দেখবে। সত্যজিতের তখন হাতে মাত্র আট হাজার টাকা, এমন একটা দৃশ্য ক্যামেরায় ধরতে চেয়েছিলেন যা দেখিয়ে ছবিটা সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে কোনো ধনী প্রযোজকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন। ‘পথের পাঁচালী’র ওই সুন্দর দৃশ্যটা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে।
প্রথম দিন আটটা শট নিতে হয়েছিল। সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় আর উমা দাশগুপ্তা অপু আর দুর্গার ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ আর স্বাভাবিক অভিনয় করেছিল। ওরা কোনোদিন অভিনয় করেনি, সত্যজিৎ ওদের পরীক্ষা করেও নেননি, একেবারে আনাড়ি নিয়ে কাজ। কিন্তু শুরুতে সত্যজিৎ মনে মনে একটা দারুণ উত্তেজনা অনুভব করলেও এই দুজনের মধ্যে কিন্তু জীবনের সত্যিকার ঘটনার মতোই সমস্ত ব্যাপারটা আচরণে ফুটে উঠেছিল, এ যেন একটা খেলা। শুরুটা ভালোই বলতে হবে।
ওই দৃশ্যের মাত্র অর্ধেকটা সেদিন তোলা সম্ভব হয়েছিল। পরের রবিবার তাঁরা আবার লোকেশনে ফিরে গেলেন, বাকি কাজটুকু শেষ করবেন। কিন্তু একি! ওঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না ঠিক জায়গায় এসেছেন কিনা। যেখানে কাশের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল সেখানে শুধু রোদে পোড়া তামাটে ঘাস। কাশ গাছ শরৎকালেই জন্মায় তা বলে এক সপ্তাহের মধ্যেই তার আয়ু ফুরোবে! ওখানকার একজন চাষিই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। গোরুতে সব কাশ ফুল খেয়ে গেছে। দুদিন আগে একপাল গোরু এসে নাকি এই কাণ্ড করে গেছে।
সবাই তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। আগের দিনের দৃশ্যের ধারাবাহিকতা রেখে কাশবনে ছেলে-মেয়ে দুটির ছবি তুলতে হবে, এখন কাশবন পাওয়া যায় কোথায়!
তখন কি আর সত্যজিৎ জানতেন প্রায় দু-বছর পরে ওই লোকেশনেই তাঁদের আসতে হবে, ওই কাশবনেই সেই একই চরিত্র নিয়ে তিনি ছবি তুলবেন এবং তা হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে! কিন্তু মাঝের ওই সময়টা কেটেছিল দারুণ উৎকণ্ঠা আর মানসিক যন্ত্রণায়।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঁবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ একাধিক প্রকাশক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল কাহিনিতে গল্প নেই। যে মাসিক পত্রিকায় ওটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সেখানেও শর্ত ছিল পাঠক সমাজ ওটা না চাইলেই বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাছাড়া ওই পত্রিকার সম্পাদক প্রথম থেকেই ওটা ছাপতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন না। ভালো বই সেলফে পড়ে থেকে ধুলো জমে আর বাজে বই নিয়ে পাঠকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, কথাটা যে কত বড়ো সত্যি তা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। সিনেমার বেলাতেও তাই। উদ্দাম হুল্লোড়ে ছবি ছেড়ে গভীর অনুভূতিসম্পন্ন ছবির জন্য দর্শক লাইন দেয় না।
তার উপর বাংলা ছবির মস্ত একটা অসুবিধে। বোম্বেতে ছবি হয় হিন্দিতে, মাদ্রাজেও এখন হিন্দি ভাষায় ছবি তোলা হচ্ছে, ফলে সারা ভারতে তারা বাজার পায়। কিন্তু বাংলা ছবি বাঙালিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র দশ কি পনেরো ভাগ বাংলা ভাষা বোঝে, সুতরাং বাংলা ছবির সুযোগও সীমিত, এ কথা বুঝতে অঙ্ক কষতে হয় না। কয়েক লাখ টাকা খরচ করে একটা ছবি তোলার পর সে টাকা যদি প্রযোজকের ঘরে তাড়াতাড়ি ফিরে না আসে, লাভের কথা ছেড়েই দিলাম, তবে তাঁরা টাকা ঢালবেন কোন দুঃখে? বহু ক্ষেত্রে আসলটাই উঠে আসে না। এর ফলে পশ্চিমবাংলার স্টুডিয়োগুলির যন্ত্রপাতিও সীমিত, প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকীকরণ হয়নি। খুঁটিনাটি কাজ করতে হলেই ছুটতে হয় বম্বে বা মাদ্রাজ।
জনসাধারণের মধ্যে পশ্চিমবাংলার এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ যদি না দেখা দেয় তবে শত চেষ্টাতেও বাংলা চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবার নয়।
রেনোয়া একবার বলেছিলেন ফরাসি জাতির সচেতনতা ও গ্রহণেচ্ছু উদারতাই তিরিশের দশকে বাঁচিয়ে তুলেছিল সে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে। শহরের শিক্ষিত বাঙালিরা যদি এ বিষয়ে তৎপর না হন তবে গ্রামের মানুষের কাছে কি আশা করা যায়? ভালো ছবি করার দুঃসাহস তাই বাঙালি পরিচালকদের খুব কম, যাঁরা সেই দুঃসাহস দেখিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।
‘পথের পাঁচালী’ যখন অর্ধেক তোলা হয়েছে, সব টাকা নিঃশেষিত। পাঁচ হাজার ফুট অপরিমার্জিত ছবিই দেখতে হয়েছিল সম্ভাব্য প্রযোজকদের, তাঁরা এক বাক্যে ছবিটাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন চলবে না, কিন্তু তবু সত্যজিতের মনোবল অটুট ছিল, নিজের ওপর আস্থা হারাননি। ও ছবি একদিন সমাদৃত হবেই, এ ধারণা তাঁর ছিল।
‘অপরাজিত’ আর্থিক দিক দিয়ে অসফল হয়েছিল, কিন্তু ভেনিস ফিলম ফেস্টিভ্যালে ‘গোল্ডেন লায়ন’ পুরস্কার পাবার পর ছবিটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে থাকে। সেই প্রথম সত্যজিৎ বোধ হয় উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা ছবির আর্থিক সাফল্যের জন্য শুধু আঞ্চলিক বাজারের দিকে তাকিয়ে থাকার দরকার নেই।
‘পথের পাঁচালী’ ১৯৫৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে আর তার পরের বছরই ‘অপরাজিত’ সোনা পেল ভেনিসে— উপর্যুপরি দু-বছর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়া তাও সারা দুনিয়ার তাবড় তাবড় পরিচালকদের ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, এ এক অসামান্য সাফল্য।
‘জলসাঘর’ ছবি করার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। কাশীতে ‘অপরাজিত’-র শুটিং করতে গিয়ে পাথরের সিঁড়িতে পড়ে হাঁটুতে খুব চোট পেয়েছিলেন সত্যজিৎ। বেশ কিছুদিন শয্যাগত থাকতে হয়েছিল। হাতের কাছে যা বাংলা বই পেয়েছিলেন তাই পড়ে সময় কাটাচ্ছিলেন। তখনই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জলসাঘর’ পড়ে তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন ওই ছবি করবেন। নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের কথা তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল। ছবি বিশ্বাসের মতো শক্তিশালী অভিনেতা খুব কমই এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। অসাধারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, স্পষ্ট বাচনভঙ্গী, সূক্ষ্ম কাজ আর চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার অসামান্য দক্ষতা।
কিন্তু জলসাঘরের মতো অতবড়ো একটা সেট বানাতে অনেক টাকার দরকার, তার চাইতে অমন একটা প্রাচীন জমিদার বাড়ি যদি পাওয়া যায় তবে সবদিক দিয়েই সুরাহা হয়। প্রায় তিরিশটা বনেদি বাড়ি দেখা হল, কোনোটাই মনে ধরল না।
ত্রিশতমটা দেখে ওঁরা মুর্শিদাবাদের লালগোলায় একটা খড়ের ছাউনি দেওয়া চায়ের দোকানে চা পান করছেন আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। ওঁদের কথাবার্তায় হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। হঠাৎ বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাদের কথা শুনছিলাম। আপনারা নিমতিতার রাজবাড়ি দেখেছেন?’
‘নিমতিতা? সেটা আবার কোথায়?’
‘এখান থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল উত্তরে, এই মুর্শিদাবাদ জেলাতেই। গঙ্গা পেরিয়ে যেতে হবে, ওখান থেকে মাইল কুড়ি গিয়ে পদ্মার পাড়ে, উলটোদিকে পাকিস্তান [তখনও বাংলাদেশ হয় নি]। ওটা চৌধুরিদের রাজবাড়ি, আসলে ওঁরা জমিদার ছিলেন। ও বাড়িটা না দেখে আপনারা যাবেন না।’

অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁরা গেলেন। বুড়ো ভদ্রলোকের কথা একবর্ণও মিথ্যে নয়। প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ি, মস্ত মস্ত খিলান। কাছেই পদ্মা। রাক্ষুসী পদ্মা গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করেছে, দিক পরিবর্তন করায় মাইলের পর মাইল বালুচর পড়েছে, কিন্তু আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়েছে চৌধুরিদের প্রাসাদ। পদ্মা যেন ওটার সামনে এসে থমকে গেছে। তবে একেবারে রেহাই দেয়নি। মস্ত বাগান, আর আস্তাবল টেনে নিয়েছে নিজের গর্ভে। একদিন সকালে বাড়ির সবাই যখন জলখাবার খাচ্ছিলেন হঠাৎ একটা ঝপ ঝপ শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখলেন জমিদারির প্রায় এক মাইল আয়তক্ষেত্র মতো জায়গা নদীর তলায় চলে গেছে। যেখানে কয়েক মুহূর্ত আগেও ছিল স্থল, সেখানে থই থই করছে জল।
চৌধুরি প্রাসাদের মালিক তখন সত্তর বছর বয়সের জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি, ইংরেজ সরকার থেকে রায় বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন। বাড়িতে একটা জলসাঘর সত্যিই আছে। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের কাকা উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি গান বাজনার ভক্ত ছিলেন, তারাশঙ্করের কাহিনির জমিদারের মতো অনেকটা তাঁর চরিত্র। কিন্তু সত্যজিৎ যেমন পরিকল্পনা করেছিলেন ওই জলসাঘরে তা কুলোবে না, ওটা স্টুডিয়োতে বানাতেই হবে। তবে আউটডোর শুটিং ওই বাড়িতে এবং বাইরে চমৎকার হবে।
আরও দুটো জিনিস দরকার, একটা সাদা ঘোড়া আর একটা হাতি। সাদা ঘোড়া কলকাতার একটা আস্তাবলে পাওয়া গেল। ওটার মালিকের একসময় খুব রমরমা অবস্থা ছিল, এখন সাদা ঘোড়ার খরচ যোগাতেই কাবু হয়ে পড়েছেন। তিনি মাত্র দু-শো টাকায় খুশি মনেই ঘোড়াটা বিক্রি করে দিলেন। একজন রাজার কাছ থেকে হাতিটা ধার করা হল। লোকেশনে আসতে ওটাকে পাঁচটা নদী পার হয়ে প্রায় ১৬৫ মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল।
নিমতিতা থেকে ফিরেই সত্যজিৎ তারাশঙ্করকে ফোন করলেন। তিনিও জমিদার বাড়িটা যাতে কাহিনির উপযুক্ত হয় সে ব্যাপারে ব্যগ্র ছিলেন।
সত্যজিৎ তাঁকে জানালেন শেষপর্যন্ত একটা রাজবাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে।
‘পেয়েছেন? কোথায়?’ তারাশঙ্কর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।
‘ও আপনি চিনবেন, জায়গাটার তেমন নাম নেই, নিমতিতা।’
‘নিমতিতা!’ তারাশঙ্করের গলা অন্যরকম শোনাল, ‘আপনি নিশ্চয়ই নিমতিতার জমিদার চৌধুরিদের বাড়ির কথা বলছেন না!’
‘হ্যাঁ, ওটাই।’
‘আরে, অদ্ভুত ব্যাপার,’ তারাশঙ্কর উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। ‘আমি নিজে নিমতিতায় কখনো যাইনি, কিন্তু বাঙালি জমিদারদের এক ইতিহাসে চৌধুরিদের কাহিনি পড়েছি। আমার গল্পের মূল চরিত্র তো গান-বাজনা পাগল ওই উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরিকে নিয়েই!’
কি আশ্চর্য যোগাযোগ! সেক্সপিয়ারের মন্তব্য উল্লেখ করে বলা যায়, এই পৃথিবীতে এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যা আমাদের দর্শনশাস্ত্রে স্বপ্নেরও অগোচর।
গুপী গাইনের আউটডোর শুটিং একটানা কিছুদিন ধরে চলেছিল রাজস্থানের জয়সলমিরে। এ ব্যাপারে ওখানকার মহারাজার অনুমতির দরকার, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ।
চিতোরের পরই জয়সলমির পশ্চিম রাজস্থানের সবচেয়ে পুরোনো দুর্গ শহর। ইতিহাস নাকি বলে ওখানকার রাজারা একসময় পরাক্রান্ত সুলতান আলাউদ্দিন খিলজিকে রুখে দিয়েছিলেন। এখনকার মহারাজাকে দেখে তেমন একটা সম্ভ্রম বোধ জাগে না। রাজা বলতে আমরা যেমন দশাসই চেহারা, ইয়া গোঁফ, ঝলমলে পোশাক বুঝি, সেসব কিছু নেই। একজন সাধারণ মানুষের মতো।
‘আপনারা কি বোম্বে থেকে ছবি তুলতে এসেছেন’ মহারাজা জিগ্যেস করলেন।
‘না, কলকাতা থেকে,’ সত্যজিৎ জবাব দিলেন।
‘আপনারা বাংলা ছবি তুলছেন?’
মহারাজা যেন একটু হতাশ হলেন, তারপরই প্রশ্ন করলেন, ‘কিন্তু জয়সলমিরে কেন?’
সত্যজিৎ বুঝিয়ে বললেন কাহিনির সঙ্গে ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পরিবেশ চমৎকার মানায় বলেই জয়সলমির তাঁর মনে ধরেছে। তাছাড়া ওখানে আগে কোনো ফিলম কোম্পানি ছবি তোলেনি সেদিক দিয়ে একটা নতুনত্ব হবে। মহারাজা শুধরে দিলেন, কয়েক বছর আগে এক পাঞ্জাবি ছবির শুটিং হয়েছিল ওখানে।
কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর মহারাজা বললেন, ‘বেশ, ছবি তুলুন আপনারা, নাচ-গান আছে আপনাদের ছবিতে?’
‘আছে, তবে সেটার ছবি এখানে তোলা হবে না, বাংলা মুলুকের এক জঙ্গলে সেটা হবে,’ সত্যজিৎ বললেন।
দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় প্রাসাদের ছাদে শুটিংয়ের অনুমতি চাইলেন সত্যজিৎ, সেইসঙ্গে কিছু পতাকা ওড়াবার অনুমতি।
‘আমার পতাকাটা সরাবেন না তো?’ মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন।
‘না, না’, তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন সত্যজিৎ।
‘তবে ঠিক আছে।’
‘আপনার ঢাকটা আমরা ধার করতে চাই, মানে ওই ভেরিটা, একটা যুদ্ধের দৃশ্যের জন্য।’
‘বেশ, তবে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।’
‘আমাদের কিছু উট চাই মহারাজা।’
‘কত?’
‘কয়েক-শো, মালিক সমেত।’
মহারাজা মুহূর্তকাল চিন্তা করলেন, তারপর কুমারবাহাদুরকে নির্দেশ দিলেন কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
‘আর কিছু চাই?’
‘না, ওতেই হবে।’
‘ভালো কথা, আমার মেয়ে আপনাদের ছবি তোলা দেখতে চায়, কুমারবাহাদুরকে জানিয়ে ব্যবস্থা করবেন।’
ওখানকার শুটিং শেষ করে ফিরে আসার আগে রাজপ্রাসাদে মহারাজার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ এবং তাঁর ইউনিটের লোকজন। কফির সঙ্গে ওখানকার বিখ্যাত মিষ্টি গুলাবজাম খেতে দেওয়া হয়েছে।
কথায় কথায় সত্যজিৎ মহারাজাকে সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর রুচি আর আগ্রহের কথা জিজ্ঞেস করলেন।
‘আমি বিশেষ ছবি-টবি দেখি না,’ মহারাজা জবাব দিলেন, ‘যখন দিল্লি যাই তখন শুধু দু-একটা দেখি। ”পরিণীতা” আমার খুব ভালো লেগেছিল। আরেকটা ছবির নাম যেন কি? সেটাও আপনাদের বঙ্গালি কহানি… হ্যাঁ, মনে পড়েছে… দেবদাস… খুব ভালো।’
রাজস্থানের এক প্রান্তে, বাংলা থেকে বহু দূরে, এক প্রায় নির্বাসিত মহারাজা বাংলা ছবি দেখেছেন, তাঁর ভালো লেগেছে, এটা ভাবতেও কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়।
বিদায় নেবার সময় সত্যজিৎ মহারাজাকে কলকাতায় ছবির উদ্বোধনীর দিন আমন্ত্রণ জানালেন। মহারাজার দু-চোখ কৌতুকে নেচে উঠল, তিনি বাঘা ওরফে রবি ঘোষের দিকে ফিরে বললেন, ‘যদি ও কথা দেয় ঢোলক বাজাবে তবেই যাব।’
সত্যজিৎ তাঁর এক বইয়ে লিখেছেন, সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর শৈশবের এক স্মৃতি হল নায়কের মুখে তাচ্ছিল্যভরা হাসি। তাঁর দু-কানে মাকড়ি, মাথায় গাঢ় রঙের একটা রুমাল বাঁধা। কয়েকজন ভীষণ দর্শন লোকের সঙ্গে সে প্রবল বিক্রমে লড়াই করছে, তাদের সবাইকে কাবু করে একটা পাঁচিল থেকে সে লাফিয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠে, সেটা পক্ষীরাজ হয়ে তাঁকে নিয়ে শূন্যে ডানা মেলল। ছবিটা হল ‘থিফ অফ বাগদাদ,’ আর ওই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস (বড়ো)। ছোটোবেলায় তাঁর একজন ভক্ত ছিলেন সত্যজিৎ।
তারপর যাঁর অভিনয় খুব ভালো লাগত, তিনি আবার মোটেই হাসতেন না, কিন্তু ফেয়ারব্যাঙ্কসের মতো লাফঝাঁপে ওস্তাদ ছিলেন, তাঁর নাম বাস্টার কীটন। একটা দৃশ্যে তিনি একতলার বাগান থেকে পোল ভল্ট করে চারতলার জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে খলনায়কের পেটের ওপর পা চেপে দাঁড়িয়েছিলেন।
চ্যাপলিনও সত্যজিতের খুব প্রিয় ছিলেন। এছাড়া ছোটোবেলা ‘আঙ্কল টমস কেবিন’ দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। ছোট্ট মেয়ে ইভার মৃত্যুর দৃশ্যে গলা ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল।
হাসির ছবি ছাড়াও রোমাঞ্চকর ছবি খুব ভালোবাসতেন সত্যজিৎ। তাই বোধ হয় পরবর্তীকালে ফেলুদাকে নিয়ে রোমাঞ্চকর সব কাহিনির সৃষ্টি। জন গিলবার্টের কাউন্ট অফ মন্টোক্রিস্টোর চরিত্র, লন চেনির হাঞ্চব্যাক অফ নতরদমে সেই কুব্জ মানুষটার চরিত্র তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। [মনে পড়ে চার্লস লটনকেও ওই ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করতে দেখেছিলাম]। আবার বেনহুরে রথের দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যে উত্তেজনা ছিল, তার রেশ অনেকটা ভুলতে পারেননি সত্যজিৎ।
পরবর্তীকালে গ্রেটা গার্বো, পোলা নেগ্নি, রোমান নোভারো, ভ্যালেনটিনো ইত্যাদির মতো নামি শিল্পীদের অভিনয় তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল। তবে এঁরা নির্বাক ছবির যুগে দাপটে বিচরণ করেছিলেন, সবাক ছবির যুগে তাঁদের আধিপত্য খর্ব হতে থাকে। শব্দের প্রবর্তনই এর মূল কারণ, যেমন শোনা যায় গার্বোর কণ্ঠস্বর নাকি কর্কশ ছিল।
[নর্মা শিয়ারার, ক্লার্ক গেবল, গ্যারি কুপার, লেসলি হাওয়ার্ড, লরেন্স অলিভিয়ার, চার্লস বয়ার, গ্লীয়ার গারসন, রোনাল্ডকোলম্যান, ওয়াল্টার পীজন, গ্রেগরি পেক, এরল ফ্লিন এবং আরও অনেকে সবাক যুগের প্রথমদিকে খুব নাম করেছিলেন। পরবর্তীকালে রিচার্ড বার্টন, মার্লন ব্র্যান্ডো, এলিজাবেথ টেলর, ইনিগ্রিড বার্গম্যান, মেরিলিন মনরো, অ্যালেক গিনেস, পিটার ওটুল, সোফিয়া লোরেন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।] হিচককের ‘রীয়ার উইন্ডো’ সত্যজিতের খুব ভালো লেগেছিল। হিচককের ছবির গুণ হল, উপভোগ করার মতো ঘটনা আর দৃশ্যের সঙ্গে উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা আর আতঙ্কের মশলা মিশিয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা।
এখানে ভারতের পটভূমিকায় হলিউডে প্রস্তুত একটা ছবির কথা বেশ কৌতুকের সৃষ্টি করবে। রোমান নোভারকে দিয়ে একটা চরিত্রে অভিনয় করানো হয়েছিল। তার নাম করিম, ব্রাহ্মণের ছেলে, মাথায় শিখদের মতো পাগড়ি। অনেক ইংরেজি বইতেও এমন ঘটনা বিরল নয়। এক ইংরেজি বইয়ে পড়েছিলাম এক গুজরাতি ডাক্তার লন্ডনে প্র্যাকটিশ করেন, তার পদবি হচ্ছে ভারতের অন্যপ্রান্তে ভারতের অন্য এক প্রদেশের অর্থাৎ একটা জগা খিচুড়ি। এমন অজ্ঞতা আমরা ভাবতেই পারি না।
মস্কোতে বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ডনস্কয়ের সঙ্গে সত্যজিতের পরিচয় হয়েছিল। তরুণ বয়সে ডনস্কয় ছিলেন সত্যজিতের আদর্শ।
‘আপনার তবে আমার গোর্কি ট্রিলজি ভালো লেগেছিল?’ প্রথম আলাপেই ডনস্কয় মৃদু হেসে বলেছিলেন, ‘ফিলম ফেস্টিভ্যালে যেসব রাশিয়ান ছবি এসেছে, তাদের সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?’
সত্যজিৎ প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য বলেছিলেন, ‘আমি এখন জুরি, আমার বোধ হয় কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়।’
‘বুঝেছি, বুঝেছি…,’ ডনস্কয় সত্যজিতের পিঠে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মেরে বলেছিলেন, ‘আমার কাছে লুকোবার কোনো দরকার নেই। ওই ছবি সম্বন্ধে কোনো মোহ থাকার মতো বুদ্ধু আমি নই। বাজে ছবি। কেন যে প্রতিযোগিতায় পাঠায় জানি না।’
চ্যাপলিনের ‘গোল্ড রাশ’ সম্বন্ধে সত্যজিৎ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। খিদে মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সামান্য দু-একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে শিল্পীর মতো তা ফুটিয়ে তুলেছেন চ্যাপলিন। একপাটি জুতো রান্না দিয়ে সেই দৃশ্যের অবতারণা। ফরাসি রাঁধুয়ের মতো স্বাভাবিক নৈপুণ্যে রান্নাটা দেখানো হয়েছে। রান্নার বস্তুটা যে কি সেটা এক ফাঁকে ছোট্ট মানুষটার বাঁ পা দেখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
তারপর প্লেটে যখন ওটা সাজানো হয়েছে, কে বলবে ওটা একটা বড়ো মাংসখণ্ড নয়! জুতোর ফিতেটা কাঁটা-চামচে জড়িয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া, জুতোর পেরেককে হাড়ের মতো চোষা— এসব দৃশ্য ভোলা যায় না। হাসি ছবির মধ্য দিয়ে যে সূক্ষ্ম করুণ রস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেখানেই চার্লির সফলতা।
‘কিড’ ছবিটাই বা কম যায় কিসে! শৈশবে ও বাল্যকালে যে অভাব অনটনের ভেতর চ্যাপলিনের দিনগুলো কেটেছে, তারই বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল বোধ হয় ‘কিড’।
১৯৩১ সালে ‘সিটি লাইটস’ যখন মুক্তি পেল তখনই ছোট্ট মানুষটি নিজেকে দারুণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নির্বাক যুগ শেষ হয়ে সবাক যুগের কাল ততদিনে এসে গেছে, কিন্তু চ্যাপলিন ছবিতে কথা বলবেন না, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। যাঁর ভ্রূভঙ্গী কিংবা কাঁধের ঝাঁকুনিতে সব কথা বলা হয়ে যায় তাঁর কথা বলার দরকারটা কি! ‘সিটি লাইটস’-এর পর চার বছর কোনো ছবি তোলেননি চ্যাপলিন, তাই নিয়ে কি কম অভিযোগ হয়েছিল! কেন আরও ঘন ঘন তিনি ছবি তোলেন না! এই হলেন চার্লি চ্যাপলিন।
আরও কয়েকটা ছবি সত্যজিৎকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, তাদের মধ্যে ‘দ্য গ্রেপস অফ র্যথ’, ‘ইয়ং মিস্টার লিঙ্কন’, ‘দ্য কোয়ায়েট ম্যান’, ‘দ্য ফিউজিটিভ’, ‘দ্য ইনফর্মার’, ‘দ্য লঙ ভয়েজ হোম’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইতালিয়ান ছবি একসময় সারা দুনিয়ায় আলোড়ন তুলেছিল। ক্যামেরিনি, ডি সিকা এবং পরবর্তীকালে ক্যাস্টেলেনি, ফেলিনি, রসেলিনি ভালো ভালো ছবি করেছিলেন। আনা ম্যাগনানি দারুণ অভিনেত্রী ছিলেন। আরেকটা ছবি তাঁর মন কেড়েছিল, সেটা হল ‘টু উইমেন।’
চলচ্চিত্র পরিচালক জন ফোর্ড সম্বন্ধে সত্যজিতের খুব উঁচু জায়গা। প্রায় ষাট বছর তিনি চলচ্চিত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নির্বাক যুগের শেষের দিকে ছোটো বড়ো মিলিয়ে পঞ্চাশটি ছবি তিনি করেছিলেন। প্রায় আশি বছর বয়সে মারা যাবার আগে তাঁর ছবির সংখ্যা ছিল এক-শোর ওপর— সিনেমা জগতে তাঁকে অন্যতম পথিকৃৎ বললে অন্যায় হবে না। কাব্যের সুষমা, সুরুচি, জীবনের প্রতি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি আর মানবিক অবদান, এই ছিল জন ফোর্ডের ছবির বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বিখ্যাত সব চিত্রনির্মাতা তাঁকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, যেমন সোভিয়েত রাশিয়ার আইজেনস্টাইন, জাপানের কুরোসাওয়া, সুইডেনের বার্গম্যান, যুক্তরাষ্ট্রের অরসন ওয়েলস এবং ভারতবর্ষের সত্যজিৎ রায়— এমন সৌভাগ্য দুর্লভ।
ইংলন্ডের স্টিল পত্রিকার ওয়েন্ডি অ্যালেন এবং রজার স্পাইকসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন একই ধরনের ছবির পুনরাবৃত্তি না করার চেষ্টাই কিনত কারণ ভারতবর্ষে ছবি করার মতো বিষয়বস্তুর অভাব নেই।
সমসাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন, বর্তমানে যা ঘটছে তা ছাড়াও তিনি অতীতে ফিরে যেতে চান, যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে। তেমন একটা ছবি হল ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ী’। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন আস্তে আস্তে তার লোলুপ আগ্রাসী থাবা বাড়াচ্ছে সেই সময়ের ঘটনা, যেটা তিনি করেছিলেন ১৯৭৭ সালে। তাছাড়া ‘দেবী’ এবং ‘চারুলতা’-তেও তিনি অতীত ঘটনাশ্রয়ী কাহিনি অবলম্বনে ছবি করেছিলেন। একটা সময়কে নতুন করে সৃষ্টি করার চেষ্টার মধ্যে চমৎকারিত্ব নিশ্চয়ই আছে।
কখনো কখনো আবার বর্তমান এমন চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে যে, তখন সমসাময়িক ঘটনা ও সমস্যা নিয়ে ছবি করার আগ্রহ বোধ না করে তিনি পারেন না। তারই ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ দিয়ে, তারপর ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘সীমাবদ্ধ’ সবশেষে ‘জন অরণ্যে’ ওই সময়টাকে তিনি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। শহুরে মানুষের সমস্যা হলেও প্রতিটি ছবির কাহিনিতে বৈচিত্র আছে, ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়। ‘জনঅরণ্য’ সম্বন্ধে সত্যজিৎ মনে করেন ওটা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। ওটা খুব জটিল ছবি, কৌতূহলোদ্দীপক, দুর্নীতি নিয়ে দুঃখবাদী একটি ছবি।
এই ধারাবাহিকতার মধ্যে ১৯৭৩ সালে সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে আরেকটা ছবি তিনি করেছিলেন, সেটা হল ‘অশনি সংকেত’। এই কাহিনিতে তিনি ১৯৪২-৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষতে চলে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে এসেছিলেন ‘পথের পাঁচালী’র সামাজিক পরিবেশে। সেই একইরকম গ্রাম্য কাহিনি আর লেখকও অপু-ত্রয়ীর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে অপু-ত্রয়ীর মতো সাদা-কালোয় ছবি নয়, রঙিন। অবিশ্যি রঙিন ছবি এখন প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সত্যজিৎ বলেন সাদা কালো ছবি যে খারাপ তা নয়, আসলে এখন কোডাক ফিলম পাওয়া যায় না, পূর্ব জার্মানি থেকে যে ফিলম আসে তা তেমন ভালো নয়। সুতরাং মাঝে মাঝে সাদা-কালো ছবি তোলার ইচ্ছে থাকলেও রঙিন ছবি করতে হচ্ছে। কিন্তু ‘জন অরণ্য’ এর ব্যতিক্রম, তিনি ইচ্ছে করেই সেখানে সাদা-কালো ব্যবহার করেছেন কারণ ছবির কাহিনি হল সাদা-কালোর উপযুক্ত।
সত্যজিৎ মনে করেন চোখের সামনে যা তিনি দেখেন সেই বাস্তবধর্মী শহুরে জীবন নিয়ে ছবি করতে তিনি স্বচ্ছন্দ ভোগ করেন। তাঁর মোট ছবির প্রায় অর্ধেকই হল শহুরে জীবন নিয়ে, আবার আধ ডজনেরও বেশি সমসাময়িক জীবন নিয়ে, যা তিনি নিজে জানেন, বোঝেন।
‘পথের পাঁচালী’-র পর গ্রাম্য পরিবেশে ছবি নিয়ে তিনি খুব বেশি করেন নি। ‘দুই কন্যা’-য় [‘তিন কন্যা’-র একটি বাদ দিয়ে] গ্রাম্য পরিবেশ ছিল। ওটা তিনি করেছিলেন ১৯৬১ সালে। যে ধরনের মানুষ তাঁর চেনাজানা, তাদের নিয়ে ছবি করতেই তিনি সবচেয়ে বেশি সহজবোধ করেন। ‘অশনি সংকেত’ ছবিতে অবিশ্যি তিনি পুরোপুরি ‘পথের পাঁচালী’র গ্রাম্য পরিবেশে ফিরে গিয়েছিলেন।
ভারতের বাইরে ছবি করার ব্যাপারে সত্যজিৎ বলেন এদেশেই এত বিষয় রয়েছে যে, বাইরে ছবি করার দরকার পড়ে না। তা ছাড়া দেশের বাইরে কাজ করতে গেলে ঘরোয়া পরিবেশের বাইরে একটা অসুবিধে থাকেই। প্রথম ছবি থেকেই যে স্বাধীনতা তিনি ভোগ করে এসেছেন তা হারাতে তিনি রাজি নন। বাইরে কাজ করার অর্থই হল বাইরের পুঁজি আর সেইসঙ্গে নানান শর্ত, সেটা পছন্দ নয়।
এই প্রসঙ্গে একটা মজার কাহিনি তিনি শুনিয়েছিলেন। ডেভিড সেলজনিকের৩ কাছ থেকে একবার তাঁর কাছে ছবি করার প্রস্তাব এসেছিল। ‘দুই কন্যা’ এবং ‘অপরাজিত’ ছবির জন্য দুবছর তিনি সেলজনিক পুরস্কার পেয়েছিলেন— তারপরই ডেভিড সেলজনিকের কাছ থেকে চিঠি এসেছিল সত্যজিৎ তাঁর প্রযোজনায় একটা ছবি করতে রাজি আছেন কিনা!
ঘটনাসূত্রে সে বছর সেলজনিকের বার্লিন যাবার কথা, কারণ বার্গম্যান সেবার ‘ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি’ ছবির জন্য সেলজনিক পুরস্কার পাচ্ছিলেন। সেলজনিক সত্যজিৎকে বার্লিনে এসে বার্গম্যানের হাতে সেই পুরস্কার তুলে দেবার অনুরোধ করেছিলেন। সেই সময় বার্লিনে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন হয়েছিল, সত্যজিতের একটা ছবি ওখানে অংশ নেবে তাই তাঁকে বার্লিনে এমনিতেই যেতে হয়েছিল, সেখানেই সেলজনিকের সঙ্গে দেখা। তাঁরা দুজন একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সেরেছিলেন। সত্যজিৎ প্রথমেই কিন্তু জানিয়ে দিয়েছিলেন সেলজনিকের চিরকুটের ব্যাপারটা তাঁর অজানা নয়। সেলজনিক তাঁর পরিচালকদের চিরকুটের মাধ্যমে ছোট্ট ছোট্ট যে নির্দেশ পাঠান, সেকথাই তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ। এই নিয়ে একটা মজার বইও আছে, নাম ‘মেমো ফ্রম ডেভিড ও সেলজনিক’। এগুলো হচ্ছে হিচকক কিংবা হাস্টনের মতো চিত্র পরিচালকদের কাছে সেলজনিকের লেখা ছোটো ছোটো চিরকুট, তার কোনোটাতে লেখা, ‘এটা এভাবে কেন করছেন না’… ‘আমার ইচ্ছে আপনি ওটা ওভাবে…’— এই ধরনের সব নির্দেশ।
সত্যজিৎ সেলজনিকের সেইসব বিখ্যাত মেমো পড়েছিলেন, তাই তিনি বললেন, ‘দেখুন মি. সেলজনিক, আমি আপনার মেমোর কথা জানি। একদিন অন্তর আপনার কাছ থেকে অমন নির্দেশ পেতে হবে এই শর্তে আমি কাজ করতে পারব বলে মনে হয় না।’
জবাবে সেলজনিক বলেছিলেন, ‘না, আপনার সঙ্গে কাজ হবে অন্যরকম। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, জন হাস্টন একটু বেশি মাত্রায় গিলে সেটে আসতেন তাই আমাকে সাবধানে থাকতে হত, তাঁকে নিমন্ত্রণ আনার জন্যই আমি ওসব নির্দেশ পাঠাতাম।’
সত্যজিৎ তখন বললেন, ‘ঠিক আছে, তিনি ভেবে দেখবেন।’
সেদিনই রাত্রে বার্গম্যানকে সেলজনিক পুরস্কার দেবার কথা। সন্ধ্যেবেলা হোটেলে ফিরে সত্যজিৎ দেখলেন তাঁর জন্য একটা লেফাফা অপেক্ষা করছে। ভেতরে ছোট্ট একটা চিরকুট। পুরস্কার দেবার সময় সত্যজিৎ যে স্বল্প ভাষণ দেবেন তার একটা খসড়া ছিল ওই চিরকুটে। নির্দেশিকার পরে লেখা ছিল সত্যজিৎ ছ-সাত লাইনের ওই সংক্ষিপ্ত ভাষণ মুখস্ত করলে ভালো হয়।
সত্যজিৎ অবিশ্যি অন্য ভাষণ দিয়েছিলেন। ওই ঘটনার পর সেলজনিক সত্যজিৎকে ছবি তোলার ব্যাপারে আর অনুরোধ করেন নি।
লন্ডনের ন্যাশনাল ফিলম থিয়েটারে সত্যজিতের সঙ্গে লিন্ডসে অ্যান্ডারসনের সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে দেওয়া হল।
এক প্রশ্নের উত্তরে সত্যজিৎ বলেছিলেন, তিনি বুদ্ধিজীবী পরিচালক নন, যা উচিত মনে করেন তা নিয়েই ছবি করেন। ছবির পরিচালনা, অভিনয়, সংগীত সবক্ষেত্রেই তিনি এটা মেনে চলেন।
পশ্চিমবাংলার ছবির ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, বাংলাদেশ (পশ্চিমবঙ্গ) ঐতিহ্যপ্রধান, বিশেষ করে বাংলার সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গল্পই অমর সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প নিয়ে তিনি ছবি করেছেন।
রবীন্দ্রনাথ একসময় পশ্চিমেও খুব জনপ্রিয় ছিলেন কিন্তু এখন আর নয় কেন, তার জবাবে সত্যজিৎ বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গল্পের মূল সুরকে অনুবাদে আনা খুবই কঠিন কাজ। তবে ভারতবর্ষের অনেক পরিচালক রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে ছবি করেছেন। তাঁর ছোটোগল্প থেকেই ছবি করা সহজ, সত্যজিৎ নিজেও তাই করেন।
‘পথের পাঁচালী’র মূল কাহিনি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, ওটা আসলে দুটো বই। ১৯৪০ সালে প্রথম বইটা তিনি পড়েছিলেন, তারপর বইটার ছবি আঁকার কাজ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তখনই ওটা ছবি করার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল। তার আগে চিত্রনাট্য লেখার একটা শখ তাঁর ছিল। সময় পেলেই চিত্রনাট্য নিয়ে বসে যেতেন, মনে একটা আশা ছিল কোনো চিত্রনাট্যকে কোনোদিন হয়তো চিত্রায়িত করতে পারবেন।
রেনোয়া সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, উনি তাঁকে ছবির ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে তিনি ‘পথের পাঁচালী’ তৈরি করেছিলেন, মাইনের অনেকটাই ব্যয় হচ্ছিল ছবির পেছনে। রেনোয়া সে কথা শুনে বলেছিলেন, ‘সাবাশ, চালিয়ে যাও।’
বোম্বের ছবি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রথমদিকে ওরা কিছু বাস্তবধর্মী ছবি করেছিল। যেমন শান্তারামের ছবি, কিন্তু পরে ওদের চিন্তাধারা বদলে যায়।
চিত্রনাট্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাঁর অভ্যেস ঘনভাবে লেখা, তবে লোকেশনে গিয়ে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন তিনি করে থাকেন। শুটিং-এর সময়েই যতটা সম্ভব সম্পাদনা তিনি করে ফেলেন।
প্রতিদিন তিনি শুটিং করেন কিনা তার জবাবে সত্যজিৎ বলেছিলেন, সবসময় নয়। তবে যতটা সম্ভব দিনের বেলা তিনি কাজ করেন, এমনকি প্রয়োজনে রবিবারেও।
ছবির ব্যাপারে তাঁর জবাব, একই ধরনের ছবি বার বার তিনি করতে চান না, কারণ তাতে তাঁর মানসিক চিন্তাধারার ক্ষতি হয়। নানা ধরনের ছবি করাতেই তিনি আনন্দ পান। একটা ছবি শেষ করার পর তিন চার মাস বিশ্রাম নিয়ে নতুন ছবির কাজে হাত দেন, নইলে তাঁর ইউনিটের লোকদের খুব অসুবিধে হয়। [এ সাক্ষাৎকারে অবিশ্যিই সত্যজিৎ রায়ের অসুখ এবং আমেরিকায় অস্ত্রোপচার করতে যাবার অনেক আগের ঘটনা]।
সংগীত পরিচালনা সম্বন্ধে সত্যজিতের বক্তব্য ‘তিন কন্যা’-র পর থেকে তিনি নিজেই তাঁর ছবির সংগীত পরিচালনা করেন। তার আগে রবিশঙ্কর, বিলায়েত খাঁ এবং আলি আকবর তাঁর ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন। ছবির জগতে আসবার আগেই সংগীতের ওপর তাঁর ঝোঁক ছিল।
গল্পের মধ্যে তিনি কি খোঁজেন তার জবাবে সত্যজিৎ বলেছিলেন, এর উত্তর দেওয়া কঠিন। একটা গল্পের মধ্যে নানান চরিত্র, নানান ঘটনা ও পরিবেশ থাকে। যেমন ডস্টয়ভস্কির উপন্যাস এত বিরাট যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ছাড়া ছবি করা প্রায় অসম্ভব।
সত্যজিতের সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছবির শেষে কোনো সমাধান থাকে না কেন, এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য শেষে তিনি কোনো সমাধান দিতে চান না। তিনি চান দর্শকরা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করুক। কোনো ছবি সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে বলে তিনি মনে করেন না।
জর্জেস সাদুলেব৪ সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন স্টুডিয়োর বাইরে স্বাভাবিক পরিবেশ ছবিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রাণবন্ত ল্যান্ডস্কেপ পরিচালককে এমন অনুপ্রেরণা যোগায় যা আইজেনস্টাইনের মতবাদকেও নস্যাৎ করে দিতে পারে। পাশ্চাত্য সংগীতের কাছে তার অশেষ ঋণ। প্রথমবার ইউরোপে গিয়েই তিনি মোৎসার্ট উৎসবে যোগদান করবেন ঠিক করেছিলেন।
নতুন নতুন মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে ছবি করার কথা তিনি ভেবেছেন, তবে তা এমন হবেনা যা দর্শকের অবোধ্য। তিনি দর্শকের কাছাকাছি থাকতে সবসময় চেষ্টা করেন।
সত্যজিৎ আরও বলেন তিনি অপব্যয় না করে যথাসাধ্য অল্প খরচে ছবি করেন। এমনকি রঙিন ছবিও তিন চার লাখ টাকা বাজেটের মধ্যে রেখে চার সপ্তাহে তিনি শেষ করেছেন। অল্প খরচের ছবি, তাই টাকা উঠে আসতে তেমন অসুবিধে হয় না।
পরিচালক হিসাবে দেবকী বসুকে৫ তাঁর খুব পছন্দ কারণ তাঁর ছবিতে বাঙালিদের আচার আচরণ গভীরভাবে ফুটে উঠেছে, যেমন তাঁর ছবি ‘কবি’। দেবকী বসুর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।
দেবকী বসু তাঁকে বলেছিলেন, ‘পথের পাঁচালী’ নিয়ে ছবি করার কথা তিনিও ভেবেছিলেন, যদি করতেন সত্যজিতের ছবির মতো অত ভালো হত না। দেবকী বসুর মতো পরিচালকের মুখে অমন কথা অনুপ্রাণিত করেছিল সত্যজিতকে।
.
এ কথা আজ আর গোপন নয় যে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কাজ করার জন্য সুপারস্টাররা পর্যন্ত উৎসুক, লোভনীয় টাকার প্রস্তাব এজন্য তাঁরা বিসর্জন দিতেও পরাঙ্মখ নন। মানিকদা একবার মুখ ফুটে বললেই হল, সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছেড়ে তাঁরা হাজির হবেন। অমিতাভ বচ্চন বলেছেন, ‘আমি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় কাজ করতে চাই। কি চরিত্র, কেমন গল্প, তাতে যায় আসেনা, সবকিছু নির্ভর করবে সত্যজিতের ওপর।’ অমিতাভ আরও বলেছেন, ‘আমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে শুটিং করতে রাজি, স্বাস্থ্য বা সময় বাধা হবেনা।’
এই মানসিকতার পেছনে একটাই কিন্তু কারণ, সেটা হল সত্যজিৎ রায়ের ছবি মানেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও খ্যাতি। যে কোনো স্টারের কাছে সেটা মস্ত বড়ো সম্মান, সত্যজিৎ রায়ের ছবির ভেতর দিয়ে তাঁরা যে পৌঁছে যাবেন বিশ্বের চলচ্চিত্রের দরবারে।
***
১. ‘অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের ভূমিকা’ চরিত্রটিতে রূপদান করেছিলেন ‘ভিকি রেডউড’ নামক এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অভিনেত্রী।
২. ‘আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক তরুণ প্রযোজক’ এই প্রযোজকের নাম মাইক উইলসন, যিনি পরবর্তীকালে সত্যজিতকে বহু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি ফেলেন ‘দ্য এলিয়েন’ ছবির সূত্রে। পরবর্তীতে শিভা কল্কি নাম নিয়ে ইনি সাধু বনে যান এবং সত্যজিৎকে ‘রাবণ’ শিরোপায় অভিহিত করে একটি চিঠি লিখে ‘দ্য এলিয়েন’-এর থেকে নিজের আরোপিত অধিকার তুলে নেন। কিন্তু ছবিটি সত্যজিতের নানা কারণে আর করে ওঠা হয়নি।
৩. ডেভিড সেলজনিক (১৯২০—১৯৬৫) প্রখ্যাত আমেরিকান প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার। ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’ (১৯৩৯), রেবেকা (১৯৪০) প্রভৃতি ছবির প্রযোজনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়কে নিজের অধীনে পেতে ইচ্ছুক হলেও, তাঁর শর্তে রাজি হননি সত্যজিৎ।
৪. জর্জেস সাদুল (১৯০৪—১৯৬৭) বিখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্র সমালোচক এবং চিত্রনাট্যকার ছিলেন সত্যজিতের একজন গুণগ্রাহী। মূলত তাঁর আগ্রহ এবং অনুরোধেই সত্যজিৎ ‘পথের পাঁচালী’র চিত্রনাট্যের মূল কাঠামো সংকলিত স্কেচখাতাটি প্যারিসের ‘সিনেমাথেক’-এর সংগ্রহে দিয়ে দেন। দুঃখের বিষয় জীবনের শেষপ্রান্তে সত্যজিৎ একবার ওই খাতাটি দেখবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তখন জর্জ সাদুল প্রয়াত হয়েছেন, প্যারিসের ‘সিনেমাথেক’-এ যোগাযোগ করা হলে তাঁরা সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়কে জানান যে খাতাটি মিউজিয়ামের সংগ্রহ থেকে খোয়া গেছে। বহু পরে ২০১৫ সালে খাতাটির একটি ডিজিটাল কপির সন্ধান পাওয়া যায় ও পুস্তকাকারে প্রকাশ পেয়ে নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে জনসমক্ষে ফিরে আসে এই সত্যজিৎ-সৃষ্টি।
৫. দেবকী বসু (১৮৯৮—১৯৭১) প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার দেবকীকুমার বসু ভারতীয় তথা বাংলা চলচ্চিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে ডি. জি.-র সহকারী হিসেবে প্রথমে ব্রিটিশ ডমিনিয়ন ফিলম-এ কাজ করা থেকে শুরু করে পরবর্তীতে প্রমথেশ বড়ুয়ার সাহচর্যে আসেন। স্বাধীনভাবে পরিচালনা এবং প্রযোজনা শুরু করেন এর পরে। ‘নিশির ডাক’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘কবি’, ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’, ‘চিরকুমার সভা’ প্রভৃতি ওঁর বিখ্যাত কাজগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৭ সালে পরিচালক জেমস বেভেরিজ যখন সত্যজিৎ রায়ের উপর তথ্যচিত্র ‘ক্রিয়েটিভ পার্সনস সত্যজিৎ রায়’ নির্মাণ করেন, তখন সেটির জন্য এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন দেবকীকুমার বসু। সত্যজিৎ তাঁর চেয়ে বয়সে নবীন হলেও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব কখনো প্রতিফলিত হয়নি দেবকী বসুর আচরণে।
