অধ্যায় : চোদ্দ – জাতিস্মর কাহিনীর প্রথম পর্যায়
এ’বার আমরা ‘আত্মা’ ও ‘জাতিস্মর’-এর অনস্তিত্ব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার খোলস ছেড়ে প্রয়োগের দিকে নজর দেব। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, ‘আত্মা’ ও ‘জাতিস্মর’ প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরও কোনও এক জাতিস্মর কাহিনীকে টেনে এনে প্রশ্নকর্তা এ বিষয়ে সরাসরি আমাদের মতামত জানাতে বলেন।
জানতে চাওয়ার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সাধারণত জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিকতাও একান্তভাবেই খাঁটি। তাঁদের এই জানতে চাওয়া কাহিনীগুলো সাধারণভাবে মাত্র কয়েকটি কাহিনীর মধ্যেই আবর্তিত হয়।
আলোচনার এই শেষ পর্যায়ে আমরা প্রচলিত সেই সব জনপ্রিয় ও সাড়া জাগানো জাতিস্মর কাহিনী নিয়েই আলোচনা করব। এই কাহিনীগুলোকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করব। প্রথম পর্যায়ে থাকবে অতি বিখ্যাত, আমাদের দেশে সবচেয়ে সাড়া জাগানো ঘটনাগুলো। এ’গুলো নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় যাব। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখব জনপ্রিয় কিন্তু আমাদের দেশে জনপ্রিয়তার নিরিখে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিখ্যাত কিছু কাহিনীকে। তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা করব অবতারদের পুনর্জন্ম নিয়ে গড়ে ওঠা রোমাঞ্চকর কিছু কাহিনী। এই পর্যায়ের অবতাররা অবশ্যই আন্তর্জাতিক পরিচিতির অধিকারী।
আসুন আমরা এ’বার প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় ঢুকি
জাতিস্মর তদম্ভ ১ : দোলনচাঁপা দোলনের কথা
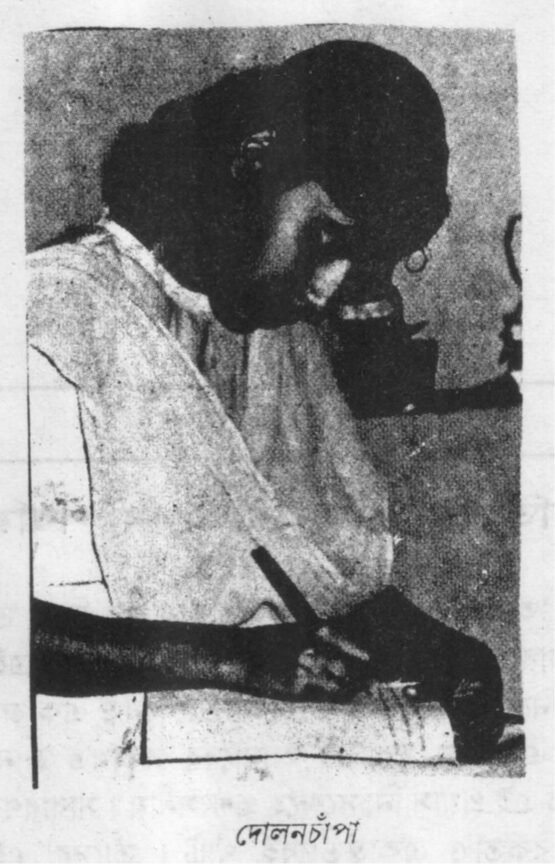
দোলনচাঁপা মিত্রের জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার প্রথম অনুরোধ জানান আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ। কলকাতার আকাশবাণী ভবনে এক প্রযোজকের ঘরে আড্ডা দিচ্ছিলাম। সম্ভবত আমার উপস্থিতির কারণেই আড্ডার আলোচনাটা এক সময় মোড় নিয়েছিল তথাকথিত নানা অলৌকিক ঘটনা নিয়ে। এরই মাঝে এক সময় এল দোলনচাঁপার কথা। পার্থ জানালেন, দোলনচাঁপা তাঁর পরিচিতা। দীর্ঘ বছর ধরেই দোলনদের পুরো পরিবারকেই চেনেন পার্থ। দোলন নাকি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে। ওর ওই জাতিস্মর-ক্ষমতা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় বেশ কিছু বছর আগে একটা খবরও প্রকাশিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক প্রবক্তা লোকেশ্বরানন্দ দোলনের জাতিস্মর ক্ষমতার দাবিকে ‘যথার্থ’ বলে সমর্থন করায় বিষয়টা খুবই গুরুত্ব পেয়েছে।
পার্থ আরও জানালেন, “আপনি তো যুক্তিবাদী, সত্যানুসন্ধানী। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখুন না, বাস্তবিকই ঘটনাটা কী! এবং তারপর আপনার মতামত, জনসাধারণকে জানান।”
দোলনের খবর আমার চোখে প্রথম পড়েছিল ১৯৮০ সাল নাগাদ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পারাসাইকোলজিস্ট, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজি বিভাগের প্রধান আয়েন স্টিভেনসন (Ian Stevenson) এর লেখা “কেসেস অফ দ্য রিইন্কারনেশন টাইপ” (Cases of The Reincarnation Type) বইয়ের প্রথম খণ্ডে প্রচণ্ড গুরুত্ব পেয়েছে দোলনের কেসটি।
‘৮৮র এপ্রিলের এক বিকেলে হাজির হলাম মানিক মিত্রের অফিসে। মানিকবাবু তখন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টারের সিনিয়র লেকচারার। ভাল নাম ঔদার্যময়, তবে মানিক নামেই বেশি পরিচিত। মানিকবাবু কাটিহারের ছেলে। চাকরি জীবন শুরু করেছিলেন পাটনাতে পশু চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক হিসেবে। ‘৫৮ সালে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে যোগ দেন। ‘৬২তে বিয়ে করেন কণিকাকে। ‘৬৩ সালে জন্ম হয় ছেলে জয়ন্ত’র। ৮ আগস্ট ‘৬৭তে দোলনের জন্ম। সন্তান বলতে এই দুটিই।
ফর্সা টুকটুকে ছোট্ট দোলন এক বছর বয়সে কথা বলা শুরু করেছিল। দু’বছরের মধ্যেই স্পষ্ট কথা বলতে শিখে ফেলল। রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমের মধ্যেই মানিকবাবুর কোয়ার্টার। হাজারো রকমের গাছ-গাছালিতে ঘেরা আশ্রমের পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়ে উঠতে লাগল দোলন। তিন বছর বয়স থেকে দোলনের পোশাক- পরিচ্ছদের ভাললাগার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেলেন মা কণিকা। দোলন ফ্রক পড়তে চায় না। ছেলেদের মত প্যান্ট-সার্ট পরার প্রতিই ওর তীব্র আগ্রহ। সুন্দর ও দামী ফ্রকের চেয়ে দাদার বেঢপ মাপের প্যান্ট-সার্ট পরেই ওর আনন্দ।
‘৭১-এর গরমকালের এক দুপুর। দোলনকে দাদার প্যান্ট পরে থাকতে দেখে মা একপ্রস্থ খুব বকা-ঝকা করলেন, “এ কি উদ্ভট স্বভাব! মেয়েদের পোশাক না পরে সব সময়ই ছেলেদের পোশাক পরা?”
দুপুরে খাওয়ার পাট চুকিয়ে মা ডাকলেন, “আয় দোলন আমার পাশে শুবি আয়।”
দোলন ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিল, “আমি তোমার পাশে শোব না। তুমি মোটেই ভাল মা নও। আমাকে খুব বকো। আগের মা আমাকে খুব ভালবাসতো।”
মেয়ের কথা শুনে হেসে ফেলেন কণিকাদেবী। “তোর আগের মা আবার কেউ ছিল নাকি?”
“ছিলই তো। সেই মা’কে দেখতে তোমার চেয়েও সুন্দর। কত গয়না পরতো। আমাকে কত আদর করতো। কখনও বকতো না।”
“তোর সেই মা এখন গেল কোথায়?” হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন কণিকাদেবী।
“কোথায় আবার? নিজের বাড়িতেই আছে।”
“নিজের বাড়ি মানে? তোমার আগের মা’র নিজের বাড়ি কোথায়?” “বর্ধমানে। ওখানে আমাদের মস্ত একটা লাল বাড়ি আছে।” ছোট্ট দোলন ঘাড় দোলাল।
“ওখানে আর কে কে থাকে রে?” কণিকা জিজ্ঞেস করলেন। “বাবা থাকেন। আমার আগের জন্মের বাবা, বাবাও আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি তো আগে ছেলে ছিলাম। আমার কত প্যান্ট-সার্ট ছিল। আমরা তো খুব বড়লোক ছিলাম।”
“ঠিক আছে, আগের জন্মে তুই ছেলে ছিলি। এবার তো মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, তাই মেয়েদের পোশাক পরতে হয়। আয় শুবি আয়।”
অভিমানী মেয়ের তাও অভিমান ভাঙে না। মায়ের কাছে এসেও দোলন গজ- গজ্ করে। “জান, আমাদের মটোর গাড়ি ছিল। আমি মটোরে করে স্কুলে যেতাম; কলেজে যেতাম। আমাদের বাড়ির কাছে একটা মন্দির ছিল। বাড়িতে দুর্গাপুজো হতো। আমার এক বন্ধু ছিল—রঞ্জিত।”
একরত্তি ছোট্ট মেয়ের মুখে ওইসব কথা শুনে মা কেমন যেন ঘাবড়ে যান। তারপর মনকে সায় দেন, ও’সবই বাচ্চাদের কল্পনা।
প্রথম সাক্ষাৎকারে কণিকাদেবীই আমাকে এ’সব কথা বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, “ওই দিনের পর থেকে দোলন যেন কেমন পাল্টে গেল। সব সময় একটা ঘোরের মধ্যে থাকত, চিন্তায় ডুবে থাকত। চোখে-মুখে বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট। প্রায়ই বর্ধমানের বাড়ির কথা বলত। সে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বায়না ধরত। ওর আগের জীবনের অনেক কথাই বলত। বলত – আমার নাম ছিল
ওর বুল্টি। একবার আমার অসুখ করেছিল। মাথায় ব্যথা হতো। হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতালের বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। পায়ে ব্যথা লেগেছিল।”
“কোন্ হাসপাতালে ছিলি?” মায়ের প্রশ্নের উত্তরে দোলন জানিয়েছিল, “কোলকাতার হাসপাতালে।”
দোলন একটু একটু করে বুল্টির জীবনের অনেক কথাই জানিয়েছিল। ফুটবল খেলত, ক্রিকেট খেলত। বাড়ির কাছেই একটা মন্দির ছিল। বাড়িতে হরিণ ছিল, ময়ূর ছিল। নীল ডোরাকাটা একটা সার্ট ছিল। বাড়ি ছিল বর্ধমান শহরে।
দোলনের কথার মধ্যে এমন একটা প্রত্যয় ছিল, যা মানিকবাবু ও কণিকাদেবীকে চিন্তিত করে তুলেছিল। দোলন কি তবে সত্যিই জাতিস্মর? এতদিন ধর্মগ্রন্থ ও অধ্যাত্মবাদের বইয়ের পাতাতেই শুধু পড়েছেন জন্মান্তরের কথা। সেই চরম বিশ্বাসকে সত্যি বলে প্রমাণ করতে তাঁদের বাড়িতেই জাতিস্মরের জন্ম হয়েছে! ভগবানের কি অপার লীলা।
যত দিন যাচ্ছিল দোলনের মধ্যে বর্ধমানে যাওয়ার আকুতি ও যন্ত্রণা ততই তীব্রতর হচ্ছিল। এমন একটা পরিস্থিতিতে বাস্তব ঘটনাকে জানার আগ্রহে মানিকবাবু ঠিক করলেন, দোলনকে নিয়ে বর্ধমানে যাবেন।
মানিকবাবু ও কণিকাদেবী দোলনকে নিয়ে প্রথম বর্ধমান গেলেন ‘৭১-এর অক্টোবরে। বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদের কাছে ওকে ছেড়েও দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও দোলন তার পূর্বজন্মের বাড়ি খুঁজে বের করতে পারল না। সে’দিনই দোলনকে নিয়ে ওর মা-বাবা নরেন্দ্রপুরে ফিরে এলেন।
দোলনের খুব মন খারাপ। ভালোমত খায় না, খেলে না। মাঝে মাঝে নিজের মনে কাঁদে আর কান্না-ভেজা গলায় মা-বাবাকে অনুরোধ করে – আর একটি বার বর্ধমানে নিয়ে চল। এই সময় থেকে দোলন তার মাথার পিছন দিকে একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকে।
নীলাচল সামন্ত বর্ধমানের মানুষ। সম্পর্কে বম্বের সিনেমাওয়ালা শক্তি সামন্তের ভাই। চাকরি করেন নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে। মানিকবাবুর বন্ধু। দোলনের কথাগুলোকে পূর্বজন্মের স্মৃতি থেকে উৎসারিত কথা ভেবে তিনিও মাথা ঘামাতে শুরু করেন। তিনি মানিকবাবুকে জানালেন—বর্ধমান মহারাজার বাড়ির কাছেই একটি ধনী পরিবার থাকেন। সেই পরিবারের চারু দে তাঁর পরিচিত। সেই সুবাদে পরিবারের অনেক কিছুই তাঁর জানা। ওই পরিবারের একটি ছেলের নাম ছিল বুল্টি। ভাল নাম নিশীথ দে। নিশীথ মাথার ব্যথায় ভুগছিল। সম্ভবত ব্রেন-টিউমার হয়েছিল। কলকাতায় এসেছিল চিকিৎসা করাতে। তারপর মারা যায়। বুল্টি মারা গেছে ১৯৬৪- তে, দোলনের জন্মের তিনবছর আগে। বুল্টির বাবা অনাথশরণ দে বর্তমানে পরিবারের কর্তা। বুল্টি ছিল অনাথবাবুর বড় ছেলে। মেজ শিশির। ডাক নাম ন্যাড়া। তিন মেয়ে। নাম যথাক্রমে শ্যামলী, জ্যোৎস্না ও রীতা।
নীলাচল সামন্তর স্ত্রী স্বপ্নাও বর্ধমানের মেয়ে। নিশীথ দে’র আত্মীয় পৃথ্বীশচন্দ্র দে’র পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। সেই সুবাদের স্বপ্না বুল্টি ও তার পরিবারের অনেক হেঁসেলের কথাই জানতেন। স্বপ্নাও দোলনের ‘আবোল-তাবোল’ কথার মধ্যেই খুঁজে পেলেন এক ধর্মীয় সত্যকে—এক জাতিস্মর দোলনকে। স্বপ্নদেবী ও নীলাচলবাবুর কথায় মানিকবাবু ও কণিকাদেবী যেন খুঁজে পেলেন দোলনের হেঁয়ালির কিছুটা হদিস।
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ তাঁর স্নেহভাজন স্বপ্নাদেবী ও নীলাচলবাবুর পরামর্শে মানিকবাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা দোলনকে নিয়ে আবার বর্ধমান গেলেন। সময়টা ‘৭২ সালের ৩০ মার্চ। বর্ধমানে ওঁরা উঠলেন স্বপ্না সামন্তর বোন প্রতিমা দাঁ’র বাড়িতে।
বর্ধমানে এসে দোলনের আনন্দ আর ধরে না। সেদিনই বিকেলে দোলনকে নিয়ে বেরুলেন কণিকাদেবী, প্রতিমা দাঁ ও পৃথ্বীশ দে’র স্ত্রী মীরা দে। ওঁরা দোলনকে নিয়ে হাজির হলেন বুল্টিদের বাড়ির কাছের অন্নপূর্ণার মন্দিরে। তারপর সেখান থেকে বুল্টিদের বাড়ির দিকে। লাল রঙের বিশাল প্রাসাদ। দোলনকে ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন এটা তোমার বাড়ি?
ছোট্ট দোলন, খুশিতে ডগমগ করতে করতে জানাল, হ্যাঁ, এটাই ওদের বাড়ি ছিল।
সদর দরজার ‘নক’ করতে দরজা খুলে দিয়েছিলেন অনাথবাবুর ছোট মেয়ে রীতা। অতিথিদের আগমনের অদ্ভুত কারণে হতবাক্ রীতা। ভিতরে নিয়ে এলেন ওঁদের। অনাথবাবু বাড়ি ছিলেন না। গিয়েছিলেন কলকাতায়। পুরুষ সদস্য হিসেবে
। সে সময় বাড়িতে ছিলেন শুধু অনাথবাবুর ছোট ছেলে শিশির। দোলনের কাহিনী শুনে বাড়ির সকলেই অতিমাত্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। সত্যিই কি বুল্টি দোলন হয়ে এ’বাড়িতে এসেছে? উপস্থিত অনেকেই দোলনকে জেরা করে নিজেদের কৌতূহল মেটাতে চান। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে ছিলেন বুল্টির খুড়তুতো ছোট- কাকীমা লক্ষ্মী দে। লক্ষ্মী দেবী দোলনকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “বল তো আমি কে?” দোলন লক্ষ্মীদেবীর দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে বলল, “তুমি ও’বাড়ির ছোট কাকীমা।” রীতা দোলনকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার আগের জন্মের মা কে বল তো?” দোলন একজন ফর্সা, মোটাসোটা মহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “এই তো আমার মা।”
দোলন বুল্টির মা’কেই নিজের মা বলে চিহ্নিত করেছিল। এমন একটা অদ্ভুত, অকল্পনীয় ব্যাপার চোখের সামনে ঘটতে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বুল্টির মা। দু’চোখে তার বিস্ময়ের ঘোর। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কোনও একটা মানসিক দ্বন্দ্বে পীড়িত হচ্ছিলেন। দোলন আদরের প্রত্যাশায় বুল্টির মায়ের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল।
কণিকাদেবী দোলনের মনোভাব বুঝে বললেন, “ওকে একটু কোলে নিন। ও আপানার আদর পেতে চায়।”
বুল্টির মা হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেলেন। দোলনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, “আপনার মেয়েকে আপনি নিন। আমার কোনও দরকার নেই।”
অভিমানী দোলন দুঃখ পেয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করেছে, “মা আমাকে আদর করেনি; আমাকে বকেছে।”
এরপরও দোলন বুল্টির জীবনের সঙ্গে জড়িত অনেক কিছুই বলতে পেরেছে, অনেক কিছুই চিনতে পেরেছে। একটা গ্রুপ ফটো থেকে বুল্টির বাবা অনাদি দে’কে চিনিয়ে দিয়েছিল। শিশিরের ছবি দেখে চিনতে পেরেছিল। দেখিয়ে দিয়েছিল বুল্টির শোবার ঘর, পড়ার ঘর, আলমারি, আলমারির চাবি। আলমারিতে একটা ডোরা- কাটা নীল সার্টও পাওয়া গিয়েছিল।
এ’সব যা লিখলাম, সবই শুনেছি দোলন ও তার মা-বাবার কাছ থেকে।
বুল্টির পরিবারের তরফ থেকে দোলনকে আগের জন্মের বুল্টি বলে মেনে না নেওয়ায় দোলন হতাশ হয়েছিল। নরেন্দ্রপুরে ফিরে এসে আগের জীবনের কথা আর খুব একটা বলত না। এরই কিছু পরে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ইচ্ছেয় এবং যোগাযোগে দোলনের জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৭২-এর ৭ মে। মানিকবাবুর কথায়— স্বামীজী চেয়েছিলেন, খবরটা প্রকাশিত হওয়ার পর এই নিয়ে গবেষণার কাজে কোনও বিজ্ঞানী বা প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসে, তবে তার মধ্য দিয়ে সত্য বেরিয়ে আসবে, প্রতিষ্ঠিত হবে বেদ, উপনিষদ, গীতার কথা— আত্মা জন্মহীন, নিত্য।
এগিয়ে এসেছিলেন একাধিক প্যারাসাইকোলজিস্ট
দোলনের খবরটা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর মানিকবাবু কয়েকজন জ্যোতিষীর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন বলে মানিকবাবু জানান। তাঁরা দোলনের জন্মসময় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।
১৯৭২-এর জুলাইতে প্রণব পাল এগিয়ে এলেন দোলনকে নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে। তিনি পেশায় অধ্যাপক হলেও নেশায় প্যারাসাইকোলজিস্ট। প্রণববাবু প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়ে ঘটনাটি জানান ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যারাসাইকোলজিস্ট আয়েন স্টিভেনসনকে।
অক্টোবরে স্টিভেনসন উড়ে এলেন। অধ্যাপক পালের সঙ্গে নরেন্দ্রপুরে যান, যান বর্ধমানে। নভেম্বরে দেশে ফিরে যান।
আবার ফিরে আসেন ‘৭৩-এর মার্চে। আবার এক দফা অনুসন্ধান। ১৯৭৫- Ian Stevenson 43 ‘Cases of The Reincarnation Type, Volume I’-এ প্রকাশিত হয় দোলনচাঁপার কাহিনী। সেখানে স্টিভেনসন লিখেছেন, “Dolan made all except a few of the Statements about the previous life…” অর্থাৎ, দোলন আগের জীবনের কয়েকটি ছাড়া সব তথ্যই মিলিয়ে দিয়েছিল।
কি কি তথ্য দোলন স্টিভেনসনের সামনে হাজির করেছিল, কি কি মেলাতে পারেনি তার একটা লিস্ট তিনি লেখাটিতে তুলে ধরেছেন। দোলনের ব্যর্থতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং অবশ্যই বিস্ময়কর দিক হলো – ও না বলতে পেরেছিল নিজের পূর্বজন্মের নাম, না বলতে পেরেছিল আগের জন্মের পরিবারের সদস্যদের নাম। স্টিভেনসনের ভাষায়, “…she never mentioned his name or that of any other member of his family”.
দোলনের দেওয়া বহু তথ্যই যে মিলে গেছে বলে স্টিভেনসন দাবি করেছেন, সে সব তথ্যের অনেকগুলোই অতি হাস্যকর। যেমন, “She had a house in Burdwan”. “She had a father in Burdwan”. অর্থাৎ ওর বর্ধমানে বাড়ি ছিল। বর্ধমানে ওর বাবা ছিল। এমনি আরও আছে। যেমন ওর মা ছিল। ওর কাকা কাকী ছিল ইত্যাদি। দোলন ছেলেদের পোশাক পরত, ছেলেদের খেলা খেলত—এ’কথা উল্লেখ করার পর স্টিভেনসন স্বীকার করেছেন, “It happened that in The Ramakrishna Mission Ashrama, where her family lived, the close neighbours had mostly boys”. অর্থাৎ, গোদা বাংলায়— দোলনের পরিবার যে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে থাকত, সেখানে ওর পড়শি ও সঙ্গীদের বেশিরভাগই ছিল ছেলে।
ওই আশ্রমটি যেহেতু ছেলেদের আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র, তাই দোলন আশ্রমের ঘেরা কমপাউন্ডে খেলার সঙ্গী-সাথী যাদের পেয়েছে, যাদের দেখেছে, যাদের সঙ্গে মিশেছে তাদের বেশির ভাগই ছেলে। ফলে ও ছেলেদের পোশাক ও ছেলেদের খেলাধুলার দিকে আকর্ষণ অনুভব করতেই পারে। সাংস্কৃতিক পরিবেশগত এই প্রভাবের ফলকে জাতিস্মর হওয়ার প্রমাণ হিসেবে ধরে নিলে তা হবে এক বিশাল ভুল।
ভারতের নামী প্যারাসাইকোলজিস্ট অর্থাৎ ভূত-প্রেত-অলৌকিক-জাতিস্মর ইত্যাদির গবেষক ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে নামলেন দোলনের জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে অনুসন্ধানের কাজে। কথাটা একটু ভুল লিখে ফেললাম। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় নামলেন দোলনকে জাতিস্মর বলে প্রমাণ করতে।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দোলনকে জাতিস্মর প্রমাণ করতে যে সব যুক্তিকে গুরুত্বের সঙ্গে হাজির করেছেন, সেগুলো হলো :
(১) “আমি এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমরা দুজনেই অনুসন্ধান করে দেখেছি মিত্র পরিবারের সঙ্গে দে পরিবারের কোন যোগাযোগ আগে ছিল না এবং দোলনের পক্ষে অন্য কোন সূত্র থেকেও দে পরিবারের বা নিশীথ (বুল্টি) সম্পর্কে কোন কিছু জানার সুযোগ ছিল না।”
(২) “দোলনই পূর্বজন্মে নিশীথ না হলে এই পড়ে যাবার ঘটনাটি (হাসপাতালের বেড থেকে) জানতে পারার আর কোন উপায় তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।”
(৩) “দোলনের আর একটি কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দোলন আগেই বলেছিল যে সে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ছিল এবং ঐ হাসপাতালেই খাট থেকে পড়ে যাবার কিছুদিন বাদেই সে মারা যায়। হাসপাতালে থাকার সময় তার মাথায় খুবই যন্ত্রণা হত।”
দোলন হাসপাতালে ছিল, সেখানে থাকাকালীন বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিল, এই দুটি তথ্যকে জাতিস্মরতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রতিষ্ঠিত করতেই হয়— এ’জাতীয় কোনও তথ্যই দোলনের পক্ষে জানা কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন এক নম্বর যুক্তিটি, তিনি ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে দেখেছেন বুল্টির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন কারও সঙ্গে দোলনের পরিবারের যোগাযোগ ছিল না। এই অনুসন্ধান যে আগাপাশতলাই ভুল অথবা ভুল পথে জনচিত্তকে চালিত করার অপচেষ্টা তারই প্রমাণস্বরূপ দুই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন বহু পরিবারের নাম হাজির করেছিলাম ‘আলোকপাত’ মাসিক পত্রিকার জুলাই ১৯৮৮ সংখ্যায়। সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেছিলাম বুল্টির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানার সুযোগ দোলনের ছিল। এ’বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনার যাব।
১৯৭৫ সালে মানিকবাবু, কণিকাদেবী ও দোলনকে নিয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান গিয়েছিলেন। মানিকবাবুর কথামত বুল্টিদের পরিবারের কাছ থেকে অনুসন্ধান চালাতে কোনও সহযোগিতা পাননি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ এই অনুসন্ধান ছিল একতরফা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এক অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান।
বুল্টি বা নিশীথ দে’র জীবনী
নিশীথ দে অনাথশরণ দে’র বড় ছেলে। জন্ম ১৯৪০ সালে। নিশীথ পড়ত বর্ধমানের রাজ স্কুলে ও রাজ কলেজে। মৃত্যুর সময় ও ছিল বি.কম.-এর ছাত্র। খেলাধুলায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল ও ক্রিকেট। একটি মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।
বুল্টিদের পরিবার ছিল শহরে অতি ধনী পরিবারের অন্যতম। বুল্টির পরিবার ধনাঢ্য পরিবার ছাড়া মিশত না। এমন কি ধনবান নয়, এমন আত্মীয়দের সঙ্গেও ওরা দূরত্ব বজায় রেখে চলত। বুল্টির স্বভাব এ বিষয়ে ছিল ভিন্ন ধরনের। ও ধনী ও গরিব সব বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গেই মিশতে পছন্দ করত।
১৯৬৪ তে যখন বুল্টির বয়স ২৪ বছর, সে সময় বুল্টি ওর মাথার পিছন দিকে একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকে। ব্যথার সঙ্গে মাঝে মাঝে বমি হত। স্থানীয় ডাক্তার ছ-আট মাস চিকিৎসা করেন। তারপর বুল্টিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ। সেখানে অনুমান করা হয় বুল্টির ব্রেন টিউমার হয়েছে। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগেই বুল্টির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পনের দিন ‘কোমা’য় থেকে ২৫ জুলাই ‘৬৪ বুল্টি মারা যায়। বুল্টির দেহ পোড়ানো হয় কলকাতার নিমতলা শ্মশান ঘাটে।
দোলন এখন
বর্ধমানের দে পরিবারের কাছ থেকে শীতল ব্যবহার পেয়ে শিশুমনে যে আঘাত পেয়েছিল তার ক্ষত একুশটি বসন্ত পার হয়ে আসা দোলন যে ভুলতে পারেনি, সে কথা ’৮৮তে নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে আমার মুখোমুখি বসে দোলন জানিয়ে ছিল। আরও জানিয়ে ছিল—আন্তরিকভাবেই ও দুঃখজনক স্মৃতিগুলো ভুলতে চায়। আর অনেকটা ভুলে থাকার তাগিদেই গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে।
ছেলেদের পোশাকের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, বর্ধমান থেকে ফিরে আসার কয়েক বছরের মধ্যে সে আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে। জানি না, এই বিচ্ছিন্ন করার পিছনে কতখানি ছিল ব্যথা, কতখানি মনের জোর।
‘৮৬-র একদিন বুল্টির খুড়তুতো ছোট কাকীমা লক্ষ্মী দে ও খুড়তুতো ছোটকাকা প্রণবকুমার দে এলেন মানিক মিত্রের কর্মস্থলে। দু’জনের পরিচয় পেয়ে মানিকবাবু খুব একটা খুশি হতে পারলেন না। বললেন, “আপনারা এত বছর পর। এখানে কি মনে করে?”
লক্ষ্মীদেবী বললেন, “আপনারা চলে আসার পর থেকেই আপনাদের খোঁজ করে চলেছি। আমার বোনের বিয়ে হয়েছে নরেন্দ্রপুরেই। ওর কাছ থেকে আপনার খোঁজ পেয়ে আসা। কোনও কূট-তর্ক করতে আসিনি। আমরা এসেছি বুল্টিকে, অর্থাৎ দোলনকে একবার চোখের দেখা দেখব বলে।”
মানিকবাবু ওদের কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী দোলনকে নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আমাকে চিনতে পারছ?”
“হ্যাঁ, তুমি ছোট-কাকীমা।” বলেছিল দোলন।
প্রণব জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আমি কে বল তো?”
“তুমি ছোট-কাকা।”
লক্ষ্মীদেবী ও প্রণববাবুর গুরুভাই বম্বের অভিনেতা অভি ভট্টাচার্য। অভি ভট্টাচার্য লক্ষ্মীদেবীর কাছে দোলনের কাহিনী শোনার পর থেকে প্রায়ই জোর তাগাদা দিতেন–যেমন করেই হোক দোলনের ঠিকানা খুঁজে বের কর।
’৮৮র জুনের এক দুপুরে লক্ষ্মীদেবী ও প্রণববাবুর সঙ্গে তাঁদের গোয়াবাগানের বাড়িতে বসে কথা বলতে বলতে এ’সব জেনেছি। আরও জেনেছি বুল্টির পরিবারের সঙ্গে প্রণববাবুর পরিবারের সম্পর্ক আদৌ মধুর নয়, বরং কিছুটা তিক্ত। তবে বুল্টিকে ওঁরা দু’জনেই ভালোবাসতেন। লক্ষ্মীদেবী ও প্রণববাবুর অকৃত্রিম ভালোবাসায় দোলন তার দমিত-দুঃখের অনেকটাই ভুলতে পেরেছিল।
দোলন ’৮৭তে দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিনাভি স্কুল থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পর দোলনের মা ঠিক করলেন, এবার ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন। মনের মত একটি পাত্রও পেয়ে গেলেন। এই সময় লক্ষ্মীদেবী দোলনকে নিয়ে যান তাঁর গুরুদেব ‘দাদাজী’র কাছে। দাদাজীর স্ত্রী দোলনের বিয়ের কথা শুনে বলেন, “এইটুকু মেয়ের এখনি বিয়ে দেবে কি? ও গান ভালবাসে, ওকে বরং শান্তিনিকেতনে গান শেখাতে ভর্তি করে দাও। দেখবে ওর ভাল বিয়েই হবে।” দাদাজীও একই মত প্রকাশ করেন। তারই ফলস্বরূপ বিয়ের সম্বন্ধ শিকেয় তুলে দোলনকে ভর্তি করা হল শান্তিনিকেতনে। বিষয় নিল— সংগীত।
এ’সব তথ্য জেনেছি দোলন, মানিকবাবু, কণিকাদেবী, লক্ষ্মী দে এবং প্রণব দে’র কাছ থেকে।
১৯৯০-এর জানুয়ারিতে দোলনের জীবনে আসেন সুব্রত রাহা। সুব্রত তখন শান্তিনিতেনেই পড়তেন। বিষয় : ব্যাচিলার অফ সোসাল ওয়েলফেয়ার। ফেব্রুয়ারিতেই দোলন বিয়ে করতে চাইলেন সুব্রত’কে। সুব্রতর কথা মত—এমন বেকার অবস্থায় বিয়ে করায় তার প্র্যাকটিক্যাল অসুবিধে ছিল। তবু এরপরও এপ্রিলেই বক্রেশ্বর মন্দিরে গিয়ে দু’জন বিয়ে করেন। কারণ হিসেবে সুব্রত জানিয়েছেন, “দোলন আমাকে হুমকি দেয় তাকে immediately বিয়ে না করলে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে এবং অস্বাভাবিক সব ব্যবহার করতে থাকে, যেমন কথা বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, বমিকরা, দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া, হঠাৎ কাউকে না চিনতে পারা, সারা শরীর কাঁপা ইত্যাদি। এসব দেখে আমিও একটু ভয় পেয়ে যাই এবং মনে মনে ভাবি একে বিয়ে না করলে বোধ হয় সে সত্যিকারের আত্মহত্যা করবে বা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে।” ২৬ এপ্রিল ‘৯০ দু’জনের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়।
বিয়ের পর সুব্রত রাহা আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে আমার প্রতি তাঁর উম্মা প্রকাশ করেন। কারণ সে সময় দোলনের জাতিস্মরতা প্রসঙ্গে যা লিখেছিলাম তার মোদ্দা কথা দোলন হয় মানসিক রোগী, নয় প্রতারক।
১৯৯৪-এ সুব্রত রাহা মানবতাবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদককে একটি চিঠি লিখে দোলন থেকে উদ্ভূত সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাতে এ কথাও চিঠিতে লেখা রয়েছে, “শ্রীযুক্ত প্রবীর ঘোষ যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন, দোলনকে মানসিক রোগী বলে দাবী করতেন তখন আমার ওনার ওপর একটু রাগ হতো, তবে আজ আমি বুঝতে পারছি উনি 100% সঠিক।”
সুব্রত’র কেন এমন মনে হলো? সে প্রসঙ্গে চিঠিটিতে সুব্রত লিখছেন, “দোলনের মিথ্যা কথা বলার অস্বাভাবিক প্রবণতা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঝামেলায় জড়িয়ে দিয়েছে এবং তার মিথ্যে কথাগুলো অত্যন্ত নীচু মনের পরিচায়ক। কিন্তু যে মুহূর্তে দোলন ধরা পড়ে যেত যে সে মিথ্যে বলছে বা বলেছে, সাথে সাথে হয় দাঁতে দাঁত লেগে অজ্ঞান হয়ে যেত”…. “আজ পরিচয় হলে আগামী কালই তাকে মনে রাখতে পারত না। তার এই শরীর কাঁপুনি বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক লাগত কারণ কোনোদিন সে এর জন্য ওষুধ খেতে রাজি হতো না” … “বেশ কয়েকবার তাকে মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাব বলি, এবং এটা শুনলেই সে প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করে উঠত এবং জিনিষপত্তর ছুঁড়তে শুরু করত” ….”আমাকে উঠতে বসতে প্রায়ই বলত যে ও হয় আত্মহত্যা করবে বা পালিয়ে যাবে যদি আমি ওর কথায় না উঠি বা বসি, সাথে ভয় দেখাত যে সুইসাইডও নোটে আমাকে ও আমার মা-ভাইকে ফাঁসিয়ে দেবে।”
সুব্রত রাহা এখন জলপাইগুড়ি জেলার বেইন্টগুড়ি টি এস্টেটে ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। দোলন ও সুব্রতর একটি কন্যা হয়েছে। কন্যার আগমনও পারেনি দু’জনের মনের ভাঙনকে জোড়া লাগাতে। ‘৯৪-এর সেপ্টেম্বরে দু’জনে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনেছেন কোর্টে।
দাদাজী ও তাঁর পত্নীর ভবিষ্যৎবাণী “দেখবে ওর ভালই বিয়ে হবে” মিথ্যে হয়ে গেছে। মিথ্যে হয়ে গেছে দাদাজীর অলৌকিক ক্ষমতার দাবি। ওঁরা সে সময় যদি দোলনকে মানসিক চিকিৎসা করাতে বলতেন, তাহলে এমনভাবে দু’টি জীবন ও দুটি পরিবারের শান্তি এভাবে নষ্ট হতো না।
আমি অনুসন্ধানে যা পেয়েছি
সেই প্রকৃত যুক্তিবাদী, যে খোলা মনের। এই খোলা মন নিয়েই দোলনের বিষয়ে অনুসন্ধানে নেমেছিলাম। উদ্দেশ্য – সত্য প্রকাশিত হোক। এই বিষয়ে যাঁদেরই সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের কয়েকজনকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, “আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তথ্য গোপন না করে বা বিকৃত না করে আপনার মতামত লিখব।” সঙ্গে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, “সত্যানুসন্ধানের নামে পাঠক- পাঠিকাদের রোমাঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে গল্প ফাঁদাটাকে আমি ঘৃণ্য অপরাধ বলেই মনে করি।” তবু একাধিক ক্ষেত্রে যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁরা আমাদের কথপোকথন টেপবন্দী করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য : সত্য, যাতে বিকৃত না করতে পারি।
প্যারাসাইকোলজিস্ট অধ্যাপক প্রণব পাল, আয়েন স্টিভেনসন এবং ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমানের দে পরিবার, অর্থাৎ বুল্টিদের পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে সহযোগিতা পাননি বলে লেখায় পড়েছি এবং শুনেছি। আমার অনুসন্ধানপর্বে কিন্তু দে পরিবার পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন।
| দোলন যা বলেছে | এই বিষয়ে যাদের সাক্ষ্য নিয়েছি | আমার মন্তব্য |
| ১। দোলন বুল্টির বর্ধমানের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল। | মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, দোলন। | বুল্টিদের প্রাসাদতুল্য বাড়ির কাছে দোলনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কাছাকাছি ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাড়ি। |
| ২। বুল্টির জীবিতকালে ওদের বাড়ির রঙ ছিল টুকটুকে লাল। | মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, দোলন, অনাথশরণ দে, শিশির দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে। | ভুল। দে পরিবারের বিভিন্ন জনের সাক্ষ্যে এবং স্থানীয় মানুষদের সাক্ষ্যে জানতে পারি বাড়ির রঙ চিরকালই হালকা গেরুয়া। |
| ৩। দোলন গ্রুপ ছবি দেখে কণিকা মিত্র, বুল্টির বাবাকে চিনিয়ে অনাথশরণ দে, দিয়েছিল। | কণিকা, দোলন, অনাথশরণ, শিশির, লক্ষ্মী। | লক্ষ্মী দে বলেন, ওঁর ঠিক স্মরণ নেই, অনাথশরণ ও শিশির জানান, দোলন বুল্টির বাবা বলে যার ছবি দেখিয়েছিল, সেটা ছিল বুল্টির কাকা অনিলকুমার দে’র ছবি। |
| ৪। দোলন বুল্টির ভাই শিশিরকে চিনিয়ে দিয়েছিল অনাথশরণ। দ্বিতীয় বর্ধমান যাত্রায় ছবিতে এবং ‘৭৫-এর তৃতীয় যাত্রায় বাস্তবে শিশিরকে চিহ্নিত করেছিল। | দোলন, কণিকা, শিশির,অনাথশরণ। | অনাথশরণ এবং শিশির জানান, গ্রুপ ছবি থেকে শিশিরকে চিহ্নিত করার কাহিনী পুরোপুরি মিথ্যে। ‘৭৫-এর তৃতীয় যাত্রায় শিশির যে বুল্টির ভাই, এটা আদৌ গোপন ছিল না। তাই নতুন করে চিনিয়ে দেবার প্রশ্নও ছিল না। |
| ৫। দোলন বুল্টির ছোটবোন রীতাকে চিনতে পেরেছিল। লক্ষ্মী। | কণিকা, শিশির, অনাথশরণ, কণিকা ও লক্ষ্মী | কণিকা ও লক্ষ্মীর কথায় দোলনের বক্তব্যের সমর্থন মেলে। অনাথশরণ ও শিশির জানান, রীতা তখন ঘরেই ছিল না। অতএব রীতাকে দেখা ও চিনে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না। |
| ৬। দোলন লক্ষ্মীকে ‘ও বাড়ির ছোট কাকীমা’ বলে জানিয়েছিল। | লক্ষ্মী, দোলন, শিশির, অনাথশরণ, প্রণবকুমার দে। | লক্ষ্মী দেবী বলেছেন, দোলন ও কথা বলেছিল। শিশির বলেন, “প্রকাশ্যে আর কারও সামনে দোলন ও কথা বলেনি সুতরাং লক্ষ্মী কাকীমার কথা সত্যি, কি মিথ্যে, বলতে পারব না।” “লক্ষ্মীদেবী ও শিশির স্বীকার করেন তাঁদের দুই পরিবারের সম্পর্ক বেশ কিছু বছর ধরে খুবই খারাপ। ১৯৭৫ সালে গোয়াবাগানের বাড়ির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে পার্টিশন স্যুট করেন প্রণব দে, ১৯৮১ তে বাড়ির দখল নিয়ে আরও একটি কেস শুরু হয়েছে বলে জানান লক্ষ্মী ও প্রণব। অনাথশরণ ও নিশীথ জানান—তাঁদের অপ্রস্তুত করার জন্য লক্ষ্মী দেবী এই বিষয়ে মিথ্যে কথা বললে তাঁরা অবাক হবেন না। |
| ৭। দোলন বুল্টির শোবার ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল। | দোলন, কণিকা, শিশির, অনাথশরণ, অনিল দে। | অনাথশরণ ও শিশির জানান, বুল্টির নির্দিষ্ট কোনও শোবার ঘর ছিল না। বেশ কয়েকটা ঘরেই ও শুতো। যে ঘরটা দোলন দেখিয়ে দিয়েছিল, সে ঘরেও বুল্টি শুতো। |
| ৮। দোলন বুল্টির পড়ার ঘর চিনিয়ে দিয়েছিল। | দোলন, কণিকাদেবী, অনিল দে, লক্ষ্মী দে, শিশির দে। | দোলন একটা পড়ার ঘরে ঢুকেছিল। সেখানে চেয়ার, টেবিলে বই-পত্র ছিল। দোলন একটু দাঁড়িয়ে বলেছিল, ‘এখানে আমি পড়তাম।’ অনাথ দে’র ভাই অনিল দে এবং শিশির এ কথা জানান। বুল্টি সত্যিই ও ঘরে পড়ত। পড়ার ঘরের পরিবেশ দেখে ‘এ ঘরে পড়তাম’ বলার মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই। |
| ৯। দোলন বুল্টির পোশাকের দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী আলমারি চিনিয়ে দিয়েছিল। | দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী দে, শিশির দে, অনাথ দে। | শিশির দে এবং অনাথ দে জানান, ‘তেমন করে নির্দিষ্টভাবে কোনও বিশেষ আলমারি দোলন দেখিয়ে দেয়নি। একট আলমারি দোলন খুলেছিল। সেটা বুল্টির নিজস্ব আলমারি নয়।’ আরও অনেকেরই পোশাক ওতে থাকত। আর একটা কথা। বুল্টির পোশাক শুধুমাত্র ওই আলমারিতে থাকত না। আরও অনেক আলমারিতেই থাকত। দোলনও বলেছে, ওই আলমারিতে আরও অনেকের জামা-কাপড় ছিল। |
| ১০। দোলন ওই আলমারির চাবি চিনিয়ে দিয়েছিল। | দোলন, কণিকা মিত্র, লক্ষ্মী দে, নিশীথ দে। | কণিকা মিত্র এবং লক্ষ্মী দে দোলনের কথা সমর্থন করলেও শিশির দে জানালেন, ‘আলমারির চাবি চেনাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ চাবিই দোলনকে দেওয়া হয়নি।’ |
| ১১। আলমারিতে নীল ডোরা-কাটা সার্ট ছিল। | শিশির দে। | ছিল। ‘কিন্তু সেটা আমার শার্ট।’ এই কথা জানিয়েছেন শিশির। |
| ১২। বাড়িতে হরিণ ও ময়ূর ছিল। | অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে। | আংশিক সত্য। তিনজনেই জানালেন হরিণ কোন দিনই ছিল না। ময়ূর ছিল। |
| ১৩। বাড়িটা দোতলা। | অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে। | বাড়িটা তিন তলা, বুল্টির আমলেই। |
| ১৪। স্কুল ছিল বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মোটরে স্কুলে যেতাম। | অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে। | বুল্টি রাজ স্কুলে পড়ত। সেটা বাড়ির খুব কাছে। স্কুলে প্রথম দিকে হেঁটে এবং পরে সাইকেলে যেত। |
| ১৫। কলেজে মোটরে যেতাম। | অনাথ দে, শিশির দে, অনিল দে, প্রণব দে, লক্ষ্মী দে। | বুল্টি রাজ কলেজে পড়ত। সাইকেলে কলেজে যেত। |
| ১৬। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতাম। | অনাথ দে, শিশির দে। | ফুটবল, ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। তাই সকলেই খেলে। বুল্টিও খেলত। শিশির জানালেন, ‘আমিও খেলতাম, প্রতিটি পাড়ার আর দশটা সাধারণ ছেলেও খেলে।’ |
| ১৭। ছোট্ট বয়স থেকেই ছেলেদের পোশাকের প্রতি আকর্ষণ ছিল। | দোলন, মানিক দে, কণিকা দে। | ছেলেদের মিশনের কোয়ার্টারে থেকে দোলন সঙ্গী হিসেবে প্রধানত ছেলেদেরই পেয়েছে। তাদের খেলাধুলায় অংশ নিয়েছে। এই পরিবেশে ছেলেদের পোশাকের প্রতি মেয়েদের পোশাকের চেয়ে বেশি আকর্ষণ অস্বাভাবিক নয়। আমি এই প্রতিবেদক স্বয়ং চার বোনের মধ্যে মানুষ হচ্ছিলাম বলে ছেলেবেলায় একবার পুজোর পোশাক হিসেবে ফ্রকের বায়না ধরেছিলাম। |
| ১৮। বাড়ি বর্ধমানে, ধনী পরিবারে জন্ম, কাছে মন্দির, পদবী দে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাই। ও মারা যাই। | দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র, অনাথ দে, লক্ষ্মী দে, প্রণব দে। | প্রতি সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণ বলছে এগুলো সত্যি। মানিক মিত্র এবং কণিকাদেবী বলেছেন তাঁরা কেউই কোনও দিনই বর্ধমানে যাননি। দোলনের প্রথম বর্ধমান যাত্রাই ওঁর মা- বাবারও প্রথম যাত্রা। অনাথবাবুর পরিবারের সঙ্গে কোনও রকম পরিচয় ছিল না বলে মিত্র পরিবারও জানিয়েছেন। অতএব মা বাবার কাছ থেকে বুল্টির কথা দোলন শুনেছিল এবং অবচেতন মনে তা ছিল, একনাগাড়ে বুল্টির কথা ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্ক- কোষের কার্যকলাপের বিশৃংখলার দরুন দোলন নিজের সত্তার মধ্যে বুল্টির সত্তাকে অনুভব করেছিল, এই মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব এক্ষেত্রে খাটে না বলে মানিক মিত্রের বিশ্বাস। বুল্টি ও তার পরিবারের গল্প দোলনের শোনার সম্ভাবনা ছিল কি না এটা জাতিস্মরের এই ঘটনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোলনদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষজনের অনেকেই বর্ধমানের মানুষ এবং অনাথবাবুদের পরিবারের পরিচিত। উদাহরণ : ১. নীলাচল সামন্ত মানিক মিত্রের বন্ধু। বুল্টিদের পরিবারকে চিনতেন। বুল্টির ঠাকুরদা চারুবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। ২. স্বপ্না সামন্ত, নীলাচল সামন্তের স্ত্রী। বুল্টিদের পরিবারের অনেক কিছুই জানতেন। ধনী পরিবারের বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। স্বপ্নাদেবীর বোন প্রতিমা দাঁ বুল্টিদের আত্মীয় পৃথ্বীশ দে এবং তাঁর স্ত্রী মীরা দে’র পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। ৩. কানাইলাল ব্যানার্জি। মানিকবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বাড়িতে আসতেন। তিনি বর্ধমানের মানুষ। দে পরিবারের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-পরিচয় না থাকলেও দে পরিবারের বিষয়ে অনেক কিছুই জানতেন। ৪. শশাংক ঘোষ। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক। মানিকবাবুর বন্ধু। বাড়িতে আসতেন। দে পরিবারের বিষয়ে জানতেন। ৫. রাজেন্দ্র চক্রবর্তী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দে পরিবারকে জানতেন। মানিকবাবুর বন্ধু হিসেবে মাঝে মধ্যে নরেন্দ্রপুরে মানিকবাবুর বাড়ি যেতেন। ৬. ডাঃ হেমাঙ্গ চক্রবর্তী। বর্ধমান থেকে এসে নরেন্দ্রপুরে বসবাস শুরু করেছিলেন। সেই সঙ্গে শুরু করেছিলেন হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস। মানিকবাবুর পরিবারের সঙ্গে হেমাঙ্গবাবুর পরিবারের সখ্যতা ছিল। হেমাঙ্গবাবু অনাথশরণ দে’র পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। হেমাঙ্গবাবুর ছেলেও ছিলেন নিশীথের বন্ধু। এদের কেউ কোনও দিন অনাথবাবু ও বুল্টির গল্প মানিকবাবুদের বাড়িতে বসে করেননি অথবা হেমাঙ্গবাবুর ছেলের কাছ থেকে বুল্টির গল্প কখনও শোনেননি এমন নিশ্চিত বিশ্বাস করার মত কোনও তথ্য আমার হাতে নেই। |
| ১৯) দোলন তার মাথায় ব্যথা অনুভব করত। | দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র। | কিছু কিছু মানুষ মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এরা আবেগপ্রবণ, মস্তিষ্ক- কোষের সহনশীলতা কম। বিশেষ সংবেদশীলতার জন্য বহু সময় এরা নিজেদের অজান্তে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে ‘সমব্যথী চিহ্ন’ বা অন্যের ব্যথা নিজের শরীরে সৃষ্টি করেন, অনুভব করেন। এই ধরনের বহু ঘটনাই মানসিক চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে। দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। ‘সমব্যথী’ চিহ্ন বিষয়ে বিস্তৃত জানতে ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ ১ম খণ্ড পড়ুন। |
| ২০) বর্তমানে দোলনের দোলন। মাথায় কোনও ব্যথা নেই। বুল্টিকে নিয়ে চিন্তা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও কমছিল। | দোলন। | মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। আবেগ-প্রবণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সত্তার মধ্যে বুল্টির সত্তাকে অনুভব করার প্রবণতা কমেছে, কমেছে স্বনির্দেশ পাঠিয়ে অন্যের ব্যথা অনুভব করার প্রবণতা। |
| ২১) অ, আ, ক, খ, A, B, C, D, ১, ২, ৩, ৪ থেকেই পড়াশুনো শুরু করতে হয়েছিল। বুল্টি বি.কম পর্যন্ত যা পড়েছে তার কিছুই দোলনের মনে ছিল না। | দোলন, মানিক মিত্র, কণিকা মিত্র। | জাতিস্মর হলে পূর্বজন্মের অন্যান্য স্মৃতির মতো পূর্বজন্মের লেখা-পড়ার স্মৃতিও উজ্জ্বল থাকা, স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মানসিকভাবে কারও সত্তাকে অনুভব করলে তার ব্যবহার অনুকরণ করতে পারে কিন্তু তার জ্ঞান প্রয়োগ সম্ভব নয়। দোলনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। |
জাতিস্মর তদন্ত ২ : চাকদার অগ্নিশিখা
অগ্নিশিখা
সাম্প্রতিককালের মধ্যে যে জাতিস্মর কলকাতাসহ তামাম ভারতের প্রচারমাধ্যমগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সে হলো পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ছোট শহর চাকদার ছোট্ট মেয়ে অগ্নিশিখা।
খবরটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা দৈনিক পত্রিকা ‘বর্তমান’এ। ১০ জুন ১৯৯৪ প্রথম পাতায় বিশাল গুরুত্ব দিয়ে ছবিসহ ছাপা হয়েছিল জেনুইন-জাতিস্মর অগ্নিশিখার লোমখাড়াকরা কাহিনী। অগ্নির প্রবল আবির্ভাবে শহর কলকাতা যেন জাতিস্মরের জ্বরে কাঁপতে লাগল।
সেদিনই জরুরি তলব পেয়ে গেলাম ‘সানন্দা’র দপ্তরে। ‘সানন্দা’ আনন্দবাজার গ্রুপের জনপ্রিয় পাক্ষিক। সানন্দার সহ-সম্পাদক সুদেষ্ণা রায়-সহ অনেকেই মনে হলো যথেষ্ট টেনশনে রয়েছেন। সানন্দার আগামী সংখ্যা জাতিস্মর নিয়ে। আর তার কেন্দ্রবিন্দু চাকদার অগ্নিশিখা। অগ্নিশিখার খবরটা এনে দিয়েছিল আনন্দবাজার গ্রুপের সাংবাদিক বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়। বাল্মীকি দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে অগ্নিকে জাতিস্মর বলে নিশ্চিত হয়ে সে কথা জানিয়েছেন ‘সানন্দা’কে। এমন এক উত্তেজক ‘ক্যাচি ম্যাটার’কে আরও আকর্ষণীয়ভাবে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে একগাদা মাথা খেটেছে। দ্রুত তৈরি হয়েছে পরিকল্পনা। বাল্মীকির অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে জাতিস্মর বিষয়ক নানা লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে আগামী সংখ্যাটি। কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে। অগ্নির জাতিস্মর হয়ে ওঠা নিয়ে অনুসন্ধান, পর্বটি চালানো হয়েছিল অতি গোপনে, যাতে অন্য কোনও পত্রিকা যেন অগ্নির বিন্দু- বিসর্গ না জানতে পারে। আজ কোনও দৈনিক জানতে পারলে, কালই তা ছেপে বের করে দেবে। পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষে আজ জানলে কাল ছাপার কোনও উপায় নেই। তাই পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষে অতি আকর্ষণীয় খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে অতি সতর্কতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা একান্তই প্রয়োজনীয়। অগ্নির ক্ষেত্রে সে গোপনীয়তা পুরোপুরি রক্ষা করার চেষ্টা সত্ত্বেও গোটা পরিকল্পনা ও পরিশ্রমই বরবাদ হয়ে গেছে। ‘বর্তমান’ এর কাছ থেকে আসা আচমকা আঘাত ওঁদের টেনশন বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী সংখ্যাটির কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু অগ্নি, তাই ‘বর্তমান’এ খবরটা বড় করে বেরিয়ে যাওয়ায় সংখ্যাটি পাঠকদের কাছে ব্রাত্য হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই পরিস্থিতিতে অগ্নিকে নিয়ে আমার অনুসন্ধানমূলক লেখা পাঠকদের টানতে পারে মনে করে এই তলব। আমিও জাতিস্মরতার মুখোশ ছেঁড়ার এমন একটা সুযোগ গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধা করিনি।
শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো আগামীকালই নেমে পড়ব কাজে। আমার অনুসন্ধান পদ্ধতিতে না জানি কি আছে ভেবেই বোধহয় সঙ্গী হওয়ার তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করলেন ‘সানন্দা’র দুই সম্পাদক সহযোগী অনিরুদ্ধ ধর ও উজ্জ্বল চক্রবর্তী।
অগ্নিশিখার দাবি সে গত জন্মে জন্মেছিল বর্ধমানের কোটিপতি ব্যবসায়ী ধনপতি দত্তের প্রাসাদে। নাম ছিল দেবযানী। বিয়ে হয়েছিল কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী চন্দন বণিকের সঙ্গে। চন্দন ও শ্বশুর চন্দ্রনাথ প্রায়ই শারীরিক অত্যাচার করত। শেষ পর্যন্ত স্বামী ও শ্বশুর ওকে হত্যা করে।
দেবযানী হত্যা মামলা
বর্ধমানের ধনী ব্যবসায়ী ধনপত্তি দত্ত’র মেয়ে দেবযানী। ১৯৭৫-এ বিয়ে। কলকাতার হিন্দুস্থান পার্ক নিবাসী ধনী ব্যবসায়ী চন্দ্রনাথ বণিকের বড় ছেলে চন্দনের সঙ্গে, বিয়ের পর কোলে আসে তিনটি সন্তান। দুই ছেলে, এক মেয়ে।
১৯৮৩ সালের ২৮ জানুয়ারি বণিকদের প্রাসাদেই খুন করা হয় দেবযানীকে। দেবযানীর মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ২৯ জানুয়ারি। মৃতদেহে ততক্ষণে পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল। মৃতার গলায় ছিল ফাঁসের দাগ।
৩০ জানুয়ারি পুলিশ ওই প্রাসাদ থেকেই গ্রেপ্তার করে দেবযানীর তিন ননদ জয়ন্তী, সুমিত্রা ও চিত্রাকে।
২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাইরে থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দেবযানীর পতি চন্দন, শ্বশুর চন্দ্রনাথ ও দেওর অসীমকে।
১৯৮৩-র ১৩ সেপ্টেম্বর আসামীদের বিরুদ্ধে দায়রা বিচার শুরু হয় আলিপুরে দশম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের আদালতে।
সরকার পক্ষে সাক্ষী ছিলেন ৬৬ জন। আসামীর পক্ষে ২ জন।
বিচারক দিলীপনারায়ণ সেন ‘৮৫-র ১১ এপ্রিল তাঁর রায়ে চন্দন ও চন্দ্রনাথের ফাঁসির আদেশ দেন।
কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করলেও রায় অপরিবর্তিতই থাকে। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চও চন্দন ও চন্দ্রনাথের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে। বহাল থাকে সুমিত্রার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ। সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপের অপরাধে অসীম ও জয়ন্তীর ২ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেন ডিভিসন বেঞ্চ।
সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন চন্দন ও চন্দ্রনাথ। ১৯৮৭-র ১১ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টে দুই বিচারপতি-বিশিষ্ট বেঞ্চে শুনানি হয়। দুই বিচারক তাঁদের রায়ে বলেন, ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। আসামী চন্দ্রনাথ উনসত্তর বছরের বৃদ্ধ। অপর আসামী চন্দন অতি তরুণ ও তিনটি শিশুর পিতা। এই বিষয়গুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে চন্দন ও চন্দ্রনাথকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।
সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে জানা গিয়েছিল দেবযানীর কোটিপতি পিতাকে বার বার দোহন করতেই দেবযানীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতেন চন্দন ও তাঁর পরিবার। ২৮ জানুয়ারি দেবযানীকে হত্যা করে মৃতদেহ ঘরের মধ্যে বিছানা জড়ানো অবস্থায় ফেলে রেখে চন্দনের পরিবারের লোকজন সিনেমা দেখেছেন। মৃতদেহ পাচারের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু পচা গন্ধই ওদের পরিকল্পনায় বাদ সেধেছিল।
দেবযানী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গোটা পশ্চিমবাংলা তোলপাড় করেছিল।
১১ জুন, ১৯৯৪
চাকদার উত্তর ঘোষপাড়ায় আমরা যখন হাজির হলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। অমিত দে’র বাড়ির হদিস জানতে পথচারীদের সাহায্য চাইতে গিয়ে অদ্ভুত ধরনের নিস্পৃহ ব্যবহার পেলাম। যে মধ্য-বয়স্ক মানুষটির কাছে শেষ সাহায্য চেয়েছিলাম, তিনি অমিত দে’র বাড়ির দু-কদম দূরেই থাকেন। চোখ মটকে দু’কাঁধ ঝাঁকিয়ে থুতনি-নির্দেশে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, “দেখুন, বোধহয় ও’বাড়িটা।” বললাম, “আমরা যে অমিতবাবুকে খুঁজছি, তার মেয়ে জাতিস্মর।”
ভদ্রলোক আবার কাঁধ ঝাঁকালেন, “কে জানে মশাই। আমরা পাড়া-পড়শিরা তো এতদিন কিচ্ছুটি জানতে পারলাম না। জানলাম কালকের কাগজ পড়ে।”
ছোট দোতলা বাড়ি। একতলার সম্মুখের দুটি ঘরেই তালা ঝুলছে। আমাদের দিকে গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এলেন এক মলিনবসনা প্রৌঢ়া, তাঁর পিছু-সঙ্গী দু’টি গৃহবধূ, ছিটের সস্তা ফ্রক পরা তিনটি বালিকা ও লুঙ্গি পরা আদুড়-গায়ের দুটি কিশোর। তাঁরা শোরগোল তুলে আমাদের বোঝাতে লাগলেন, বাইরে তালা ঝোলানো থাকলেও ভিতরে লোক আছে। গলা তুলে ডাকুন।
আমরা সেই শুনে হাঁক-ডাক পাড়তেই দোতলার জানালা দিয়ে একটি-দুটি করে মোট একজোড়া পুরুষ ও একজোড়া নারীর মুখ উঁকি মেরেই সরে গেল। একটু পরেই সরু গলিপথ দিয়ে এলেন এক পঞ্চাশ উত্তীর্ণ মহিলা। একটা ঘরের তালা খুলে দিয়ে চাপা গলায় প্রায় ফিফিস্ করে বললেন, “আপনারা কি কোনও পত্রিকার থেকে এসেছেন?”
সম্ভবত আমাদের গাড়ি দেখে অনুমান করে থাকবেন। বললাম, “হ্যাঁ।”
—”কোন পত্রিকা?”
—”আনন্দবাজার গ্রুপের ‘সানন্দা’র তরফ থেকে আসছি।”
ঘরের ভিতরে পা দিয়েই বললেন, “তাড়াতাড়ি ভিতরে আসুন।”
ঘরে ঢুকলাম আমি, অনিরুদ্ধ, উজ্জ্বল ও চিত্র-সাংবাদিক সুদীপ আচার্য। তখনই প্রৌঢ়া চাপা গলায় ফিসফিস করলেন, “দরজাটা বন্ধ করে দিন, ছিটকিনি আর খিল দু’টোই বন্ধ করে দিন,”তারপর বিড়বিড় করে আপনমনেই বললেন, “সব হিংসা….হিংসুকগুলো আড়িপাতার চেষ্টায় আছে……
পড়শিদের হিংসে কেন? এবাড়ির শিশুকন্যাটি আগের জন্মে এক কোটিপতির আদরের তনয়া ছিল প্রমাণ হলে কোটিপতি পরিবারের দাক্ষিণ্যের কিছুটা এই পরিবারের উপর বর্ষাতে পারে অনুমান করেই কি? তারই সূত্র ধরে পড়শিদের ঈর্ষার কথা ভেবেই উষ্মা প্রকাশ করলেন কি অধৈর্য এই প্রৌঢ়া?
উজ্জ্বল দরজার খিল ও ছিটকিনি আটকালেন, প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার পরিচয়?”
—”জাতিস্মর অগ্নিশিখার ঠাকুমা। মানে ওর বাবার মা।” তারপরই দ্রুততার সঙ্গে বললেন, “বর্তমানের লোক বিষদ্বার এসেছিল। কাল শুক্রবারই ওরা বের করে দিয়েছে। আপনাদেরটাও বের করে দ্যান তাড়াতাড়ি করে।”
—”আর কোনও পত্রিকা ইতিমধ্যে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কি?”
—”আজকে দুটো ছেলে আসছিল, বুঝলেন। ওরা দুটো ফটো দেখাল আমাদের। একটা দেবযানী ও দেবযানীর বরের। আর একটা দেবযানীর বর একটা বাচ্চা নিয়ে। অগ্নিশিখার কাছে ওরা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল—এই ছবি দেখে ও ওর বর আর মেয়েকে চিনতে পারছে কি না! ওরা ফল্স্ দিচ্ছিল।”
—”ফস্ যে দিচ্ছিল, এটা কে ধরল, অগ্নিশিখা?”
—”না, আমার বউ ধরে ফেলছে। আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছে, মা মা শোনেন, ওরা কিন্তু মিথ্যা। একজন ভদ্রলোকের মেয়ের হাতে তো চুড়ি থাকবে না, ন্যাংটো থাকবে না। আমরা অমনি অগ্নিশিখাকে সরিয়ে নিয়ে গেছি।”
—”এঁরা কারা?”
—”দিল্লির হিন্দী পত্রিকার লোক, কাঁচড়াপাড়া বাড়ি। আপনাদের মত গাড়ি নিয়ে আসেনি।”
–“আপনারা ছবিগুলো অগ্নিশিখাকে দেখতে যদি দিতেনও তাতেই বা কি হতো?”
—”আমরা চাইনি এই জিনিসটা বাইর হোক। দেড় বছর ধরেই আমার নাতনি কথা-বার্তাগুলো বলছিল। আপনারা কি বললেন না, কি বইটা বের করবেন?”
— “সানন্দা।”
—”সানন্দায় তাড়াতাড়ি বের করে দ্যান, দেরি করতেছেন কেন? “
তারই মাঝে ঘরে ঢুকলেন অগ্নিশিখার বাবা অমিত দে। উচ্চতা পাঁচফুট চার ইঞ্চি থেকে পাঁচ ইঞ্চি। স্বাস্থ্য ভালো। বয়স পঁয়তিরিশের মধ্যে। ওষুধের ব্যবসায়ী। এসে প্রথমেই জানালাটার ছিটকিনি লাগিয়ে সতর্কতার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেককেই একবার ভালোমত ‘মেপে’ নিলেন, ঠাকুমা দরজার আড়ালে দাঁড়ানো বউমা সন্ধ্যাকে দেখে এগিয়ে গিয়ে অগ্নিশিখাকে নিয়ে এলেন। অগ্নিশিখা ঠাকুমাকে আঁকড়ে তখন পুতুল। শ্যামলা রঙ। মিষ্টি মুখ। কদমফুলের মতো চুল।
অমিতবাবু একটা চেয়ারে বসে, ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, “সানন্দা তো সবই ইনভেসটিগেশন করেছে। সবকিছু টেপিংও করা আছে। ওখান থেকে তো সবই শুনতে পারবেন, জানতে পারবেন। আজ সকালে একজন আসছিল। তাকেও এ’কথা বলেছি।”
—”কিন্তু বর্তমান’কে তো বলেছেন।”
—“কথার ছলে একটু হয় তো বলা হয়েছে।”
—”বর্তমানের ছবিটা দেখে মনে হলো ওটা পুরনো ছবি। আপনারাই দিয়েছেন।”
—“হ্যাঁ, আমাদের অ্যালবাম থেকেই কথায় কথায় দিয়ে দিয়েছি।”
অগ্নিশিখার ঠাকুরদা অজিতবাবুর বয়েস ষাটের কাছাকাছি হলেও স্বাস্থ্য দেখে বোঝার উপায় নেই। উনি সরাসরি জানতে চাইলেন আমরা যে ‘সানন্দা’রই লোক, অন্য কোনও পত্রিকার প্রতিনিধি নই, তার কোনও প্রমাণপত্র সঙ্গে আছে কি?
সুদীপ পকেট থেকে ‘প্রেস কার্ড’ বের করে হাতে ধরিয়ে দিতে অজিতবাবু শুধু কার্ডটাই পড়লেন না, ছবির সঙ্গে সুদীপকে মিলিয়ে নিলেন, মাঝবয়সী এক প্রতিবেশী ইতিমধ্যে ঘরের চৌকাঠে। আমাকে দেখিয়ে বললেন, “কিন্তু ওঁকে আগে যেন কোথাও দেখেছি।”
অনিরুদ্ধই জিজ্ঞাসায় লাগাম পরালেন। “সাংবাদিক তো, কত জায়গায় ঘোরাফেরা করেন, দেখতেই পারেন।”
গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। অগ্নিকে দেবযানী বলে প্রচার করার জন্য পত্র- পত্রিকাগুলোকে ব্যবহার করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অগ্নির পরিবারের মানুষজনের আছে— এ যেমন সত্যি; তেমনই সত্যি—ওরা প্রচার-মাধ্যমগুলোর মধ্যে কার কাছে মুখ খুলবে,কার কাছে খুলবে না এ বিষয়ে অতি মাত্রায় সতর্ক। একটি বিশেষ ব্যক্তি (অনুমান করতে পারি-প্রবীর ঘোষ) ও একটি বিশেষ পত্রিকার (অনুমান করতে পারি, সাধারণত আমাদের সমিতির ও আমার সত্যানুসন্ধান যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেই ‘আজকাল’) আবির্ভাব ঘটার সম্ভাবনায় সদা শঙ্কিত ও সতর্ক!
এমন সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই আমি নাম ভাঁড়িয়েছিলাম। পরীক্ষান্তে সন্দেহের মেঘ কাটতে পরিবারের সকলের মাথা থেকে যেন একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নামল। অগ্নির মা সন্ধ্যা দে গুটোন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মুখ খুলেছেন। “বছর দেড়েক ধরেই অগ্নি বলেছে, ওর কলকাতায় বিশাল বাড়ি আছে। গাড়ি আছে। ছ’মাস আগে জানিয়েছে, ওর আগের জন্মের বাবার নাম ছিল ধনপতি দত্ত। তারপর তো সবই বলেছে—বিয়ের পর স্বামী চন্দন, শ্বশুর চন্দ্রনাথ বণিক আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুব মারত। চাইত, দেবযানী যাতে বাপের বাড়ি থেকে মাঝে- মাঝেই টাকা এনে দেয়। শেষ পর্যন্ত চন্দন, চন্দ্রনাথ ওরা তো মেরেই ফেলল দেবযানীকে।”
অগ্নির বন্ধু হয়ে উঠতে একটুও দেরি হল না আমার। খাটের উপরে মাদুর বিছানো। তার উপরে আমি আর অগ্নি দুই বন্ধুতে তুমুল হুটোপুটি, খেলাধুলো শুরু করে দিলাম। অগ্নি আদৌ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। খেলতে খেলতে তারই মাঝে এটা- ওটা কথার মাঝে আমার প্রশ্নগুলো গুঁজে দিচ্ছিলাম। উত্তরও পাচ্ছিলাম।
—”আগের জন্মে তুমি স্কুলে পড়েছ?”
—”বল কোন স্কুলে পড়েছ।” ঠাকুমা বললেন।
—“নার্সারি।”
উত্তরটা ভুল। তবু সে কথা না বলে হৈ-চৈ করা খেলার মাঝখানে পরের প্রশ্নটা করলাম।
— “তুমি যে স্কুলে পড়েছ, সেটা ছোট না বড়?”
—”বড়।”
—”স্কুলটার কী রঙ ছিল?”
—”লাল রঙ।”
— “দিদিমণিদের নাম মনে আছে?”
—”দিদিমণি, দিদিমণি।”
—”স্কুলের বন্ধুদের নাম মনে আছে?”
—”বন্ধু, বন্ধু।”
—”বন্ধু, তার নাম।”
—”বন্ধুই বন্ধু।”
—”তার নাম শুধু বন্ধুই বন্ধু। বাঃ খুব ভাল বলেছ।”
— “তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল?”
—”হ্যাঁ।”
—”তোমার সুজাতা নামে এক বন্ধুর কথা মনে আছে?” (সুজাতা নামের বন্ধুটি আমারই কল্পনায় সৃষ্টি।)
অগ্নিকে চুপ করে থাকতে দেখে বললাম,
“তোমার বিয়েতে এসেছিল, অনেক গয়না দিয়েছিল। একটা জড়োয়ার সেট দিয়েছিল। মনে আছে?”
—”আমার আছে সেট। বাড়িতে আছে।”
—”সুজাতা নামে কোনও বন্ধুর কথা মনে পড়ে?”
ঠাকুমা অগ্নিকে বললেন, “লজ্জা কোরো না, বলো। ওই দেখুন ও হ্যাঁ বলছে, মুখ দিয়ে বলো।”
— “হ্যাঁ।”
—”তোমার মনে আছে রীতা দিদির কথা, তোমাকে পড়াত?”
–“হ্যাঁ…..হ্যাঁ।”
—”বাঃ।”
ঠাকুমা পুতুলরানী নাতনীর এমন উত্তরে খুশি গদগদ কণ্ঠে বললেন, “হ্যাঁ ঠিক বলেছে। ও বলেছিল ওর মাকে।”
শুনে হাসবো, কি কাঁদবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। রীতা দিদি এক কাল্পনিক চরিত্র। আর তাকে নিয়েই কি না….। শিশুর খামখেয়ালিপনাকেও কাজে লাগিয়ে যেভাবে পুতুলরানী অগ্নিকে দেবযানী প্রমাণ করতে তৎপরতা দেখালেন, তাতে বিষয়টাকে নতুন করে ভাবতে বসাটাই অতিমাত্রায় যুক্তিসঙ্গত মনে হলো,
—”আমার বই দেখবে?”
—”নিশ্চয়ই দেখব, দেখাও, দেখাও।”
—অগ্নি কাচ-আলমারি থেকে একটা ছড়া-ছবিতে এ-বি-সি-ডি’র বই বের করতে গিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল আর একটি চটি বই। বইটি পর্নো-পুস্তক। পুতুলরানী দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে পর্নো-পুস্তক বা ‘নীল-বই’টি তুলে রাখলেন তাকে। যে বইটির উপর রাখলেন, সেটিও একটি ‘নীল-বই’। ওই আলমারিতে কেন, গোটা ঘরেই আর কোনও বইয়ের দেখা পেলাম না। দেখা পেলাম না গত কালকের ‘বর্তমান’ ছাড়া আর কোনও পত্রিকার। পড়শুনার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন একটি পরিবারের পক্ষে আমার সম্বন্ধে জানা ও তার দরুন শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক নয়, কখনই স্বাভাবিক নয়। কেউ তবে আমার আগমনের সম্ভাবনা বিষয়ে অগ্নির পরিবারকে অবহিত করেছেন, সতর্ক করেছেন? কে?? সেই কি তবে অগ্নিদের চালিত করছে আড়ালে থেকে??
অগ্নি বইয়ের ছবিগুলো দেখাচ্ছিল। আমি একটা করে ছবি দেখিয়ে বলে চলেছিলাম, “এটা জবা, এটা গ্যাদা, এটা গোলাপ।” অগ্নিও ছবিগুলোতে আঙুল ঠেকিয়ে বলে চলেছিল, “জবা, গ্যাদা, গোলাপ।” পদ্মফুলের ছবি দেখিয়ে বললাম, “এটা পদ্ম। মনে আছে পদ্ম তোমাদের বাড়িতে কাজ করত?”
পুতুলরানী বললেন, “ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে চাইছে,” তারপর অগ্নিকে বললেন, “মুখ দিয়ে হ্যাঁ বল, মুখ দিয়ে বলো।”
অগ্নি, সরল শিশুটি ঠাকুমার কথায় বলল, “হ্যাঁ।” এখানেও গোলমাল। ‘পদ্ম’, আমারই সৃষ্ট একটি চরিত্র।
—”আমাদের বাড়িতে একতা ব্যাঙ আছে।”
—“সেটা কি করে? টাকা দেয়? না লাফায়?”
—বাইরের উঠোনের দিকে আঙুল দেখিয়ে অগ্নি বলল, “ওই জায়গায় ব্যাঙ থাকত। ধুপ্ ধুপ্ করে লাফাত। ব্যাঙ আবার টাকা দেয় না কি! কি বোকা!” বুঝতে আমাদের কারুরই অসুবিধে হলো না, ‘ব্যাঙ’ বলতে অগ্নি ‘ব্যাঙ’ই বুঝিয়েছিল ‘ব্যাঙ্ক’ নয়।
—”তোমাদের কটা গাড়ি ছিল মনে আছে?”
—”হ্যাঁ।”
— “কটা।”
—”একটা।”
—”কী রঙের গাড়ি গো?”
—”সাদা রঙের।”
—”কোন বাড়িতে, বিয়ের আগে?”
— “না।”
অগ্নির বাবা একটুক্ষণের জন্য বেরিয়েছিলেন। ফিরে এলেন একটা ছোট্ট ঠোঙায় চানাচুর নিয়ে। অগ্নির হাতে ঠোঙাটা দিতেই ও মহা-আনন্দে শোরগোল তুলে ঢেলে দিল বইয়ের উপর। তারপর খুঁটে খুঁটে দুটো-চারটি দানা মুখে ফেলতে লাগল। আমার মুখেও ফেলল কয়েকবার।
—”তুমি ক্যাডবেরি খেতে ভালবাস?”
—”অগ্নির বাবাই উত্তর দিলেন, “না না, ক্যাডবেরি দেবেন না। খাবে না, ফেলে দেবে। সানন্দার বাল্মীকিবাবু ক্যাডবেরি দিয়েছিলেন। ও ফেলে দিয়েছে।”
ধাক্কা খেলাম, বড় একটি ধাক্কা! বাল্মীকি কেন মিথ্যে তথ্য হাজির করলেন তাঁর লেখায়? কেন জানালেন, অগ্নি ক্যাডবেরি ভালবাসে, ক্যাডবেরি ভালবাসত দেবযানী। দেবযানীর ক্যাডবেরি প্রেমের খবর দিয়েছিল দেবযানীরই মেজভাই গোরা। দেবযানী ও অগ্নির খাবারের পছন্দেও মিল ছিল—এমন মিথ্যে তথ্য হাজির করার মধ্যে আর যাই থাক, সত্যানুসন্ধান ছিল না। তবে কি ছিল??
দ্বিধা ও সংশয়ে দীর্ণ হতে হতেও আবার মন দিলাম বন্ধু অগ্নির দিকে।
—”আগের জন্মে তোমার বাবার নাম কী ছিল গো?” অগ্নিকে জিজ্ঞেস করলাম।
—”ধনপতি দত্ত।”
“কী করে জানতে পারলে তোমার বাবার নাম ধনপতি দত্ত? কে বলেছে তোমাকে?”
উত্তর দিল না অগ্নি। “এখনকার বাবার নাম কী? মনে আছে?” প্রশ্ন করলাম।
—”অমিত দে।”
—”কে তোমাকে শেখালো বাবার নাম অমিত দে?”
উত্তর পেলাম না, আমি নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বললাম, “এই জেঠুটার নাম কী বলত?”
অগ্নি চুপ। বললাম, “এই জেঠুর নাম সঞ্জয়। মনে থাকবে? কী বলতো আমার নাম?”
— “ছঞ্জয়।”
—”তাহলে এই জেঠুটার নাম?”
—”ছঞ্জয়।”
— “আমার নাম যে ছঞ্জয়, কে শেখাল গো
— “তুমি।”
—”কে বলল গো, তোমার বাবার নাম ধনপতি দত্ত?”
-–“মা।”
—”তোমার বিয়ে হয়েছিল ওগুলো কে বলল গো?”
–“ মা।”
সরবৎ খেতে খেতে আমরা অগ্নির বাবার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি, “দেবযানীর মেজ’দা কী আজ-কালের মধ্যে আসবেন?”
উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্ন খচ খচ্ করছে, দত্ত পরিবারের সব্বাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু মেজদার কথাই তুললেন কেন অমিতবাবু? উনি কি তবে খবর পেয়েছেন, দেবযানীর মেজদা দেবযানীর ফিরে আসার খবরে আপ্লুত? কী করে এই খবর অমিতবাবু পেলেন? এটাও একটা কোটি টাকার প্রশ্ন।
অগ্নি আমাদের কাছে দেবযানীর জীবনের কিছু কিছু ঘটনা ও কিছু কিছু ব্যক্তির উল্লেখ করেছিল। তার কিছু ঠিক; কিছু ভুল। অগ্নি সেই সেই তথ্যই ঠিক-ঠাক দিতে পেরেছিল, যে’সব তথ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; অথবা একটু চেষ্টা করলেই সংগ্রহ করা সম্ভব। ১২ জুন ‘৯৪ সকালে আমাদের সমিতির সদস্য সুদীপ দে সরকার এসেছিলেন আমার ফ্ল্যাটে। বরাহনগরে ছোটখাট একটি কারখানার অংশিদার। কাজের সুবাদে বর্ধমানেও যান-টান। তিনি ধনপতি দত্ত পরিবারের নানা ধরনের ব্যবসার খোঁজ-খবর রাখেন, দেখলাম। দত্ত-পরিবারের কোল্ডস্টোরেজ, পেট্রলপাম্প, বাজার, সিনেমা হল, পুকুর, স্টিলের নৌকো ইত্যাদি অনেক কিছুর হদিসই দিলেন। চন্দ্রনাথ বণিক পরিবারের অনেক কথাই সুদীপের জানা, যে-সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এমন জানা মানুষ নিশ্চয়ই সুদীপ একা নন। এমন দুই বিখ্যাত ধনী পরিবার দেবযানী হত্যার পর আরও বেশি প্রচারের আলোয় এসেছেন। ফলে, ওই দুই পরিবারের বিভিন্ন হাঁড়ির খবর জানা মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে।
অগ্নি সেই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন; অথবা শুধুমাত্র দেবযানী এবং তার ঘনিষ্ঠদের পক্ষেই জানা সম্ভব।
অগ্নির কিছু সাফল্য ও কিছু ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণ করলে এমনটা সন্দেহ করার অবকাশ থেকেই যায়, একটি সরল শিশুকে ‘টোপ’ হিসেবে ব্যবহার করতেই শিশু মনে বারংবার ঢোকানো হয়েছে—তোর আগের জন্মের বাবার নাম ধনপতি দত্ত : তোর বিয়ে হয়েছিল বণিক পরিবারে….ইত্যাদি, ইত্যাদি।
এমন একটা সিদ্ধান্তে কেন এলাম? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে, অনেক মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ-চিকিৎসক নিশ্চয় বলতে পারেন—এমনও তো হতে পারে, অগ্নি কারও কাছ থেকে দেবযানীর কথা শুনেছিল এবং দেবয়ানী-কাহিনী ওর শিশু মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, আকৃষ্ট করেছিল। ফলে অগ্নি প্রায়ই দেবযানীর কথা ভাবতে শুরু করে এবং ভাবতে ভাবতে এক সময় মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলার জন্য অগ্নি নিজেকে দেবযানী বলে ভাবতে শুরু করেছে এবং দেবযানী সংক্রান্ত শোনা তথ্যগুলো উগরে দিচ্ছে।
কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের এই যুক্তি অগ্নির বেলায় খাটে না। কারণ অগ্নির মা-বাবা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার জবানবন্দী অনুসারে তাঁরা কেউই অগ্নির দেওয়া দেবযানীর তথ্যগুলো আগে জানতেনই না। অগ্নির কাছে দেবযানীর জীবনের কথা তাঁরা নাকি আগে কোনও দিনই বলেননি। অন্য কোনও আপনজনের পক্ষেও নাকি অগ্নিকে দেবযানীর গল্প শোনানো সম্ভব নয়। কারণ অগ্নির অভিভাবকদের অগোচরে অগ্নি তেমন কোথাও যায় না। তিন বছরের শিশু বলেই যায় না, সম্ভাব্য দিকগুলো নিয়ে বিচার করলে এককথাই বলতে হয়—অগ্নি কোনও মানসিকরোগী নয়, যেমনটা অনেক সময় মানসিক রোগীরা ভাবতে থাকে সে আগের জন্মে অমুক ছিল, বা তাকে ভূতে ধরেছে, অথবা তার উপর ঈশ্বরের ভর হয়েছে। অগ্নিকে কেউ দেবযানীর জীবনের বেশ কিছু কথা বার-বার শুনিয়েছে এবং বুঝিয়েছে—সে ছিল দেবযানী।
কেন এমনটা বোঝাবে? দেবযানী দত্ত পরিবারের ‘চোখের মণি’, ‘আদরের ধন’ ছিল—এ’কথা অনেকেরই অজানা নয়। ওই আদরের ধন আবার ফিরে এসেছে প্রমাণিত হলে কোটিপতি দত্ত পরিবারের ভালোবাসার কিছুটা চুঁইয়ে নামলেও বিশাল লাভ—এই হিসেব কষেই কি অগ্নিকে দেবযানী দত্ত (বণিক) বানাবার এক চক্রান্ত দানা বাঁধতে শুরু করেছে?
এই জিজ্ঞাসাটা বিশাল হয়ে ওঠে, যখন দেখি, পাড়া-প্রতিবেশী কেউই অগ্নির জাতিস্মর হওয়ার খবর জানতে পারলেন না গত দেড় বছরে। তাঁরা জানলেন একটি পত্রিকা পড়ে। অথচ মেয়ে ‘জাতিস্মর’—এমন আবিষ্কারের কথা অগ্নির পরিবারের মানুষদের সবচেয়ে আগে বলার কথা প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠদেরই। এটাই ছিল মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ। কেন এই স্বাভাবিক প্রবণতার প্রকাশ দে-পরিবারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত?
পাড়া-পড়শিরা কেউ জানতে পারলেন না, অথচ কলকাতার বড়-বড় পত্রিকাগুলোকে এই জাতিস্মরের খবর খাওয়ানো হয়েছে। কারা খাওয়ালেন? কারা ছিলেন এই প্রচার মাধ্যমগুলোর যোগাযোগ মাধ্যম?
দে পরিবার কেন চাইছেন না, অগ্নি তার পূর্বজন্মের স্মৃতি ভুলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক? কেন তাঁরা হাঁক-পাঁক করছেন—অগ্নি যে দেবযানী এটা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খুব দ্রুত প্রচারিত হোক?
এটা আমাদের চারজনের (আমি, অনিরুদ্ধ, উজ্জ্বল ও সুদীপ) কাছেই পরিষ্কার ছিল, দে পরিবার অগ্নির বিষয়টা প্রচারে আনতে আগ্রহী হলেও কোনও এক পত্রিকা- লেখকের আগমন আশংকায় অতিমাত্রায় সতর্ক। আমরা অনুমান করতে পারি, লেখকটি আর কেউ নন, স্বয়ং আমি। সত্যানুসন্ধানে কেন ভয় থাকবে? ঘটনা সত্যি হলে, এমন ভয় থাকতেই পারে না। তবে কি দে পরিবার তাঁদের মিথ্যে ধরা পড়ার আশঙ্কায় ভুগছেন?
পত্র-পত্রিকা ও লেখা-পড়ার জগৎ থেকে শত কিলোমিটার দূরে থাকা দে- পরিবারের পক্ষে ভয়ের কারণ হিসেবে আমাকে চিহ্নিত করা স্বাভাবিক নয়। পরিবারের বাইরের অন্য কোনও পরিপক মাথা কি তবে গোটা ব্যাপারটা ঘটিয়ে চলেছেন, এবং তিনি আমার সম্পর্কে ভালমতই খোঁজ-খবর রাখেন?
এরপরও কেউ যদি প্রশ্ন করেন, তিন বছরের একটা বাচ্চার পক্ষে কি এত কিছু মনে রাখা সম্ভব? তাহলে বলবো, সাধারণ ও স্বাভাবিক বুদ্ধির একটি তিন বছরের বাচ্চার উপর পরীক্ষা চালালেই প্রশ্নকর্তা দেখতে পাবেন, এই ধরনের গপ্পো ওরা কী দারুণ রকম মনে ধরে রাখে।
পরিশেষে সম্ভাব্য পরিপক্ক মাথা ও দে পরিবারের প্রতি আন্তরিক অনুরোধ— একটি মেয়ের সুস্থ জীবনকে অসুস্থ করে তোলার অমানবিক খেলা থেকে বিরত হোন। অর্থ-লোভে পরমাত্মীয়ের বুকে ছুরি মারার ইতিহাস যেমন নতুন নয়, বরং বহমান তেমনই বহমান সমাজে মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষদের উপস্থিতি। তাই তো আজও দেখা মেলে রেল ক্রসিং এর গেটকিপার শুকদেবের, যে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচায় পরের জীবন; ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বপন সাহা এক সাপে কাটা অপরিচিতকে নিয়ে হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরে নিজের শেষ সম্বলটুকুও উজাড় করে দেয়। সমাজের এমন সচেতন মানুষরাই পারেন এমন ঘটতে যাওয়া অমানবিক ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে।
২৪ জুন ১৯৯৪ সংখ্যার ‘সানন্দা’য় আমার প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল কিঞ্চিৎ বাড়তি গুরুত্ব সহকারে (সম্পাদকীয়তে জানানো হয়েছিল আমাকে অকুস্থলে তদন্তে পাঠাবার কথা, ছবি-সহ ছাপা হয়েছিল আমার একটি সাক্ষাৎকার। আর প্রতিবেদন সে তো ছিলই)। প্রতিবেদনটির শেষে লিখেছিলাম, “আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মতো সুন্দর এক শিশুর জীবনে নেমে আসতে পারে কয়েক জোড়া কঠিন হাতের শাসন। যেমনটা অনেক সময়েই ফেল করা শিশুদের উপর নেমে আসে। সেখানে অগ্নির প্রতিবেশীদের প্রতি অনুরোধ— অগ্নির খারাপ দিন এলে, তার পাশে দাঁড়ান। ‘মানুষ’ হয়ে উঠতে সাহায্য করুন।”
যে আবেদন অগ্নির প্রতিবেশীদের কাছে রেখেছি, সেই আবেদনই রাখছি আগামী কোনও অগ্নির প্রতিবেশীদের উদ্দেশেও। আপনারাই পারেন বুজরুকি বন্ধ করতে, আপনারাই পারেন লোভীর অত্যাচার থেকে তথাকথিত জাতিস্মরকে বাঁচাতে, মানুষ করে গড়ে তুলতে।
| অগ্নিশিখা সম্বন্ধে বাল্মীকি যা বলেছেন | বাস্তবে যা দেখেছি |
| ১. অগ্নি আধো-আধো ভাষায় কিন্তু বড়দের মতো গুছিয়ে কথা বলে। যেমন, “আমি দুম করে পড়ে গেলাম। মাতিতে। মাথায় খুব লাগল। এখানতায়, দেখো দেখো, তখন আমাকে পেতাল। পেতে লাথি মারল। দমাদ্দম, দমাদ্দম লাথি মারল। বলল, তোকে মারব….” ইত্যাদি। | ১. অগ্নি আর পাঁচটা মধ্য-বিত্ত বাঙালি পরিবারের তিন বছরের শিশুর মতই এলোমেলো ভাষায় কথা বলে। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ওর সঙ্গে কাটিয়েছি খেলে, গল্প করে। দেখেছি অগ্নি আদৌ গুছিয়ে কথা বলে না। |
| ২. “অগ্নিশিখার চাঞ্চল্যকর কথাবার্তা শোনার পরই লাইব্রেরিতে গিয়ে বণিক হত্যার যাবতীয় ফাইলপত্র আবার ঘেঁটে ফেলা হয়। কীভাবে মারা গিয়েছিল দেবযানী? কে কে মেরেছিল? বাপের বাড়ি কোথায়? কিন্তু এত তথ্য কোনও কাজেই লাগল না। কারণ, ওই ছোট মেয়েটি নিজে থেকে তার আগের জন্ম নিয়ে যতটুকু বলেছে তার বেশি কিছু পাইনি ফাইল ঘেঁটে।” | ২. অগ্নি ততটুকুই ঠিক বলেছে, যতটুকু ফাইলে আছে, কাগজে প্রকাশিত হয়েছে অথবা যতটুকু একটু কষ্ট করলেই জানা সম্ভব। অগ্নি সে’সব তথ্য ভুল দিয়েছে, যে’সব ফাইলে নেই, সামান্য আয়াসে জানা সম্ভব নয়। অথচ অগ্নি আগের জন্মে দেবযানী হলে ওইসব তথ্য অবশ্যই জানা উচিতই। |
| ৩. অগ্নি জানিয়েছিল—বাড়ির নীচে ‘উবি ব্যাঙ’ আছে। বাস্তবিকই কলকাতায় ধনপতি বণিকের (দেবযানীর শ্বশুর) বাড়ির নীচে রয়েছে ইউনাইটেড কী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সংক্ষেপে ইউ.বি.আই.। অগ্নিশিখা আধো-আধো কথায় ‘উবি ব্যাঙ’ বলে ‘ইউ.বি.আই. কেই বোঝাতে চেয়েছিল। | ৩. অগ্নি দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিল ওর বাড়ির ব্যাঙটা টাকা দেয় না, লাফায়। অর্থাৎ ওর ‘ব্যাঙ’ ব্যাঙই ছিল, ‘ব্যাঙ্ক’ নয়। |
| ৪. অগ্নিশিখা ক্যাডবেরি ভালবাসে, যেমনি ভালবাসতো দেবযানী। | ৪. অগ্নির বাবা জানিয়েছিলেন, অগ্নি ক্যাডবেরি এতটাই অপছন্দ করে যে, ফেলে দেয়। |
মন্তব্য : গন্ধটা খুব সন্দেহজনক
জাতিস্মর তদন্ত ৩ : সুনীল সাক্সেনা
‘সুনীল সাক্সেনা’ বিশ্বের তাবৎ প্যারাসাইকোলজিস্টদের কাছে একটি অতি পরিচিত নাম—এক অতিবিতর্কিত নাম! সুনীলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার কথা প্রথম প্রকাশিত হয় ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের ৩ জানুয়ারি। সুনীলের জন্ম ও নিবাস উত্তরপ্রদেশের ছোট্ট শহর আওনলায় ১৯৫১-এর ৭ অক্টোবর। ছ’ ভাই-বোনের মধ্যে সুনীল তৃতীয়।
সুনীলের বাবা চাদাম্মিলাল সাক্সেনা চালাক-চতুর ও কর্মঠ মানুষ। সুনীলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার সময় চাদাম্মিলাল একটা কোল্ড-স্টোরেজে কাজ করতেন। সঙ্গে কিছু বাড়তি আয়ের জন্য বুটিক প্রিন্টের কাজ করতেন। প্রিন্টের কাজটা করাতেন একজন কর্মচারীকে রেখে, অর্ডারটা নিতেন নিজের নামে। মা রামেশ্বরী ছোট্ট একটা স্কুলে পড়াতেন। মোটামুটি আয়, পেট অনেক। টেনে-টুনে দিন চলত।
একবার সুনীল মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল কাকা জয়নারায়ণ সাক্সেনার বাড়ি। কাকা থাকে নিউ দিল্লি। সময়টা ১৯৬৩ সাল। কাকার অবস্থা ভাল। বাড়িতে রেডিও, ফ্রিজ, ফোন সবই আছে। রেডিওর গান শুনে, ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল আর আইসক্রিম খেয়ে, ফোনের মধ্যে দিয়ে দূরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে দেখে চার বছরের চালাক-চতুর সুনীল দারুণ উত্তেজিত, বেজায় খুশি।
কাকার বাড়ি থেকে ফিরে এলেও রেডিওর গান, আইসক্রিমের স্বাদ, ঠাণ্ডা জল খাওয়ার মজা ও ফোনে কথা বলার আকর্ষণকে এড়াতে পারল না। এই সময় প্রথম মা’কে জানায়—ও আগে খুব বড়লোক, ‘শেঠ আদমী’ ছিল। ওর বাড়িতেও রেডিও, ফ্রিজ, ফোন, সবই ছিল।
মা প্রথম প্রথম সুনীলের ও’সব কথাকে একটুও গুরুত্ব দেননি। কিন্তু এরপর থেকে নাকি সুনীল পূর্বজন্মের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে এমন সব বর্ণনা দিতে থাকে, যাকে আর ‘ছেলেমানুষি’ বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। সুনীল নাকি এই সময় জানিয়েছিল ও ছিল ‘বুধায়ুন’ শহরের এক ‘শেঠ’ বা ধনী ব্যবসায়ী। নিজের বিশাল বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, টাঙা ছিল। কারখানা ছিল। বুধায়ুনে কলেজ তৈরি করে দিয়েছিল ও। চার বিয়ে। দুটি ছেলে, একটি নিজের। আর একটিকে দত্তক নিয়েছিল। চতুর্থ স্ত্রী জলে বিষ মিশিয়ে পান করিয়েছিলেন। তাতেই মৃত্যু। বুধায়ুন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বন্ধু পাঠকজী। টাউন স্কুলে পড়েছিল। সেই স্কুলের এক মাস্টারের কথা খুব মনে পড়ে, যাকে ডাকত ‘মাস্টার সাহেব’ বলে।
সুনীলের কাছে এ’সব কথা শুনেছিলেন ওদের বাড়িওয়ালা গোবিন্দ মুরারীলাল। গোবিন্দ সব শুনে সুনীলের কথাগুলো যাচাই করে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেন। সুনীলের বাবা চাদাম্মিলালকে চাপ দিতে থাকেন, বোঝাতে থাকেন—সুনীল বাস্তবিকই জাতিস্মর না এ’সবই ওর পাগলামি, এটা জানার জন্যই সুনীলকে একবার বুধায়ুনে নিয়ে যাওয়াটা জরুরি। গোবিন্দ আরও বলেন, তাঁর আপাতভাবে মনে হচ্ছে সুনীল বোধহয় শেঠ শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়ালের কথা বলছে। শেঠ শ্রীকৃষ্ণ বুধায়ুনের বিশাল নামী-দামী মানুষ ছিলেন। মারা গেছেন সুনীলের জন্মের বছর কয়েক আগে।
আওনলা থেকে বুধায়ুন মাত্র ৩৫ কিলোমিটারের পথ। তবু যাচ্ছি-যাব করে আরও দু-একটা মাস গড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সুনীলকে নিয়ে ওর বাবা-মা গেলেন বুধায়ুন। নির্দিষ্ট লক্ষ্য—সুনীল সত্যিই জাতিস্মর কি না, এ’বিষয়ে সত্যানুসন্ধান, সঙ্গী হিসেবে গেলেন চাদাম্মিলালের এক বন্ধু। তারিখটা ২৯ ডিসেম্বর। সাল : ১৯৬৩।
সুনীল ও ওর মা-বাবার বক্তব্য অনুসারে—সুনীল ওখানে গিয়ে সত্যিই আমাদের সব্বাইকে অবাক করে দিল। শুধু আমাদেরই বা বলি কি করে! শেঠ শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় এবং পরিচিতেরাও দারুণ রুকম অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ও চিনতে পেরেছিল শেঠজীর চতুর্থ পত্নী শকুন্তলাদেবীকে, দত্তক পুত্র শ্যামপ্রকাশ ও শেঠজীর ঘনিষ্ঠজনদের। শেঠজী-প্রতিষ্ঠিত কলেজ দেখে সুনীল জানিয়ে ‘ছিল—এই কলেজই আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম, শেঠজীর প্রাসাদতুল্য বাড়িটি দেখেই নিজের বাড়ি বলে চিনতে পেরেছিল।
সুনীলের বুধায়ুনে আগমন ও তার পরবর্তী ঘটনা প্রচারমাধ্যগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুনীলের উপর অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে ছুটে এসেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির (নাকি অখ্যাতি?) অধিকারী প্যারাসাইকোলজিস্টরা। ‘৬৪-র ডিসেম্বরেই সুনীলকে নিয়ে অনুসন্ধানে নামলেন প্রণব পাল। তারপর ‘৭১- এ এলেন আয়েন স্টিভেনসন। ‘৭৪-এ ময়দানে নামলেন আর এক পরামনোবিজ্ঞানী ডঃ এল.পি.মেহরোত্রা। অনুসন্ধান শেষে তিনজনই দাবি জানালেন সুনীল জাতিস্মর। কারণ হিসেবে তিনজনই জানালেন – সুনীলের দেওয়া বেশিরভাগ তথ্যই আশ্চর্য রকম ঠিক এবং শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠদের সকলকেই ও চিনতে পেরেছিল। আয়েন স্টিভেনসন তো সুনীলকে নিয়ে বই-ই লিখে ফেললেন, তারপর পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে গেল। ‘অধ্যাত্মবাদের দেশ ভারত’ও চুপ করে রইল না। নানা ভাষাভাষি পত্র- পত্রিকাও গা ভাসাল সুনীলের স্রোতে।
শেঠ শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল–এর শেষ জীবন এবং
শেঠ শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল ছিলেন সম্ভবত শহরের সবচেয়ে বড় ধনী। শেঠজী’র ঘনিষ্ঠমহল থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তাঁর শেষ বয়সের উপর কিছু আলোকপাত করছি।
শেঠজীর দুটি বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। এক : ধর্ম-কর্ম; দুইঃ যৌন-আকাঙ্ক্ষা। শেঠজী প্রতিদিন পুজো করতেন। বহু দেব-দেবতাতেই ভক্তি থাকলেও রামের প্রতি ছিল একটু বাড়তি ভক্তি। শহরের গান্ধী পার্কে প্রতিবছর রামলীলা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসাতেন শেঠজী। অনেক দূর দূর থেকেও লোক আসত মেলায়। উত্তরপ্রদেশের অনেক জায়গাতেই ধর্মশালা করে দিয়েছিলেন। শহরে নিজের প্রাসাদ ছাড়াও ছিল আরও কয়েকটি বাড়ি। তৈরি করে দিয়েছিলেন কলেজ। তেলের বিরাট মিল ছাড়াও ছিল আরও ব্যবসা
চারটি বিয়ে করেছিলেন শেঠজী। চতুর্থ বিয়ের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। এক উত্তরপ্রদেশের আদিবাসীর স্ত্রীর রূপ-যৌবনে মোহিত হয়ে শেঠজী আদিবাসী পুরুষটিকে মোটা টাকা দেন। সেই সঙ্গে বাঁধা মাসোহারার ব্যবস্থা। তারপর ষোড়শী সুন্দরীটিকে বিয়ে করে প্রাসাদে তুললেন। নাম দিলেন শকুন্তলা। শকুন্তলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। অন্য জায়গা থেকে শকুন্তলাকে বিয়ে করে নিয়ে আসায় বিয়ের পিছনের ঘটনা হাতে গোনা দু-চারজন ছাড়া প্রায় সকলেরই ছিল অজানা। কিন্তু শকুন্তলার স্বামী এক সময় বুধায়ুনে এসে ‘ব্ল্যাকমেল’ করতে থাকে শেঠজীকে। শহরে এই নিয়ে দ্রুত কানাকানি শুরু হয়। এই কেলেংকারি শেঠজীর বিপুল জনপ্রিয়তায় কিছুটা ফাটল ধরিয়েছিল।
শেঠ শ্রীকৃষ্ণ কলেজের অধ্যক্ষ এস.ডি. পাঠক ছিলেন শেঠজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঘনিষ্ঠতা এতই গভীর ছিল যে পাঠকজী থাকতেন শেঠজীর প্রাসাদেই। শেঠজী শেষ বয়সে এই পাঠকজীর কাছ থেকেও গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। শেঠজী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন পাঠকজীর সঙ্গে শকুন্তলার একটি অবৈধ সম্পর্ক আছে। শেঠজী নিজে যৌন অক্ষম ছিলেন না। যৌন ক্ষমতাকে ধরে রাখতে শরীরচর্চার পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক ওষুধও সেবন করতেন। শেঠজী বাস্তবিকই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ভালোবাসার (?) বিনিময়ে শকুন্তলার এমন বিশ্বাসঘাতকতা শেঠজীর মন ভেঙে দিয়েছিল। ভাঙা মন আরও খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ে, যখন শেঠজী আবিষ্কার করলেন তাঁরই দত্তক পুত্র শ্যামপ্রকাশের সঙ্গেও শকুন্তলা একই সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলেছে।
১৯৫১ সালের ২৪ এপ্রিল সকালে শেঠজী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। বিকেলে মৃত্যু। শহরে গুজব ছড়ায় শেঠজীকে বিষ পান করিয়ে মারা হয়েছে। মেরেছেন শকুন্তলা। ষড়যন্ত্রের আড়ালে শ্যামপ্রকাশ ও পাঠকজীই আছেন বলে রটে যায়। পরবর্তীকালে বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়ে আমার মনে হয় এটা স্রেফ গুজবই।
শেঠজীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয় ও ব্যবসার অংশীদারদের মধ্যে নানা ধরনের ঝগড়া-বিবাদ-ষড়যন্ত্র ইত্যাদি মাথা চাড়া দেয়। এরই মধ্যে শকুন্তলাদেবী কলেজের প্রেসিডেন্ট হলেন, যদিও তিনি লেখাপড়া জানতেন না। সম্ভবত একই সঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ ও শেঠজীর দত্তক পুত্রকে নাচাতে পারারই পুরস্কার এটা। শেঠজীর নিজের ছেলে রামপ্রকাশ তখনও নাবালক এবং শকুন্তলাই তার অভিভাবক।
শকুন্তলা এক সময় খোলামেলাভাবেই শ্যামপ্রকাশের সঙ্গে তাঁর প্রেম-প্রেম খেলা চালাতে লাগলেন। শেঠজীর স্ত্রী শেঠজীরই ছেলের সঙ্গে প্রেম করছেন—এটা মেনে নিতে পারেনি শহরের তামাম মানুষ। সম্পর্কে মা-ছেলের এই জৈবিক প্রেম শেঠজীর কলেজের ছাত্র ও অভিভাবকদের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে শকুন্তলাদেবী কলেজের প্রেসিডেন্টের পদ হারান; হারান রামপ্রকাশের অভিভাবকত্বও। এতে শকুন্তলাকে বাগে আনা গিয়েছিল, বা তাঁর স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আনা গিয়েছিল, এমন ভাবার মত কোনও দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েনি। শকুন্তলা শ্যামপ্রকাশকে বিয়েই করে ফেললেন। এ’ভাবে শকুন্তলা ‘অফিসিয়াল’ তৃতীয় বিবাহ সেরে ফেললেন ছেলের সঙ্গে।
ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষ পাঠকজীর যৌন-কেলেংকারি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি জন-রোষে কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। অধ্যক্ষ পদে আনা হয় নরেন্দ্র মোহন পাণ্ডাকে। নরেন্দ্র মোহনও শেঠজীর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি।
অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি
১৯৭১-এর শেষে সুনীলের আওনলায় যাই। আওনলা বেরিলি শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে। সুনীল তখন সিক্সের ছাত্র। সুনীলের মা-বাবা জানালেন ও ছাত্র-ও ভাল। সেকেন্ড স্ট্যান্ড করে ক্লাসে উঠেছে। সুনীল পোশাক-আশাকে যে টিপ্ থাকে, সেটা দেখেছিলাম। বিভিন্ন সাক্ষীরা জানিয়েছিলেন টিপ্ থাকটাই সুনীলের অভ্যেস। সুনীল আমার সঙ্গে চা খেয়েছিল। খাদ্যাভাসের পরিচয় নিতে গিয়ে জেনেছি—আমিষাশী।
এই অনুসন্ধান পর্বে আমি বুধায়ুনেও গিয়েছিলাম। শেঠজীর ঘনিষ্ঠ মানুষজনদের সাক্ষ্য থেকে জেনেছি শেঠজী পোশাক-আশাকের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। সাজগোজে কোনও বিলাসিতা ছিল না। চা কখনই খেতেন না। নিরামিষাশী ছিলেন।
তিন প্যারাসাইকোলজিস্ট অন্তত একবার করে ঘোষণা রেখেছিলেন, তাঁরা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন শেঠজী’র পরিবারের সঙ্গে সুনীলের পরিবারের কোনও যোগসূত্র ছিল না। সুতরাং শেঠজী সম্পর্কে খুঁটিনাটি বহু কিছু জানা সুনীলের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। তিন প্যারাসাইকোলজিস্টের মধ্যে যিনি সবচেয়ে নামী-দামী সেই আয়েন স্টিভেনসন ‘India Cases of the Reincarnation Type’ গ্রন্থে সুনীল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ১১০ পৃষ্ঠায় লিখছেন, “So far as I could ascertain, the two families had no prior acquaintance before the development of the case. Sakuntala Devi, widow of Seth Sri Krishna, on the one side, and Chadammi Lal Saxena, Sunil’s father, on the other side, both denied any previous knowledge of the other’s family. Chadammi Lal Saxena said he had never heard of the Seth or his college in Budaun until Sunil began talking about him.” অর্থাৎ—আমি নিশ্চিত, দুটি পরিবার এই ঘটনার আগে উভয়ের বিষয়ে কিছুই জানত না। শকুন্তলাদেবী এবং সুনীলের বাবা চাদাম্মিলাল দু’জনেই জানিয়েছিলেন, দুই পরিবারই এই ঘটনার আগে দুই পরিবারের পরিচিত ছিল না। চাদাম্মিলাল আরও জানিয়েছিলেন, তিনি শেঠজী বা শেঠজীর কলেজের নামও সুনীলের কাছ থেকে শোনার আগে কখনও শোনেননি।
এই প্যারাসাইকোলজিস্টদের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, অথবা অন্য কোনও প্রভাবশালী মহলের দ্বারা চালিত হয়ে পত্র-পত্রিকাগুলো এ’ভাবে শোরগোল তুলেছিল যে, স্থানীয় জনগণ সুনীলকে বাস্তবিকই শেঠজী বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি, তা এবার আপনাদের সামনে হাজির করছি।
| সুনীলের দাবি | যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি | আমার মন্তব্য |
| ১. আমি বুধায়ুনে ছিলাম। নাম ছিল কিষেণ। | ১. রামেশ্বরী সাক্সেনা ২. চাদাম্মিলাল সাক্সেনা ৩. গোবিন্দ মুরারীলাল (সুনীলদের বাড়িওয়ালা) | বুধায়ুনের ধনী শেঠ হিসেবে সুনীল যাকে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁর নাম কিন্তু কিষেণ ছিল না। ছিল শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল। তথ্য ভুল |
| ২. বাড়িতে রেফ্রিজারেটর ছিল। | ১. জয়নারায়ণ সাক্সেনা (সুনীলের নয়াদিল্লির কাকা) ২. সুনীলের বাবা ৩. সুনীলের মা ৪. শকুন্তলাদেবী | সুনীল রেফ্রিজারেটর কথাটি না বলে ফ্রিজ দেখিয়ে বলেছিল—আমার বাড়িতেও এটা ছিল, জানিয়েছিলেন জয়নারায়ণ সাক্সেনা। শকুন্তলাদেবীর সাক্ষ্যে জানতে পারি, শেঠজীর মৃত্যু পর্যন্ত বাড়িতে কোনও ফ্রিজ ছিল না। তথ্য ভুল। |
| ৩. মটোর ছিল কালো রঙের। | ১. সুনীলের বাবা ২. সুনীলের মা ৩. শকুন্তলাদেবী ৪. রামপ্রকাশ (শেঠজীর পুত্র) | সুনীল জানিয়েছিল ওঁর মটোর ছিল। রামপ্রকাশ জিজ্ঞেস করে, “মটোরের রঙ কি ছিল?” উত্তরে সুনীল জানিয়েছিল কালো। শকুন্তলা ও রামপ্রসাদের সাক্ষ্য নুসারে গাড়ির রঙ ছিল ‘চকোলেট’। তথ্য ভুল। |
| ৪. কলেজ ‘পাড়া মহল্লা’য় অবস্থিত। | ১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. নরেন্দ্রমোহন পাণ্ডা ‘(শ্রীকৃষ্ণ কলেজের অধ্যক্ষ) ৪. স্থানীয় মানুষজন | ‘পাড়া মহল্লা’ বলে বুধায়ুনে কোনও অঞ্চল বা পাড়াই নেই। কলেজ যে অঞ্চলে, তার কাছে রয়েছে ‘বড়া বাজার’। তথ্য ভুল। |
| ৫. টাঙা ছিল। টাঙার ঘোড়ার রঙ ছিল কালো। | ১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. এস. ডি. পাঠক (কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ৪. সাফাৎ উল্লা (শেঠজীর ‘মুনশি’) | ঘোড়ার রঙ ছিল লালচে বাদামী। কালো নয়। তথ্য ভুল। |
| ৬. চার বিয়ে, এক স্ত্রীর গায়ের রঙ কালো। তিনজন ফর্সা। | ১. সুনীলের মা ২. স্থানীয় মানুষ ৩. পাঠকজী | চার বিয়ে। এবং তৃতীয় স্ত্রীর গায়ের রঙ কালো ছিল। তথ্য ঠিক। |
| ৭. বড় মেলা বসাত বুধায়ুনে। | ১. রামেশ্বরী (সুনীলের মা) ২. স্থানীয় মানুষ। | মেলা বসত রামনবমী উপলক্ষে। মেলা বসাতেন শেঠজীই। তথ্য ঠিক। |
| ৮. একটা সিনেমা হল ছিল। | ১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. পাঠকজী ৪. রামেশ্বরী ৫. স্থানীয় মানুষ | না। কোনও সিনেমাহল ছিল না। একটা হল তৈরি করেছিলেন বটে। কিন্তু সেই হলটা ছিল ‘স্টোর হাউজ’। সিনেমা হল নয়। তথ্য ঠিক নয়। |
| ৯. ‘মুনশি’ সাফাৎ উল্লাকে চিনতে পেরেছিল। | ১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. ‘মুনশি’জী | সুনীলের মা ও বাবা যদিও বলেছিলেন সুনীল শেঠজীর মুনশিকে চিনিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মুনশিজী দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন সুনীলের মা- বাবার এই দাবি ‘বিলকুল ঝুট’। তথ্য ঠিক নয়। |
| ১০. একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল। | ১. সুনীলের মা ২. শকুন্তলাদেবী ৩. পাঠকজী ৪. গোপাল বৈদ্যজী (শেঠজীর পারিবারিক চিকিৎসক) | ঘোড়া থেকে কোনওদিনই পড়ে যাননি। পা’ও মচকায়নি। একবার এক দুর্ঘটনায় পা ভাঙে। তবে তা ঘোড়া থেকে পড়ে নয়। তথ্য ভুল। |
| ১১. শেঠজীর বোন, বোনের জামাই সুন্দরলাল ও বোনের মেয়ে আনন্দীকে চিনতে পেরেছিল। | ১. সুনীলের মা ২. সুনীলের বাবা ৩. রামপ্রকাশ ৪. শকুন্তলাদেবী ৫. পাঠকজী | সুনীলের মা-বাবার সাক্ষ্যকে সমর্থন করেননি কেউই। বাকি তিনজন জানিয়েছিলেন, তাঁদের সামনে এই ঘটনা ঘটেনি। পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ কারও সামনে সুনীল এঁদের চিহ্নিত করেছিল, এমন ঘটনাও ওঁরা শোনেননি। |
| ১২. শেঠজীর প্রাসাদে তিনজনের একসঙ্গে তোলা একটা ছবি দেখে বলে দিয়েছিল,একজন—নিজে, বাকি দু’জন—স্ত্রী ও পুত্ৰ। | ১. শকুন্তলাদেবী ২. শ্যামপ্রকাশ | সুনীল শেঠজীকে চিনতে পেরেছিল। কিন্তু বাকি দু’জনকেই চিনতে ভুল করে ছিলেন। ঘরে শেঠজীর এতই ছবি ছিল, যে সে’সব দেখে শেঠজীকে যে কোনও শিশুর পক্ষেই চিনে ফেলা সহজ। |
| ১৩. গোপাল বৈদ্যজীকে চিনতে পেরেছিল। | ১. সুনীলের বাবা ২. গোপাল বৈদ্যজী। | গোপল বৈদ্যজী’র কথামত তিনি যখন রোগী দেখছিলেন, সেই সময় সুনীলরা এসেছিল। বৈদ্যজী প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি আমাকে চিনতে পারছ? উত্তরে সুনীল বলেছিল—হ্যাঁ, আপনি রোগীদের ওষুধ দেন। সুনীলের এই উত্তর থেকে কখনই স্পষ্টতর হয়নি সুনীল গোপালজীকে গোপালজী হিসেবে চিনতে পেরেছিল। |
| ১৪. শেঠজীর বন্ধু রামগোপাল ব্যাস’কে চিনতে পেরেছিল। আরও জানিয়েছিল- শেঠজীর আর এক বন্ধু শিবনারায়ণ দাসের গয়নার দোকান ছিল। | ১. রামগোপাল ব্যাস ২. শিবনারায়ণ দাস | রামগোপাল ব্যাস ছিলেন শেঠজীর বন্ধু। সুনীল রামগোপালকে চিনতে পেরেছিল। রামগোপালকে শুধু সুনীলই নয়, সুনীলের মা- বাবাও চিনতেন। |
| রামগোপাল সুনীলদের বাড়ি যেতেন, কারণ, সুনীলের বাবা চাদাম্মিলাল রামগোপালের কোল্ড স্টোরেজেই কাজ করতেন। শুধু রামগোপালই শেঠজী ও সুনীলদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত একমাত্র ব্যক্তি নন। স্বল্প আয়াসেই আর কয়েকজনের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি যাঁরা একই সঙ্গে দুটি পরিবারকেই জানতেন। দু’নম্বর ব্যক্তির নাম সেবতি প্রসাদ। সেবতি সম্পর্কে সুনীলের বাবার কাকা। বুধায়ুনের বাসিন্দা সেবতি মাঝে-মাঝেই আসতেন সুনীলদের বাড়ি। সেবতি প্রসাদের কথা—শেঠ শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভালমতই চিনতাম। তিন : সুনীলের এক কাকা জয়নারায়ণ সাক্সেনা সেই সময় ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব বা Personal Assistant । বুদ্ধিমান, রাজনীতিবিদ, বৈষয়িক জয়নারায়ণ শেঠ শ্রীকৃষ্ণের পরিচিত ছিলেন। চার : শেঠ শিবনারায়ণ দাস। শিবনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বুধায়ুনে শিবনারায়ণের একটি অলঙ্কারের দোকান আছে। আওনলায় শিবনারায়ণ রামগোপাল ব্যাসের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসা হিসেবে কোল্ড স্টোরেজের ব্যবসা করতেন। সুনীলের বাবা ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত ওখানে কাজ করতেন এবং শিবনারায়ণের পরিচিত ছিলেন। সুতরাং শিবনারায়ণের বুধায়ুনে অলঙ্কারের দোকানের খবর সুনীলের জানতে পারার মধ্যে অবাক হবার মত কিছুই দেখতে পাই না। মাত্র এইটুকু তথ্য পাওয়ার পরই আমরা বলতে পারি, যে সব প্যারাসাইকোলজিস্টরা জানিয়েছিলেন—”আমি নিশ্চিত, দুটি পরিবার এই ঘটনার আগে উভয়ের বিষয়ে কিছুই জানত না”—তাঁরা নিশ্চিতভাবেই ভুল করেছিলেন। অবশ্য এই ভুল ইচ্ছাকৃত, কি অনিচ্ছাকৃত সে আর এক গবেষণার বিষয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতেই পারি এ ক্ষেত্রে সুনীলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে দু’টির যে কোনও একটি কারণ ক্রিয়াশীল। এক : সুনীল উভয় পরিবারের পরিচিত কারও কাছ থেকে শেঠজীর বিষয়ে কিছু কিছু কথা শুনেছিল। শেঠজীর বিচিত্র জীবন সুনীলের মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সুনীল গভীরভাবে শেঠজীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের অজ্ঞাতেই নিজের মধ্যে অন্যের সত্তাকে খুঁজে পেতে থাকে। অর্থাৎ নিজেকে শেঠজী বলে ভাবতে শুরু করে। এটা সুনীলের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা থেকে সৃষ্ট অবস্থা। দুই : শেঠজীর বিশাল সম্পত্তিতে ভাগ বসাবার লোভেই সুনীলকে পূর্বজন্মের শেঠজী বলে হাজির করা হয়েছিল। শেঠজী সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য সুনীলের মাথায় ঢোকানো হয়েছিল। সুনীল বাস্তবিকই জাতিস্মর হলে ওর দেওয়া তথ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকত না। ওর প্রচুর ভুলই প্রমাণ করে ও জাতিস্মর নয়। প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে অন্যান্য প্যারাসাইকোলজিস্টরা সুনীলের তথ্যে প্রচুর মিল খুঁজে পেলেন কি করে? উদাহরণ হিসেবে সবচেয়ে নামী-দামি প্যারাসাইকোলজিস্ট আয়েন স্টিভেনসনের লেখা থেকে অংশ তুলে দিচ্ছি। এ’থেকেই আসল রহস্যের হদিস আপনারা পেয়ে যাবেন : আমি বুধায়ুনে থাকতাম। আমার বাবা ছিল। আমার মা ছিল। আমার বউ ছিল। আমার সন্তান ছিল। আমার ফ্যান ছিল। আমার চাকর ছিল। আমার জামাকাপড় ছিল। আমি বউয়ের জন্য গয়না কিনেছিলাম। আমার বাড়ি ছিল—ইত্যাদি অকিঞ্চিতকর সব কথা-বার্তা। এইসব তথ্য মেলাতে জাতিস্মর হতে হয় না। একটি সাধারণ মানুষ- ছানা হলেই চলে। কিন্তু এমন ধরনের গোটা চল্লিশের মিলের পর (যে সব মিলের মধ্যে ধরে নিতেই পারেন রয়েছে, চুল কাটাতাম নাপিতের কাছে, মন্দিরে যেতাম, বাড়িতে পুজো করতাম, দুধ ভালবাসতাম, প্যাড়া ভালবাসতাম, লাড্ডু ভালবাসতাম, ইত্যাদি ইত্যাদি) গোটা দশ-পনের অমিল পাত্তাই পায় না প্রচার মাধ্যমগুলোর কাছে, তা সে’সব অমিল যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন! সাংবাদিকদের মাইনে দেয় ‘সত্যবাদিতা’ নয়, ‘সংবাদপত্র’। সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করতে হলে সংবাদপত্রের পলিসির সঙ্গে মানিয়েই কলম চালাতে হবে। নইলে ‘আউট’। তাই একজন সাংবাদিক ব্যক্তিগতভাবে চান বা না চান পত্রিকা চাইলে তাঁকে দিনকে রাত করতে হয়, রাতকে দিন। তাই তো পত্রিকার লাগাতার প্রচারে ‘জোনাকি’ ‘নক্ষত্র’ হয়, আর সত্যের সূর্যকে ঢাকতে নেমে আসে ‘ব্ল্যাক আউট’-এর কালো মেঘ বা ‘ইয়েলো জার্নালিজম্’- এর নোংরা ধোঁয়া। | ||
জাতিস্মর তদন্ত ৪ : যমজ জাতিস্মর রামু ও রাজু
উত্তরপ্রদেশের ছোট্ট গ্রাম শ্যামনগর হঠাৎই পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে উঠল। পৃথিবীর তাবড় প্যারাসাইকোলজিস্টরা উড়ে আসতে লাগলেন কানপুর। তারপর সেখান থেকে ফারাক্কাবাদ জেলার অনামী স্টেশন যশোদা’তে। যশোদায় নেমে দু’কিলোমিটার উত্তরে গেলেই শ্যামনগর। শ্যামনগরের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বা কবিরাজমশাই পণ্ডিত রামস্বরূপ শর্মার যমজ পুত্র রামু ও রাজু সত্তরের দশকের শুরুতে বিশাল হইচই ফেলে দিয়েছিল তামাম দুনিয়ায়। ওরা গত জন্মেও ছিল যমজ ভাই ভীমসেন ও ভীষ্ম ত্রিপাঠী।
ওরা গতজন্মে যে বাস্তবিকই ভীমসেন ও ভীষ্মই ছিল, তার স্বপক্ষে এত সব জোরালো যুক্তি, কাঁপন ধরাবার মত সব তথ্য প্যারাসাইকোলজিস্টরা হাজির করেছিলেন যে প্রচারমাধ্যমগুলোর নাড়া না খেয়ে উপায় ছিল না।
কে এই রামু ও রাজু
রামু ও রাজুর জন্ম ১৯৬৪-এর আগস্টে। জন্মতারিখ ঠিক মত বলতে পারেননি ওদের বাবা পণ্ডিত রামস্বরূপ শর্মা ও মা কাপুরীদেবী। অতটা স্মরণে না রাখার কারণ সম্ভবত ষষ্ঠ ও সপ্তম সন্তান হিসেবে ওদের আগমন। ছা’পোষা পরিবারে এত সন্তান—কিছুটা অবহেলা, কিছুটা বিতৃষ্ণা হয় তো বা মনের কোণে জমে উঠেছিল। অবশ্য এর পরও একটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন কাপুরীদেবী।
কাপুরীদেবী নাকি রামু ও রাজুর জন্মের আগে স্বপ্ন দেখেছিলেন। অদ্ভুত স্বপ্ন। দুটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তাঁর গর্ভ থেকে। স্বপ্ন সত্য হওয়ায় কাপুরীদেবী বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে উল্লেখ করার মত আর কিছু স্বপ্নে দেখেননি।
গাঁয়ের আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত সন্তানের মতই মাঠে-ময়দানে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সময় কাটছিল রামু-রাজু’র। পড়াশুনোর চেয়ে মাঠ-ময়দানই ওদের মন টানত বেশি করে। রামুর একটা ভালনাম হয়েছে—রামনারায়ণ; রাজুর শেষনারায়ণ। সম্ভবত নারায়ণরূপী সন্তানদের আগমন ঠেকাতেই এমন বিচিত্র নামকরণ। এক সময় এদেশের অনেকেই ভাবতেন এই ধরনের বিচিত্র নামকরণ করে পরবর্তী সন্তানদের জন্ম ঠেকানো যাবে! জৈবিক কারণে যে জন্ম, তাকে ‘ক্ষমা’, ‘রেহাই’, ‘মরণ’ ইত্যাদিজাতীয় হেলাফেলার নাম রেখে নাকি ঠেকানো যাবে!
আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের সন্তান লেখা-পড়া শিখবে না, এমনটি কি হয়। আর সব ভাই-বোনদের সঙ্গে দু’বছর পার না হতেই স্লেট-পেন্সিল নিয়ে বসতে হতো রামু ও রাজুকে। পড়াতেন পাশের গাঁয়ের পণ্ডিত মান্নালাল।
একদিনের ঘটনা, পণ্ডিত মান্নালালের বাড়ি যাচ্ছিলেন তাঁরই এক আত্মীয় চন্দ্রসেন ত্রিপাঠী। চন্দ্রসেন থাকেন উঁচা লারপুর’এ। উঁচা লারপুরও একটি গাঁ। শ্যামনগর থেকে ১২-১৪ কিলোমিটারের পথ, মান্নালালের বাড়ি যেতে শ্যামনগর গাঁ পার হয়েই যেতে হয়। যাচ্ছিলেন, কিন্তু যাওয়া আর হলো কই! তার আগেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।
বছর তিন-চারেকের দুটি যমজ শিশু পথে খেলছিল। চন্দ্রসেনকে দেখে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে একেবারে প্রণাম। চন্দ্রসেন ভাবলেন, বাচ্চা তো, বুঝি বা অন্য কারও সঙ্গে তাঁকে গুলিয়ে ফেলেই এমন প্রণাম। তবু রহস্য করে জিজ্ঞেস করলেন,আমাকে চেন?
—কেন চিনব না, আপনি তো আমাদের দাদা। –দাদা মানে? কেমন দাদা আমি তোমাদের? —দাদা, আমরা হলাম ভীম ও ভীষ্ম।
— ভীম, ভীষ্ম মানে? তোমাদের বাড়ি কোথায় ছিল? চন্দ্রসেন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন না।
—থাকতাম উঁচা লারপুরে। এখন আমরা এই গাঁয়ে জন্মেছি। আমাদের নাম রামু ও রাজু।
বিভ্রান্ত চন্দ্রসেন মান্নালালের বাড়ির পথ ধরে এগোন। কিন্তু বাস্তবিকই ব্যাপারটা কি ঘটল? সত্যিই কি ওরা গতজন্মের ভীম ও ভীষ্ম? নাকি গোটা ব্যাপারটাই নেহাতই নিষ্ঠুর রসিকতা? নেপথ্যে থেকে কোনও মানুষ ওদের দিয়ে এমন কিছু কথা বলিয়ে ওকে নিয়ে কি রসিকতা করল!
মান্নালালের বাড়িতে পৌঁছে চন্দ্রসেন নাকি এই ধরনের নানা অনুমানের কথা ব্যক্ত করেছিলেন।
মান্নালালের কাছ থেকেই রামু ও রাজুর বাবা-মা পণ্ডিত রামস্বরূপ ও কাপুরীদেবী এই ঘটনার কথা নাকি জানতে পেরেছিলেন।
কিন্তু এটুকুতেই থেমে থাকেনি রামু ও রাজু। একটু একটু করে আরও অনেক কথাই জানিয়েছে সবচেয়ে আপনজন জেঠামশাই গয়াপ্রসাদ শর্মা এবং বাবা-মা’কে। জানিয়েছে—রামুর নাম ছিল ভীম, রাজুর ভীষ্ম। প্রধান জীবিকা ছিল, ক্ষেতি-জমি। ষাট বিঘার মত জমি ছিল। মোটামুটি সাচ্ছল্যের অভাব ছিল না। ভীমের প্রথম বিয়ে হয়েছিল। পাত্রী আতরাউলি গ্রামের। তারপর ভীষ্মের বিয়ে হয়। পাত্রী ভাওয়ালপুরের। ভীমের একটিই সন্তান। পুত্র। নাম—দ্রোণ। ভীষ্মের তিন পুত্র। রামকিশোর, রাজকিশোর ও নেত্রকিশোর। দু’ভাইয়ের যেমন ছিল স্বাস্থ্য, তেমনই ছিল সাহস। হয় তো কিছুটা উগ্রও। অবশ্য উগ্রতা ও অঞ্চলের পরিবেশেই রয়েছে। ওখানে খুন-খারাবি, বদলা, রক্তের হোলিখেলা নতুন কিছু নয়। বাবা মারা গিয়েছিলেন। ক্ষেতি-জমির দেখভাল করতেন ভীম ও ভীষ্ম। সংসারের অন্যান্য দায়িত্ব সামলাতেন বড় ভাই চন্দ্রসেন।
জমি নিয়েই শত্রুতার শুরু জগন্নাথের সঙ্গে। জগন্নাথ থাকতেন পাশের গাঁ কুন্দরিপুরায়। বয়স ৪০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। গাঁয়ের ‘দাদা’। অর্থাৎ শক্তিমান পুরুষ হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি। জমিতে দেওয়াল তুলেছিলেন জগন্নাথ। ভীম ও ভীষ্ম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন এ দেওয়াল বেআইনিভাবে ভীমদের জমিতে তোলা হয়েছে। জগন্নাথের দাদাগিরি টেকেনি ভীম ও ভীষ্মের দুই বন্দুকের নলের মুখে। জগন্নাথ তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সামনেই অপমানিত হয়েছিলেন। তারই মাসখানেক পরে জগন্নাথ দু’ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে নেন। একদিন নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন দু’ভাইকে। খাটিয়ায় বসে লাড্ডু, প্যাড়া সহযোগে ঘটি ঘটি দুধ পান করতে করতে হঠাৎই দু’ভাই লক্ষ্য করেন তাঁদের ঘিরে ফেলেছে জগন্নাথের লোকজন। ওঠার চেষ্টা করতেই শুরু হল প্রহার। ততক্ষণে জগন্নাথের আহ্বানে একজন অ্যাসিড এনে ঢেলে দিয়েছে ভীমের চোখে। ভীমের বীভৎস চিৎকারের মাঝেই ভীষ্ম নিজেকে মুক্ত করে ছুটতে থাকে। তারপর এক সময় নিজেই ঘুরে দাঁড়ায়। আবার ফিরে যায় জগন্নাথের কুঠিতে। বদলার রক্ত তখন টগ্ৰগ করে ফুটছে। অত সশস্ত্র রক্তপিপাসু মানুষের সঙ্গে নিরস্ত্র ভীষ্ম পেরে ওঠেনি। ওর চোখে- মুখেও ঢালা হয়েছে অ্যাসিড। তারপর দু’জনকে হত্যা করে বস্তায় পুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে কুয়োয়। মৃতদেহকে বস্তাবন্দি করার কথা এবং কুয়োতে ফেলে দেওয়ার কথাও রামু-রাজু বলেছে। রামু, রাজুর কথা থেকে আমরা বরং জানতে পারলাম, আত্মা চিন্তাই হোক, বা চিন্তার কারণ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষই হোক—আত্মার দেখার মত চোখ আছে। মানতে পারলাম কি না, সে প্রসঙ্গে না গিয়ে আপাতত এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারি, আমরা নতুন কিছু জানতে পারলাম।
ভীম ও ভীষ্ম নিখোঁজ হওয়ার চারদিন পর ওদের দু’ভাইয়ের পচা-গলা দেহ পুলিশ উদ্ধার করে কুয়ো থেকে। গ্রেপ্তার করা হয় জগন্নাথ ও তার কিছু সাথীকে।
প্যারাসাইকোলজিস্টরা কী পেলেন
যমজ জাতিস্মরের ঘটনা নিয়ে বারবার করে অনুসন্ধানের (নাকি জাতিস্মর প্রমাণের) কাজে এই অঞ্চলে এসেছিলেন বিশ্বের তিন নামী-দামি প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ আরলেন্ডার হারাল্ডসন (Dr. Erlendur Haraldson), আয়েন স্টিভেনসন (Ian Stevenson) ও ডঃ মেহরোত্রা। এঁরা প্রত্যেকেই একাধিকবার এখানে এসে অসুসন্ধান চালিয়েছেন। ওঁদের অনুসন্ধানের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী সেই সময় এদেশের ও বিদেশের বহু ভাষাভাষি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস রামু-রাজুর অসাধারণ জাতিস্মর কাহিনী দু’মলাটে বন্দি করে বাজারে ছাড়েন। এবং দারুণ বাজারও পান।
এঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানতে পারি, রামু ও রাজু শুধুমাত্র ভীম ও ভীষ্মের জীবনের নানা জানা ও অজানা কাহিনীই শোনায়নি, পূর্বজীবনের অনেককেই চিনিয়ে দিয়েছিল। রামু ও রাজুর কাহিনী দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে। রামু-রাজুকে দেখতে প্রতিদিন ছুটে আসছিল প্রচুর মানুষ। ছুটে এসেছিলেন ভীম ও ভীষ্মের মা রামদেবী ত্রিপাঠী। সঙ্গে এনেছিলেন ভীম ও ভীষ্মের পুত্রদের ও বোনকে। রামু ও রাজু ওদের প্রত্যেককেই চিনতে পেরেছিল এবং প্রকাশ্যেই চিনিয়ে দিয়েছিল। প্রমাণ করেছিল, ওদের দাবির মধ্যে কোনও অসারতা ছিল না। এই ঘটনার সাক্ষ্য হিসেবে প্যারাসাইকোলজিস্টরা রামু ও রাজুর শিক্ষক পণ্ডিত মান্নালাল, মা কাপুরীদেবী, বাবা রামস্বরূপ শর্মা ও জেঠা গয়াপ্রসাদ শর্মার কথা উল্লেখ করেছেন। রিপোর্টগুলো থেকে আরও জানতে পারি, উঁচা লারপুরের অনেককেই ওরা দু’ভাই চিনতে পেরেছিল। ভীম ও ভীষ্ম খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ন’জনের মধ্যে যারা জামিন পেয়েছিল, তারাও ছুটে এসেছিল রামু ও রাজুকে দেখার চুম্বকীয় আকর্ষণে। রামু ও রাজু তাদের প্রত্যেককেই চিনতে পেরেছিল। যমজ জাতিস্মর এও জানিয়েছিল, তাদের খুন করার ব্যাপারে জগন্নাথের প্রধান সঙ্গী ছিল রাজারাম, বংশীগোপাল ও হরি। পুলিশের রেকর্ড ওদের এই বক্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করে।
প্যারাসাইকোলজিস্টরা দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে এই বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে-রামু-রাজুদের পরিবার ও ভীম-ভীষ্মদের পরিবার প্রথম উভয়ের সঙ্গে পরিচিত হয় রামু-রাজু জাতিস্মর হয়ে ওঠার পর। রামু ও রাজুর বাবা ও জেঠা এই ঘটনার আগে ভীম-ভীষ্মের ঘটনা জানতেন না। এমত অবস্থায় প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, রামু ও রাজু বাস্তবিকই পৃথিবীর ইতিহাসে জাতিস্মরের এক অনন্য উদাহরণ। যমজ ভাই মৃত্যুর পরও যমজ ভাই হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন- এ’এক অনন্য নজির।
পত্র-পত্রিকায় এইসব প্যারাসাইকোলজিস্টদের অনুসন্ধান পর্বের কথা ও তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা প্রচারিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ সন্ধান পেয়েছেন অসাধারণ যমজ জাতিস্মরের।
অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি
১৯৭৩’এর মার্চে আমি যখন রামু ও রাজুর রহস্য নিয়ে সত্যানুসন্ধানে নামি, তখন ওরা দু’জনেই ক্লাস থ্রি’তে পড়ে। বয়স দশ ছুঁই ছুঁই।
জাতিস্মর রহস্যের জট ছাড়াবার আগে আমি কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :
১. শ্যামনগর ও উঁচা লারপুর গ্রাম দু’টি একই পুলিশ স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ স্টেশনের নাম—গুরসাহিগঞ্জ।
২. দুই গ্রামের বাজার বলতে গুরসাহিগঞ্জ।
৩. দুই গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন যশোদা।
৪. ভীম ও ভীষ্মের হত্যা এতই ভয়ংকর ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছিল যে এই হত্যা কাহিনী শুধুমাত্র গুরসাহিগঞ্জ থানা এলাকার চৌহুদ্দিতে আলোড়ন তুলে থেমে থাকেনি; ফারাক্কাবাদ জেলা, তথা উত্তরপ্রদেশ জুড়েই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ১৯৬৪ সালের ৫ মে, স্থানীয় পত্রিকাগুলোয় গুরুত্বের সঙ্গেই খবরটি পরিবেশিত হয়।
৫. শ্যামনগর গ্রামের বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই রামু-রাজুর জাতিস্মর হয়ে ওঠার কাহিনী শোনার আগেই ভীম- ভীষ্মের হত্যা কাহিনী শুনেছিলেন।
৬. রামু ও রাজুর জেঠামশায় গয়াপ্রসাদ শর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন— রামু-রাজুর মুখ থেকে শোনার আগে তিনি ভীম-ভীষ্মের কথা জানতেন না।
গয়াপ্রসাদের এই ধরনের বক্তব্য মেনে নেওয়া একান্তই কঠিন। গাঁ-গঞ্জে যাঁরা থাকেন, তাঁরা জানেন, আশে-পাশের কোনও গাঁয়ে এমন এক ধনী পরিবারের ডাকাবুকো, টগবগে দুটি মানুষকে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করার পর লাশ পাচারের চেষ্টা, লাশ আবিষ্কার, পাশের পাড়ার আর এক জবরদস্ত শক্তিমান মানুষের সদলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ঘটনা ঘটলে সেই রোমাঞ্চকাহিনী কী বিপুলভাবে আশে-পাশের দশ-বিশটা গাঁয়ের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়, আলোচনার লোভনীয় চাটনি হয়ে ওঠে। ভীম-ভীষ্মের হত্যা ও জগন্নাথের দলবল সহ ধরা পড়ার উত্তেজক কাহিনী একইভাবে আশে-পাশের গাঁয়ের মানুষদের নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু একজন সুস্থ-সবল, সামাজিক মানুষ গয়াপ্রসাদ ওই ঘটনার বিন্দু-বিসর্গ কিচ্ছু জানতে পারলেন না—বিশ্বাস করা খুবই কষ্টসাধ্য।
৭. রাজু ও রামুর মা তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন এই যমজ সন্তান জন্মাবার আগেই তিনি ভীম-ভীষ্মের হত্যা ও সেই সূত্রে ভীমদের ও তাদের পরিবারের বিষয়ে অনেক কথাই শুনেছিলেন।
৮. ভীম ও ভীষ্মের মা রামদেবী তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তিনি রামু ও রাজুকে প্রশ্ন করেছিলেন, “আমি কি তোমাদের মা?” ওরা উত্তর দিয়েছিল, “হ্যাঁ”। রামদেবী ভীম ও ভীষ্মের ছেলেদের হাজির করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “ওরা কি তোমাদের ছেলে?” রামু ও রাজু উত্তর দিয়েছিল, “হ্যাঁ”। ভীমের বোনকে দেখিয়ে রামদেবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, “এ কি তোমাদের বোন?” ওরা উত্তর দিয়েছিল, “হ্যাঁ”।
এগুলো কোনওভাবেই রাজু ও রামুর আগের জন্মের মা, সন্তান ও বোনকে চিহ্নিত করার সঠিক পদ্ধতি নয়। একই বয়সের একাধিকের সঙ্গে মিশিয়ে হাজির করার পর ওরা যদি আগের জন্মের ওইসব আপনজনদের চিহ্নিত করত, সেইক্ষেত্রে ‘সঠিক চিহ্নিতকরণ’ বলে মেনে নেওয়াটা হতো যুক্তিসঙ্গত।
যে’ভাবে রামদেবী প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে উত্তর “হ্যাঁ” হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।
৯. চন্দ্রসেন তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, “আমরা যে রামু ও রাজুকে দেখতে হাজির হয়েছি, তা রামু-রাজুর অজানা ছিল না। বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসা কথা শুনতে পাচ্ছিলাম—ভীম-ভীষ্মের মা, বোন, ছেলেরা ও দাদা এসেছেন। তারপর যে ভাবে মা ওদের দু’জনকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে ওরা ‘হ্যাঁ’ বলবে এটাই স্বাভাবিক। এটা কোনওভাবেই সঠিক পরীক্ষা ছিল বলে আমি মনে করি না।”
১০. রামুর সাক্ষাৎকার নেবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তোমার সম্পর্কে এক ভাই রামকিশোর উঁচা লারপুরেই থাকে। তাকে তোমার মনে আছে?” জবাবে রামু বলেছিল, “হ্যাঁ”।
—”রামকিশোর তোমার খুড়তুতো ভাই, তাই না?”
এবারও রামু জবাব দিয়েছিল, “হ্যাঁ”।
আমি ভীমদের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ‘রামকিশোর’ নামে কোনও তুতো ভাইই ভীমদের ছিল না। ভীমদের পরিবারে এক এবং অদ্বিতীয় ‘রামকিশোর’ হলো ভীমেরই পুত্র।
১১. পুলিশ রেকর্ড থেকে জানতে পারি, দু’ভাইয়ের লাশ বস্তাবন্দি অবস্থায় ছিল না। কুয়ো থেকে মৃতদেহ তুললে দেখা যায় ওদের হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল।
১২. এবার যে তথ্যটা পেশ করতে চলেছি, সেটাই রামু-রাজুর জাতিস্মর হয়ে ওঠার দাবিকে বাতিল করার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো তথ্য।
পুলিশ রেকর্ড বলছে ভীম ও ভীষ্মকে সর্বশেষ দেখা যায় ২৮ এপ্রিল ১৯৬৪। মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় চারদিন পর। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট লেখা হয় ৪ মে ১৯৬৪।
অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কোর্ট রেকর্ড বলছে ২৮ এপ্রিল’ ৬৪ দু’ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল।
রামু ও রাজুর জন্ম আগস্ট ১৯৬৪। অর্থাৎ ভীম-ভীষ্মের মৃত্যুর সাড়ে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে রাজু-রামুর জন্ম। অথচ রাজু-রামুর বাবা ও মায়ের সাক্ষ্য অনুসারে কাপুরীদেবীর স্বাভাবিকভাবেই দশমাস গর্ভ ধারণের পরই যমজ সন্তানের জন্ম হয়েছিল।
রাজু ও রামুর যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল ভীম-ভীষ্মের মৃত্যুর প্রায় মাস ছয়েক আগে, সেখানে ভীম-ভীষ্মের আত্মার কাপুরীদেবীর গর্ভে আসার প্রসঙ্গ আসে কি করে?
জাতিস্মর তদন্ত ৫ : পুঁটি পাত্র
পুঁটি পাত্র ওরফে কাজল পাত্র’র জাতিস্মর হয়ে ওঠার খবরটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। দিনটা ৩১ মে। সালটা ১৯৬৮।
পুঁটি তখন সাড়ে তিন বছরের মেয়ে। নিবাস-মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন শহর তমলুক’এর লাগোয়া গ্রাম কাপাশবেড়িয়া। কাপাশবেড়িয়া তমলুক থেকে পাঁচ কিলোমিটারের পথ
পুঁটি পাকা মেয়ের মত পটাপট বলে যেত অনেক কথাই। বিয়ে করেছিল ‘কচি’র বাবা’কে। স্বামীর নাম কি মুখে আনতে পারে হিন্দু ঘরের কোনও সতী?পুঁটিও পারেনি! হোক না আগের জন্মের স্বামী! স্বামী তো! পদবিটা অবশ্য বলেছিল- ‘বেরা’।
আগের জন্মের সন্তানদের কথাও মনে পড়ে বইকি! এক মেয়ে আর এক ছেলে ছিল। ছেলের নাম ছিল খোকা। আর সেই সুবাদে ছেলের বাবাকে খোকার বাবাও ডাকত পুঁটি। আর মেয়ের নাম কচি।
নিজের নাম? তাও মনে আছে বই কি? ললিতা। রাধার সখী। রাধা মানে– কৃষ্ণ-প্রিয়া।
নিজেদের বাড়ি ছিল কাঠের পুলের কাছে। অবস্থা ভাল ছিল না। বিয়ের পর সচ্ছলতার মুখ দেখেছিল। বাজারের সামনে বাড়ি। পুকুর ভরা মাছ, কলমি, হিঞ্চে, শুশনি শাকের দল। গোয়ালে গরু। জোয়ান স্বামী। কোলও ভরিয়ে দিয়েছিল। প্রথমে এলো মেয়েটা। তারপর খোকা।
না, না; খোকার বাবা খারাপ মানুষ ছিল না। মাঝে-মধ্যে আমাকে মারত, মদ খেত। পুরুষ মানুষ মদ খাবে, নিজের বউকে মারবে, খারাপ কি আছে? কিন্তু শাশুড়িটা বড় ট্যাক-ট্যাক্ করত আমার পিছনে।
আমিও মাথা গরম করতাম। বাঁ করে আগুন জ্বলে যেত মাথায়। ওইটাই আমার দোষ ছিল। শ্বশুর-বাড়ি ছিলাম ভালই, খাওয়ার কষ্ট ছিল না, পরার কষ্ট ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাল থাকলাম কই! খোকার বাবাই আমাকে মেরে ফেলল। সেদিনকার সব কথা মনে পড়লে এখনও আমার সারা শরীরে আগুন ধরে যায়।
সারাটা দিন সংসারে গতর খাটিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমিয়েছি। খোকার বাবা এলো টলতে টলতে। দুপুরবেলাতেই অনেক মদ গিলেছে। আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল-খেতে দে।
দুপুরে ফিরে এসে ভাত খেতে চাইবে, জানতাম না। দুপুরে ফিরবে, তাই বলে যায়নি। ভেবেছিলাম রাতে ফিরবে। বললাম—মুড়ি দিই। খোকার বাবা বলল— ভাত খাব।
ভাত কোথায় যে দেব। দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাত খাবে বলে গিয়েছিলে? বাইরে মদ গিলতে পারলে, ভাত খেয়ে আসতে পারলে না?
দু’জনেই ঝগড়া করছিলাম। হঠাৎ খোকার বাবা গালে একটা বিশাল চড় মারল। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ছিল না। আমাকে নড়তে-চড়তে না দেখে খোকার বাবা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। ঘটি করে জল এনে চোখে-মুখে জল দিল। তাও জ্ঞান ফিরছে না দেখে ভাবল- আমাকে মেরেই ফেলেছে। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলো গোয়াল ঘরে। তারপর একটা গরু-বাঁধা দড়ি আমার গলায় বেঁধে গোয়াল ঘরে ঝুলিয়ে দিল।
এ’সব কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছে পুঁটি, বলেছেন পুঁটির বাবা বলাই পাত্র, মা বীণাপাণি পাত্র ও পুঁটির দাদা লক্ষ্মীকান্ত।
এ’সব কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন ও লিখেছেন পুঁটির গন্ধে ছুটে আসা প্যারাসাইকোলজিস্টরা। এদের মধ্যে আছেন ডঃ যমুনাপ্রসাদ, ডঃ এল. পি. মেহরোত্রা, অধ্যাপক প্রণব পাল, আয়েন স্টিভেনসন।
প্যারাসাইকোলজিস্টরা অনুসন্ধানে কী পেয়েছিলেন
১. পুটি বলেছিল ও ছিল বংশী বেরার স্ত্রী। প্রথমে স্বামীর নাম ‘কচির বাবা’ বা ‘খোকার বাবা” বললেও পরে জানিয়েছিল বরের নাম ছিল বংশী।
শালগাছিয়া গাঁ পুঁটিদের গাঁ ঘেঁষেই। সেখানে অনেক বেরা পরিবারের বাস। তাদেরই একটি পরিবারে ‘বংশী’ নামের এক মাঝ বয়সী পুরুষের হদিস মেলে, যার স্ত্রী মারা গেছেন।
২. পুঁটি বলেছিল ওর পূর্বজন্মের নাম ছিল ললিতা। বংশী বেরার মৃত বউটির নামও ছিল ললিতা।
৩. পুঁটিও কথা মত গতজন্মে ওকে গলায় ফাঁসি দিয়ে মারা হয়েছিল। বংশীর কথা মত-ললিতা গলায় ফাঁসি দিয়েই মারা গিয়েছিল।
৪. ফাঁসি দিয়েছিল গরুর দড়ি দিয়ে। গামছা বা কাপড় দিয়ে নয়। বংশী তাঁর সাক্ষ্যে জানিয়েছিলেন—পুঁটির কথাই ঠিক। ললিতা ফাঁসি দিতে গরুর দড়িই বেছে নিয়েছিল।
৫. পুঁটি জানিয়েছিল—বংশী ঘটনার দিন মদ খেয়ে বাড়ি এসেছিল এবং খাবার না পেয়ে ললিতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।
বংশী এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন।
৬. পুঁটির কথা মত বংশীদের বাড়ি ছিল শালগাছিয়া বাজারের কাছে। বাস্তবেও তাই।
৭. পুঁটি জানিয়েছিল—বংশীদের পুকুর ছিল। সত্যিই ওদের পুকুর ছিল। ৮. পুঁটি বলেছিল—ওর শ্বশুরবাড়িতে গোয়াল ছিল। বাস্তবেও তাই ছিল। ৯. পুঁটির কথা মত—ললিতার দুই সন্তান ছিল। এক মেয়ে, এক ছেলে। তাই ছিল। ললিতার মৃত্যুর সময় ছেলের বয়স ছিল এক বছর, মেয়ের বয়স তখন তিন বছর।
১০. ললিতার বাড়ি ছিল ওই গ্রামেরই প্রান্তে এক কাঠের পুলের কাছে। বাস্তবেও তাই ছিল। পুঁটির কথা সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল।
১১. শ্বশুরবাড়ির কাছে ছিল নারকোলগাছ। এ’ক্ষেত্রেও পুঁটি ঠিকই বলেছিল। বংশী বেরার বাড়ির কাছেই ছিল নারকোল গাছ।
১২. বংশী বেরার বাড়ি পুঁটি চিনিয়ে দিয়েছিল।
সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্যারাসাইকোলজিস্টরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, ঘটনাটা সত্যি।
প্যারাসাইকোলজিস্টরা বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধানের কাজে এলেও তাঁরা পুঁটিকে নিয়ে শালগাছিয়ায় বংশীর বাড়ির কাছে গিয়েছিলেন। পুঁটি বংশীর বাড়ি ঠিক-ঠিক দেখিয়ে দিয়েছিল। দেখিয়ে দিয়েছিল পুকুর, গোয়ালঘর।
এ’সব প্রমাণ হাতের কাছে পাওয়ার পর তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—পুঁটি বাস্তবিকই জাতিস্মর। এ’ছাড়া আর কী সিদ্ধান্তেই বা পৌঁছোতে পারতেন বলুন!!!
পুঁটি : কিছু তথ্য
পুঁটির জন্ম নভেম্বর ১৯৬৪। বাবা বলাই পাত্র বা মা বীণাপাণি পাত্র জন্ম তারিখ জানাতে পারেননি।
ললিতার মৃত্যু পুঁটির জন্মের ৮ বছর আগে, ১৯৫৬ সালে।
পুঁটির বাবা ছিলেন দিনমজুর। পুঁটির ঠাকুমা গঙ্গামণি আনাজপাতি নিয়ে বসতেন বাজারে।
পুঁটিদের বাড়ি যদিও কাপাশবেড়িয়ায়, তবু ঠাকুমা আনাজ নিয়ে বসতেন শালগাছিয়ার বাজারেই। কারণ কাপাশবেড়িয়ার লোকদেরও দোকান-বাজার করতে আসতে হতো শালগাছিয়াতেই। দু’টি গাঁয়ের দূরত্ব বেশি হলে দু’কিলোমিটার।
পুঁটির মা’র কথামত পুঁটি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটু বেশি মেজাজি এবং একটু গিন্নি স্বভাবের।
পুঁটির ওপরে ছিল এক দাদা ও তিন দিদি, কিন্তু পুঁটি নাকি দিদিদের ওপরও ‘দিদি-গিরি’ করত।
দেড় বছর বয়স থেকেই পুঁটি নাকি ওর পূর্বজন্মের কথা বলতে শুরু করে।
পুঁটির জাতিস্মর হয়ে ওঠার ঘটনা খুব দ্রুতই জেনেছিল আশে-পাশের দশ- বিশটা গাঁ। তমলুক শহরেও লোকের মুখে নাকি ফিরত পুঁটির কাহিনী। মুখে-মুখে ফেরার আরও একটা কারণ সম্ভবত—বংশী বেরার বউয়ের মৃত্যুর পিছনে একটা রসালো কাহিনীর সম্ভাবনাকে খুঁজে পাওয়া। বংশীর বউ আত্মহত্যা করেনি, তাকে হত্যা করেছে বংশী স্বয়ং। এমন একটা খবর সাধারণ মানুষ খাবে ভাল, এটাই স্বাভাবিক। প্রশংসার খবর ছড়ায় গরুর গাড়ির গতিতে। নিন্দা ছড়ায় রকেট গতিতে,মহামারীর মত ব্যাপকতা নিয়ে।
তারপর পুঁটির খবর গ্রাম, জেলা, দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে গোটা পৃথিবীতেই প্রচারিত হয়েছে বিশ্বের নামী-দামী প্যারাসাইকোলজিস্টদের কল্যাণে। পুঁটি আজও গ্রামের মানুষদের কাছে বিস্ময়।
অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি
১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে গিয়েছিলাম পুঁটির গাঁয়ে। মধ্যরাতে খড়গপুরে পৌঁছে যখন বাসে উঠলাম, তখন গোটা বাসে আমার সহযাত্রী মাত্র দু’জন। যার একজন কন্ডাকটর ও একজন পুলিশ। নকশাল আন্দোলন ডেবরা, গোপীবল্লবপুরের গণ্ডি ছাড়িয়ে যে মেদিনীপুর জেলার অনেকাংশতেই ছড়িয়ে পড়েছে, শ্বেত-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে পাল্টা লাল-সন্ত্রাস, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি রাতের বাসে এমন যাত্রীর আকাল দেখে।
মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুনো শীতের ভোরে পৌঁছেছিলাম পুঁটির বাড়ি। ‘ভোর’ বেছে নেবার কারণ—বলাইবাবুর জীবিকা।
অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব তথ্য জানতে পেরেছি, তার থেকেই কিছু তথ্য এখানে আপনাদের জন্য হাজির করছি, যেগুলো ‘পুঁটি-রহস্য’ উন্মোচনে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি।
১. বলাই পাত্র তার পরিবার নিয়ে কাপাশবেড়িয়ায় আসার আগে থাকতেন শালগাছিয়ায়। এ’কথা জানিয়েছিলেন বলাইবাবু স্বয়ং ও তাঁর স্ত্রী বীণাপাণি।
২. শালগাছিয়ায় বংশী বেরার বাড়িতেই তাঁরা ভাড়াটে হিসেবে বাস করতেন। এ’কথাও জানিয়েছিলেন বলাইবাবু, বীণাপাণিদেবী, বংশী বেরা ও শালগাছিয়ার কিছু অধিবাসী।
৩. ললিতার গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুর খবর বলাইবাবুদের পরিবারের কারোরই অজানা ছিল না।
৪. গলায় যে গরুর দড়ি দেওয়া হয়েছিল, তাও বলাইবাবু, বীণাপাণিদেবীদের অজানা ছিল না।
৫. মৃত্যু যে গোয়ালঘরেই ঘটেছিল তাও পুঁটির মা-বাবা জানতেন। জানত পুঁটির ভাই-বোনেরা।
এই তথ্যগুলোর সাহায্য নিয়ে আমাদের পক্ষে এই সন্দেহ প্রকাশ করাটাই স্বাভাবিক—এই খুঁটি-নাটি তথ্য পুঁটিরও অজানা ছিল না।
অনুসন্ধানে আরও জেনেছিলাম :
৬. ললিতার বাড়ি যে কাঠ-পুলের কাছে তা পুঁটির বাবা-মা জানতেন।
৭. পুঁটির বাবা-মা জানতেন, ললিতার এক মেয়ে ও এক ছেলে।
৮. ওঁরা এও জানতেন ললিতা বংশী বেরাকে ‘খোকার বাবা’ বা ‘কচির বাবা’ বলে ডাকতেন।
৯. যে-হেতু বংশীদের বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন বলাইবাবুরা তাই জানতেন বংশীদের পুকুরের কথা, গোয়ালের কথা, নারকোলগাছের কথা।
১০. বংশীবাবুর বাড়ি বাজারের কাছে—এটা পুঁটিদের পরিবারের অজানা ছিল না।
১১. ললিতার মৃত্যুর দিন বংশী মদ খেয়ে এসেছিলেন, ভাত না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তার থেকে দু’জনে ঝগড়া এবং ললিতার আত্মহত্যা—এ’সব তথ্য বংশীবাবুই গাঁয়ের মানুষদের জানিয়েছিলেন।
বংশীবাবু তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, ললিতা গলায় দড়ি দিয়েছিল বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটে নাগাদ।
বংশীবাবুকে হত্যাকারী বলে গাঁয়ের কেউই সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তাই পুলিশকে খবর দিয়ে বংশীকে অস্বস্তিকর অবস্থায় সেদিন ফেলতে চাননি। কারণ তাঁরাও অনেকেই মনে করতেন-ললিতার একটু মাথায় গোলমাল ছিল। যখন তখন দুম-দাম্ খেপে যেত। এমনই এক রাগের মুহূর্তে ললিতা গলায় দড়ি দিয়েছিলেন বলে পাড়া-পড়শিরা বিশ্বাস করেছিলেন।
১২. পুঁটির জাতিস্মর হয়ে ওঠার কথা গোটা তল্লাটে চাউর হওয়ায় অনেক গাঁ-গঞ্জের মানুষ ভিড় করে এলেও যাননি বংশীবাবু।
“কেন যাননি?” আমার কথার উত্তরে বংশীবাবু জানিয়েছিলেন, “ও ললিতা নয়। তাই ফালতু সময় নষ্ট করতে যাইনি।”
“কি করে নিশ্চিত হলেন ও ললিতা নয়?”
“পুঁটি যদি সত্যিই ললিতা হতো, তাহলে নিশ্চয়ই বলতো ললিতা আত্মহত্যা করেছিল।”
১৩. বংশী তাঁর বউ ললিতাকে যে ভাবে হত্যা করেছিলেন বলে পুঁটি বর্ণনা করেছিল, সেই বর্ণনার দিকে পাঠক-পাঠিকাদের মনোযোগ আর একটি বারের জন্য ফেরাতে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখছি—ললিতার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তগুলোর এই বর্ণনাই অন্যান্য প্যারাসাইকোলজিস্টদের লেখাতেও পাবেন।
পুঁটির কথা মত ললিতা বংশীর চড় খেয়ে মারা যাননি, জ্ঞান হারিয়েছিলেন মাত্র। যদিও জ্ঞান হারিয়েছিলেন, তবুও বুঝতে পারছিলেন ওঁর চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন বংশী। জলের ঝাপটায় কাজ হয়নি। জ্ঞান ফেরেনি। এত চেষ্টাতেও ললিতার জ্ঞান না ফেরায় ও মারা গেছে মনে করে ভীত বংশী ওকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে গেছেন গোয়ালঘরে। ঘর থেকে গোয়ালঘরের দূরত্ব আনুমানিক ১২৫ ফুট। এতটা পথ দোল খেতে খেতে যেতে যেতেও ললিতার জ্ঞান ফেরেনি। অজ্ঞান হলেও ললিতা জ্ঞান হারাননি! বুঝতে পারছিলেন ওঁকে বংশী গোয়ালঘরে নিয়ে চলেছেন। ললিতাকে গোয়ালঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখেছেন বংশী। ললিতা বুঝতে পেরেছেন। ললিতার গলায় গরুর দড়ির ফাঁস পরিয়েছেন বংশী। ললিতা তাও বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ বোঝার মত টল্টনে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞানতার জন্য ‘টু’ শব্দটি করতে পারেননি। তারপর ললিতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সব বুঝে-সমঝেও ললিতা ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছেন। রা’টি কাটেননি কোনও অভিমান থেকে নয়, অজ্ঞান থাকার জন্য। ললিতা এত কিছু বুঝলেও, কিচ্ছুটি বুঝতে পারেননি বংশী। বুঝতে পারেননি, চড় খাওয়ার পর ললিতার মৃত্যু হওয়া তো দূরের কথা, জ্ঞানটি পর্যন্ত টনটনে রয়েছে। আহাম্মক আর কাকে বলে! বোধহয় এরপরও যাঁরা অজ্ঞান ললিতার স্বজ্ঞানে ফাঁসিতে চড়ার গল্প সরল বিশ্বাসে মেনে নেন, তাঁদেরই বলে।
জাতিস্মর তদন্ত ৬ : গুজরাটের রাজুল
যেখানে জাতিস্মর, সেখানেই দৌড়োও। ‘চরৈবতি’র সেই কথাগুলো আমাকে সেই থেকে আজও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে—চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। এমনি চলতে চলতে, জাতিস্মর তদন্তের পুঁটলি আজ দস্তুর মতো এক ভারী বোঝা। সেই বোঝা ঘেঁটে খুব সতর্কতার সঙ্গে মাপ-জোক করে, ঝাড়াই-বাছাই করে সেইসব জাতিস্মর রহস্যকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাইছি যেগুলো বিস্ফোরক, অনেক মানুষের চেতনাকে নাড়িয়ে দেবার মত, আচ্ছন্ন করার মত, অথবা যেগুলো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতি বা কুখ্যাতির অধিকারী প্যারাসাইকোলজিস্টরা ‘উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রি’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের নানা সাক্ষাৎকারে ও লেখায়। এইসব ‘উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রি’ নিয়ে বিদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে দারুণ দামের গাবদা-মোটা ঝাঁ-চকচকে বই। ভারত থেকে ‘জন্মান্তরবাদ’ নিয়ে যে’সব বই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোতেও এইসব “কেসহিস্ট্রি’ জাগয়া করে নিয়েছে। এ’বার যে ঘটনা নিয়ে আলোচনায় যাব, সেটাও বিশ্ব-বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য জাতিস্মর কেসহিস্ট্রির অন্যতম।
“এই ঘটনার মুখ্য চরিত্রদের আমি ব্যাপকভাবে অনুধাবন করার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে গীতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তার বিদেহী আত্মা অন্য এক মাতৃগর্ভে একটি ভ্রুণের প্রাণ সঞ্চার করে—ন’মাস পরে যে শিশুটি রাজুল নামে জন্মগ্রহণ করেছিল।”
কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন? কে স্থির ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—রাজুল পূর্বজন্মে ছিল গীতা? ভারতবর্ষের সবচেয়ে নামী-দামী প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জন্মান্তর : রহস্য ও রোমাঞ্চ’ গ্রন্থে (‘রহস্য ও রোমাঞ্চ’ সিরিজের জন্মান্তর নিয়ে গুল্প-কাহিনী বললেও খুব একটা ভুল বলা হবে না) এই রাজুল কাহিনী স্থান পেয়েছে। স্থান দিয়েছেন কতটা গুরুত্বের সঙ্গে? ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, “রাজুল শাহ-র পুনর্জন্মের ঘটনাটিকে আমি আমার দশটি উল্লেখযোগ্য কেসহিস্ট্রির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করি।”
এ’পর্যন্ত নানা ধরনের কিছু উল্লেখযোগ্য জাতিস্মর-কাহিনী আপনাদের সামনে হাজির করেছি। বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে ছিল সত্য-গোপন, তথ্যের বিকৃতি ঘটানো, সত্যানুসন্ধানে আন্তরিকতার অভাব—ইত্যাদি জাতীয় বেশ কিছু ফাঁক-ফোকর। এ’বার আমরা দৃষ্টিকোণ পাল্টাব। এই রাজুল-কাহিনীর সূত্র ধরে আমরা একটু একটু করে বে-আব্রু করব ‘প্যারাসাইকোলজিস্ট’ নামধারীদের গবেষণার নামে প্রতারণার বীভৎস দগদগে রূপের একটি নমুনা।
স্রষ্টা সৃষ্টির চেয়ে মহান। জাতিস্মর-স্রষ্টা প্যারাসাইকোলজিস্টরাও তাঁদের সৃষ্টির চেয়ে মহান। এই মহান মানুষদের মুখোশহীন করা একান্তই জরুরি, সাংস্কৃতিক- দূষণ রোধের জন্যই জরুরি। প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আসুন, এই জরুরি কাজের জন্য আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ পাল্টাই।
গুজরাটের রাজকোট জেলা হঠাৎই গোটা ভারতের পত্র-পত্রিকায় অনেকটা জায়গা করে নিয়েছিল ১৯৬৫-র নভেম্বর-ডিসেম্বরে। রাজকোটের পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে রাজুল শাহ জাতিস্মর।
রাজুলের জন্ম ১৯৬০ সালের ১৪ আগস্ট। বাবা প্রভীনচন্দ্র শাহ। মা প্রভাবেন। রাতুল প্রভীন-প্রভাবেন-এর পঞ্চম সন্তান। মেয়ে। রাজুল জন্মেছিল ছোট্ট শহরে ভিনচিয়াতে। প্রভীন ব্যাঙ্কে কাজ করেন। বদলির চাকরি। রাজুলের জন্মের পর প্রভীন বদলি হলেন রাজকোট থেকে কেশর শহরে। রাজকোট গুজরাটের জেলা শহর। কেশর ওই জেলারই ছোট্ট একটি শহর।
রাজুলের ঠাকুরদা ভি.জে.শাহ (ডাক নাম ভজু) পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কাজ থেকে অবসর নেবার পর ১৯৬০ সাল থেকে সস্ত্রীক থাকতে শুরু করেন ওয়াঙ্কানের-এর গ্রামের বাড়িতে। এ’বাড়িতে থাকতেন ভজু শাহু’র আর এক ভাই হিম্মৎলাল ও হিম্মৎলালের স্ত্রী সুশীলবেন।
বুড়ো-বুড়িদের সংসার। বুঝিবা কিছুটা নিঃসঙ্গতা কাটাতেই ভজু শাহ তাঁর নাতনি রাজুলকে মাঝে-মধ্যে নিজের কাছে এনে রাখতেন। শিশুবয়সের একটা দীর্ঘ সময় রাজুলের কেটেছে দুই ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার সঙ্গে।
১৯৬৩ সালে রাজুল প্রথম এমন কিছু কথা বলল, যার মধ্যে লুকোন ছিল ওর পূর্বজন্মের স্মৃতিমন্থন ক্ষমতার পূর্বাভাস। রাজুল এই সময় জানিয়েছিল, ও থাকত জুনাগড়-এ। জুনাগড়? এমন শহরের নাম তো তিন বছরের ছোট্ট রাজুলের জানার কথা নয়! বিস্ময় আকাশ ছুঁয়েছিল যখন রাজুল জানাল, ওর নাম ছিল গীতা। গীতা? এমন নামে তো ভুলেও কেউ কোনও দিন ডাকেনি রাজুলকে? আর তা ছাড়া এমন হিন্দু নাম তো এই জৈন পরিবারের নিকট কি দূর, কোনও আত্মীয়েরই নেই! গীতার প্রিয় বান্ধবীটির নাম জ্যোৎস্না। এতদিন রাজুলের সব বন্ধু আর বান্ধবীদের নামই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু, জ্যোৎস্না নাম তো এই প্রথম শোনা গেল রাজুলের মুখে। প্রথম শুনলে কি হবে, জ্যোৎস্নাই নাকি সেরা বন্ধু! গোটা ব্যাপারটাই কমন যেন রহস্যময়! কিন্তু কৌতূহলী ও কিছুটা বিস্মিত ঠাকুরদা-ঠাকুরমা রাজুলকে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি। কারণ পরদিনই রাজুলকে বাবা প্রভীন নিজের বাসা-বাড়ি কেশর-এ নিয়ে যান। প্রভীনকে অবশ্য তাঁর বাবা রাজুলের এইসব অদ্ভুত কথাবার্তার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রভীন সে’সব কথায় বিশেষ কান দেননি। এইটুকু বাচ্চা মেয়ের ও’সব আজগুবি কথায় গুরুত্ব দেওয়া নেহাতই পাগলামি।
কেটে গেছে আরও দুটি বছর। ‘৬৫-র মে’তে রাজুল এলো ঠাকুরদাদের বাড়িতে। রাজুলের বয়স এখন পাঁচ। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে রাজুল এ’বার এসেই শুরু করল, ও যখন গীতা ছিল তখনকার নানা কথা। এ’বার আর বুঝতে অসুবিধা হল না রাজুল ওর গতজন্মের কথা বলছে। এতদিন যে সব কথা বাবা-মা ও ভাই- বোনদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি ওদের কল্পনা বলে উড়িয়ে দেবার প্রবণতায়, সে-সব না বলা কথাই বেরিয়ে আসতে লাগল এ’বাড়িতে উৎসাহী শ্রোতাদের পেয়ে।
একদিনের ঘটনা। রাজুল আপন মনে গোল হয়ে ঘুরছিল, আর মুখে কি যেন বলছিল। ঠাকুরদা ভজু শাহ রাজুলের কাছে জানতে চাইলেন, এটা কি খেলা? রাজুল জানাল, “আমি ‘জুনাগড় গিরভি’ খেলছি। আগের জন্মে যখন গীতা ছিলাম, তখন তো জুনাগড়ে থাকতাম, তখন এই খেলা খেলতাম।”
তারপর একটু একটু করে গীতার জীবনের অনেক কথাই বলেছে। কি কি বলছে, তা ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি থেকেই তুলে দিচ্ছি :
এক : “আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন সকলে আমাকে ‘বেবী’ বলে ডাকত। তারপরে যেদিন বসন্তের টিকা দেওয়া হয়ে গেল তখন থেকে আমাকে সবাই ‘গীতা’ নামে ডাকত।’
দুই : “খুব ছোট বেলাতেই আমার একবার ভীষণ বেশি জ্বর হয় আর তাতেই আমি মারা যাই।”
তিনঃ “আমার আগের বাবার লোহালক্কড়ের দোকান ছিল।”
চার : “আমার এখনকার বাবা তো ফুলপ্যান্ট করে কিন্তু আগের বাবা বেশির ভাগ সময়েই ধুতি পরত।”
পাঁচ : “আমরা সবাই পিতলের বাসনে খেতাম। কেবল বাবা স্টিলের থালা ছাড়া খেত না।”
ছয় : “তখন আমরা বেশ রাত্রি হলে খাবার খেতাম ঘুমোতে যাবার আগে। এখন তো সূর্য ডোবার আগেই রাতের খাবার খেয়ে নিতে হয়।” (জৈনরা সূর্য ডোবার আগেই রাতের খাবার খান।)
সাত : “আমাদের পুরোনো বাড়ির ঠাকুরেরা সব জামা কাপড় পরা চেহারার কিন্তু এখনকার ঠাকুরের গায়ে কোন কাপড় নেই।” (রাজুলরা ছিল জৈন ধর্মের দিগম্বর সম্প্রদায়ের। দিগম্বর সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা নগ্ন।)
আট : “আগের মা খুব লম্বা ও রোগা দেখতে ছিল।”
নয় : “যখন তার নাম গীতা ছিল তখন তারা যে বাড়িতে থাকত সেটা এখনকার মত অত বড় নয়।”
দশ : “সে বাড়িতে বারান্দা ছিল।”
এগারো : “দীপাবলীর সময়ে তার আগের জীবনের বাবা বাড়িটাতে লাল রঙে চুনকাম করেছিল।”
বারো : “থ্যাকাররা প্রচুর দুধ কিনতেন এবং বড় বড় পাত্রে সেই দুধ রাখা থাকত।”
রাজুলের ঠাকুরদা ভজু শাহ এ’সব দেখে-শুনে সত্য জানতে দারুণ-রকম উৎসাহী হয়ে পড়েন—সত্যিই কি রাজুল জাতিস্মর? নাকি, গোটাই ওর কল্পনা- বিলাস? ভজু শাহর এক জামাতা থাকেন সুরেন্দ্রনগর। নাম—প্রেমচাঁদ শাহ। প্রেমচাঁদের ব্যবসা আছে। ব্যবসার কাজে মাঝে-মধ্যে জুনাগড় যেতে হয় তাঁকে। শ্বশুর ভজু জামাই প্রেমকে অনুরোধ করলেন এ’বার জুনাগড়ে গেলে ও যেন গীতাদের পরিবার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়।
‘৬৫-র জুনেই কাজে জুনাগড়ে এলেন প্রেমচাঁদ। কাজের ফাঁকে এক সময় গেলেন মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার’স অফিসে। রাজুলের জন্মের বছরখানেকের মধ্যে ‘গীতা’ নামের কেউ মারা গিয়েছিল কি না, এটা দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। একজন ক্লার্ক বাবুলাল এ’বিষয়ে প্রেমচাঁদকে সাহায্য করেন। (১৯৬৯-এ আমি যখন জুনাগড় মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার’স অফিসে গিয়েছিলাম, তখন এই বাবুলালই মৃত্যু নথিভুক্তির রেজিস্টার খুলে আমাকে দেখিয়েছিলেন গীতার নাম, গীতা থ্যাকার। মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ১৯৫৯। বাবার নাম গোকুলদাস থ্যাকার।)
রাজুলের কথা এ’ভাবে সত্যি হয়ে ওঠায় শিহরিত হলেন ভজু শাহ। তিনি ঠিক করলেন রাজুলকে নিয়ে গোকুলদাসের বাড়ি যাবেন। যাওয়ার আগে রাজুলের বক্তব্যগুলো মিলিয়ে দেখার জন্য একটা ‘লিস্ট’ তৈরি করে ফেললেন। রাজুলের পূর্বজীবনের বাইশটা বক্তব্যের তালিকা। (ভজু শাহই আমাকে এই বাইশটা বক্তব্যের তালিকা তৈরির কথা জানিয়েছিলেন। এই তালিকার বারোটি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালিকায় উল্লেখ করেছি। বাকি এখানে তুলে দিচ্ছি।)
এক : গীতার বাবা দেওয়ালী উপলক্ষে বাড়ির বাইরেটা লাল রঙ করার আগে বাড়ির রঙ ছিল সবুজ।
দুই : ওরা থাকত একতলায়।
তিন : উনুনে রান্না হতো। দুধ গরম হতো।
চার : মায়ের নাম শান্তা, অথবা কান্তা।
পাঁচ : রাজুলের বাবা ছিলেন গীতার বাবার বয়সী।
ছয় : বাবার মিষ্টির দোকান ছিল। (ওদের যে লোহার ব্যবসা ছিল, এ’কথাও বলেছিল রাজুল।)
সাত : গীতার একটি ছোট ভাই ছিল।
আর্ট : প্রিয় বন্ধু জ্যোৎস্নারা থাকত বাড়ির কাছেই।
নয় : মা প্যাঁড়া বানাত।
দশ : বাড়ির পুজোয় ঠাকুরকে খেতে দেওয়া হতো প্যাঁড়া।
(১৯৬৯’এর ডিসেম্বরে শ্রীশাহ আমাকে জানয়েছিলেন, আমার আসার প্রায় আগে আগেই ডঃ আয়েন স্টিভেনসন ও ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন রাজুল রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে। তাঁদের দু’জনকেই শ্রীশাহ রাজুলের বাইশটি বক্তব্যের তালিকা দেখিয়েছিলেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “জন্মান্তরবাদ : রহস্য ও রোমাঞ্চ” গ্রন্থে দেখেছি তিনি তালিকার এগারোটি বক্তব্য আলোচনায় এনেছেন। এগারোটি বিষয়ে অদ্ভুত নীরবতা পালন করেছেন। এটি অবশ্যই একটি তথ্য গোপনের দৃষ্টান্ত। কেন তথ্য গোপন? এই তথ্য গোপন কি সত্যকে বিকৃত করেছে? নাকি এই তথ্য ছিল অতি অপ্রয়োজনীয়?
না, এ’বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করে নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য হাজির করব, যার সাহায্যে প্রিয় পাঠক-পাঠিকারাই উত্তর খুঁজে নিতে পারবেন।
আয়েন স্টিভেনসন তাঁর লেখা “The Case of Rajul Shah” -তে এই ধরনের সরাসরি তথ্য গোপনের কোনও স্থূল চেষ্টা করেননি। তিনি শ্রীশাহের তৈরি বাইশ-দফা তালিকা হিসেবে আইটেমগুলোর উল্লেখ না করলেও রাজুল যে এ’সব কথা বলেছিল, গ্রন্থটিতে তা জানিয়েছেন। )
১৯৬৫-র নভেম্বরে ভজু শাহ রাজুল রহস্য সন্ধানে জুনাগড়ে এলেন। সঙ্গে স্ত্রী,ভাই হিম্মৎলাল, জামাই প্রেমচাঁদ ও রাজুল। গোকুলদাস থ্যাকারের বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু গোকুলদাসকে পাওয়া গেল না। কারণ, গীতার মৃত্যুর পর গোকুলদাস বাড়ি পাল্টেছেন। সেদিন না পাওয়া গেলেও পাওয়া গেল। দু’লাখ লোকের ছোট শহর জুনাগড়ে ব্যবসায়ী গোকুলদাসের ঠিকানার হদিস পাওয়া অসম্ভব ছিল না বলেই পাওয়া গেল।
তারপর যা যা ঘটল তা সবই নানাভাবে নানা রঙে নানা ঢঙে প্রকাশিত হলো নভেম্বর, ডিসেম্বর ধরে ভারতের নানা পত্রিকায়। সবারই মোদ্দা কথা—রাজুল এক নির্ভেজাল জাতিস্মর!!
সে খবর পড়ে অনেক প্যারাসাইকোলজিস্টই এলেন। এলেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আয়েন স্টিভেনসন, ডঃ এল.পি. মেহরোত্রা, ডঃ যমুনা প্রসাদ, স্বামী কৃষ্ণানন্দ; যাকে বলে একেবারে স্টার-মেগাস্টার-সম্মেলন। একটা কাকতালীয় ব্যাপার হলো, এঁরা প্রত্যেকেই এসেছিলেন ঝড় তোলা খবরটি প্রকাশের চার বছর বাদে ১৯৬৯-এ। এবং এঁরা প্রত্যেকেই এলেন নভেম্বর-ডিসেম্বরে। এই সময়ই এইসব বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্টদের দারুণ উজ্জ্বলতার পাশে একটি নিরুজ্জ্বল অতি সাধারণ মানুষও সত্যানুসন্ধানে এসেছিলেন। সেই অকিঞ্চিৎকর মানুষটি এই লেখক।
‘৬৫ ও তার পরবর্তী রাজুল রহস্যের অনুসন্ধান পর্বে কি কি ঘটেছিল? সেটা জানতে আসুন আমরা উঁকি মারি ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জন্মান্তরবাদ : ….’এর পাতায়। পাশাপাশি আমরা ফিরে তাকাব এই একই প্রসঙ্গে সম্পর্কিত সাক্ষীরা কি বলেছেন, তার দিকে।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
১. ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ভজু শাহ’র বক্তব্য হিসেবে যা লিখেছেন : “থ্যাকারদের বাড়ির কাছে পৌঁছনোর আগেই এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা রাস্তার ধারে এক দোকান থেকে দুধ কিনছিলেন। তাঁকে দেখেই রাজুলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। রাজুল ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে জানায় : “আমার আগের জন্মের মা”।”
শ্রীভজুভাই শাহ তারপর ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন, “আমরা ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি কিছুটা সন্দিহানভাবে আমাদের লক্ষ্য করতে করতে জানালেন, তাঁর নাম কান্থাবেন— তিনি গোকুলদাস থ্যাকারের স্ত্রী।”
“আমাদের তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিছুটা আত্মস্থ হয়ে আমি ভদ্রমহিলাকে আমার নাতনির কথা বললাম, জানালাম সে তাঁর মৃত কন্যা ‘গীতা’ বলে নিজেকে মনে করে।
”কান্থাবেন বিমূঢ়ভাবে রাজুলকে লক্ষ্য করতে থাকেন। দ্বিধা এবং অবিশ্বাসের দোলায় তিনি বিচলিত বোধ করতে থাকেন। কিন্তু ক্রমশ রাজুলের উৎসাহী এবং উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখে জল ভরে আসে। সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত না হতে পারলেও তিনি গভীর স্নেহে কোলে তুলে নেন। তিনি আমাদের সকলকে তাঁর বাড়িতে আসতে বললেন….”
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. শ্রীভজু শাহ (রাজুলের ঠাকুরদা), ২. হিম্মৎলাল শাহ (ভজু শাহ’র ভাই), ৩. কান্থাবেন থ্যাকার (গীতার মা)।
আমি কি পেয়েছি এবং মন্তব্য
ক. ভজু শাহ্’র কথামত, “সকালে আমরা থ্যাকারদের বাড়ি একটা প্রাথমিক ভ্রমণ সেরে এসে দ্বিতীয় দফায় যখন ও বাড়ি যাচ্ছি, তখন গীতার মা কান্থাবেন থ্যাকারের সঙ্গে আবার দেখা। কান্থাবেনকে দেখিয়ে রাজুলকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই ভদ্রমহিলাকে চেন?’ রাজুল একটু ভেবে উত্তর দিল, ‘আমার ও’জন্মের মা।”
খ. হিম্মৎলাল ভজু শাহের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।
গ. কান্থাবেন একটু অন্য কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, “আমাকে দেখিয়ে শ্রীভজু শাহ রাজুলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘ইনি কি গীতা’র মা?’ উত্তরে রাজুল জানিয়েছিল, ‘হ্যাঁ, গীতার মা’।”
কান্থাবেনও জানিয়েছিলেন, “শ্রীশাহদের পরিবারের লোকেরা জানতেন আমি কে। কারণ এই ঘটনার দিন সকালেই শাহ পরিবারের লোকেরা আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।
আয়েন স্টিভেনসন “The Case of Rajul Shah”-তে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “V.J. Shah himself had met Kantaban Thacker that morning (in a preliminary visit to the Thacker family), and, so he knew who she was when Rajul recognized her;”
স্টিভেনসনের এই বক্তব্য আমার কথাকেই সমর্থন করছে, যদিও স্টিভেনসন রাজুলকে শেষ পর্যন্ত জাতিস্মর বলে চালাতে চেয়েছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
২. ভজু শাহ’রা থ্যাকারদের বাড়িতে পৌঁছনোর পর কান্থাবেন “তাঁর স্বামী গোকুলদাস থ্যাকারকে খবর পাঠালেন তখনি বাড়িতে আসবার জন্যে।”
“গোকুলদাস ঘরেতে এসে কিছু বলবার আগেই বা তার সঙ্গে অন্য কেউ কথা বলার আগেই রাজুল সকলকে বিস্মিত করে হাসিমুখে বলে ওঠে, ‘আমার আগের বাবা এসে গেছে।”
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. হিম্মৎলাল শাহ (ভজু শাহ’র ভাই); ৩. গোকুলদাস থ্যাকার (গীতার বাবা), ৪. কান্থাবেন থ্যাকার।
আমি কি পেয়েছি এবং মন্তব্য
ক. ভজু শাহ’র বক্তব্য : “আমরা গোকুলদাসের ঘরে বসে। এমন সময় গোকুলদাস এলেন। কেউ একজন রাজুলকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ও কে বল তো?’ রাজুল উত্তরে বলেছিল, ‘গোকুলদাস’।”
খ. আমার এক প্রশ্নের উত্তরে হিম্মৎলাল শাহ জানিয়েছিলেন, “সেই সময় অবশ্য আমরা গোকুলদাসের আসা নিয়ে কথা বলছিলাম। ওদের পরিবারের কেউ একজন বলছিলেন, ‘খবর পাঠানো হয়েছে। এখুনি গোকুলদাস এসে পড়বেন। হতে পারে রাজুল এ কথা শুনেছিল।
গ. গোকুলদাস অবশ্য অন্য কথা বলেছিলেন। তাঁর কথা মত, “আমি ঘরে ঢুকতেই ভজু শাহ রাজুলকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘গোকুলদাস কে বল তো?’ রাজুল তখন আমাকে দেখিয়ে বলে, ‘এ, এ আমার বাবা’।”
ঘ. কান্থাবেনের কথা মত, “গীতার বাবা আসার আগে ওকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি ও আমাদের পরিবারের আর একজন কেউ কোনও একটা প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলাম, ‘গীতার বাবা এখুনি এসে পড়বেন।”
ঙ. কান্থাবেন এও জানিয়েছিলেন, তাঁর মনে আছে, ‘গীতার বাবা এখুনি এসে পড়বে’ বলার পর প্রথম যিনি ঘরে ঢুকেছিলেন, তিনি গীতার বাবা।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে এরপর বলতেই পারি—উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করেছেন। ১৯৬৯-এ আমি যখন সত্যানুসন্ধানে নামি তখনও পর্যন্ত রাজুল একবারের জন্যেও গীতার বাবার নাম জানাতে পারেনি। পূর্বজন্মের এত স্মৃতি মনে রেখে বাবার নামটাই ভুলে যাওয়া খুবই অস্বাভাবিক!
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
৩. “রাজুল জানায় যে তার আগের বাবার লোহালক্কড়ের দোকান ছিল। এটা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়…”
কাদের মন্তব্য গ্রহণ করেছি
১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. ভজু শাহ।
আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
ক. গীতার বাবা গোকুলদাসের ব্যবসা ছিল চাল, গম, ডাল ইত্যাদি বিক্রির। খ. ‘সাইড-বিজনেস’ হিসেবেও লোহালক্কড়ের ব্যবসা ছিল না।
গ. রাজুল এও বলত-গীতার বাবার মিষ্টির দোকান ছিল। এটিও ছিল ভুল তথ্য। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
৪. “বাড়ি ঘর দোরের বর্ণনা বাইরের রঙ ইত্যাদি নিয়ে তার সব কথাই মিলে যায়।”
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি
১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. আমি নিজে দেখে এসেছি, ৩. ভজু শাহ। আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
ক. রাজুল বলেছিল, ওদের ঘরের রঙ ছিল সবুজ।
খ (১). গোকুলদাস জানিয়েছিলেন, গীতার জীবনে বাড়ির রঙ কোনও সময়ের জন্যেই সবুজ ছিল না।
খ (২). বাড়ির রঙ ছিল হলদে। আমিও হলদেই দেখেছি।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
৫. “গোকুলদাস থ্যাকার দেওয়ালির সময়ে বাড়িতে লাল চুনকাম করিয়েছিলেন।”
রাজুলের দেওয়া এই তথ্য মিলে গিয়েছিল।
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি
১. গোকুলদাস থ্যাকার (গীতার বাবা)।
আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
গীতার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনও দেওয়ালিতেই বাড়িতে লাল রঙ লাগাননি।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
৬. গোকুলদাসের বাড়িতে বারান্দা ছিল।
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি
১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. আমি নিজে দেখে এসেছি।
আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
ও বাড়িতে কোনও বারান্দা ছিল না।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
৭. “প্রচুর দুধ কিনতেন এবং বড় বড় পাত্রে সেই দুধ রাখা থাকত।”
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. কান্থাবেন থ্যাকার।
আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
খুব সামান্য পরিমাণ দুধই কেনা হত। পরিমাণটা আধ সের থেকে বেশি হলে কখন-সখন এক সেরের মত।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
৮. “রাজুল জানায় : ‘আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন সকলে আমাকে ‘বেবী’বলে ডাকত। তারপর যেদিন বসন্তের টিকা দেওয়া হয়ে গেল তখন থেকে আমাকে সবাই ‘গীতা’ বলে ডাকত।”
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. গোকুলদাস থ্যাকার, ২. কান্থাবেন থ্যাকার। আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
গীতার বাবা ও মা দু’জনেই জানিয়েছিলেন, গীতা নামকরণের আগে তাঁরা মেয়েকে ডাকতেন ‘টিকুডি’ বলে।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
৯. “যখন তার নাম গীতা ছিল তখন তারা যে বাড়িতে থাকত সেটা এখনকার মত অত বড় নয়।”
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস থ্যাকার, ৩. প্রভীনচন্দ্র শাহ (রাজুলের বাবা)। আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
গীতারা যে বাড়িতে থাকত, তাতে ছিল দুটি শোয়ার ঘর ও একটি রান্নাঘর। রাজুলের বাবা থাকতেন যে বাড়িতে, তাতেও ছিল দুটি ঘর ও একটি রান্নাঘর। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
১০. “সঠিক সনাক্তকরণ থেকে রাজুলকে জাতিস্মর অর্থাৎ গীতার পুনর্জন্ম ছাড়া
অন্য কোন সংজ্ঞায় বিচার করা যায় না।”
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. নির্মলা (গীতার দিদি), ৩. কান্থাবেন, ৪. গোকুলদাস। আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
ক. গীতার মা কান্থাবেন থ্যাকারের সনাক্তকরণ কখনই ত্রুটিমুক্ত সঠিক সনাক্তকরণ নয়।
খ. গীতার বাবা গোকুলদাস থ্যাকারের সনাক্তকরণও কখনই ত্রুটিমুক্ত সঠিক সনাক্তকরণ ছিল না।
দুটি সনাক্তকরণই যে ত্রুটিযুক্ত, সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এবার বাকি সনাক্তকরণের দিকে চোখ ফেরাই :
গ. গীতার দিদি নির্মলা’কে সনাক্ত করতে রাজুল ব্যর্থ হয়েছিল। ভজু শাহ যখন রাজুল সহ গোকুলদাসের বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন নির্মলা কৌতূহলী চোখে রাজুলকে দেখছিল। গোকুলদাস পরিবারের একজন রাজুলকে জিজ্ঞেস করেন, ‘এই মহিলাকে চিনতে পার?” উত্তরে রাজুল জানিয়েছিল, “ও ছিল আমার পিসি।” নির্মলা ছিল গীতার দু’বছরের এবং রাজুলের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়।
ঘ. কাকিমা সেই সময় ঘরে উপস্থিত ছিলেন। কাকিমা’কে দেখিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয়, “একে চিনতে পারছ?” রাজুল চিনতে পারেনি।
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কি বলা হয়েছে
১১. “বাড়িতে পৌঁছে রাজুল গোকুলদাস আসার আগে অন্যসব বৃদ্ধাদের মধ্যে
থেকে গীতার ঠাকুমা শ্রীমতী জাদোবেনকে সনাক্ত করে।”
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস, ৩. কান্থাবেন, ৪. নির্মলা, ৫. হিম্মৎলাল শাহ
(ভজু শাহর ভাই)।
আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
পাঁচ সাক্ষ্যের বক্তব্য থেকে একই কথা জানতে পারি, সেই সময় গোকুলদাসের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন একজনমাত্র বৃদ্ধা, এবং তিনি হলেন গীতার ঠাকুমা। রাজুল তার দুই ঠাকুমাকে দেখছে। দু’জনেই বৃদ্ধা। ফলে ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে “এদের মধ্যে কে গীতার ঠাকুমা, বলতে পার?” রাজুল উপস্থিত একমাত্র বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বলেছে, “এই গীতার ঠাকুমা”। কারণ রাজুলের চোখে—ঠাকুমা ও বৃদ্ধা সমার্থক শব্দের মত হয়ে গেছে। ফলে বৃদ্ধাকে ঠাকুমা বলে চিহ্নিত করবে, এটাই স্বাভাবিক।
এটা কোনওভাবেই সঠিক সনাক্তকরণের দৃষ্টান্ত নয়। সঠিক সনাক্তকরণ বলা যেতে পারত তখন, যখন সমবয়স্ক বৃদ্ধাদের সঙ্গে ঠাকুমা হাজির, এবং রাজুল তাকে ঠাকুমা বলেই চিনিয়ে দিচ্ছে। সঠিক সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার ধরন অবশ্যই খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। কারণ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েও যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তাকে চালিত করা যায়, তাকে সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করা যায়। প্রশ্নের মধ্যে এমন কোনও ইঙ্গিত থাকলে সনাক্তকরণ’ আর নিরপেক্ষ থাকে না। মূল্যহীন হয়ে পড়ে।
রাজুল যে পরিস্থিতিতে গীতার ঠাকুমাকে সনাক্ত করেছিল, তা কোনওভাবেই সঠিক সনাক্তকরণ ছিল না।
.
ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটিতে এরপরও ছাপার অক্ষরে লেখা আছে “পুনর্জন্মের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজুল গীতার জীবনের যা কিছু উল্লেখ করেছে তার সবকটিই অভ্রান্ত সত্য এবং বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে তার একশভাগ মিল ছিল।”
প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জগতে এমন নিটোল একশভাগ মিথ্যাচারিতার দৃষ্টান্ত খুব বেশি একটা দেখেছেন কি?
এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজুলের কথার সঙ্গে রাজুলের পূর্বজীবনের যে সব আশ্চর্য (!) মিল খুঁজে পেয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থটিতে যেসব কথা মুদ্রিত হয়নি, অথচ সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে যার উল্লেখ থাকা একান্তই জরুরি ছিল, সেগুলোর দিকে আমরা এ’বার নজর দেব।
রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
১. গীতার বাবা দেওয়ালি উপলক্ষে বাড়ির বাইরেটা লাল রঙ করেছিল। যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজুশাহ, ২. গোকুলদাস।
আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
গীতার জীবনকালে কোনও সময়ের জন্যেই বাড়ির বাইরে বা ভিতরে লাল রঙ করা হয়নি।
রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
২. লাল রঙ করার আগে বাড়ির রঙ ছিল সবুজ।
যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস।
আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
গীতার জীবনকালে কখনই বাড়ির বাইরের রঙ সবুজ ছিল না। রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
৩. গীতারা থাকত একতলায়।
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস, ৩. কান্থাবেন। আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
গীতা তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়েছে তিনতলার ফ্ল্যাটে।
এই ভুলকে কিভাবে ঢাকা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন আয়েন স্টিভেনসন, একটু দেখুন। স্টিভেনসন বলছেন, “The error is a natural one for a small girl who played much of the time in the downstairs area, returning to the family apartment mainly to eat and sleep.”
অর্থাৎ একটা ছোট মেয়ের পক্ষে এ ধরনের ভুল করাটা স্বাভাবিক, কারণ সারা দিনের বেশির ভাগ সময়ই ও একতলায় খেলত। সাধারণত নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরত খেতে ও ঘুমোতে।
অতএব ‘সাত খুন মাপ’। রাজুল মুখে ভুল বললেও আসলে ঠিকই বলেছিল।
প্যারাসাইকোলজিস্টদের এমনি সব কুযুক্তির হেলায় একশভাগ ভুলও একশভাগ ঠিক হয়ে যায়।
রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
৪. উনুনে রান্না হতো। দুধ গরম হতো।
যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. কান্থাবেন থ্যাকার।
আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
রান্না ও দুধ গরম হতো স্টোভে। এখানেও স্টিভেনসনের মত প্যারাসাইকোলজিস্টদের অদ্ভুত যুক্তি—এতটুকু মেয়ে কি উনুন ও স্টোভের পার্থক্য বোঝে? অতএব এ’ক্ষেত্রেও রাজুলের বক্তব্য একশভাগ ঠিক।
ভারি বিচিত্র ওঁদের একশভাগের হিসেব!
রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
৫. গীতার মায়ের নাম ‘শান্তা’ অথবা ‘কান্থা’।
যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. সুশীলাবেন শাহ (হিম্মৎলালের স্ত্রী), ৩. কান্থাবেন। আমি কি পেয়েছি ও মন্তব্য
ক. ভজু শাহ’র কথামত, রাজুল জানিয়েছিল ওর আগের জন্মের মায়ের নাম ছিল ‘কান্থা’।
খ. সুশীলাবেনের কথা মত, রাজুল জানিয়েছিল ওর আগের জন্মের মায়ের নাম ছিল ‘শান্তা’।
গ. গীতার মায়ের নাম ‘কান্থাবেন’।
ঘ. ভজু শাহ এ’কথায় স্বীকার করেছিলেন, হ্যাঁ, রাজুল অবশ্য মাঝে-মধ্যেই গীতার মায়ের নাম ‘শান্তা’ বলত।
ঙ. সুশীলাবেন জানিয়েছিলেন, না, তাঁর কাছে রাজুল গীতার মায়ের নাম ‘শান্তা’ ছাড়া আর কোনও নাম কখনও বলেনি।
অর্থাৎ, রাজুল গীতার মায়ের নাম ঠিক বলেছিল, কি ভুল বলেছিল- এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে প্রিয় পাঠক- পাঠিকাদের একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই—রাজুল কিন্তু কখনই ওর গত জন্মের বাবার নাম বলতে পারেনি।
রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
৬. রাজুলের বাবা ছিলেন গীতার বাবার বয়সী।
কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. সুধাবেন দেশাই (ভজু শাহর মেয়ে), ২. ভজু শাহ, ৩. গোকুলদাস, ৪. রাজুল। আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য
ক. রাজুল এ’কথা বলেছিল ওর পিসি সুধাবেনকে। সুধাবেনের কাছ থেকে ভজু শাহ এই তথ্য জেনেছিলেন।
খ. রাজুলের বাবার জন্ম সাল ১৯৩২, গীতার বাবার জন্ম সাল ১৯২৭। গ. দুজনের বয়সের পার্থক্য ৫ বছর।
রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
৭. গীতার বাবার মিষ্টির দোকান ছিল।
যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. গোকুলদাস, ৩. রাজুল। আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য গীতার বাবার কোনও দিনই মিষ্টির দোকান ছিল না। রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
৮. গীতার একটি ছোট ভাই ছিল।
যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. কান্থাবেন, ৩. গোকুলদাস, ৪. রাজুল। আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য
গীতার কোনও ছোট ভাই ছিল না।
রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
৯. গীতার প্রিয় বন্ধুর নাম জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না থাকত গীতাদের বাড়ির কাছেই। যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. হিম্মৎলাল শাহ, ৩. রাজুল, ৪. গোকুলদাস, ৫. কান্থাবেন,
৬. নির্মলা (গীতার দিদি)
আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য
গীতার মা, বাবা ও দিদি তিনজনই জানিয়েছিলেন ওরা গীতার খেলার যতজন সঙ্গীদের চেনেন, তাদের মধ্যে ‘জ্যোৎস্না’ নামের কেউ ছিল না।
নির্মলা এ’কথাও বলেছে, “বোনের সঙ্গী সক্কলকেই চিনতাম। ওর প্রিয় সঙ্গী, অথচ চিনতাম না—এমনটা হতেই পারে না।”
রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
১০. গীতার মা ‘প্যাড়া’ (ক্ষীরের সন্দেশ) বানাতেন।
যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. কান্থাবেন, ৩. রাজুল।
আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য
গীতার মা কান্থাবেন কখনই প্যাড়া বানাতেন না। প্যাড়া খাওয়ার ইচ্ছে হলে দোকান থেকে কিনে আনতেন।
গুজরাটে প্যাড়া জনপ্রিয় মিষ্টি। অনেক বাড়ির মহিলারাও বাড়িতেই প্যাড়া তৈরি করেন। রাজুল ওর মা প্রভাবেনকেও প্যাড়া বানাতে দেখেছে। রাজুল পূর্বজন্ম বিষয়ে ভজু শাহ পরিবারকে যা বলেছিল
১১. গীতাদের বাড়ির পুজোয় ঠাকুরকে খেতে দেওয়া হতো প্যাড়া। যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি
১. ভজু শাহ, ২. কান্থাবেন, ৩. নির্মলা।
আমি যা পেয়েছি ও মন্তব্য
বাড়ির পুজোয় ফল দেওয়া হতো, প্যাড়া নয়।
সত্যানুসন্ধানের স্বার্থে স্বীকার করছি রাজুলের পূর্বজীবন বিষয়ে কিছু কথা গীতার জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। কোন্ কোন্ কথাগুলো মিলে গিয়েছিল একটু দেখা যাক।
এক : গীতা ছোটবেলাতেই মারা যায়।
দুই : বাবা বেশিরভাগ সময় ধুতি পরত। (গুজরাটের হিন্দুদের বেশিরভাগই ধুতি পরেন। রাজুলও তেমনটাই দেখে এসেছে। ফলে রাজুলের পক্ষে এমনটা বলাই স্বাভাবিক।)
তিন : গোকুলদাস স্টিলের বাসনে খেতেন।
চার : গীতারা রাতের খাবার খেত রাতে। (রাজুলের খেলার সঙ্গীদের অনেকেই ছিল হিন্দু। তারা রাতের খাবার রাতে খায়, এটা রাজুলের যে অজানা ছিল না, সে কথা রাজুল নিজেই বলেছে।)
পাঁচ : গীতাদের বাড়ির ঠাকুরের গায়ে থাকত পোশাক।
(রাজুলরা জৈন, দিগম্বর সম্প্রদায়ের। রাজুল যেমনভাবে জানত ওদের ধর্মের ঠাকুরের শরীরে পোশাক থাকে না, তেমনভাবেই জানত, ওর হিন্দু বন্ধুদের ঠাকুর পোশাক পরে। রাজুল বলতে চেয়েছিল, ও গত জন্মে হিন্দু পরিবারে জন্মেছিল। তাই গীতার ঠাকুর পোশাক পরেছিল—রাজুলের বর্ণনায়।)
প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই কথাগুলোই বা কি করে মিললো? আসলে, এ’সব মিলিয়ে দেওয়া খুবই সোজা। ধরুন, আপনি বললেন-
১. গতজন্মে আমার নাম ছিল গোপাল।
২. জন্মেছিলাম কলকাতায়।
৩. মারা যাই শৈশবে।
৪. আমার বাবা ছিল।
৫. আমার মা ছিল।
৬. আমার কাকা ছিল।
৭. আমার মামা ছিল।
৮. বাবা প্যান্ট-সার্ট পরতেন।
৯. ঘরে পরতেন পাজামা অথবা লুঙ্গি।
১০. বাবা দাড়ি কামাতেন।
১১. বাবা বাজার থেকে আলু, তরকারি এ’সব নিয়ে আসতেন।
১২. বাবার উচ্চতা ছিল মাঝারি।
১৩. বাবা মাঝে-মাঝে পেটের গোলমালে ভুগতেন।
১৪. বাবা আমাকে বকতেন।
১৫. বাবা আমাকে আদর করতেন।
১৬. মা রান্না করতেন।
১৭.. মা খেতেন আমাদের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর।
১৮. আমরা ভাত খেতাম।
১৯. মাঝে-মাঝে রুটি খেতাম।
২০. আমি মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি।
২১. মা-বাবার সঙ্গে দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখেছি।
২২. আমাদের পাড়ায় দুর্গাপুজো হতো।
২৩. আমার মা গয়না পরতেন।
২৪. মা সিঁদুরের টিপ দিতেন।
২৫. বাবা মাঝে-মাঝে মাকে বকতেন।
২৬. মামা-মাসিরা বেড়াতে এলে মা’র খুব আনন্দ হতো।
২৭. আমি সেলুনে চুল ছাঁটতাম।
২৮. আমি স্কুলে পড়েছি।
২৯. আমার বই খাতা ছিল।
৩০. আমার নীল রঙের একটা সার্ট ছিল।
আপনার এই তিরিশটা মন্তব্য মিলে যাওয়া একগাদা গোপাল আপনি পেয়ে যাবেন। ধরুন আপনার বয়স এখন তিরিশ। একত্রিশ বছর আগে থেকে ঘাঁটতে থাকুন কলকাতা কর্পোরেশনের মৃত্যু নিবন্ধিকরণের খাতা। এক বছরের পাতা ওল্টালেই বহু গোপালের মৃত্যুর হদিস পেয়ে যাবেন। পাঁচ-দশ বছরের খাতা ঘাঁটলে এত গোপালের মৃত্যু দেখতে পাবেন যে তখন বলতে ইচ্ছে হবে ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি’। এ’বার ওইসব গোপালদের ঠিকানা নিয়ে তিরিশ দফা মন্তব্য মেলাতে শুরু করুন। তাতেও পেয়ে যাবেন বহু গোপাল।
আপনি গোপাল ছেড়ে নিজেকে আগের জন্মের ফতেমা ঘোষণা করুন, তাতেও অসুবিধে নেই। বলতে শুরু করুন—
১. আমি কলকাতায় থাকতাম।
২. অল্প বয়সে মারা যাই।
৩. আমার বাবা ছিল। ৪. আমার মা ছিল।
৫. আমার বাবার দু’বিয়ে।
৬. আমার ভাই-বোন ছিল।
৭. আমার মা শাড়ি পরতেন।
৮. বেড়াতে গেলে শাড়ির ওপর বোরখা পরতেন।
৯. মা’র কালো রঙের বোরখা ছিল।
১০. আমি বোরখা পরতাম না।
১১. আমি সালোয়ার-কামিজ পরতাম।
১২. আমার কালো রঙের জরি বসানো সালোয়ার-কামিজ ছিল।
১৩. আমার সুন্দর রঙিন চটি ছিল।
১৪. বাবা লুঙ্গি পরতেন।
১৫. বাবা সার্ট ও পাঞ্জাবি দুইই পরতেন।
১৬. বিশেষ বিশেষ দিনে বাবা টুপি পরতেন।
১৭. আমাদের বাড়ি আতর আসত।
১৮. আমাদের বাড়ি সুর্মা আসত।
১৯. আমরা ভাত ও রুটি দুই খেতাম।
২০. মা রান্না করতেন।
২১. মা মাঝে-মাঝে মাংস রাঁধতেন।
২২. আমি বিরিয়ানি খেয়েছি।
২৩. আমার কাকা ছিল।
২৪. আমার বই ছিল।
২৫. আমার খাতা ছিল।
এমনি আরো অনেক কিছুই সামান্য মাথা খাটিয়ে গড়গড় করে বলে যেতে পারেন। একজন প্যারাসাইকোলজিস্ট পাকড়ে যদি তাঁকে এ’সব কথা শোনাতে পারেন, তাহলে একগাদা ফতেমার খোঁজে আপনাকে আর দৌড়ো-দৌড়ি করতে হবে না। বরং এত ফতেমা নিয়ে পাগল হবার যোগাড় হবেন সেই প্যারাসাইকোলজিস্ট। অবশ্য যদি তিনি শিক্ষানবিশ হন, তবেই। পাকা মাথা হলে এক ফতেমার খোঁজ পেতেই প্রচার-মাধ্যমগুলো তোলপাড় করে ছাড়বেন। কোন তথ্য হাজির করবেন, কোনটা চেপে যাবেন, এ’সব করেই তো মাথা পেকেছে। তারপর এ’গুলো খাওয়াবেন প্রচার-মাধ্যমগুলোকে। আর এ’ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি প্রচার মাধ্যমেরই অবস্থা, “এই কাঙাল, তুই ভাত খাবি?” “নুন নিয়ে তো বসেই আছি।”
আসুন, এবার ‘রাজুল’ নাটকে যবনিকা ফেলার আগে জরুরি আর দু’একটি তথ্য আমরা জেনে নেই।
রাজুলের জন্ম ১৯৬০-এ আগস্টে। রাজুলের বাবা ১৯৬০-এর ডিসেম্বর থেকে থাকতে শুরু করেন ‘কেশর’-এ। ঠাকুরদা থাকতেন ‘ওয়াঙ্কানের’-এ। রাজুল থেকেছে কেশর ও ওয়াঙ্কানের-এ। দুটি স্থানই গীতার শহর জুনাগড়ের কাছেই। জুনাগড় থেকে কেশরের দূরত্ব মাত্র ৩০ কিলোমিটারের পথ। আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে এক শহর থেকে আর এক শহরে যেতে। ওয়াঙ্কানেরও জুনাগড়ের কাছেরই এক শহর। এই তিন শহরের লোকজনদের মধ্যে যাতায়াত আছে, আত্মীয়তা আছে, পরিচিতি আছে। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি—আছে। রাজুল ওর বন্ধু বা অন্য কারও কাছ থেকে গীতার বিষয়ে কিছু কিছু কথা শুনে থাকতে পারে। এটা সম্ভব। তারপর শিশু রাজুল তার আবেগ ও কল্পনার সাহায্যে একসময় নিজের অজান্তে নিজেকে পূর্বজন্মের ‘গীতা’ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। সেই বিশ্বাস থেকে উৎসারিত কথার কিছু কিছু মিলে যেতেই কেউ কেউ আবেগতাড়িত হয়েছেন, উত্তেজিত হয়েছেন। আঁকড়ে ধরা প্রাচীন বিশ্বাসকে সত্যি হয়ে উঠতে দেখার উত্তেজনা।
অতি আবেগের স্রোতে অনেক সময়ই যুক্তি ভেসে যায়। এখানেও অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটেছে। তাঁরা ‘না মেলা’ বিষয়ে অনেক সময়ই সচেতন বা অচেতভাবে নীরব থেকেছেন। সোচ্চার হয়েছেন ‘হ্যাঁ মেলা’ নিয়ে। রাজুলকে ‘গীতা’ বলে চালিয়ে দিয়ে ভজু শাহ পরিবারের কোনও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা ছিল না। কারণ রাজুলদের পরিবার গীতাদের পরিবারের তুলনায় বিত্তবান। গীতারা নেহাতই মধ্যবিত্ত।
সমস্ত দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার পর একথা বলতে পারি—রাজুলের জাতিস্মর হয়ে ওঠার পিছনে কোনও প্রতারণার ষড়যন্ত্র ছিল না, ছিল রাজুলের মানসিক অবস্থা।
