৫. সামাজিক জীবনের প্রবাহ
বর্তমান থেকে অতীতের দিকে যখন আমরা ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় মানুষের জীবন অনেকটা বহতা নদীর মতো। জীবনের এই প্রবাহ পরিবর্তনশীল, কিন্তু সমাজের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর দিক থেকে বিচার করলে এই পরিবর্তনের গতি মন্থর। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আমূল পরিবর্তন মানবসমাজে হয় না। যে—কোনও যুগে যে—কোনও সময় যদি সমাজে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক—জীবন ও নানা রকমের গোষ্ঠীজীবনের ধারা লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে সম্পূর্ণ নতুন বা সম্পূর্ণ পুরানো ধারা বলে কিছু নেই, নতুন—পুরানো একসঙ্গে মিলেমিশে আছে। চিন্তাধারায় হোক, ধর্মাচরণে হোক, পারিবারিক ও সামাজিক প্রথা—রীতি—নীতির আবর্তনে হোক, নতুনের সঙ্গে পুরানো মন ও আচরণ সব সময় মিলেমিশে থাকে। সামাজিক জীবনে, কোনও সময় এমন কোনও ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, যেখানে দেখা যায় পুরানো ধারা সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে এবং নতুন ধারা পরিপূর্ণরূপে শুরু হয়েছে। জীবনের বহুমুখী ধারা কখন কোনটি কোথায় শেষ হয় এবং কোথায় শুরু হয় তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না।
সামাজিক ইতিহাসবিদ ট্রেভেলিয়ান তাঁর English Social History গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন : “In everything the old overlaps the new–in religion, in thought, in family custom. There is never any clear cut; there is no single moment when all Englishmen adopt new ways of life and thought.” ইংরেজদের ক্ষেত্রে যা সত্য, বাঙালিদের ক্ষেত্রেও তা সত্য, অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও তা মিথ্যা হবার কথা নয়। ইতিহাসের গতিপথে এমন কোনও একটি মুহূর্তও খুঁজে পাওয়া যায় না—কোনও শতাব্দীতেই না—যখন দেখা যায় বাংলা দেশে প্রত্যেক বাঙালি একই চিন্তাভাবনা ও একই জীবনধারার পথিক ছিল। সমাজের গতির যখন এই বিশেষত্ব তখন তার একশো বছরের ইতিবৃত্ত নির্বাচিত ও শ্রেণিবদ্ধ বিষয়ে ভাগ—ভাগ করে বিচার করলে তার মধ্যে জীবনের সমগ্রতা ও অখণ্ডতা যথাযথ প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। বহমান ঘটনার আবর্তে জীবনের পরিবর্তনশীল দৃশ্য যেমনভাবে উদঘাটিত হয়—“by a series of scenes divided by intervals of time” (Trevelyan)—কতকটা তেমনিভাবেই তার বর্ণনা করতে হয়।
কালের যাত্রায় যতিচিহ্ন যেখানে খুশি টানা যায় না। যেমন ১৮০০ থেকে ১৮২৫, তারপর থেকে ১৮৫০, অথবা এই ধরনের পর্বভাগ ইতিহাসের ধারাবিচারে অনাবশ্যক মনে হয়। যদিও সমাজের গতিপথে ঐতিহাসিক তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে (ট্রেভেলিয়ান যে অর্থে ঐতিহাসিককে ‘Dry as dust at bottom is a poet’ বলেছেন) এই যতিচিহ্ন লক্ষ করতে পারেন, তাহলেও তা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সংগত বলে মনে হয় না। তথাপি এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে জীবনের স্রোত একটানা বা মন্দাক্রান্তা নয়, তার জোয়ারভাঁটা আছে, ঢেউ আছে, ছোট—বড় ঢেউ—ঘূর্ণি আছে, বাঁক আছে, তীর—ভাঙা বিক্ষোভ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, আবার একটানা কলতানও আছে। যতিচিহ্ন এই গতিধারা ইঙ্গিত করে টানা যায়, কিন্তু একেবারে সঠিকভাবে টানা যায় কি না সন্দেহ।
১৮০০—২৯
আঠারো শতকে কলকাতার নব্য—অভিজাতদের কালে তো বটেই, উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও—যখন নবযুগের পথিক রামমোহনের কাল প্রায় আরম্ভ হয়েছে বলা চলে—কলকাতা শহরের রাস্তায় হাতি চলে বেড়াত। হাতি মধ্যযুগের স্থূল ও স্থবির প্রতিমূর্তি। আঠারো শতক থেকে কলকাতা শহরের রাস্তায় যখন যাত্রীবাহী ঘোড়ার গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, খোয়া—ভাঙা রাস্তায় চলন্ত ঘোড়ার চক্রযানের ঘর্ঘর শব্দে যখন কলকাতায় মানুষের ঘুম ভাঙতে আরম্ভ করল, তখন মনে হল মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙার রাত শেষ হয়ে নতুন দিনের ভোর হচ্ছে—একটি পুরানো যুগ অস্ত যাচ্ছে, আর—একটি নতুন যুগের অভ্যুদয় হচ্ছে। “If the fowls no longer cackled at dawn, the restless stomp of a highbred horse might be heard at night from rear windows : The man on horseback had taken possession of the city.” (Lewis Mumford)১ নতুন যুগের ঘোড়সওয়াররা নতুন শহর দখল করেছে। তাদের জীবন আলাদা, মন আলাদা, আগেকার যুগের জীবন ও মনের সঙ্গে অনেক জায়গায় মিল নেই—
And this is a city
In name but in deed
It is a pack of people
That seek after meed [gain]
For officers and all
Do seek their own gain
But for the wealth of the Commons
Not one taketh pain.
And hell without order
I may it well call
Where every man is for himself
And no man for all.২
(Robert Crowley)
‘প্রত্যেক মানুষ নিজের জন্য, পরের জন্য নয়’—এই হল আধুনিক শহরের মানুষ। কলকাতা সেই আধুনিক শহর।
উনিশ শতকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে ইতিহাসের মঞ্চে কয়েকটি দৃশ্য দেখা যায়। ১৮০০ সালে ‘ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ’ স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুরে ‘ব্যাপটিস্ট মিশন’—এর প্রতিষ্ঠা হয়, সম্ভবত ডেভিড হেয়ার কলকাতা শহরে ঘড়ির ব্যাবসা করতে আসেন। রামমোহন রায় কলকাতা শহরে আসা—যাওয়া করতে আরম্ভ করেন। ১৮০২ সালে (২০ আগস্ট) সাগরদ্বীপে সমুদ্রের জলে দেবতার উদ্দেশে হিন্দুদের সন্তান উৎসর্গ করার নিষ্ঠুর প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়।৩ রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার গ্রাস’ কাহিনিকাব্যের মর্মান্তিক দৃশ্য যখন সাগরতীর্থে অনুষ্ঠিত হত, তখন (১৮০১ সাল) বার্টলেট নামে একজন ব্রাঞ্চ—পাইলট অন্যান্য ইউরোপীয় বন্ধুর সঙ্গে এই দৃশ্য দেখতে গিয়ে একটি ছেলেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ন্যাসী—ফকিরদের চক্রান্তে ব্যর্থ হন।৪ সনাতন সামাজিক প্রথায় এ দেশে ব্রিটিশ শাসকরা প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত করেন সাগরদ্বীপে হিন্দুদের সন্তান উৎসর্গ আইনত নিষিদ্ধ করে। যত দূর জানা যায়, বিদেশি শাসকের এই নিষেধাজ্ঞার জন্য তখন হিন্দুসমাজে বিশেষ কোনও আন্দোলন বা প্রতিবাদের কলরব শোনা যায়নি। যদি কোনও প্রতিবাদ হয়েও থাকে, তাহলেও তার নির্জন ক্ষীণকণ্ঠের কোনও প্রতিধ্বনি শোনা যায়নি। অথচ ১৮২৯—৩০ সালে যখন একই রকমের নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা ‘সতীদাহ’ আইনত নিষিদ্ধ করা হয়, তখন ধর্মগোঁড়ামির উগ্রমূর্তি সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করে।
উনিশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতা শহরে গোলাম—পোষণ, গোলাম—নির্যাতন ও গোলাম—ব্যাবসা পুরোদমে চলত। ১৭৮৫ সালে উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় গোলামের ব্যাবসা সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের একটি মামলার রায় প্রসঙ্গে বলেন : ”গোলামদের দুরবস্থার কথা যা আমি জানি তা এত নিষ্ঠুর ও বর্বর যে বলতেও আমার সংকোচ হয়। প্রতিদিন বহু গোলাম—নির্যাতনের কাহিনি আমার কানে পৌঁছোয়। এই জনবহুল কলকাতা শহরে এমন অবস্থাপন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোক খুব কমই আছেন যাঁর অন্তত একটি বালক বা বালিকা গোলাম নেই। কলকাতা শহর সম্প্রতি গোলাম কেনা—বেচার একটি বড় আড়ত হয়ে উঠেছে।” আঠারো শতকের শেষদিকে জোন্স এই কথা বলেন। ১৭৯৩ সালে কোম্পানির ডিরেক্টররা বাংলা দেশের বাইরে গোলাম—রপ্তানি বন্ধ করার জন্য একটি আদেশ জারি করেন। তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশে, এবং কলকাতা শহরে, গোলাম কেনা—বেচা নির্বিবাদে চলতে থাকে।
গোলামির প্রতি ইংরেজদের মনোভাব ইংলন্ডেই বদলাতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের গোড়া থেকে, শিল্পবিপ্লবের পর। ১৮০৭ সালে ইংলন্ডে গোলামের ব্যাবসা আইনত নিষিদ্ধ করা হয়। বর্বর গোলামিপ্রথার বিরুদ্ধে মানুষের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত করার জন্য যাঁরা ইংলন্ডে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় পুরুষ হলেন উইলবারফোর্স (Wilberforce)। কিন্তু ইংলন্ডেও গোলামিপ্রথা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়। প্রায় পঁচিশ—ছাব্বিশ বছর আন্দোলনের পর ফাউয়েল বাক্সটন (Fowell Buxton) প্রমুখ সমাজনেতাদের আন্দোলনের ফলে, ১৮৩৩ সালে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে গোলামিপ্রথা আইনত বিলুপ্ত হয়। এই বছরে উইলবারফোর্স মারা যান। উইলবারফোর্সের মানবমর্যাদার আন্দোলন, ট্রেভেলিয়ান বলেছেন, ইংলন্ডের শহর—নগর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিশাল মধ্যবিত্তশ্রেণির মনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার ফলে ইংরেজ জাতির মধ্যে যেন এক নবচেতনার উদবোধন হয়—“English of the best, and something new in the world.”৫
উনিশ শতকের প্রথমদিকে ইংলন্ডের মতো বাংলা দেশে শিল্পবিপ্লবোত্তর সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি, নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ হয়নি তেমন, এবং স্বভাবতই তাই উইলবারফোর্সের মতো সমাজনেতারও আবির্ভাব হয়নি। গোলামিপ্রথা বাংলার সামাজিক জীবন কলঙ্কিত করেছে বহুদিন। ১৮২৭ সালে আঠারো বছর বয়সে ইংরেজ কবি ক্যাম্পবেলের উক্তি “And as the Slave departs, the Man returns.” উদ্ধৃত করে ডিরোজিও এ দেশের গোলামদের মুক্তি চিন্তা করে লেখেন :৬
How felt he when he first was told
A slave he ceased to be;
How proudly beat his heart, when first
He knew that he was free!
অথচ এর মধ্যে রামমোহন রায় প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে, স্থায়ীভাবে কলকাতা শহরে বসবাসের সিদ্ধান্ত করেন (১৮১৪), ‘আত্মীয় সভা’ স্থাপন করেন (১৮১৫), কলকাতা শহরে পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান ‘হিন্দু কলেজ’ স্থাপিত হয় (১৮১৭), সতীদাহ—সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রচারকার্য শুরু করেন (১৮১৮—১৯), ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররা সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র তর্কবিতর্ক আরম্ভ করেন (১৮২৭—২৮), ‘ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮২৮) এবং সতীদাহ—নিবারণ আইনও বিধিবদ্ধ হয় (১৮২৯)। কিন্তু গোলামির বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন বা আইন কিছু হয়নি। অপরাধের মধ্যযুগীয় বিচার ও দণ্ডদান, এমনকী ফাঁসি পর্যন্ত, কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথেই চলেছে। ইতিহাসের এই বিচিত্রমুখী ধারা দেখে বাস্তবিকই বিভ্রান্ত হতে হয় এবং ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় বলতে হয় : ৭ “The pattern of history is indeed a tangled web. No simple diagram will explain its infinite complication.” ইতিহাসের এই কুটিল গতি শুধু আমাদের দেশে নয়, ইংলন্ড বা অন্যান্য দেশেরও বিশেষত্ব। ট্রেভেলিয়ানও তাই প্রশ্ন করেছেন, মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতির শেষ কোথায় বলে আমরা ঠিক করব—চোদ্দো, ষোলো না আঠারো শতকে? ইংরেজ জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গেই তাঁকে এই প্রশ্ন করতে হয়েছে। নিজেই এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন : “Perhaps it matters little; what does matter is that we should understand what really happened.”৮ রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের সময় থেকে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে, না শিল্পবিপ্লবের পর থেকে? আসল কথা, মানুষের সামাজিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় বটে, কিন্তু অত্যন্ত ধীরে ধীরে বদলায়, এবং সর্বকালে একই গতিতে বদলায় না। আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় দু—হাজার বছরের পরিবর্তনের এই গতি উনিশ শতকের একশো বছরের গতির তুলনায় অনেক মন্থর। আবার বিশ শতকে গত পঁচিশ—তিরিশ বছরের পরিবর্তনের গতি আগেকার তুলনায় অনেকগুণ বেশি দ্রুত। বাস্তব জীবনের পরিবর্তনের উপর মানসিক জীবনের পরিবর্তন অনেকাংশে নির্ভরশীল বলে, ইতিহাসে সর্বকালে, এক—একটি শতাব্দীর মধ্যেও, পরিবর্তনের গতির তারতম্য ঘটে, এবং পরস্পরবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ হয় সমাজে। বাংলা দেশে উনিশ শতকেও তা—ই হয়েছিল।
উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ‘ক্যালকাটা গেজেট’ ও অন্যান্য পত্রিকায় কলকাতার বউবাজার—লালবাজার অঞ্চলে প্রচুর ট্যাভার্ন—কফি হাউসের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। হারমনিক, ক্রাউন অ্যান্ড অ্যাঙ্কর, ব্রিটিশ কফি হাউস—এইরকম সব নাম। এই ট্যাভার্ন ও কফি হাউসগুলি আমাদের স্বদেশি সমাজের স্বাভাবিক দৃশ্য নয়, আঠারো শতকের জনসনের ইংলন্ডের সামাজিক দৃশ্যের একটা প্রতিচ্ছবি মাত্র, লন্ডনের বদলে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে।৯ সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন : “The Coffee-houses became the first centres of opinion in a partially democratized society.”১০ কলকাতার নগরকেন্দ্রিক বাঙালি সমাজে যদিও গণতন্ত্রের বহু দূর পদধ্বনি উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই শোনা যাচ্ছিল—ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং খানিকটা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে—তাহলেও লালবাজার বউবাজারের ট্যাভার্ন—কফি হাউসের মধ্যে তার কোনও প্রতিশব্দই শোনা যায়নি। লক্ষণীয় হল, এইসব ট্যাভার্ন—কফি হাউসের সঙ্গে এ দেশের লোকের কোনও সম্পর্কই ছিল না। এমনকী হারমোনিকের মতো অভিজাত ট্যাভার্নের কোনও সম্ভ্রান্ত বাঙালি, যাঁরা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে খানাপিনা—উৎসবে যথেষ্ট মেলামেশা করতেন, তাঁরাও যাতায়াত করতেন না। সম্ভ্রান্ত বাঙালিরা মেলামেশা করতেন শহরের বাবুদের বৈঠকখানায়, আখড়াই—কবিগানের আসরে, অথবা বটতলায় নিধুবাবুর টপ্পাগানের মজলিশে। ”শোভাবাজার বটতলার পশ্চিমাংশে বড় একখানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল। নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সংগীত বিষয়ের আমোদ করিতেন, ঐ স্থানে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত শৌখিন, ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সঙ্গীত স্বরে মুগ্ধ হইতেন।”১১
১৮৫১ সালে রামমোহন রায় ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ প্রকাশ করেন। তারও আগে অবশ্য (১৮০৩—০৪ সালে) তিনি ‘তুহফাৎ—উল—মুয়াহ হিদীন’ গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যতে পৌত্তলিকতা—বিরোধী ধর্মমতের বীজটি ছিল দেখা যায়। পরে ১৮৮৪ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মৌলবি ওবেদুল্লা “A Gift to Deists’ নামে এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। কলকাতায় আসার অল্পদিন পরেই তাঁর ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ প্রকাশিত হয় (১৮৫১)। তখন বাংলাদেশে বেদ—উপনিষদের অনুশীলন এরকম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। রামমোহন নতুন করে শুধু যে বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন তা নয়, বাংলা ভাষায় তিনি বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার এবং জনসমাজে প্রচারক। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লেখেন : ”অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বন্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রবন্ধে এবং পূর্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলতে অনেক অনেক সুবোধ লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথা সাধ্য প্রকাশ করিলেক।”১২ এই গ্রন্থ প্রকাশের কী উদ্দেশ্য ছিল তা এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। পশুপক্ষী, মৃত্তিকা—পাষাণ প্রভৃতি বস্তুকে অনেকে উপাস্য দেবতা মনে করেন, তাঁরা দেবতার স্বরূপ কী তা জানেন না। সাধারণ লোকের মধ্যে বেদান্তের প্রচার হয়নি বলে ”স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের” বাক্যে এবং নিজেদের পূর্বসংস্কারের জন্য এরকম ধর্মবিশ্বাসের প্রসার হয়েছে সমাজে। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ কী এবং বেদান্তে তা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা যাতে সাধারণ লোক নিজেরা পাঠ করে বিচার করতে পারেন, তার জন্যই তিনি বেদান্ত বাংলা ভাষায় প্রচার করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কুক্ষিগত শাস্ত্রকে রামমোহন বাঙালি সাধারণের কাছে মুক্ত করে দেন। মুদ্রণশিল্প (Printing) প্রতিষ্ঠা এ দেশে না হলে এই মুক্তিদান অবশ্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বা পুঁথি জনসমাজে প্রচার করা যায় না। শুধু সংস্কৃত পুঁথি মুদ্রিত হলেও জনসমাজে তার প্রচার হত না। মাতৃভাষা বাংলায় সংস্কৃত শাস্ত্র প্রচার করে রামমোহন সেই দুরতিক্রম্য বাধাও অপসারণ করেছিলেন। মুদ্রণ ও মাতৃভাষা—এই দুটি অস্ত্রের সাহায্যে রামমোহন বাংলার জনসমাজে শাস্ত্রজ্ঞান প্রচারের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দূর করেন। আধুনিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে তাই মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রিকার দান অসামান্য। লুইস মামফোর্ড লিখেছেন :১৩
“More than any other device, the printed book released people from the domination of the immediate and the local. Doing so, it contributed further to the dissociation of medieval society.”
মামফোর্ড মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে যা বলেছেন, ‘ঘড়ি’ সম্বন্ধে সে কথা সত্য। মামফোর্ডের ভাষায় “The clock was the most influential of machines, mechanically as well as socially.” এবং আঠারো শতকের মধ্যভাগেই এই যান্ত্রিক ঘড়ির পরিপূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয়, সমাজে তার প্রচলনও হতে থাকে।১৪ উনিশ শতকের সূচনাতেই বাংলা দেশের সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুদায়িত্বপূর্ণ আধুনিক শিক্ষাব্রতীর ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি ঘড়ির ব্যবসায়ী হয়ে কলকাতা শহরে আসেন। তাঁর নাম ডেভিড হেয়ার। এটা একটা ‘strange coincidence’ বটে, কিন্তু ইতিহাসে এরকম আশ্চর্য ঘটনার মিলন অনেক সময়ে ঘটে।
১৮১৬ সালে রামমোহনের Translation of An Abridgment of the Vedant গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তার ভূমিকায় তিনি লেখেন :
“By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my realtions, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system.”
সামাজিক বাধা নয় শুধু, পারিবারিক নির্যাতন রামমোহনকে অনেক সহ্য করতে হয়, স্বাধীনভাবে তাঁর ধর্মমত মুদ্রিত গ্রন্থাকারে লোকসমাজে প্রচার করার জন্য। তাতে তিনি বিচলিত হননি। ১৮১৫ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যে রামমোহন বাংলা ভাষায় প্রায় ২৯খানি, সংস্কৃতে ৩খানি এবং ইংরেজিতে প্রায় ৩৩খানি পুস্তক—পুস্তিকা প্রচার করেন।১৫ অর্থনীতি সমাজ ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে এই পুস্তক—পুস্তিকাগুলি তিনি রচনা করেন এবং তার ফলে বাংলার সামাজিক জীবনে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নের গণ্ডি শ্রেণিগতভাবে যতই সীমাবদ্ধ হোক—না কেন, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রামমোহনের রচনা ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে অনেকের রচনা পুস্তকাকারে এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং সামাজিক ও নানাবিধ বিষয়ে সাময়িকপত্রও সাধারণের মতামত গঠনে সাহায্য করে।
পুস্তক—পত্রিকার পাশাপাশি উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে বাংলাদেশে (প্রধানত কলকাতা শহরে) স্বাধীন মতামতের পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন সভাসমিতির (Associations, Societies) প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। নবযুগের সন্ধিক্ষণে “societies of this type became centres of reforming zeal as well as literary and philosophic illumination.”১৬ বাংলাদেশে বাঙালির উদযোগে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের সভাসমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ‘আত্মীয় সভা’ (১৮১৫)। প্রথমে ‘আত্মীয় সভা’র অধিবেশন হত রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে, পরে হত তাঁর সিমলার বাড়িতে। কেবল যে রামমোহনের গৃহে সভার অধিবেশন হত তা নয়, অন্যান্য সদস্যদের গৃহেও মধ্যে মধ্যে হত। প্রত্যেক অধিবেশনে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসংগীত হত এবং নানা রকমের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত। ১৮১৯ সালের ৯ মে বিবরণ থেকে সভার উদ্দেশ্য অনেকটা বোঝা যায়।১৭ সভার আলোচ্য বিষয় ছিল জাতিভেদ সমস্যা, বালবিধবাদের সমস্যা, বহুবিবাহ ও সতীদাহ বা সহমরণের সমস্যা। সমস্যাগুলি অধিকাংশই সামাজিক। আলোচিত সমস্যাগুলি নিয়ে দেখা যায় পরবর্তীকালে প্রায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশে বেশ বড় বড় সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে।
‘আত্মীয় সভা’র সভ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন রামমোহনের বন্ধু বা অনুরাগী। তাঁরা সকলেই প্রায় সম্ভ্রান্ত উচ্চসমাজের লোক ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, তেলিনিপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকির জমিদার কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রর পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, ভূকৈলাসের (খিদিরপুর) রাজা কালীশংকর ঘোষাল, জাস্টিস অনুকূলচন্দ্রর পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও আন্দুলের জমিদার রাজা কাশীনাথ। ইউরোপে আধুনিকযুগের প্রথম পর্বে দেখা যায়, প্রগতিশীল সামাজিক ভাবধারার মুখপাত্ররূপে নতুন ধনিক অভিজাতশ্রেণির সঙ্গে উদীয়মান বুদ্ধিজীবীশ্রেণির বিচিত্র মিলন হয়েছিল, বিত্ত ও বিদ্যার অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। বাংলাদেশেও আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে অভিজাতশ্রেণি ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণির মধ্যে এই ধরনের মিলনের পরিচয় পাওয়া যায় ‘আত্মীয় সভা’য়। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের প্রথম পর্বে ধনিকশ্রেণির সামাজিক—সাংস্কৃতিক ভূমিকা সম্বন্ধে ম্যানহাইম বলেছেন, “It is essential to note how with the rise of modern capitalism, the wealthy merchant and banking families play their part in cultural life.”১৮ ‘আত্মীয় সভা’র মধ্যে অবশ্য ধনিক ব্যবসায়ী ও ব্যাকিং পরিবারের লোক ছিলেন না, অধিকাংশ ছিলেন নতুন জমিদারশ্রেণির লোক। এই পার্থক্যের মধ্যে ইংলন্ডে ও আমাদের দেশের আর্থনীতিক—সামাজিক জীবনের মূল পার্থক্য প্রতিফলিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথম পর্বে আদৌ হয়নি, নতুন জমিদারিপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, এবং তার ফলে নতুন একশ্রেণির জমিদারের উদ্ভব হয়েছিল সমাজে। এই নতুন জমিদারের মধ্যে কেউ কেউ প্রগতিশীল ভাবধারার পোষকতা করতেন। রামমোহনের পার্শ্বচরদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশি।
‘গৌড়ীয় সমাজ’ স্থাপিত হয় ১৮২৩ সালে, উদ্দেশ্য ”এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন”। প্রাচীনপন্থী, মধ্যপন্থী ও আধুনিকপন্থী সকল শ্রেণির বাঙালির সমাবেশ হয় ‘গৌড়ীয় সমাজ’—এ। যেমন ‘আত্মীয় সভা’র দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য উদারপন্থী ব্যক্তিরা সমাজের সভ্য ছিলেন, তেমনি ছিলেন রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এবং অন্যান্য প্রাচীন ও নব্যপন্থীরা। ‘গৌড়ীয় সমাজ’—এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, সভ্যরা প্রধানত উচ্চ—অভিজাত শ্রেণিভুক্ত ছিলেন না, মধ্যবিত্তশ্রেণিরও অনেকে ‘সমাজ’—এ যোগ দিয়েছিলেন। ‘আত্মীয় সভা’র সভ্যদের মধ্যে মোটামুটি একটা মতৈক্যের বাঁধন ছিল, ‘গৌড়ীয় সমাজ’ তা ছিল না। সেখানে নানারকম মতামতের আদানপ্রদান হত, ব্যক্তিগতভাবে সভ্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে কোনও বাধা ছিল না।
১৮২৮—২৯ সালের মধ্যে আরও অনেক সভাসমিতি স্থাপিত হয়, অবশ্য প্রধানত ইংরেজদের উদযোগে। যেমন Literary Society, Oriental Literary Society, Phrenological Society, Agricultural and Horticultural Society, Commercial and Patriotic Association (রামমোহন রায় এই সভার ট্রেজারার ছিলেন), Ladies’ Society (বৈদ্যনাথ রায় ও কাশীনাথ মল্লিক এই সভা প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সহযোগী ছিলেন), Calcutta Medical and Physical Society ইত্যাদি। সমাজ সাহিত্য শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে যেমন ইংরেজরা তেমনি বাঙালিরা স্বাধীনভাবে মতামত বিনিময় করতে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন সভার আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায়, একশ্রেণির বাঙালিদের সামনে সামাজিক সমস্যাগুলি তখন বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছিল।
সামাজিক জীবনের ধারার মধ্যে তখন অবশ্য প্রাচীন গতানুগতিক ধারারই প্রাবল্য ছিল। উৎসব—পার্বণে, আমোদপ্রমোদে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বাঙালি সমাজের কোনও শ্রেণির মধ্যেই তেমন উল্লেখ্য পরিবর্তন কিছু হয়নি। গ্রাম্য সমাজে তো হয়ইনি, কলকাতার নতুন নাগরিক সমাজেও সাংস্কৃতিক উৎসবাদি কোনও বিশেষ রূপ ধারণ করেনি। গ্রাম্য উৎসবের ধারা গতানুগতিকই ছিল (যেমন শিব ও ধর্মঠাকুরের গাজন, মনসার ঝাঁপান এবং আরও নানা রকমের লোকোৎসব)। কলকাতার সমাজেও এই গ্রাম্য উৎসবের ধারা বেশ প্রবল ছিল। তার সঙ্গে নতুন নাগরিক চালচলন ও রুচির মিশ্রণে নতুন উৎসব—আমোদ—প্রমোদেরও বিকাশ হচ্ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কলিকাতা কমলালয়’ (১৮২৩) ও ‘নববাবুবিলাস’ (১৮২৫) নামে দুটি ব্যঙ্গরচনায় তখনকার বাঙালি সমাজের নকশাচিত্র এঁকেছেন। ‘কলিকাতা কমলালয়’—এ বিষয়ী বাঙালি ভদ্রলোকদের তিনটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হল যাঁরা বড় বড় কাজ করেন, ”অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম করিয়া থাকেন” এবং ”অপূর্ব পোশাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পালকি বা অপূর্ব শকটারোহণে কর্মস্থানে গমন করেন।” দ্বিতীয়টি হল মধ্যবিত্তরা, ”অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন” জীবনযাত্রা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির লোকের প্রায় একরকম, মধ্যবিত্তদের ”কেবল দানবৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।” তৃতীয়টি হল ”দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক”। এঁদেরও মধ্যবিত্ত বলা যায়, তবে নিম্নমধ্যবিত্ত। এঁদের জীবনযাত্রার মধ্যেও বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না, ”কেবল আহার ও দানাদি কর্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম করিয়া থাকেন।” ”অসাধারণ ভাগ্যবান” বলে আর—একশ্রেণির লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ”ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমিদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়।” বোঝা যায়, এঁরা হলেন শহরের নতুন বাঙালি অভিজাতশ্রেণি। ‘নববাবুবিলাস’—এ এই নব্য—অভিজাতদের সামাজিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ‘ইহারা অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিত পরিসেবিত।”
শহরের বাঙালি অভিজাতরা আমোদপ্রমোদ ও বিলাসিতায় অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। দুর্গোৎসবে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে পানভোজনের মজলিশে শহরের গণ্যমান্য ইংরেজরাও আমন্ত্রিত হতেন, তাঁদের জন্য বিশেষ নাচগান ও আতসবাজির ব্যবস্থা করা হত। নাচগানের মধ্যে হিন্দুস্থানি সুর ও ভঙ্গির সঙ্গে কিছু কিছু ইংরেজি সুর ও ভঙ্গি মিশিয়ে একটি বিচিত্র বস্তু সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশন করা হত। বিদেশি পর্যটকদের বৃত্তান্তে এবং সমসাময়িক পত্রিকায় অভিজাত বাঙালি গৃহের এইসব উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।১৯
আঠারো শতকে কলকাতার বাঙালি নব্য—অভিজাতরা যে বিলাসিতা ও আমোদপ্রমোদের উৎকট ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, তা উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় যাঁরা, এমনকী, রামমোহন ও দ্বারকানাথের মতো নতুন চিন্তাধারার পথপ্রদর্শকও এই বিলাসের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছিলেন। অথচ বাংলার সমাজজীবনে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা প্রবর্তনের পথে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা তখন বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। ‘আত্মীয় সভা’ ও কয়েকটি পত্রিকার ভিতর দিয়ে রামমোহন তখন কীভাবে সামাজিক জীবনে নতুন পথ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সে কথা আগে বলেছি। তিনি যে নতুন ধর্মচিন্তা করেছিলেন, সমাজে তখন তারও খানিকটা প্রচার হয়েছিল তাঁর বেদান্ত—উপনিষদের বাংলা ভাষ্য থেকে। তাঁর ধর্মমতের বিরুদ্ধে তখন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বেশ জোর আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ ছিল রক্ষণশীলদের প্রধান মুখপত্র।
রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁর ধর্মমতের সংঘাত যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, খ্রিস্টান সমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। গোঁড়া হিন্দু শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধে এবং খ্রিস্টান পাদরিদের বিরুদ্ধে রামমোহন সমানে তাঁর ধর্মমত নিয়ে তর্কবিতর্ক করেন (১৮২০—২৮)। খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। বাইবেলের মূল পুরাতন পাঠ অধ্যয়ন করার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা পর্যন্ত শিখেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টান শাস্ত্রে পরবর্তীকালে যে সমস্ত নৈতিক সমাচার অলৌকিক কাহিনিসহ সংযোজিত হয়েছে তার অভ্রান্ততা তিনি স্বীকার করতেন না এবং যিশুখ্রিস্টকে অবতার বলেও বিশ্বাস করতেন না। মানুষের চরিত্র ধর্মবুদ্ধি বিবেক ও মন উন্নত করার জন্য যিশু যে সমস্ত কথা বলে গিয়েছেন, সেইগুলিই তাঁর কাছে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে হত। এই সম্পদের সন্ধান এ দেশের লোকদের দেবার জন্য তিনি যিশুর বাণীর একটি সংকলন প্রকাশ করেন ইংরেজিতে—The Precepts of Jesus (১৮২০)। তারপর ১৮২০—২১ সালের মধ্যে যখন এই সংকলন ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে খ্রিস্টান পাদরিদের সঙ্গে তাঁর ঘোর বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন খ্রিস্টানদের কাছে তাঁর দুটি আবেদন প্রকাশিত হয়। ১৮২৩ সালে এই বিষয়ে তাঁর Final Appeal to the Christian Public etc. রামমোহনকে কেন্দ্র করে গোঁড়া খ্রিস্টান ও গোঁড়া হিন্দুদের বাদ—প্রতিবাদ যখন বেশ তীব্র হয়ে ওঠে, সমাজে যখন রীতিমতো দলাদলি আরম্ভ হয়, তখন ‘আত্মীয় সভা’র সভ্যরা অনেকে ভয় পেয়ে সভায় আসা বন্ধ করে দেন। ‘আত্মীয় সভা’র সভ্যদের যে শ্রেণিগত পরিচয় আগে দিয়েছি (জমিদারশ্রেণি) তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সমাজের ভয়ে ভীত হওয়া তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। জমিদাররা যতই উদার হন, সামাজিক অনুশাসন উপেক্ষা করার মতো সৎসাহস তাঁদের প্রায় ছিল না বললে ভুল হয় না। কাজেই ‘আত্মীয় সভা’ ১৮২১—২২ সালের পর থেকে কেবল নামেই টিকে ছিল বলা চলে।
‘আত্মীয় সভা’র যখন সংকট দেখা দিল তখন রেভারেন্ড অ্যাডামের সহযোগিতায় রামমোহন ‘ইউনিটেরিয়ান কমিটি’ নামে একটি সভা স্থাপন করেন (১৮২১)। এই সভায় ইউনিটেরিয়ান খ্রিস্টান মতে উপাসনা হত। তারপর রামমোহন তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সভা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করেন। এই সভার নাম হয় ‘ব্রাহ্মসমাজ’। ২০ আগস্ট ১৮২৮ ‘ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপিত হয়। তখন সাধারণত লোকে এই সভাকে ‘ব্রাহ্মসভা’ বলত। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় কলকাতায়, চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসু নামে এক ভদ্রলোকের বাইরের বৈঠকখানা ভাড়া করে। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় সভায় ব্রহ্মোপসনা হত। দু—জন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করতেন, পরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন। তারপর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করতেন। অবশেষে সংগীতের পর সভার কাজ শেষ হত। সংগীত করতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী ও পাখোয়াজ বাজাতেন গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান।২০ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হবার পর রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে রামমোহন—বিরোধিতা ক্রমে আরও তীব্রতর হতে থাকে। বাইরের লোক অনেকে কৌতূহলী হয়ে ব্রাহ্মসভার সাপ্তাহিক সান্ধ্য অধিবেশনে যাতায়াত করতে থাকেন। উপাসনার পদ্ধতি ও উপাসকদের আচার—ব্যবহার দেখে তাঁদের মনে হত, এ বোধহয় খ্রিস্টান গির্জা—উপাসনার এ দেশীয় অনুকরণ। তাঁরা এই কথা ভেবে শঙ্কিত হন যে রামমোহনের দল দেশীয় পদ্ধতিতে ব্রহ্মোপাসনার নাম করে এ দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারেই অগ্রসর হয়েছেন। লোকে তাঁকে খ্রিস্টান বলে উপহাস করতেও কুণ্ঠিত হত না। রামমোহনের কার্যকলাপ নিয়ে পথেঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায় সর্বদা তখন কটূক্তি বর্ষিত হত।
‘আত্মীয় সভা’, ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ইত্যাদির কার্যকলাপের বাইরের হিন্দুসমাজ যখন বিক্ষুব্ধ, তখন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনও কয়েকটি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রবল আকার ধারণ করে। রামমোহন ১৮১৮ সালে ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮১৯ সালে এ বিষয়ে তাঁর ‘দ্বিতীয় সম্বাদ’ প্রকাশিত হয়। ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন। শোনা যায় ১৭৮৬ সালে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি সতীদাহের সংবাদ পুনার রেসিডেন্ট ম্যালেট সাহেব ১৭৮৭ সালে ইংলন্ডে পাঠান।২১ তারপর রামমোহন যে সময় থেকে আন্দোলন আরম্ভ করেন প্রায় তখন থেকেই ইংলন্ডের পার্লামেন্টে এ বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হতে থাকে। এই সমস্ত বিতর্কের বিবরণের মধ্যে সতীদাহ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়।২২ যে—কোনও কারণেই হোক, বাংলা দেশে উনিশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে সতীদাহের ভয়ংকর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। বিলেতের ‘পার্লামেন্টারি পেপার’—এ সতীদাহের সংখ্যার যে হিসেব পাওয়া যায় তা বাস্তবিকই ভয়াবহ। যেমন :
বাংলা দেশে সতীদাহের সংখ্যা
(কলকাতা ঢাকা মুর্শিদাবাদ পাটনা বেরিলি বেনারস)
১৮১৭ : ৭০৭
১৮১৮ : ৮৯৩
১৮১৯ : ৬৫০
১৮২০ : ৫৯৭
১৮২১ : ৬৫৪
১৮২২ : ৫৮৩
১৮২৫ : ৬৩৯
১৮২৬ : ৫১৮
ফাউয়েল বাক্সটন ১৮২৫ সালে কমনস সভায় বলেন যে পাঁচ বছরে বাংলাদেশে সহমৃত সতীর সংখ্যা হয় ৩৪০০ জন। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যা এই হলেও, আসল সতীদাহের সংখ্যা অনেক বেশি, প্রায় ১০ হাজারের মতো। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, অধিকাংশ সতীদাহই বাংলা দেশে কলকাতা শহরের আশপাশের জেলাতেই অনুষ্ঠিত হত। ডিভিশন ও জেলা অনুযায়ী ১৮১৮—১৯ সালে সতীদাহের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, কলকাতা ডিভিশনে ৪২১, ঢাকা ডিভিশনে ৫৫, মুর্শিদাবাদ ডিভিশনে ২৫টি সতীদাহ হয়েছে, তার মধ্যে কলকাতা ডিভিশনে জেলাপ্রতি সংখ্যা এই :
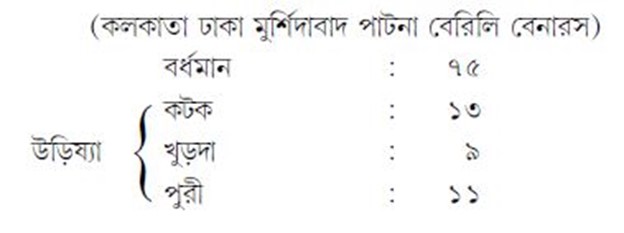
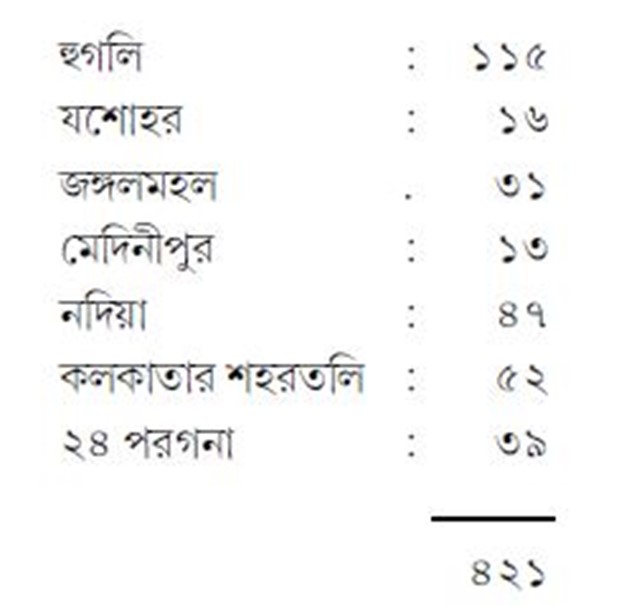
এখানে দেখা যায়, কলকাতার শহরতলি ও পাশাপাশি অঞ্চলে এবং শহরের কাছে হুগলি জেলায় সতীদাহের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ‘সমাচার দর্পণ’ লিখেছেন (২৭ মার্চ ১৮১৯) : ”অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না। এবং বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।” এই পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ১৮১৭ সালে হুগলি জেলাতে ”দুইশত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে।” কলকাতা শহর থেকে পঁচিশ—তিরিশ মাইল ব্যবধানের মধ্যে চারদিকে হিন্দুসমাজে কেন এরকম সতীদাহের আধিক্য হয়েছিল, তা সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বিষয়। সতীদাহ যে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ১৮১৯ সালে কলকাতা ডিভিশনের সতীদাহের সংখ্যা বর্ণভেদে (caste-wise) ও বয়সভেদে (age-wise) ভাগ করলে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায় :
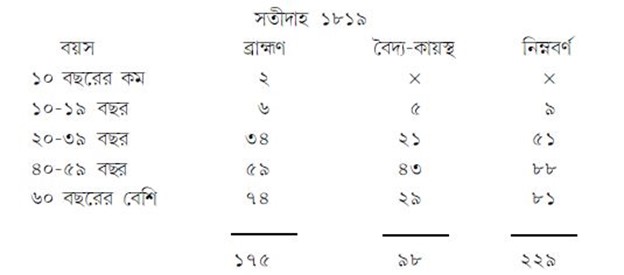
বর্ণগতভাবে বিচার করলে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি বলতে হয়। তাহলেও বিভিন্ন নিম্নবর্ণের মিলিত সংখ্যা কম নয়। বাংলা দেশে সতীদাহের আধিক্যের অন্যতম কারণ মনে হয় কৌলীন্যপ্রথা এবং এই কৌলীন্যপ্রথার অন্যতম আদিকেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল (হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি)। এই কৌলীন্যপ্রথা এমন একটি বিকৃত সামাজিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে, যে বহু পত্নীর অকালবৈধব্য শেষ পর্যন্ত একটা ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রধান সমস্যা ছিল দুটি—একটি আর্থনীতিক, আর—একটি বৈধব্যযন্ত্রণা। আর্থনীতিক সমস্যা হল বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণের সমস্যা এবং বৈধব্যযন্ত্রণা অল্পবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনেকদিন থেকেই অসহ্য। এ সমস্যার সমাধান দুটি উপায়ে হতে পারে। আর্থনীতিক অবস্থার সাচ্ছল্য এবং বিধবাবিবাহের সামাজিক প্রচলন। সাধারণভাবে বিচার করলে ব্রাহ্মণরা বর্ণশ্রেষ্ঠ হলেও অর্থনীতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্রই ছিলেন বেশি। অধ্যাপনা—যজমানি—পৌরহিত্য ছিল তাঁদের বর্ণগত পেশা এবং অধিকাংশই ছিলেন রাজা—মহারাজা, জমিদার—যজমানদের বৃত্তিজীবী। কাজেই কুলীন ব্রাহ্মণপত্নীদের আর্থিক সমস্যা ও বৈধব্যযন্ত্রণা উভয়সংকটের সম্মুখীন হতে হত। ধর্মের নামে এই উভয়সংকটের সমাধান সম্ভব হয়েছিল সহমরণের মধ্যে। বাংলা দেশে সহমরণের আধিক্যের এই ধরনের কতকগুলি আর্থিক সামাজিক কারণ ছিল বলে মনে হয়। তারপর সহমরণ যখন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল এবং সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সংযুক্ত হল, তখন ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণের মধ্যেও এই প্রথা সংক্রামিত হল। এই সংক্রমণের কারণ অব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা। একে সামাজিক প্রথা ‘Brahminization’ বা ‘Sanskritization’ বলা যায়।
ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক উইলবারফোর্স, ফাউলার বাক্সটন, জন পয়েন্ডার এবং আরও অনেকে কমনস সভায় ও তার বাইরে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। এ দেশের খ্রিস্টান মিশনারিরাও সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক—পুস্তিকা ও রচনা প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় স্বভাবতই এই আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক হন। তার জন্য হিন্দুসমাজের কাছ থেকে অনেক অপমান ও অপবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয়। এই আন্দোলনের ফলে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ বেন্টিঙ্ক সহমরণপ্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিলে যেমন হয়, বাংলার হিন্দুসমাজেরও প্রায় সেই অবস্থা হল সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ হবার পর। সামাজিক জীবন সংঘাতের একটা নতুন স্তরে পৌঁছোল।
১৮৩০—৩৩
নতুন সচলতা (dynamism) সঞ্চারিত হল সমাজে। কেবল সতীদাহ নিষেধ আইন পাশ হওয়ার জন্য নয়, আরও কতকগুলি ঘটনার দ্রুত ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজজীবনে প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হল ১৮৩০ সাল থেকে। রামমোহনের ব্রাহ্মসভার বিরুদ্ধে ‘ধর্মসভা’ গঠিত হল ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০। ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি থেকে ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ জোড়াসাঁকোর নিজস্ব নতুন বাড়িতে ‘ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপিত হল। ২৭ মে ১৮৩০ বিখ্যাত স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় এসে পৌঁছোলেন। ১৯ নভেম্বর ১৮৩০ রামমোহন রায় বিলেত যাত্রা করেন। ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ হিন্দু—কলেজের তরুণ শিক্ষক, বিদ্রোহী সমাজচিন্তার অগ্রদূত ডিরোজিও হিন্দুধর্মবিরোধী মতামত ও নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে পদচ্যুত হন, ২৬ ডিসেম্বর তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় কয়েকদিনের অসুখে। এই ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘটে যায় মাত্র তিন—চার বছরের মধ্যে, এবং প্রত্যেকটি ঘটনার এমন প্রত্যক্ষ গভীর প্রতিক্রিয়া হয় সমাজে যে হঠাৎ যেন মুখোমুখি তরঙ্গের আঘাতে সমাজের মগ্নচৈতন্য সবেগে সজাগ হয়ে ওঠে।
সতীদাহ নিষেধ আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার হিন্দুসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা দলবদ্ধ হয়ে একটি সভা গঠন করেন। ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ সংস্কৃত কলেজে কলকাতার হিন্দু বাঙালি ও হিন্দুস্থানি ‘সম্ভ্রান্তসমূহ’ সমবেত হয়ে এই সভার নামকরণ করেন ‘ধর্মসভা’। সভার স্থাপনের দিন প্রথম কর্তব্য নির্ধারিত হয়—এই আইনের বিরুদ্ধে একটি আরজি বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। সভাস্থাপনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ দে, গোপীমোহন দেব ও রামগোপাল মল্লিক। যদিও ”এই নগর মধ্যে এবং মফঃস্বলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধর্মরক্ষাহেতুক বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার লক্ষ দুই লক্ষ টাকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন।” তাহলেও সিদ্ধান্ত হয় যে সর্বসাধারণের সভায় সকলের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়াই ভালো। প্রথম দিনের সভাতেই ২৫০০, ২০০০, ১০০০, ৫০০ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে দেন। এই সময় আর কোনও প্রতিষ্ঠান বা সভাস্থাপনে একদিনে এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সনাতন হিন্দুধর্মের পবিত্রতা রক্ষার নামে কলকাতার ধনিক ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দুরা সেদিন প্রায় একডাকে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ধর্মসভার একটি শাখা ভবানীচরণের উদযোগে ভবানীপুর অঞ্চলেও স্থাপিত হয়েছিল। সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে আপিল ইংরেজি ভাষায় রাধাকান্ত দেব রচনা করেন। ফেব্রুয়ারি মাসের এক সভায় স্থির হয় যে, ”যাঁহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহারদিগের সহিত কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না।” অর্থাৎ যাঁরা হিন্দু হয়ে সতীদাহ সমর্থন করবেন না তাঁদের সমাজচ্যুত করা হবে।২৩
১৯ নভেম্বর ১৮৩০ রামমোহন রায় স্টিমারে বিলেত যাত্রা করে ৮ এপ্রিল ১৮৩১ লিভারপুল শহরে পৌঁছোন। তাঁর বিলেতযাত্রার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম ছিল ‘ধর্মসভা’র আপিলের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করা এবং সেখানকার ইংরেজ সমর্থকদের সাহায্যে আপিলটি নাকচ করার ব্যবস্থা করা। আগে বলেছি যে পয়েন্ডার, বাকসটন, উইলবারফোর্স প্রমুখ সমাজসংস্কারকরা ইংলন্ডে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। পয়েন্ডার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের এক সভায় সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের যুক্তি—প্রমাণের কথা উল্লেখ করে আবেগময় ভাষায় বক্তৃতা দেন।২৪ এই সময় উইলবারফোর্স একটি চিঠিতে (২২ মার্চ ১৮২৭) পয়েন্ডারকে লেখেন :
“I have long considered the conduct of our Indian Government in relation to the Burning of Widows as justly deserving of very severe censure and I cannot but hope that ere long so foul a reproach on Christian Nation will be done away for ever.”
মার্শম্যান একটি চিঠিতে লেখেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭) :
“On the human nature of this practice and the case with which in might be stopped, we have written various essays in this ‘Friend of India’, from which my son in 1823 selected four and a few on other subjects and published then… as these Essays contain the opinion of all of us including Dr. Carey on the subject, I scarcely think I can add anything in a letter which will be stronger. The dreadful practice prevails most in the neighbourhood of Calcutta than anywhere.”
ইংলন্ডে গিয়ে রামমোহন রায় এরকম প্রভাবশালী কয়েকজন ইংরেজের সমর্থন পেয়েছিলেন। ১১ জুলাই ১৮৩২ ধর্মসভার আপিল বাতিল করা হয়। রামমোহন রায় তখন বেডফোর্ড স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের পরিবারের গৃহে বাস করেছিলেন। আপিল বাতিল হবার পর স্বভাবতই পয়েন্ডার তাঁকে খুশি হয়ে একখানি চিঠি লেখেন। উত্তরে রামমোহন রায় লেখেন :*
48 Bedford Sq.
July 14–1832
My dear Sir,
Pray accept my sincere thanks for your kind enquiry after my health and for your hearty congratulation on the protection afforded by the Privy Council to the female community of India. Thereby they have removed the odium from out character as a people. As we can be no longer guilty of female murder, we now deserve every improvement, temporal and spiritual. I find my self perfectly well-to-day and with my best regards and thanks for your truely Christianlike treatment of me I remain.
My dear Sir
Yours very faithfully & sincerely
Rammohun Roy.
এই চিঠি লেখার অল্পদিন পরে, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। জেরিমি বেন্থামের মতো চিন্তানায়ক, উইলবারফোর্স প্রমুখ সমাজসংস্কারক এবং অন্যান্য অগ্রগামী রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ রামমোহন ইংলন্ডে পেয়েছিলেন। রবার্ট ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। যদি অকস্মাৎ বিদেশে তাঁর মৃত্যু না হত এবং স্বদেশে বাংলা দেশে তিনি ফিরে আসতেন, তাহলে বাংলার পরবর্তী সামাজিক জীবনধারা কোন পথে কীভাবে পরিচালিত হত তা বলা যায় না।
সামাজিক জীবনের আদর্শ—সংগ্রাম ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ও ‘ধর্মসভা’ মোটামুটি এই দুটি পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে গেল ১৮৩০—৩১ সালের মধ্যে। দুটি দলেরই প্রধান কর্মকেন্দ্র হল কলকাতা শহর, আন্দোলনও হল মূলত নগরকেন্দ্রিক। দলাদলি ও আন্দোলনের ঢেউ নাগরিক সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে যে একেবারে পৌঁছোয়নি তা নয়। ঢেউয়ের খানিকটা উচ্ছ্বাস গ্রামেও পৌঁছেছিল। রামমোহনপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রামে বাস করতেন—যেমন রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু বোড়ালে (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), কালীনাথ রায় টাকিতে (২৪ পরগনা), অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনি পাড়ায় (হাওড়া—হুগলি), রাজা কাশীনাথ আন্দুলে (হাওড়া)। ধর্মসভাপন্থীদের মধ্যে অনেকে কলকাতার কাছাকাছি গ্রামে বাস করতেন। কাজেই ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ও ‘ধর্মসভা’ দুই দলেরই আদর্শ—সংঘাতের প্রতিক্রিয়া অন্তত কলকাতার কাছাকাছি গ্রাম্য জীবনে বেশ কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু এই দুটি দলেরই গড়নের মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। সেটি হল সামাজিক শ্রেণির সাদৃশ্য। ‘আত্মীয় সভা’ ও পরবর্তী ‘ব্রাহ্মসমাজ’ তখনপ্রধানত সম্ভ্রান্ত বাঙালি উচ্চশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ‘ধর্মসভা’র মধ্যে কলকাতার ধনিক উচ্চশ্রেণিভুক্ত বাঙালির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। কলকাতার অধিকাংশ ধনকুবের বাঙালি হিন্দু ‘ধর্মসভা’র সমর্থক ছিলেন। আর্থিক সংগতির দিক থেকে বিচার করলে ‘ধর্মসভা’র ক্ষমতা, প্রভাব—প্রতিপত্তি ‘ব্রাহ্মসমাজ’—এর তুলনায় যথেষ্ট বেশি ছিল। তা ছাড়া ‘ব্রাহ্মসমাজ’—এর পোষকদের মধ্যে সমাজভয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব—জড়িত মনোভাব প্রকাশ পেত ‘ধর্মসভা’র সভ্যদের মধ্যে তার কোনও চিহ্নই ছিল না। ‘ধর্মসভা’র আদর্শ বিশ্বাস ও আবেগের ভিত্তি ছিল দৃঢ়মূল, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের মূল তখন সমাজমানসের সামান্য গভীরেও প্রবেশ করেনি। তাই সামাজিক দলাদলিতে ‘ধর্মসভা’র প্রতাপ ছিল অখণ্ড, ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ছিল দোদুল্যমান। যদিও ‘ধর্মসভা’ তখন জাতিগত ও ব্যক্তিগত (অর্থাৎ বিত্তগত) দলাদলিতে অত্যধিক মত্ত হয়ে উঠেছিল,২৫ তা সত্ত্বেও ‘ব্রাহ্মসমাজ’ সেই সুযোগ গ্রহণ করে তখন নতুন শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে ধর্মসভার আক্রোশের প্রচণ্ডতা রামমোহন লক্ষ করেছিলেন এবং বিদেশযাত্রার আগে আসন্ন ঝড়ের আভাসও পেয়েছিলেন। কিছু ঝড়ের ঝাপটা তাঁকেও সহ্য করতে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়কার কথা স্মরণ করে লিখেছেন :২৬
”তখন সমাজের প্রতি অনেকেই অনেক নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় ‘নাচ তামাশা’ নৃত্যগীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও বিশেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপর মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্মসভার দল সতী দগ্ধ করিবার দল।… সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মণসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন, কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গার বা জগন্নাথের যাত্রীরা দূর হইতে পদব্রজে আইসে, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে সমাজে আসিতেন।”
রামমোহনের বিলেতযাত্রা এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হবার পর ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহ উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রধানত দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাসিক ৬০—৮০ টাকা অর্থসাহায্যে ব্রাহ্মসমাজ কোনওরকমে বাতি জ্বালিয়ে ছিল বলা চলে। আর্থিক অভাবের জন্য সমাজেরও কাজকর্ম ভালো চলত না। ধনিক ব্রাহ্মরা ধর্মসভার পৃষ্ঠপোষকদের মতো সভার কাজে পর্যাপ্ত অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন। বোঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল কৃত্রিম, অন্তরের কোনও টান ছিল না, বিশ্বাসের মূলও দৃঢ় ছিল না। তাই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যখন প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় (১৮৪০ সালের গোড়ায়) তখন তিনি দেখেন—”সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদপাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালীর মত ব্যাখ্যান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন।২৭ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের বেদি থেকে তখন ‘অবতারতত্ত্ব’ ও ‘পৌত্তলিকতা’র মাহাত্ম্য প্রচারিত হচ্ছে।
রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর দশ বছরের মধ্যে (১৮৩০—৪০) ব্রাহ্মসমাজ একেবারে মুহ্যমান হয়ে যায়। ওদিকে ধর্মসভাও বিভিন্ন গোষ্ঠীপতির সামাজিক দলাদলিতে এমন মত্ত হয়ে ওঠে যে তার আসল উদ্দেশ্যের অনেকটা এই মত্ততার মধ্যে হারিয়ে যায়। সামাজিক জীবনে যে নতুন গতি সঞ্চারিত হয় (১৮১৫—৩০ সালের মধ্যে) তা ব্রাহ্মসমাজ—ধর্মসভার কার্যকলাপের দিক থেকে এই সময় প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। আবার নতুন আঘাত ও নতুন সামাজিক গতিসঞ্চারের প্রয়োজন দেখা যায়।
এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাতে বাংলার সমাজমঞ্চে আবির্ভাব হয় ‘ইয়ং বেঙ্গল’ দলের। নাম শুনেই বোঝা যায় এই দলভুক্ত সকলে বয়সে তরুণ ছিলেন। ১৮৩০ সালে ইয়াং বেঙ্গল দলের অগ্রগণ্যদের বয়স ছিল এই :
(১৮৩০)
শিক্ষক ডিরোজিও : ২১ বছর
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৭ বছর
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় : ১৬ বছর
রামগোপাল ঘোষ : ১৫ বছর
রাধানাথ শিকদার : ১৭ বছর
রসিককৃষ্ণ মল্লিক : ২০ বছর
হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিভিয়ান লুই ডিরোজিওর ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন বলে এই তরুণ গোষ্ঠীকে ‘Derozians’—ও বলা হত। এই তরুণরা সকলে কলকাতা শহরে বাস করতেন বলে কেউ কেউ তাঁদের ‘ইয়াং ক্যালকাটা’ও বলতেন।
‘আত্মীয় সভা’, ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ও ‘ধর্মসভা’ গঠন করে যাঁরা আগে সামাজিক আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবয়সি ও প্রবীণ। মধ্যবয়সিদের কর্মশক্তি যা—ই থাকুক, উৎসাহ ও আবেগ সাধারণত তাঁদের অনেক হিসেবি ও সংযত হয়, তাঁরা আগুপিছু বিবেচনা করে, ভালোমন্দ ফলাফলের কথা চিন্তা করে কাজ করেন। তাঁরা দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোনও সামাজিক ঘটনাবর্তে ঝাঁপিয়েপড়তে পারেন না, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে পারেন না, পদে পদে পূর্ব—অভিজ্ঞতা ও হাজার রকমের হিসেবি নিষেধের বন্ধনে তাঁদের চলার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এক—পা করে তাঁরা এগিয়ে চলেন, মধ্যে মধ্যে অবস্থাগতিকে দু—পা পিছিয়েও আসেন। ব্রাহ্মরা ঠিক তা—ই করছিলেন। কিন্তু তরুণের ধর্ম তা নয়। তরুণের বিদ্রোহ পরিপূর্ণ বিদ্রোহ, মনে হয় যেন তার কোনও দিগন্তরেখা নেই। তরুণ ডিরোজিয়ানদের বিদ্রোহের প্রথম উল্লাসে ঠিক তা—ই মনে হয়েছিল। উনিশ শতকের তিনের দশক নবযুগের বাংলার তরুণদের প্রথম বিদ্রোহকাল এবং তার ফেনোচ্ছ্বসিত প্রবল প্রকাশ তিন—চার বছরের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যায়, যদিও চারের দশক পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়ার ঢেউ বইতে থাকে।
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯—৩১) হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮২৬—২৭ সালে, ১৭—১৮ বছর বয়সে। একটি পোর্তুগিজ ফিরিঙ্গি পরিবারে ডিরোজিওর জন্ম হয়। মৌলালি ও সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলের কাছে ডিরোজিও পরিবারের বাস ছিল। ছেলেবেলায় ডিরোজিও লেখাপড়া শেখেন ধর্মতলায় ড্রামন্ড নামে এক স্কচ সাহেবের বিদ্যালয়ে। ড্রামন্ড ছিলেন সংস্কারমুক্ত, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, প্রগতিবাদী। ডিরোজিও তাঁর নিজের জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে ও চরিত্রে, গুরু ড্রামন্ডের যোগ্য শিষ্য হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া একটি যুগান্তকারী ঘটনা—“It opened up, so to speak, a new era in the annals of the college.”২৮ এটি কিশোরীচাঁদ মিত্রর উক্তি। ডিরোজিও ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু ড্রামন্ডের মতো “a successful teacher of youth”। তরুণদের আদর্শ শিক্ষক ডিরোজিও হতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের চারিত্রিক গুণের জন্য তো বটেই, নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি ও আদর্শের জন্যও। নিজে বয়সে তরুণ ছিলেন বলে তরুণ ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। ছাত্রদের মাথায় পাঠ্যবস্তু ঠেসে দিয়ে তিনি তাদের কৃতী পরীক্ষার্থীতে পরিণত করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তার পরিবর্তে তাদের মনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগিয়ে দিতেন, এবং মানুষ, জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে উদার চিন্তার পথ খুলে দিতেন। কিশোরীচাঁদ বলেছেন : “He felt it his duty as such to teach not only words but things, to touch not only the head but the heart. He sought not to cram the mind but to inoculate it with large and liberal ideas.” সেজন্য তাঁর ক্লাস ছাত্রদের কাছে ক্লাস মনে হত না, জ্ঞানের অসীম কৌতূহল জাগরণের নির্মল মুক্ত বায়ুচল পরিবেশ বলে মনে হত। দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস, যখন যে বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন তখন সেই বিষয়ের রহস্যের দ্বার একটির পর একটি তিনি ছাত্রদের মনের সামনে খুলে দিতেন। তাঁর ক্লাস একটি বিতর্কসভা বলে মন হত। ক্লাসের বাইরে কলেজে, কলেজের বাইরে তাঁর নিজের বাড়িতে ছাত্ররা এরকম আলোচনাচক্রে তাঁর সঙ্গে মিলিত হত। এইভাবে হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা ডিরোজিওর সাহচর্যে বেকন (Bacon), লক (Locke), বার্কলে (Berkeley), হিউম (Hume), রিড (Reid), স্টুয়ার্ট (Stewart) প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। পরিচয়ের ফলে তরুণদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সূত্রপাত হয়।
কলেজের মধ্যে যে—কোনও বিষয়ে স্বাধীন আলোচনা ও বিতর্ক সম্ভব নয় বলে তরুণরা বাইরে একটি বিতর্কসভা স্থাপন করেন। এই সভার নাম ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’ (Academic Association)। ১৮২৭—২৮ সাল থেকেই এই সভার নিয়মিত বৈঠক আরম্ভ হয়। শুধু যে তরুণ ছাত্ররাই এই সভায় যোগ দিতেন তা নয়, ডেভিড হেয়ার, গভর্নর—জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি, বিশপ’স কলেজের অধ্যক্ষ মিলস সাহেব, সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস, এঁরাও নিয়মিত আসতেন। সভার সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও, সম্পাদক উমাচরণ বসু। তরুণদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ প্রতিভাবান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই চারজনকে ইয়াং বেঙ্গল দলের মধ্যে ‘fire-brands’ বলা হত।২৯ সাধারণত সাপ্তাহিক বৈঠক বসত এবং এই বৈঠকে “The young lions of the Academy roared out, week after week, Down with Hinduism! Down with Orthodoxy!”৩০ ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, নৈতিক ভণ্ডামি ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, বিচারবুদ্ধিহীন শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণহীন আচার—অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে, নিয়তিবাদ ও দেবতা—বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে তরুণরা নিয়মিত তর্কবিতর্ক করতেন। ১৮২৯—৩০ সালে তরুণদের এই বিতর্কসভার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রামমোহনের ‘ব্রাহ্মসমাজ’ এবং গোঁড়া হিন্দুদের ‘ধর্মসভা’। ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ও ‘ধর্মসভা’ উভয়ের প্রতিই তরুণরা বিরূপ ছিলেন। ‘ধর্মসভা’র গোঁড়ামি স্বভাবতই তাঁদের ভালো লাগত না, আর ‘ব্রাহ্মসমাজ’—এর উদারতার অন্তরালে দোলায়মান অতিসাবধানি মনোভাবও তাঁদের মনঃপূত হত না। ইয়াং বেঙ্গল দল তাই ব্রাহ্মদের ‘মডারেট’ ও ‘হাফ—লিবারেল’ বলতেন এবং ব্রাহ্মরা তরুণ ডিরোজিয়ানদের ‘আলট্রা—র্যাডিক্যাল’ বলতেন। তরুণদের বিরুদ্ধে প্রবীণদের প্রধান অভিযোগ ছিল, তাঁরা হিন্দুধর্ম—বিদ্বেষী ও নাস্তিক।
উনিশ শতকের তিরিশে বাংলাদেশের সমাজচিন্তায় তিনটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—একটি ধর্মসভাপন্থীদের প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী গতানুগতিক চিন্তাধারা, একটি ব্রাহ্মসভাপন্থীদের উদার অথচ মধ্যপথগামী চিন্তাধারা, আর—একটি বন্ধনমুক্ত যুক্তিবাদী, কিছুটা উন্মার্গ চিন্তাধারা। সমাজচিন্তার এই তিনটি ধারা তখনকার বিভিন্ন সাময়িকপত্রেও প্রতিফলিত হয় :
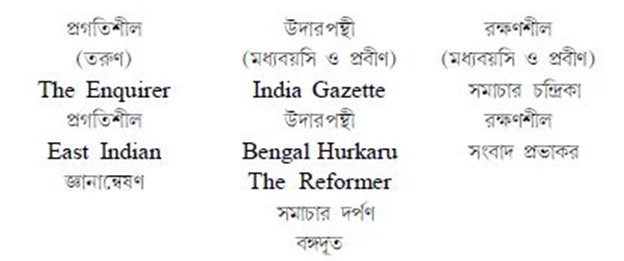
উদারপন্থীরা ধীরেসুস্থে সামাজিক উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন, তরুণ প্রগতিবাদীদের অত ধৈর্য ছিল না, তাঁরা ছিলেন অস্থির চঞ্চল, কাজেই তাঁদের কথায় ও লেখায় বেশ খানিকটা অস্থিরতা ও অসংযম প্রকাশ পেত। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ‘রিফর্মার’, মিশনারিদের ‘সমাচার দর্পণ’, ‘হরকরা’ ও ‘ইন্ডিয়া গেজেট’ অধিকাংশ রচনায় তরুণদের স্থির ও সংযত হয়ে ‘মডারেট’দের অনুগামী হতে উপদেশ দিতেন। উত্তরে তরুণরা বলতেন, “We disregard all that they say or do, and are engaged in measuring our success with the rising generation.”–The Enquirer৩১
বিদ্রোহী তরুণদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মবিদ্বেষ ও নাস্তিকতার অভিযোগের একটি বড় কারণ হল পাদরি আলেকজান্ডার ডাফ ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ২৭ মে ১৮৩০ ডাফ কলকাতায় আসেন খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। কলকাতায় এসে তিনি হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের স্বধর্ম ও সমাজের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব দেখে খুব উল্লসিত হন। ডাফ লিখেছেন : “We hailed it as heralding the dawn of an auspicious era.”৩২ কিন্তু হিন্দু কলেজ ছিল তাঁর মতে “the very beau-ideal of a system of education without religion.” কাজেই ডাফ প্রথমেই এই তরুণ ছাত্রদের মনে ধর্মভাব জাগাবার জন্য সচেষ্ট হন। এই ধর্মভাব যে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য তা বলাই বাহুল্য। ঠিক হল তাঁরা কয়েকজন মিলে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন। দু—মাসের মধ্যেই তিনি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। আগস্টের (১৮৩০) গোড়ার দিকে প্রথম বক্তৃতা হয়, বক্তা পাদরি হিল। গরম বক্তৃতা, যেমন জলপ্রপাতের মতো আবেগ, তেমনি ক্ষুরধার যুক্তি—বিষয়বস্তু ‘সবার উপরে খ্রিস্টধর্ম সত্য’। হিল সাহেবের বক্তৃতায় কলকাতার হিন্দুসমাজের পাঁজর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। ডাফ সাহেবের নিজের ভাষায়, “the whole town was literally in a uproar.” তাঁর ছাত্র—শিষ্য রেভারেন্ড লালবিহারী দে’—র ভাষায়, “that lecture fell like a bombshell among the College authorities.”৩৩ কলকাতার হিন্দুসমাজের উপর, বিশেষ করে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অভিভাবকদের উপর, এই বক্তৃতার যে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে ডাফ যা লিখেছেন তার মর্ম এই :
”বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে হিন্দুসমাজে নানারকমের গুজব রটতে আরম্ভ করে হুলুস্থুল পড়ে যায় শহরে। হিন্দুদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয় যে খ্রিস্টান পাদরিরা যে—কোনও প্রকারে হোক, ভয় বা লোভ দেখিয়ে হিন্দু তরুণদের ধর্মান্তরিত করার চক্রান্ত করেছেন। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সভা ডেকে হিন্দুসমাজের কর্ণধাররা আমাদের হীন চক্রান্তের কথা জনসাধারণকে বোঝাতে আরম্ভ করেন। আমাদের কবল থেকে কী উপায়ে হিন্দু তরুণদের রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য জনসভায় ও সংবাদপত্রে খুব উত্তেজিত আলোচনা হতে থাকে। ছাত্রদের অভিভাবকরা হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন যে কলেজের ধর্মনীতিহীন বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই তরুণদের নৈতিক চরিত্রের স্খলন হয়েছে।”
হিন্দু কলেজের পরিচালকরা এই সময় রীতিমতো ভীত হয়ে ওঠেন। ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে একদল তরুণ যে কীরকম স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছিল, তা তাঁরা আগে থেকেই লক্ষ করেছেন। তার উপর ডাফের নেতৃত্বে খ্রিস্টান পাদরিরা কীভাবে তরুণদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিলেন তা—ও তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে কলেজের ম্যানেজিং কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকা হয় এবং বৈঠকে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ধর্ম বিষয়ে কোনও আলোচনাসভায় বা বক্তৃতায় ছাত্ররা যোগ দিতে পারবে না।
শনিবার, ২৩ এপ্রিল ১৮৩১। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষরা জরুরি সভায় মিলিত হন। সভায় উপস্থিত থাকেন উইলসন, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, রসময় দত্ত, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ। সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে সম্পাদক বলেন, ‘অধ্যক্ষদের এই জরুরি সভা আহ্বান করার অন্যতম কারণ হল, এই বিদ্যালয়ের কোনও একজন শিক্ষকের অদ্ভুত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলে হিন্দুসমাজে আশঙ্কার সঞ্চার হচ্ছে এবং তার ফলে বিদ্যালয়েরও ক্ষতি হচ্ছে। এই শিক্ষকের উপর বহু তরুণ চরিত্র গঠনের দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু তাঁর অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ছাত্রদের রুচিনীতিবোধ ক্ষুণ্ণ তো হচ্ছেই, উপরন্তু তাদের নৈতিক চরিত্র ক্রমে সমাজ ও পরিবারের পক্ষে অকল্যাণ ও অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের প্রায় ২৫ জন ছাত্র বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেছে। আরও প্রায় ১৬০ জন ছাত্র নানাবিধ অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করেছে। অতএব এ বিষয়ে অধ্যক্ষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত।’৩৪ বলা বাহুল্য, এই শিক্ষক হলেন ডিরোজিও।
ডিরোজিওকে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। ডিরোজিও পদত্যাগ করেন ২৫ এপ্রিল ১৮৩১। পদত্যাগের আট মাস পরে ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ হঠাৎ অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স ২২ বছর কয়েক মাস।
ডিরোজিওর পদত্যাগের পর তরুণ ছাত্ররা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। ছাত্রদের বয়স তখন ১৬ থেকে ১৮ বছর, তাঁর নিজের বয়স ২২ বছর। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে তারুণ্যের বন্ধন সংকটকালে আরও দৃঢ় হয়। তাঁরা বুঝতে পারেন যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের চার দেয়ালের গণ্ডির মধ্যে কেবল বাকযুদ্ধ করে দিন কাটালে চলবে না, নিজেদের মুখপত্রের ভিতর দিয়ে বাইরে বৃহত্তর জনসমাজে তাঁদের মতামত পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে হবে। এক মাসের মধ্যেই The Enquirer নামে ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় (মে ১৮৩১)। ডিরোজিও নিজেও The East Indian নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ‘এনকোয়্যারার’ পত্রিকার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন : “Having thus launched our bark under the denomination of Enquirer, we set sail in quest of truth and happiness.” আরও এক মাস পরে (জুন ১৮৩১) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাংলা সাপ্তাহিক পত্র ‘জ্ঞানান্বেষণ’ প্রকাশিত হয়। মানুষের জ্ঞানের তিমির হরণ করে, দয়া করেও সত্যকে সংস্থাপন করে, শঠতা সংহার করে জ্ঞানের বিকাশের পথ প্রশস্ত করা পত্রিকার আদর্শ।
তিরিশের গোড়া থেকেই আদর্শ—সংগ্রাম বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মুখপত্রের ভিতর দিয়ে অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। ‘ধর্মসভা’র মুখপত্র ‘সমাচারচন্দ্রিকা’ নয় শুধু, উদারপন্থী ও ব্রাহ্মরাও (যেমন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের The Reformer পত্রিকা) তরুণ ডিরোজিয়ানদের কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। তরুণরা ধর্মসভাকে বলতেন ‘গুডুমসভা’, যেহেতু তরুণদের বিরুদ্ধে সর্বদা তাঁরা কটূক্তির গোলাগুলি বর্ষণ করতেন।
বিদ্বৎসভার বাকযুদ্ধ ক্রমে মসিযুদ্ধে পরিণত হয়। তরুণদের উত্তেজনা স্বভাবতই বন্ধনহীন। এই সময় উত্তেজনার চরম সীমায় পর পর কয়েকটি নাটকীয় ঘটনাও ঘটে যায়। কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক বাড়ি ছিল মধ্য কলকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। তাঁর বাড়ির পাশে ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী নামে দু—জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ঘটনার তারিখ হল ২৩ আগস্ট ১৮৩৯ সাল। কোনও কাজে কৃষ্ণমোহন বাইরে বেরিয়েছিলেন, বাড়িতে ছিলেন না। এই সময় তাঁর বন্ধুরা তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে করতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। উত্তেজনার বশে কাছে মেছুয়াবাজারের এক মুসলমানের দোকান থেকে রুটি—গোমাংস কিনে এনে তাঁরা উল্লসিত হয় ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। শুধু ভক্ষণ করেই তাঁদের তৃপ্তি হয় না। ভক্ষণের শেষে উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে গোমাংসের হাড়গুলি তাঁরা পাশের চক্রবর্তীদের বাড়ির ভিতরে নিক্ষেপ করেন। গোহাড় বলে চিৎকার করতে করতে চক্রবর্তীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়ায় নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবেশীরা তরুণদের প্রহার করতে উদ্যত হন, অজস্র ধারায় তাদের উপর কটুবাক্য ও অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকে। তরুণরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। প্রতিবেশীরা ঠিক করেন যে কৃষ্ণমোহনকে বাড়িতে বা পাড়ায় আর বাস করতে দেওয়া হবে না। তা—ই হয়, কৃষ্ণমোহন গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিছুদিন এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিয়ে পরে চৌরঙ্গিতে একজন সাহেবের গৃহে তিনি অতিথি হন। কলকাতা শহরে কোনও হিন্দু পল্লিতে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করেননি।
এই সময় কৃষ্ণমোহন ছোট একটি নাটিকা লেখেন ইংরেজিতে—The Persecuted or Dramatic Scenes Illustrative of the Present State of Hindoo Society in Calcutta. নাটিকাটি তিনি উৎসর্গ করেন হিন্দু তরুণদের :৩৫
To
Hindoo Youths
The following pages are inscribed to them with sentiments of affection, and strong hopes of their appreciating those virtues and mental energies which elevate man in estimation of a philosopher.
By their ever devoted
Firend & Servant
Krishna Mohana Banerjea.
Caldutta, 12th November,1831
ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন লেখেন যে নাটকীয় উৎকৃষ্টতার দিক থেকে বিচার করলে পাঠকরা তাঁর নাটক পড়ে হতাশ হবেন। রচনাগুণের চেয়ে রচনার উদ্দেশ্যই বড় কথা। সেই উদ্দেশ্য হল, হিন্দুসমাজের কর্ণধার যাঁরা তাঁদের চরিত্রের অসংগতি ও অসাধুতা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা। বিশেষ করে হিন্দুসমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা যে কত দূর শঠ ও ধূর্ত তা এই নাটকখানি পাঠ করলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন এবং নিজেরা সাবধান হতে পারবেন। এই ভূমিকা থেকেই জানা যায় যে ইংরেজদের মধ্যে অনেকে নাটকখানি লিখতে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং দু—কপি ছ—কপি পর্যন্ত অগ্রিম কেনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।
তরুণ ডিরোজিয়ানরা শুধু যে সনাতনধর্মী গোঁড়া হিন্দুদের লক্ষ্য করে বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করতেন তা নয়, ব্রাহ্মধর্মানুরাগীদেরও কঠোর সমালোচনা করতেন তাঁদের উভয় কুল রক্ষার হাস্যকর প্রচেষ্টার জন্য। ব্রাহ্মরা নীতিগতভাবে পৌত্তলিকতা—বিরোধী হয়েও স্বগৃহে ও পরিবারে পৌত্তলিকের মতো আচরণ করতেন। তরুণ অতিপ্রগতিবাদীদের (ultra-radicals) কাছে ব্রাহ্মদের প্রচারিত আদর্শ ও আচরণের এই অসংগতি অত্যন্ত বিসদৃশ বলে মনে হত। এই কারণে তাঁরা মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম মডারেটদের আচার—ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করতেন।
তরুণ ছাত্ররা যখন সমাজসংস্কারের অত্যুৎসাহে চারদিকে “noise and confusion” সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁদের শিক্ষক ও দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর হঠাৎ মৃত্যু হয় (ডিসেম্বর ১৮৩১)। তার জন্য কোলাহল থামেনি। ১৮৩২—৩৩ সালে কোলাহল আরও কিছুটা বাড়ে। এবারে উত্তেজনায় ইন্ধন জোগান দেন খ্রিস্টান পাদরিরা। ১৮৩০ সালে আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় আসার পর খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে বক্তৃতায় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় হিন্দুসমাজে, ১৮৩২ সাল থেকে তার ফল ফলতে আরম্ভ করে । হিন্দু কলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন (আগস্ট ১৮৩২) :৩৬ “We hope ere long to be able to witness more and more such happy results in this country.” কয়েক মাস পরে (নভেম্বর ১৮৩২) কৃষ্ণমোহন নিজেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তরুণ ডিরোজিয়ানদের প্রবক্তা হিসেবে কৃষ্ণমোহনের নাম প্রায় সকলেই জানতেন। চাঞ্চল্যকর ঘটনা তাঁকে কেন্দ্র করে কম হয়নি। ‘এনকোয়্যারার’ পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক হিসেবেও অনেকর কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন। কাজেই তাঁর ধর্মান্তরের সংবাদে কলকাতার হিন্দুসমাজে আর—একবার উত্তেজনার উত্তাল জোয়ার বয়ে গেল। এই উত্তেজনা সম্বন্ধে ডাফ লিখেছেন :৩৭
“These baptisms, though small in number, were in quality of inestimable value… These were the first that had ever taken place in Eastern India among the better classes of natives who had acquired a through European education…”
এতদিন পর্যন্ত খ্রিস্টান পাদরিরা হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত ও অনাদৃত বর্ণের দরিদ্র অসহায় লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে তাদের ‘খ্রিস্টান’ করেছেন। এই ‘নেটিভ খ্রিস্টানরা’ অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং দরিদ্র। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আত্মাভিমানের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মনে যে চাপা অসন্তাোষ ও অভিযোগ ধূমায়িত হত তার সুযোগ নিয়ে আগে ইসলামধর্ম, এবং পরে খ্রিস্টান ধর্ম, বাঙালি হিন্দুসমাজের নিচের স্তরে প্রবেশ করে। আগে যাঁরা ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশ নিম্নবর্ণের হিন্দু ও দরিদ্র। খ্রিস্টান ধর্মের আমলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজধর্ম গ্রহণ করলে দারিদ্র্য দূর হতে পারে, এরকম আশাও ধর্মান্তরিতদের পক্ষে মনে মনে পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়। উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু পরিবারে, আধুনিক ইংরেজি—শিক্ষিতদের মধ্যে, খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের সূচনা হল মহেশচন্দ্র ও কৃষ্ণমোহনকে দিয়ে। তরুণ কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তরে হিন্দুসমাজে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল।
হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদল, ‘পাতিফিরিঙ্গি কেষ্টা বান্দা’, মডারেট ব্রাহ্মগোষ্ঠী ও সনাতনধর্মী হিন্দুরা ১৮৩২—৩৩ সালে যখন প্রত্যক্ষ আদর্শ—সংঘাতের ভিতর দিয়ে সমাজজীবন কলরবমুখর করে তোলেন তখন বিদেশে ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩)। ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে বিলেতযাত্রার আগে রামমোহন এই আদর্শ—সংঘাতের প্রস্তুতি দেখে গিয়েছিলেন, এবং দু—তিন বছরের মধ্যে তার যে চরম প্রকাশ হয়, হয়তো তার কিছু কিছু সংবাদও তাঁর কানে পৌঁছেছিল। তিনি ফিরে এলে বাংলার সামাজিক জীবনের গতি তাঁর ইচ্ছামতো কতখানি তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন তা বলা যায় না। তার কারণ সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের গতি কতকটা নদীর গতির মতো, সহজে তা ভিন্নমুখী করা যায় না।
ইয়ং বেঙ্গলের আবির্ভাব ও বিদ্রোহ বাংলার সমাজজীবনে একটা যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। ইয়াং বেঙ্গলের বিদ্রোহ এ দেশের আধুনিককালের ইতিহাসে প্রথম তরুণ—বিদ্রোহ (Youth Revolt), প্রথম ছাত্র—বিদ্রোহ (Students’ Revolt)। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে এই তরুণ ছাত্র—বিদ্রোহের মূল কারণ তা “discrepancy between the family structure and the total social structure”—এর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হয়।৩৮ আঠারো শতক থেকে কলকাতার নাগরিক সমাজের একটা নতুন রূপায়ণ আরম্ভ হয়েছিল, যাকে বিত্তকেন্দ্রিক নতুন শ্রেণিবিন্যাস বলা যায়। সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত কতকটা পরিমাণে সামাজিক মর্যাদা—প্রতিষ্ঠা (Social Status) ক্রমেই বিত্তমুখী হয়ে উঠছিল, অথচ শ্রেণিমধ্যস্থ বিভিন্ন পরিবারের গড়ন ও পুরাতন নীতিগত বন্ধন বিশেষ শিথিল হচ্ছিল না। সমাজে বেশ কিছুটা পরিমাণে ব্যক্তিকৃতিমুখী (Achievement-oriented) হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরিবার তা হচ্ছিল না। পারিবারিক ও সামাজিক গড়নের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের অভাব বা বিরোধ থেকে, অবস্থান্তরের ফলে, ক্রমে পরিবারভুক্ত তরুণদের মনে বিদ্রোহের সঞ্চার হতে থাকে। এই অবস্থান্তর ঘটে উনিশ শতকের তিরিশে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ইয়াং বেঙ্গলের আন্দোলন দেখা দেয়। সমাজে তরুণদের ভূমিকা ও সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞানী আইজেনস্টাডট বলেছেন :৩৯
“Most of these movements arise in societies in which a traditional social order is undermined by the impact of modern, universalistic, social, political and economic developments—either through internal developments or through the penetration of foreign European groups and interests. Significantly enough, in most of these countries the polictical and intellectual development has been much more advanced than the economic.”
এখানে পরাধীন দেশের অবস্থা বিচার করা হয়েছে। পুরাতন ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজের সঙ্গে যখন নতুন বহুমুখী বিচিত্রগামী সমাজের সংঘাত হয়, তখন তরুণদের মধ্যে এই ধরনের সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বাধীন দেশে আর্থনীতিক বিকাশের ধারা যখন সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়, তখন ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের ফলে আধুনিক শিল্পসমাজ ও পরিবারের সঙ্গে সেকালের সামন্তসমাজ ও পরিবারের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরাধীন দেশে—যেমন ভারতবর্ষে বা বাংলা দেশে বিদেশি শাসকরা এই সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন। তবে স্বাভাবিক আর্থনীতিক বিকাশের ভিতর দিয়ে পরাধীন দেশে সামাজিক—পারিবারিক নীতিবিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না, নতুন শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানসিক বিকাশের ফলে পুরাতন—নতুনে সংঘাত হয়। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার ফলে তরুণ ছাত্রদের যে নতুন মানসিক বিকাশ হয়েছিল তা সমকালীন ইউরোপীয় মানসিক বিকাশের সমকক্ষ বললে অত্যুক্তি হয় না। নবযুগের ইউরোপের সমাজদর্শন ও জীবনদর্শন তরুণ ছাত্রদের মানসলোকে যে নতুন সমাজ ও নতুন জীবনে ভাবমূর্তি (image) সৃষ্টি করেছিল, বিরোধ হয়েছিল সেই জীবন ও সমাজপ্রতিমার সঙ্গে পুরাতন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সমাজের। তরুণদের এই আদর্শ সমাজপ্রতিমা হল ‘universalistic’ ও ‘achievement-oriented’ এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সমাজ হল ‘particularistic’, ‘ascriptive’, ‘traditional’—অর্থাৎ তরুণদের ‘মডেল’ সমাজ ও পরিবার তখন মনে মনে গড়া হয়ে গিয়েছে এবং তার রূপ হল বহুমুখী ও ব্যক্তিকৃতিমুখী, পুরাতন সমাজের মতো একমুখী, পূর্বারোপিত আদর্শবদ্ধ ও ঐতিহ্যিক নয়।
আইজেনস্টাডট বলেছেন :৪০
“A purposeful attempt usually takes place to disconnect the young people from their families, to turn them against the latter and the order they represent, and to intensify the conflict between the generations.”
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়তো হতে পারে, না—ও হতে পারে, তবে ইয়াং বেঙ্গলের মুখপাত্র ও আদর্শপন্থীদের যে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সমকালীন সাময়িকপত্রে হিন্দু কলেজের ডিরোজিও—অনুরাগী ছাত্রদের অভিভাবকদের এত চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাদের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, রীতিনীতি, আচার—ব্যবহার, ধ্যানধারণা, এমনকী পোশাক—পরিচ্ছদ ও প্রাত্যহিক চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে পারিবারিক বিরোধ ও বিচ্ছেদের লক্ষণটি তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণারঞ্জন, রসিককৃষ্ণ প্রত্যেকেই প্রায় একরকম নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, এবং যাঁরা তা হননি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের বিরোধের যন্ত্রণা প্রতিদিন নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। মানসলোকের আদর্শ জীবন ও আদর্শ সমাজের সঙ্গে বাস্তব জীবন ও সমাজের এই সংঘাত ছাড়াও, তার ফলে “the conflict between the generations”—ও তীব্রতর হয়েছে।
১৮৩৪—৪৩
নবীন—প্রবীণদের এই দ্বন্দ্ব—বিরোধের তীব্রতা তিরিশের শেষদিক থেকে চল্লিশের মধ্যে অনেকটা কমে যায়। তারুণ্যের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের চূড়া থেকে ‘ইয়াং বেঙ্গল’ ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন। তারুণ্যের নভশ্চারী স্বপ্ন যৌবনে বাস্তবমুখী হতে থাকে। আর্থনীতিক বা রাজনৈতিক অভিযোগের সঙ্গে যেহেতু ‘ইয়াং বেঙ্গল’—এর বিদ্রোহের কোনও সম্পর্ক ছিল না, প্রধানত মানসলোকের কতকগুলি সামাজিক ভাবমূর্তির সঙ্গে তার গভীর সংযোগ ছিল, সেইজন্যও খানিকটা তাঁদের আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস হঠাৎ শীর্ষে পৌঁছে প্রচুর বুদবুদ সৃষ্টি করে, দ্রুত ছোট ছোট ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়ে।
মধ্যে মধ্যে পাদরিদের দু—একটি বক্তৃতা ছাড়া তখন মাঠে—ময়দানে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতাদির প্রচলন হয়নি। সামাজিক বিষয় নিয়ে এরকম প্রকাশ্য সভায় বিতর্ক বা আলোচনা বর্তমানকালেও হয় না। জনসভার প্রধান আলোচ্য বিষয় রাজনীতি। তখন সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, জীবনদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও আলোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল নানা রকমের বিদ্বৎসভা। নবযুগের সন্ধিক্ষণে ইংলন্ড ও ইউরোপে, নতুন জ্ঞানবিদ্যার আলোক বিচ্ছুরিত হবার পর সমাজে এরকম বিদ্বৎসভার পর্যাপ্ত বিকাশ হয়। বিদ্বৎসভা প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ছিল, কিন্তু তার রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক যুগের বিদ্বৎসভার পার্থক্য অনেক। সামাজিক ইতিহাসবিদরা বলেন :৪১
“…the world had not known until the eighteenth century any societies organised for collective thinking and discussion. There had been religious sects, guilds or merchants and artisans, colleges of doctors and parliaments of lawyers; but there had never been… anything like societies, let alone a whole network of societies, for the avowed purpose of collective thinking and talking.”
স্বাধীন ব্যক্তিচিন্তার প্রাথমিক স্ফূর্তির মধ্যেই আধুনিক সভাসমিতিতে সমষ্টিচিন্তা ও বিতর্কের উদ্ভব হয়। ইংলন্ড—ইউরোপের ইতিহাসেও তাই দেখা যায় :৪২
“Closely connected with the growth of education and enlightenment among the younger generations of merchants is the creation of Literary and Philosophical Societies in the leading mercantile towns. …societies of this type became centres of reforming zeal as well as of literary and philosophic illumination.”
বাংলাদেশে প্রধানত আধুনিক শিক্ষিত গোষ্ঠীর দিক থেকে এই বিদ্বৎসভা গঠনের তাগিদ আসে এবং নবজাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা শহরেই সেগুলি স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররাই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রেরণা সঞ্চার করেন। আলেকজান্ডার ডাফ লিখেছেন :৪৩
“New societies started up with the utmost rapidity in every part of the native city. There was not an evening in the week, on which one, two or more of these were not held; and each individual was generally enrolled a member of several. Indeed, the spirit of discussion became a perfect mania; and its manifestation, both in frequency and variety, was carried to prodigious excess…”
তিরিশের কথা। বাস্তবিক উনিশ শতকের তিরিশে বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠায় বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। কতকগুলি উল্লেখ্য সভার নাম করছি :
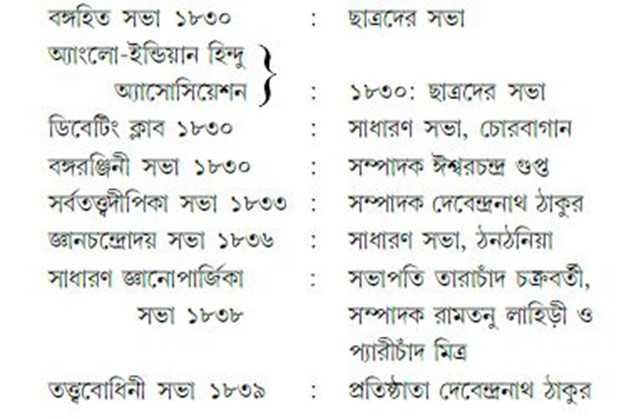
এ ছাড়া ছোট ছোট আরও অনেক সভা স্থাপিত হয়েছিল। একটি দশকের মধ্যে এতগুলি বিদ্বৎসভার বিকাশ থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় যে বিগত শতকের তিরিশে একশ্রেণির বাঙালির মনের আকাশ একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আলোয় হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এই আলো স্বাধীন চিন্তা, যুক্তি ও বুদ্ধির আলো। ‘ইয়াং বেঙ্গল’ গোষ্ঠী একহাতে ব্র্যান্ডি এবং আর—এক হাতে বই নিয়ে এই আলোর মশাল জ্বালিয়েছিলেন। বেকন, হিউম প্রমুখ মনীষীদের দার্শনিক বই ছাড়াও, টম পেইনের (Tom Paine) দু—খানি বিখ্যাত বই ‘Rights of Man’ ও ‘The Age of Reason’ তরুণদের চিন্তাবিপ্লবের খোরাক জুগিয়েছিল সবচেয়ে বেশি, বিশ শতকে কার্ল মার্কসের চিন্তাধারার প্রভাবের সঙ্গে কতকটা তুলনা করা যায়। ডাফ লিখেছেন যে টম পেইনের বইগুলি “were abundantly supplied” এবং আমেরিকার একজন পুস্তক ব্যবসায়ী, ডাফের ভাষায়, “basely taking advantage of the reported infidel leaning of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars”—কলকাতায় এক জাহাজ ভরতি বই পাঠিয়ে দেন। টম পেইনের যুগান্তকারী বই দু—খানিকে ডাফ মনে করতেন “The most malignant and pestiferous of all anti-Christian publications”—কারণ টম পেইন তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে মানুষের ঈশ্বরমুখী চিন্তাধারাকে আত্মনির্ভর ও মানবমুখী করতে চেয়েছিলেন।৪৪
‘ইয়াং বেঙ্গল’ বাংলা দেশে যে নতুন সমাজমুখী ও মানবমুখী চিন্তার আলো জ্বালিয়েছিলেন, কলকাতা শহরের বহু বিদ্বৎসভায় তারই স্পর্শে একে একে অনেক জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। তিরিশের মধ্যেই কয়েকটি প্রদীপের শিখা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’ (১৮৩৮) ও ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র (১৮৩৯) ভিতর দিয়ে। নব্যচিন্তার মূলভিত্তি ক্রমে প্রসারিত হচ্ছিল এবং তার তারুণ্যের অসংযত উদ্দামতাও ক্রমে শান্ত সংযত হয়ে আসছিল। তিরিশের শেষদিক থেকে এই দুটি বিদ্বৎসভা নব্যচিন্তার এই রূপায়ণের প্রধান সহায় হয়। ‘জ্ঞানোপার্জিকা সভা’ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম ও কর্মের যোগসাধনে আরও অনেকটা এগিয়ে যায়। উনিশ শতকের চারের দশকটিকে বলা যায় ‘তত্ত্ববোধিনী যুগ’।
তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে—এই পাঁচজনের স্বাক্ষরিত একটি প্রচারপত্রে ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’র (Society for the Acquisition of General Knowledge) উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলা হয় যে ছাত্রজীবনের পর তরুণরা যখন বাইরের সমাজে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনের প্রয়োজন আর বিশেষ বোধ করেন না, জ্ঞানের অঙ্কুরগুলি ফল—ফুলের গাছপালায় পরিণত হয় না। কাজেই এমন একটি বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন “which should be the means of promoting frequent mutual intercourse among the educated Hindus and of exciting an emulation for mental excellence.” সভায় সকল রকমের বিষয় নিয়ে আলোচনা হত—ভূগোল সংস্কৃতি বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য শিক্ষা সমাজনীতি, এমনকী রাজনীতি পর্যন্ত, কোনও বিষয় বাদ যেত না।৪৫
‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র যুগে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ‘জ্ঞানোপার্জিকা সভা’ প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় বছরের মধ্যে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় (৬ অক্টোবর ১৮৩৯)। প্রথমে নাম ছিল ‘তত্ত্বরঞ্জিনী সভা’, পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রস্তাবে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ নাম হয়। সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দান হল রামমোহনের পর মৃতকল্প ও প্রায়বিস্মৃত ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবনদান এবং একটি বিশেষ মূলনীতির উপর ‘ব্রাহ্মধর্ম’ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু শুধু যদি ‘ব্রাহ্মধর্ম’ প্রচার অথবা বেদান্ত আলোচনা ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র কাজ হত, তাহলে ১৮৩৯ সালে মাত্র দশজন সভ্য নিয়ে যে সভা স্থাপিত হয়েছিল, সেই সভার সভ্যসংখ্যা ১৮৪১—৪২ সালের মধ্যে ৫০০ পর্যন্ত হত না। আরও কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনীর সভ্যসংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত হয়।৪৬ তত্ত্ববোধিনীতে ধর্মতত্ত্বের আলোচনারও বিশেষত্ব ছিল, গোঁড়ামির কোনও সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত না। তা থাকলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তর মতো বেদ—বেদান্ত বা যে—কোনও শাস্ত্রীয় বচনের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী ব্যক্তির স্থান হত না সভায়। ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও, সাহিত্য ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হত। সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধির গতি থেকে বোঝা যায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র প্রতি কত দূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আকর্ষণের কারণ, উনিশ শতকের চল্লিশ থেকে নবযুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা পূর্বদশকের বয়ঃসন্ধির চিত্তবিক্ষেপ ও বুদ্ধিবিভ্রম কাটিয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডিও প্রসারিত হচ্ছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রথম সংঘাতের ফেনোচ্ছ্বাস কেটে গিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মনে দেশকালপাত্রবোধসম্ভূত একটা আদর্শ—সমন্বয়ের ইচ্ছা জাগছিল। স্বদেশের প্রতি অবজ্ঞা, স্বজাতিধর্মের প্রতি বৈরাগ্য ও বিতৃষ্ণা, প্রাচীন ও প্রবীণের প্রতি অশ্রদ্ধা—নব্যশিক্ষিতদের এই নাস্তিবাচক মনোভাবেরও ক্রমে পরিবর্তন হচ্ছিল। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ এই পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।
সভার সঙ্গে একটি পাঠশালা স্থাপন করা হয় ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’ (জুন ১৮৪০)। হিন্দু কলেজের ধর্মহীন শিক্ষার প্রতি রামমোহনের আস্থা ছিল না, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথও সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেই অভাব পূরণ করার জন্য রামমোহন যে বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮২৬), তারই নবপরিকল্পনা ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’। পাঠশালা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হল, ইংরেজি ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রিস্টধর্মকে পৈতৃক ধর্ম বলে গ্রহণ করার প্রবৃত্তি দমন করা এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ধর্ম দর্শন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও আলোচনা করা। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি উপায় হল এই পাঠশালা, দ্বিতীয় উপায় হল ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ (আগস্ট ১৮৪৩)। পাঠশালা প্রথমে কলকাতা শহরে স্থাপিত হয়, কিন্তু কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারে তখন ধর্মশিক্ষা ও বাংলা শিক্ষা কোনওটার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, কারণ ধর্ম বা বাংলা কোনওটাই অর্থকরী শিক্ষা নয়। পাঠশালা তাই কলকাতায় চলল না, বাঁশবেড়িয়া গ্রামে (হুগলি) স্থানান্তরিত হল। অক্ষয়কুমার দত্ত পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং এই দুটি বিষয়ে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বাঁশবেড়িয়া পাঠশালায় শিক্ষক নিযুক্ত হন শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ। রামগোপাল ঘোষ হন পাঠশালার পরিদর্শক। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ যখন প্রকাশিত হয়, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত হন তার সম্পাদক। তত্ত্ববোধিনী যুগের মধ্যমণি যদি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা যায়, তাহলে অক্ষয়কুমার দত্তকে বলা যায় তার সর্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’য় এবং ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র পেপার—কমিটিতে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার এই দু—জনের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ হতে থাকে। ব্রাহ্মধর্মের মূলনীতি ও স্বরূপ নির্ণয় থেকে আরম্ভ করে পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি নির্বাচন পর্যন্ত ব্যাপারে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ক্রমে বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। মতামতের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের প্রধান সমর্থক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র সভ্য ছিলেন, পরে সম্পাদক হন; ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র পেপার—কমিটিরও তিনি একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। দেবেন্দ্রগোষ্ঠী ও অক্ষয়গোষ্ঠী মতামতের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তত্ত্ববোধিনীর যুগে শিক্ষিত বাঙালির মননক্ষেত্রে প্রসারিত হতে থাকে।
১৮৪৩ সাল—৯ ফেব্রুয়ারি মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন; ২০ এপ্রিল ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি’ স্থাপিত হয়; পঞ্চম আইন দ্বারা (১৮৪৩) ভারতবর্ষে দাস কেনা—বেচার প্রথা বেআইনি ঘোষিত হয়; ১৬ আগস্ট ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়; ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ ১৭৬৫ শক) বৃহস্পতিবার, দেবেন্দ্রনাথ কুড়িজন বন্ধুসহ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। এগুলি বড় বড় ঘটনা এবং প্রত্যেকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই বছরে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম বিলেতযাত্রার পর (৯ জানুয়ারি ১৮৪২) কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আসেন ইংলন্ডের ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি’র অন্যতম সভ্য, প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সমাজসংস্কারক জর্জ টমসন (George Thompson)। টমসন শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁর প্রেরণায় ও ইয়াং বেঙ্গলের উদযোগে ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি’ স্থাপিত হয়। মধুসূদন দত্তর ধর্মান্তরে বাঙালি হিন্দুসমাজে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়, এগারো বছর আগে কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তরের সঙ্গে তার কতকটা তুলনা করা যায়। অল্পদিনের মধ্যেই তত্ত্ববোধিনী—গোষ্ঠীর সঙ্গে খ্রিস্টান পাদরিদের প্রচণ্ড সংঘাত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা করে।
‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হবার কয়েক মাস পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ‘আত্মজীবনী’তে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন :
”তত্ত্ববোধিনী সভা প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে এই আর একদিন। ১৭১৬ শক হইতে (১৮৩৯ সাল) ক্রমে ক্রমে আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?”
দীক্ষাগ্রহণের সময় আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সামনে দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিবেদন করেন : ”যাহাতে পরিণত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুক্ত করুন।” বিদ্যাবাগীশ বলেন, ”রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।” দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দীক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, ”ব্রাহ্মসমাজে এ একটা নতূন ব্যাপার। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।”
ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তির ঐতিহাসিক তাৎপর্য গভীর। ‘ব্রাহ্মসমাজ’ রামমোহন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু ‘ব্রাহ্মধর্ম’ নামটি রামমোহন—প্রবর্তিত নয়, এবং এরকম কোনও পৃথক ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তোলার পরিকল্পনা আদৌ রামমোহনের ছিল কি না সন্দেহ। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম মূলত ব্রাহ্মধর্ম হলেও তখন ‘বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম’ নামেই তা অভিহিত হত। অবশ্য রামমোহন তাঁর রচনায় একাধিকবার ‘ব্রাহ্ম’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। যে বিষয় প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয়, পৌত্তলিকতাবর্জিত এক ও অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের উপাসনায় যাঁরা প্রবৃত্ত হবেন, ভবিষ্যতে তাঁরাই ‘ব্রাহ্ম’ নামে অভিহিত হবেন, এরকম একটা ধারণা হয়তো তাঁর মনে ছিল। রামমোহনের সেই ধারণাকেই দেবেন্দ্রনাথ বাস্তব রূপ দেন। আচার্য বিদ্যাবাগীশ এইজন্যই বলেছিলেন যে রামমোহনের ইচ্ছা এতদিন পরে পূর্ণ হল, যে আগে ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হল। দেবেন্দ্রনাথের সময়ে কিছুকাল ‘বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম’ কথাটি প্রচলিত ছিল। ২৮ মে ১৮৪৭ (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৯ শক) ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র অধিবেশনে এই নামের পরিবর্তে ‘ব্রাহ্মধর্ম’ নামটি গ্রহণ করা হবে সিদ্ধান্ত করা হয়।
ব্রাহ্মধর্মে ‘দীক্ষা’ গ্রহণ করাকে দেবেন্দ্রনাথ ‘ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার’ বলেছেন। কেন বলেছেন? আগে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময় যাঁরা সমবেত হতেন তাঁদেরই ব্রাহ্মধর্মানুরাগী মনে করা হত। কিন্তু তা মনে করার কোনও সংগত কারণ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে অনেকে নিছক কৌতূহলবশে উপস্থিত হতেন, এমনকী ব্রাহ্মসমাজ—বিরোধী গোঁড়া হিন্দুরাও কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য আসতেন। তা ছাড়া সপ্তাহে একদিন বা দু—দিন উপাসনার কেউ যোগ দিলেই যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ বা আনুগত্য প্রকাশ পাবে এমন কোনও কথা নেই। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট নৈতিক বন্ধন ছিল না। সেই কারণে রামমোহনের কালে, এবং পরে তাঁর অবর্তমানে, ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত অনুবর্তীদের মধ্যে একটা নৈতিক বিশৃঙ্খলা ও দৌর্বল্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাঁদের প্রচারিত ধর্মাদর্শের সঙ্গে আচরিত কর্মজীবনের, অথবা প্রাত্যহিক ব্যাবহারিক জীবনের কোনও সংযোগ ও সামঞ্জস্য ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্বলতা দূর করার জন্যই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষার প্রবর্তন করেন এবং উদ্দেশ্য ও আচরণের মধ্যে সুদৃঢ় সেতুবন্ধনের জন্য কতকগুলি অবশ্যপালনীয় বিধিবিধানও রচনা করেন। এই নিয়মানুবর্তিতার বন্ধনে, দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে একটি ‘বিশিষ্ট সমাজ’ হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মধর্মীরা প্রায় একটি স্বতন্ত্র ধর্মগোষ্ঠীতে পরিণত হন। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের এই নবরূপান্তরিত পর্বের প্রচারক ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ ও সংগঠক ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’। মৃতকল্প ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’।
১৮৪৪—৫৯
উনিশ শতকের চল্লিশে বাঙালি সমাজের একটা বড় সমস্যারূপে দেখা দিল হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিদের ব্যাপক অভিযান। তিরিশের তুলনায় চল্লিশের এই অভিযানের গুরুত্ব একাধিক কারণে অনেক বেশি। খ্রিস্টান পাদরিরা যখন দেখলেন যে ব্রাহ্মসমাজ শুধু একটি ‘সমাজ’ নয়, বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত একটি ‘ধর্মের’ মুখসংস্থা হয়ে উঠেছে, তখন তাঁরা বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। তা ছাড়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিদের নিন্দাবাদের প্রধান কারণগুলি ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র সংযোগে নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজ যখন অপসারণের সংকল্প করেন, তখন পাদরিদের বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। ১৮৪৩ সালের রূপান্তরের পরেও ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যানের মধ্যে কতকগুলি আপাতবিরোধ ও অসংগতি থেকে যায়। এই বিরোধ ও অসংগতিকে সরাসরি আক্রমণ করে পাদরিরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় এই বাদ—প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য প্রকাশিত হয় (১৮৪৫)। বাদ—প্রতিবাদের ভিতর দিয়ে একদিকে ব্রাহ্মসমাজের উপকার হয় এই যে ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ ব্রাহ্মদের ঘোলাটে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়।
ব্রাহ্মধর্ম ছিল বেদান্ত—প্রতিপাদ্য ধর্ম। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রবর্তন করলেও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই বেদের অভ্রান্ততা নিয়ে যেমন তাঁর খ্রিস্টান প্রতিপক্ষদের সঙ্গে বাদানুবাদ চলতে লাগল, তেমনই অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ তাঁর সহযোগীদের সঙ্গেও মতবিরোধ দেখা দিল। দেবেন্দ্রনাথের যুক্তির প্রতিবাদ শুধু পাদরিরাই যে করতেন তা নয়, অক্ষয়কুমারের মতো ঘোর যুক্তিবাদী লেখকদের পত্রেও দেবেন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ করা হত। তখন ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ‘পেপার কমিটি’তে অক্ষয়পন্থীদের সংখ্যাই ছিল বেশি, কাজেই দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এই সময় খ্রিস্টান প্রতিপক্ষদের সামলাতে গিয়ে নিজের গোষ্ঠী ও ঘর সামলানোই দায় হয়ে উঠল। দলের ভিতরে মতভেদ হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথ বেদের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটনের জন্য আরও তিনজন ছাত্রকে কাশীতে পাঠান এবং নিজেও পরে কাশীতে গিয়ে বেদ বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তা সত্ত্বেও বেদ—বেদান্তের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলাতে সময় লেগেছিল। এই সময় আলেকজান্ডার ডাফ সাহেবের লেখা India and India Missions (১৮৪০) গ্রন্থ এ দেশে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে ডাফ সাহেব হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধে কুৎসিত কটাক্ষ ও নিন্দাবাদ করেন। এই গ্রন্থের বক্তব্য সমর্থন করে কলকাতার অন্যান্য খ্রিস্টান পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আরও অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় তার প্রতিবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।৪৭ এই ইংরেজি বাদানুবাদের মধ্যে বেদান্তকে দেবেন্দ্রনাথ ‘Revelation’ অর্থাৎ ঈশ্বর—প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘আত্মচরিত’ লিখেছেন : ”ইংরাজী ১৮৪৮—৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কি না ইহা সর্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।” রাজনারায়ণ বসু এখানে যে সালতারিখ নির্দেশ করেছেন তা ১৮৫৪—৫৭ হলে ঠিক হয়। তাঁর Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj পুস্তিকা পাঠ করলেও ব্রাহ্মদের এই বিশ্বাসের কথা জানা যায়। এই বিশ্বাস বর্জন করতে যেমন খ্রিস্টান পাদরিরা পরোক্ষে ব্রাহ্মদের সাহায্য করেন, তেমনই প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেন তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ সত্যানুরাগী যুক্তিবাদী ডিরোজিয়ানদের এবং অক্ষয়কুমার দত্তর মতো বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তানুরাগীদের।
১৮৪৬ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বেদ—উপনিষদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তের ঈশ্বর—প্রত্যাদিষ্ট ব্যাখ্যা বর্জন করেন। ব্রাহ্মধর্মের এই ঐতিহাসিক রূপান্তরে অক্ষয়কুমারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন : ”অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন।”৪৮ বাস্তবিকই তা—ই। শিবনাথ শাস্ত্রী পরিষ্কার করে সে কথা লিখেছেন :৪৯
”ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। …তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন না।… সুতরাং তাঁহাকে বেদান্তধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।”
১৮৪৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থ প্রথম সংকলন করেন, ১৮৪৯—৫০ সালের মধ্যে বইখানি বাংলা দেশে প্রচারিত ও সমাদৃত হয়। ১৮৫১ সালের মাঘোৎসবে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজ থেকে ঘোষণা করা হয় যে বেদ—বেদান্ত ঈশ্বর—প্রত্যাদিষ্ট নয় এবং ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রও নয়। স্মরণীয় ঘটনা হল, অক্ষয়কুমার তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন, অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে অক্ষয়কুমারের দানের গুরুত্ব যে কত বেশি তা এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায়।
খ্রিস্টান পাদরিদের সঙ্গে আদর্শ—সংঘাতে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মবিহীন শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধেও খুব চিন্তিত হন। হিন্দু কলেজের এই শিক্ষার প্রতি রামমোহনও সন্তুষ্ট ছিলেন না, তার জন্য তিনি আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল তা—ই। কিন্তু ডাফ সাহেবের ধর্মান্তরের অভিযান যখন হিন্দু বালক—বালিকাদের দিকেও চালিত হল, তাঁর স্কুলের চোদ্দো বছরের বালক উমেশচন্দ্র সরকার ও তার এগারো বছরের বালিকাবধূকে যখন তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিলেন (এপ্রিল ১৮৫৪), তখন দেবেন্দ্রনাথ খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন। পাদরিদের দৃষ্টি যদি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত ধাবিত হয় তাহলে উৎকণ্ঠা ও উদবেগ স্বাভাবিক। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : ৫০ ”অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খ্রীস্টান করিতে লাগিল! তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’তে প্রকাশ হইল।” পত্রিকাতে অক্ষয়কুমার লেখেন :৫১
”অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না। আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ—নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব। ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এদেশে যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল!… অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতির প্রতীক্ষা কর এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারীদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ।”
অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়ি করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁদের অনুরোধ করেন যেন হিন্দুসন্তানের আর তাঁরা পাদরিদের বিদ্যালয়ে না পাঠান এবং নিজেদের একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এই সময় ধর্মসভা, ব্রাহ্মসভা ও ডিরোজিয়ান গোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হন। ২৫ মে ১৮৪৫ একটি বড় সভা ডাকা হয়, তাতে প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত হন। পাদরিদের বিদ্যালয়ে যেমন বিনা বেতনে ছেলেরা পড়তে পারে, তেমনি বিনা বেতনে হিন্দুর ছেলেদের শিক্ষার জন্য ‘হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়’ স্থাপনের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। সেইদিনই চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : ”সেই অবধি খ্রিস্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারীদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।৫২
১৮৪৬ সালের গোড়ায় রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি ‘আত্মচরিত’—এ লিখেছেন :৫৩ ”যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল; কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে।” এটা ইয়াং বেঙ্গলের আবির্ভাবকালের (১৮৩০—এর) প্রগতিবাদের লক্ষণ, বোঝা যায় পরবর্তী দশকে তরুণ ব্রাহ্মরাও কিছুটা প্রগতিবাদের এই উপসর্গ মেনে চলতেন। ইয়াং বেঙ্গলও সেই সময় নীতি ও আদর্শের দিক থেকে ব্রাহ্মসমাজের সহযাত্রী ছিলেন, তাঁরা তখন পরিণত যুবকগোষ্ঠী, তরুণ ব্রাহ্মরা বোধহয় তাই কিছুটা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের অনুশীলন ও প্রচারকার্যে পরে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম সহযোগী হন, অক্ষয়কুমারের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু। ব্রাহ্মসমাজের কাজও এই সময় থেকে বেড়ে যায়।
‘হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়’ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ একটু বেশি আশান্বিত হয়েছিলেন, কারণ খ্রিস্টান পাদরিদের ধর্মান্তরের অভিযান তাতে বিশেষ মন্দীভূত হয়নি। বরং কিছুদিনের মধ্যে গভর্নমেন্ট একটি আইন পাশ করে পাদরিদের এই অভিযানের পথ আরও সুগম করে দেন। আইনটি Lex Loci বা স্বধর্মত্যাগী এ দেশি খ্রিস্টানদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারের আইন। এই আইন পাশ হবার পর হিন্দুসমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, এবং আইনের বিরুদ্ধে আবেদনও করা হয়। কিন্তু ‘সংবাদ প্রভাকর’ অভিযোগ করেন যে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা এই প্রতিবাদ—আন্দোলনে বিশেষ যোগদান করেননি : ”এই স্থলে প্রকাশ্যরূপে উল্লেখ করিতে একত্রে লজ্জা এবং দুঃখের উদয় হইতেছে, ‘লেক্সলোসি’ আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের মধ্যে কেহই তাহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। কেহই এক কপর্দক সাহায্য করেন নাই।”
এরপরেই ‘প্রভাকর’ লিখেছেন যে পাদরিদের দৌরাত্ম্য অনেক বেড়েছে এবং কিছুদিন আগে মিশনারি স্কুলে হিন্দুর ছেলেদের না—পাঠানোর জন্য সভা করে যে স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল তাতে কোনও ফল হয়নি। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার পর মিশনারিদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে বলে যে অনুমান করেছিলেন তা সত্য নয়। মিশনারিদের উপদ্রব তার জন্য আদৌ কমেনি, বরং বেড়ে গিয়েছিল। হিন্দুসমাজে কেন মিশনারিরা ধর্মান্তরিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং কেনই বা হিন্দুরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ই সবিস্তারে আলোচনা করেন (১৮৫৪)।৫৪ তত্ত্ববোধিনী বলেন যে ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে কোনও ধর্মকে অন্য ধর্মের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তত্ত্ববিচারে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে প্রচারকরা মাথা ঘামান, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তা চিন্তনীয় বিষয় বলে মনে করেন না। তাহলে হিন্দুদের খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ কী? কেউ যদি যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ—প্রয়োগ অনুসন্ধান করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁকে নিবৃত্ত করা কঠিন হত না। কিন্তু সাধারণত কেউ সেভাবে খ্রিস্টান হন না। তত্ত্ববোধিনীর মতে হিন্দুদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের একটি কারণ হল ‘গৃহ—কলহ’। পিতা—মাতা বা পরিবারের কারও সঙ্গে কলহ হলে অনেকে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে মিশনারিদের আশ্রয় নেন এবং মিশনারিরা যত শীঘ্র সম্ভব তাঁদের ”নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন।” দ্বিতীয় কারণ হল ‘দারিদ্র্য’। ”স্থলবিশেষে দৈন্যদশা এতদ্দেশীয় লোকের খ্রীস্টীয় ধর্ম গ্রহণের… কারণ বলিয়া অবশ্যই গণ্য করিতে হইবে।” আর—একটি কারণ হল ”আমারদিগের অশেষ দোষাকর দেশাচার সমুদয়।” তত্ত্ববোধিনী লিখেছেন : ”ইদানীন্তন সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হন, গৃহমধ্যে তাহার বিপরীত ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া অসহ্য ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন। একমাত্র খ্রীস্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিলেই এই সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এই বিবেচনায় অনেকে তাহাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছেন।” ‘কলঙ্ক ও নিগ্রহ ভয়’ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের আর—একটি কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও ধর্মাচরণের বিরোধিতা করে অনেকে নিগ্রহ ও কলঙ্কের ভয়ে সমাজ ও পরিবার ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মের আশ্রয় নেন।
হিন্দুদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের যে কারণ বিশ্লেষণ করেছেন ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, তা তৎকালের হিন্দুসমাজ ও হিন্দু পরিবারের দিক থেকে বিচার করলে যুক্তিসংগত মনে হয়। গৃহ—কলহের কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তরুণ—প্রবীণে সংঘাত, অর্থাৎ ইংরেজি—শিক্ষিত তরুণদের সঙ্গে সেকালের প্রবীণ অভিভাবকদের মতবিরোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ‘দারিদ্র্য’ একটি বড় কারণ এবং তার ফলে সাধারণত মিশনারিদের হিন্দুসমাজে নিম্নবর্ণের লোকদের ধর্মান্তরিত করার সুযোগ হয়েছে। ‘দেশাচার’ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এবং নিন্দনীয় দেশাচারের প্রতি যেমন উচ্চসমাজের শিক্ষিত তরুণদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে, তেমনি নিম্নস্তরের উপেক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসমাজে বিদ্রোহের মনোভাব জেগেছে। উভয় স্তরেই সুবর্ণসুযোগ হয়েছে মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার। তখনকার হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির কথা ভাবলে ‘কলঙ্ক ও নিগ্রহভয়ে’ দেশাচার—বিরোধীদের সমাজ—পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে স্বধর্মত্যাগী হওয়া বাস্তব সত্য বলে মনে হয়। তবে এই কারণগুলির মধ্যে ‘দারিদ্র্য’ই প্রধান কারণ এবং তার জন্য বাংলার হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত বর্ণ—স্তরে বেশি ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান দেখা যায়। নদিয়া চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলায় এ দেশীয় খ্রিস্টানবহুল অঞ্চলের প্রত্যক্ষ সামাজিক সমীক্ষা করলে আজও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।
চল্লিশের শেষদিক থেকে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার চেতনা ও আন্দোলন কিছুটা প্রসারিত হতে থাকে। এর মধ্যে ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের যে বিকাশ হয় (১৮১৭—৪৯) তা নিতান্ত নগণ্য নয়। প্রধানত তাঁদেরই উৎসাহে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত সূচনা এই সময় থেকে হয়। তার আগে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার আরম্ভ হয় এবং কতকগুলি স্কুলও স্থাপিত হয় কলকাতায়। কলকাতা শহরের বাইরে উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদযোগী হন (১৮৪৫)। ১৮৪৭ সালে বারাসাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়টি সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দুদের উদযোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলা দেশে প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার, বারাসাতের স্বনামধন্য কালীকৃষ্ণ মিত্র ও তাঁর ভাই নবীনকৃষ্ণ মিত্র এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম।
শোনা যায়, শিক্ষাসংসদের সভাপতিরূপে বেথুন বারাসতে যান বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। কলকাতায় এরকম একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেরণা তিনি নাকি বারাসত থেকে পান। বছর দুই পরে বেথুন কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (৭ মে ১৮৪৯)। প্রথমে এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’, পরে ১৮৫১ সালে বেথুনের মৃত্যুর পর নাম হয় ‘বেথুন স্কুল’। সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েরা এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখবে এই ছিল বেথুনের ইচ্ছা। তিনি হিন্দুসমাজের বড় বড় কর্ণধারদের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও শলাপরামর্শ করা প্রয়োজনবোধ করেননি, অথবা মিশনারিদের সহযোগিতা চাননি। বরং সেকালের দু—একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে এই ব্যাপারে গোড়া থেকেই স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করেছিলেন, যেমন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকার ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্কুল প্রতিষ্ঠার পরে বেথুন বিদ্যাসাগরকে অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্বগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন, বিদ্যাসাগর সম্মত হন (ডিসেম্বর ১৮৫০)। দূর থেকে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে আসার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যাসাগর গাড়ির গায়ে একটি শাস্ত্রবচন খোদাই করে দেন—’কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ’। এর অর্থ হল—”পুত্রের মতো কন্যাকেও যত্ন করে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে।” বেথুনের এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম ২১ জন ছাত্রীর মধ্যে দু—জন হলেন পণ্ডিত মদনমোহনের দুই কন্যা ভুবনবালা ও কুন্দমালা। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন ছাড়া বেথুন সাহেবকে যাঁরা অকুতোভয়ে এই কাজে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইয়াং বেঙ্গলের মুখপাত্র রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এতদিন পর্যন্ত কোম্পানির ডিরেক্টররা ও তাঁদের ভারতীয় প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে একরকম উদাসীন ছিলেন। বেথুনের চেষ্টা সার্থক হবার পর তাঁরা এই মনোভাব পরিত্যাগ করেন। স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনও এই সময় থেকে বাংলা দেশে ক্রমে ব্যাপক ও শক্তিশালী হতে থাকে।৫৫ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে শিক্ষিত সমাজে ও তার বাইরে রীতিমতো বিতর্ক ও আলোচনা আরম্ভ হয়। ইয়াং বেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজ ও ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র পক্ষ থেকে কেবল যে ইংরেজি—শিক্ষিতরাই স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন তা নয়, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও কয়েকজন স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে নানাভাবে আন্দোলন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের কথা আগে বলেছি। আরও একজন বাঙালি পণ্ডিত উদার সমাজসংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রবক্তা ছিলেন, তিনি গৌরীশংকর তর্কবাগীশ। পণ্ডিতদের মধ্যে আরও কেউ কেউ প্রগতিশীল সমাজচিন্তা করতেন, কিন্তু গৌরীশংকরের মতো নির্ভয়ে সেই চিন্তা সমাজজীবনে প্রয়োগ করতে আর কেউ অগ্রসর হয়েছেন কি না সন্দেহ। রামমোহনের সহমরণ নিবারণ আন্দোলনে গৌরীশংকর সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ইয়াং বেঙ্গলের সঙ্গেও তিনি নানাভাবে সহযোগিতা করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি এই কথা উল্লেখ করে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকায় লেখেন (২৫ মে ১৮৪৯) :
”সহমরণ পক্ষাবলম্বী পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আমারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না, মানব কোথায় আছেন…।”
এই কথা বলে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, ”সহস্র সহস্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্য কহিব…।” অনেকটা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপাদান দিয়ে গঠিত ছিল পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের চরিত্র।
ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যে সকলের দৃষ্টি কিন্তু কুসংস্কারের কুয়াশামুক্ত ছিল না। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ইংরেজিবিদ্যায় সুশিক্ষিত, ‘হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার’ পত্রিকার সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ। কাশীপ্রসাদ ইংরেজি রচনায় দুরন্ত ছিলেন, বেশ ভালো ইংরেজি কবিতাও লিখতে পারতেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনে তিনি গোঁড়া প্রাচীনপন্থীদের দলে ভিড়ে তার বিরুদ্ধে তাঁর ইংরেজি পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এবিষয়ে পণ্ডিত গৌরীশঙ্করের সঙ্গে কাশীপ্রসাদের রীতিমতো মসীযুদ্ধ চলে।৫৬
উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা দেশে সমাজসংস্কার আন্দোলন স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করে। রামমোহনের সহমরণ নিবারণ আন্দোলনের পর (১৮২৯—৩০) এরকম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন আর হয়নি। লক্ষণীয় হল, দুটি আন্দোলনই স্ত্রীজাতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে—সহমরণ নিবারণ ও স্ত্রীশিক্ষা—দুই। স্ত্রীশিক্ষার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও যে দু টি আন্দোলন এই সময় আরম্ভ হয় (১৮৫৫—৫৬)—বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণের জন্য—তা—ও স্ত্রীজাতিকে কেন্দ্র করে। নবযুগের বাঙালির সমাজসংস্কারের ধারার মধ্যে এই সংগতি কি আকস্মিক, না ঐতিহাসিক, না আত্মিক? বাংলা দেশ মাতৃরূপে শক্তিসাধনার দেশ। মাতৃধ্যান, মাতৃচিন্তা ও মাতৃকাতরতার মধ্যে বাঙালির আত্মিক রূপটি যেমন প্রকট হয়ে ওঠে, তেমন আর অন্য কিছুতে হয় না। ‘মা’ বাঙালির মর্মমূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই দেখা যায়, সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই বাঙালি শক্তিস্বরূপা মাতৃচিন্তার উৎস থেকেই অনুপ্রাণনা আহরণ করেছে সবচেয়ে বেশি। নবযুগের বাংলার নবজাগরণের প্রথম পথিক রামমোহন রায় যে তন্ত্রশাস্ত্রানুশীলনে গভীর অনুরাগী ছিলেন এবং কুলাবধূত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তাঁর গুরু ছিলেন, এ শুধু তথ্যমাত্র নয়, একটি জাতীয় তত্ত্বও বটে।৫৭ তাঁর পরবর্তীকালের যোগ্যতম উত্তরসূরি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তন্ত্রশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, এবং তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অনন্যসাধারণ, হিন্দুসমাজের অন্যায়—অবিচার—ব্যভিচার ও কুসংস্কারগুলি তাই মনে হয় বাংলার মাতৃমূর্তির মালিন্যের মধ্যে সর্বাগ্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই মনে হয় সমাজের মানবগোষ্ঠীর উপেক্ষিত ও নির্যাতিত অর্ধাঙ্গ (স্ত্রীজাতি) যে বাঙালিকে (হিন্দু) সামাজিক কুসংস্কারমুক্তি ও অগ্রগতির আন্দোলনে প্রেরণ সঞ্চার করেছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।
বেথুন শুধু স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতিক্ষেত্রেও নতুন জাতীয়তাবোধের প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন, ‘কালা আইন’ বা ‘Black Acts’—এর পরিকল্পক ও রচয়িতা হিসেবে। তখন বেথুন ছিলেন বড়লাটের আইনসচিব। ১৮৪৯ সালে তিনি আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে ভারতীয়—ইয়োরোপীয়দের পারস্পরিক বৈষম্য দূর করার জন্য চারটি আইন খসড়া করেন। আইনগুলি এই : মফস্সলের ফৌজদারি আদালতে ইয়োরোপীয়দের অপরাধের বিচার হতে পারবে, ইয়োরোপীয়দের অধিকারের একটা সীমা থাকবে, বিচারের সময় জুরি নিয়োগ করা চলবে, এবং বিচারবিভাগে অফিসারদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করতে হবে। এই আইনগুলি যে এ দেশে ইয়োরোপীয়দের মাত্রাহীন অধিকারবোধ এবং শাসকশ্রেণিগত ঔদ্ধত্য ও দম্ভ সংযত করার উদ্দেশ্যে রচিত তা বোঝা যায়। স্বভাবতই তাই ইংরেজরা এই আইনের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং শ্বেতাঙ্গ—কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্যবোধ থেকে এগুলিকে ‘কালা আইন’ বলে বাতিল করার জন্য রীতিমতো আন্দোলন করতে থাকেন। এরকম প্রত্যক্ষ জাত্যভিমানের সংঘাত আগে এতটা ব্যাপকভাবে কখনো হয়নি। শ্বেতাঙ্গদের স্পর্ধার জবাব কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে রামগোপাল ঘোষ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজরা এ দেশে জাতিগত বৈষম্য ও শাসক—শাসিতের শ্রেণিগত দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যেরকম বদ্ধপরিকর হয়েছেন তাতে কি তাঁদের স্বদেশবাসীরাই খুব গৌরব বোধ করবেন? তা মনে হয় না, বরং তাঁরা লজ্জিত হবেন—“On the contrary will not the generous and the noble sons of Britain feel ashamed of their countrymen in India, who are anxious to perpetuate an invidious distinction, and preserve their exalted position at the expense of their native fellow subjects?”৫৮
‘কালা আইন’ বাতিল করার জন্য ইংরেজরা যখন দলবদ্ধ হন, তখন তাঁদের প্রতিপক্ষরাও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন। আগেকার জমিদারসভা বা বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির লক্ষ্যসীমাও এবারে অতিক্রম করার প্রয়োজন হয়। ১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্থাপিত হয় ‘ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন’, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিছুদিন পরে ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ স্থাপিত হয় (২৯ অক্টোবর ১৮৫১), সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ। একে ‘ভারতবর্ষীয় সভা’ বলা হত। এই সভার প্রধান বিশেষত্ব হল শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ বর্জন। কাজেই এই সভাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত আমাদের দেশের প্রথম জাতীয় সভা বলা যায়। আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল, দেশীয় দলগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক উদ্দেশ্যে সভায় মিলিত হন। সভা গঠনে সামাজিক শ্রেণিগত সীমানাও কিছুটা প্রসারিত হয়। আগেকার মতো শুধু উচ্চশ্রেণির জমিদার ও ধনিকদের মধ্যে এই সভা সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার বাইরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেও এর প্রসার বিস্তৃত হয়। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সভার প্রথম পদক্ষেপ শোনা যায় ‘ভারতবর্ষীয় সভা’র মধ্যে।৫৯
ধনিক বাঙালিরা ভারতবর্ষীয় সভার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হননি। সভার কাজকর্মে (প্রধানত আবেদন—নিবেদন) সামান্য যেটুকু রাজনীতির গন্ধ ছিল, বোঝা যায় ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে সেটুকুও তাঁরা সহ্য করতে পারেননি। ১৮৫২ সালের মধ্যে এই সভার দুটি শাখা বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থাপিত হয়। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠার পথে এটাই প্রথম পদক্ষেপ।
বিদ্বৎসভা ও সমাজসংস্কারসভা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উৎসাহ এই সময় অক্ষুণ্ণ থাকে। ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র কাজকর্ম পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকলেও তার আলোচনা যেহেতু ধর্মতত্ত্বের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল, তাই প্রকৃত বিদ্বৎসভার দায়িত্ব তার পক্ষে পালন করা সব সময় সম্ভব হত না। ১৮৫০—এর দিকে শিক্ষিত বাঙালিরা আরও উদার ও স্বাধীন চিন্তার অনুকূল একটি বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠায় উদযোগী হন। ওই উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল কলেজের একটি সভায় (১১ ডিসেম্বর ১৮৫১) ডক্টর ম্যুয়ট এ দেশে এই ধরনের সভাস্থাপনের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সকলের সম্মতিক্রমে স্ত্রীশিক্ষার অধিবক্তা সমাজহিতৈষী মৃত বেথুন সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সভা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়। সভার নাম হয় ‘বেথুন সোসাইটি’। এক বছরেই (১৮৫২) সোসাইটির সভ্যসংখ্যা হয় ১৩১ জন, তার মধ্যে ১০৬ জন বাঙালি। ১৮৫৭ সালের মধ্যে সভ্যসংখ্যা হয় ৩৪৫ জন। শিক্ষিত বাঙালি ‘এলিট’ গোষ্ঠী (Elite) অধিকাংশই এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বোঝা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৫৯—৬০ সালের মধ্যে দেখা যায়, সভার অধিবেশনে বিশেষ সভ্য—সমাগম হয় না, নিয়মিত চাঁদাও অনেকে দেন না। তার কারণ মনে হয়ে, বিশুদ্ধ বিদ্যানুশীলনে (সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা) তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিরা তেমন উৎসাহ পেতেন না এবং সভায় ধর্ম—রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল বলে কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। পরে আলেকজান্ডার ডাফের সভাপতিত্বে বেথুন সোসাইটির নতুন পর্বারম্ভ হয় (১৮৫৯—৬৯)।৬০
বেথুন সোসাইটি ছাড়া এই সময় ‘পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি’ (১৮৪৭), সর্বশুভকরী সভা (১৮৫০), সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪), বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৪—৫৫) প্রভৃতি নানা রকমের সভা, প্রধানত সমাজোন্নতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বড়বাজার অঞ্চলে নব্যশিক্ষিত যুবকরা ‘পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি’ গঠন করেন সাহিত্যচর্চা ও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে। গৌরদাস বসাক (মাইকেল মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু) এই সভার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগের কয়েকজন ছাত্র কলকাতার ঠনঠনিয়া অঞ্চলে ‘সর্বশুভকরী সভা’ স্থাপন করেন, প্রধান উদ্দেশ্য সমাজসংস্কার। এই সভার সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালংকার যুক্ত ছিলেন। সভার মুখপত্র ছিল ‘সর্বশুভকরী পত্রিকা’। প্যারীচাঁদ মিত্রর সহোদর কিশোরীচাঁদ মিত্রর উদযোগে ‘সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি’ তাঁর কাশীপুরের গৃহে স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি ছিলেন। সভার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র। সভার নাম থেকেই বোঝা যায়, সমাজসংস্কারই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহর উৎসাহে ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ স্থাপিত হয়। সভার মুখপত্র ছিল ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’। সাহিত্য অনুশীলন ও সমাজসেবা ছিল সভার উদ্দেশ্য।
এই সময়কার সভাগুলির সঙ্গে প্রধানত ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তরা (বিশ্ববিদ্যালয়—পূর্ব যুগের) সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। বিদ্যানুশীলন ও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত সভাগুলির সঙ্গে ইয়াং বেঙ্গল ও তত্ত্ববোধিনী—গোষ্ঠীর প্রধানরা যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি অনুশীলনের আগ্রহ এই সমস্ত সভার ভিতর দিয়ে বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে আরও একটি আগ্রহ মনে হয় তীব্রতর হয়েছে, সেটি হল সমাজোন্নতির আগ্রহ। সমাজের অনেক সমস্যাই আগে থেকে আলোচিত হচ্ছিল রামমোহন রায়ের ‘আত্মীয় সভা’র কাল থেকে। যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, চিরবৈধব্য ইত্যাদি কুসংস্কার থেকে যে সামাজিক জীবন মুক্ত করার প্রয়োজন, অনেকেই তা অনুভব করছিলেন। অন্তত উন্নত চিন্তার মুখপত্র ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তদের বেশ বড় একটা অংশ যে রীতিমতো তা অনুভব করছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সভাসমিতি ও পত্রিকার আলোচনার গতি থেকে তা বোঝা যায়। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় হল, সমাজসংস্কারকর্মের প্রেরণা সঞ্চার থেকে আরম্ভ করে সংস্কারমুখী চেতনা দেশবাসীর মনে খানিকটা জাগ্রত করা এবং প্রত্যক্ষভাবে ধর্মসংস্কার, সতীদাহপ্রথা নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি দুঃসাহসিক সংস্কারকর্মে দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়—পূর্ব যুগের শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তেরই কৃতিত্ব। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যায় সুশিক্ষিত কয়েকজন বাঙালি পণ্ডিতও যে সংস্কার কর্মের গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলেন, তা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো।
উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংস্কারকর্মের এই প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থ পুরুষ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন না, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। পাঠ শেষ করার পর কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজ করে বিদ্যাসাগর ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেখানে সম্পাদকের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে মতভেদ হওয়ার জন্য তিনি পদত্যাগ করেন। ১৮৫০ সালে আবার সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন সাহিত্যের অধ্যাপকপদে। ১৮৫১ সালে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠিয়ে দিয়ে অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হলে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রথমেই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর তিনি সংস্কার করেন। তাঁর ‘Notes on the Sanscrit College’ (অপ্রকাশিত) শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি অত্যন্ত মূল্যবান খসড়া। এর মধ্যে তাঁর শিক্ষাসংস্কারের আসল উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার রূপ নিয়েছে।৬১ খসড়াতে প্রথমেই তিনি বলেছেন, বাংলা দেশে শিক্ষার দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত বাংলা সাহিত্যের সম্ভার যথাসম্ভব সমৃদ্ধ ও উন্নত করা। এ কাজ শুধু ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শীদের দ্বারা সম্ভব হবে না, কারণ পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় তাঁদের পক্ষে কিছু রচনা করা কঠিন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্যে সুশিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে তাঁরাই বরং সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের রচয়িতা হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের যে শিক্ষাসংস্কার করেন তাতে এ দেশে প্রাচ্য বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংযোগের পথ খুলে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য—পাশ্চাত্যের এই মিলনের পথ উন্মুখ করে দেওয়া সংস্কারক বিদ্যাসাগরের অনন্যসাধারণ কীর্তি।
স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গোড়া থেকেই বিদ্যাসাগর বেথুনের অন্যতম সহযোগী ছিলেন এবং তাঁর অনুরোধে তিনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫০)। ১৮৫৪ সালে বাংলার ছোটলাট এফ. জে. হ্যালিডে বাংলা শিক্ষার প্রসারে মনোযোগী হলে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রধান সহায়ক হন। ১৮৫৭ সালের গোড়া থেকে হ্যালিডে যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হন তখন বিদ্যাসাগরই তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে সেই কাজে সাহায্য করেন। এর মধ্যে বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ‘মডেল স্কুল’ স্থাপনে বিদ্যাসাগর যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তিনি অগ্রসর হন। শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক গুরুদায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকের কর্তব্য পালন করেও তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদযোগী হন। তার জন্য তাঁকে শুধু যে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা—ও একজন মানুষের পক্ষে করা কঠিন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্মের সঙ্গে বিদ্যাসাগর এই সময় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তার সঙ্গে বহুবিবাহ প্রতিরোধ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।
উনিশ শতকের মধ্যভাগে একজন ব্যক্তির মধ্যে সমাজসংস্কারের উদ্দীপনা যে এমনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তার কারণ তার আগে প্রায় তিরিশ বছর ধরে নানা রকমের সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার ভিতর দিয়ে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, অথবা বহুবিবাহ নিবারণের সংকল্প বিদ্যাসাগরের মনে অকস্মাৎ বা সর্বপ্রথম উদয় হয়নি। রামমোহন ও তাঁর ‘আত্মীয় সভা’, ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী ‘ইয়াং বেঙ্গল’, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’, ‘ব্রাহ্মসমাজ’, ‘ধর্মসভা’, নানারকমের বিদ্বৎসভা, এবং বহু নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাবে ও ক্রিয়াকর্মে নিস্তরঙ্গ বাঙালি সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিমানসে নতুন উন্নতিশীল সমাজগঠনের ইচ্ছা ও উৎসাহ জেগেছিল। বিদ্যাসাগর পরোক্ষে ছাত্রজীবন থেকে, এবং প্রত্যক্ষভাবে কর্মজীবনের গোড়া থেকে এইসব নতুন সামাজিক গোষ্ঠী ও সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই পরিবর্তনশীল সামাজিক চিন্তাধারা থেকেই তিনি তাঁর জীবনের ‘সর্বপ্রধান সৎকর্ম’ বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের প্রেরণাও পেয়েছিলেন।
বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার অবশ্যম্ভাবী ফল হল বহু নারীর অকাল বৈধব্য। সতেরো—আঠারো শতক থেকে এইসব কুপ্রথার বিষময় প্রতিক্রিয়া সমাজে দেখা দিয়েছিল। রাজা রাজবল্লভের মতো দু—একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নিজস্বার্থে বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য দেশের পণ্ডিতদের কাছ থেকে শাস্ত্রীয় অনুমোদনলাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৮৩৭ সালে ভারতীয় ল কমিশনের সেক্রেটারি গ্র্যান্ট সাহেব (J. P Grant) হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে কোনও আইন পাশ করা যায় কি না সে বিষয়ে বিশিষ্ট ইংরেজ আইনজ্ঞদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ আইনজ্ঞদের প্রতিকূল মতামতে তিনি আদৌ উৎসাহিত হননি।৬২ ল কমিশনের প্রচেষ্টার ফলে সমাজে এই সময় কিছু আলোচনা ও আন্দোলনও হয়েছিল। তারই উল্লেখ করে ইয়াং বেঙ্গলের মুখপত্র ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ ১৮৪২ সালে লেখেন :৬৩ ”যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দুজাতি ও বিধবার পুনর্বিবাহের বাদানুবাদ হইয়া থাকে…”
বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ বা আন্দোলনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে ঘটে। বিদ্যাসাগর—সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর—জীবনচরিতে লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর আগে কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন ব্রাহ্মণ ও কয়েকজন বিষয়ী লোক দলবদ্ধ হয়ে একটি বালবিধবার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পটলডাঙা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস কর্মকার তাঁর নিজের বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়ার জন্য পণ্ডিতের কাছ থেকে একটি ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। এই পত্রে কাশীনাথ তর্কালংকার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও আরও কয়েকজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। পরে আবার এই পণ্ডিতরাই বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেন। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের আগে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ বিষয়ে তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিতদের দিয়ে বিচার করান। এই সময় কালীকৃষ্ণ মিত্র ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদযোগে বারাসত অঞ্চলের একদল তরুণ একটি সভা স্থাপন করে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই আন্দোলন অবশ্য খুব বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। সাময়িকপত্রেও এই সময় দু—একটি বিধবাবিবাহের বিচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে।
এই সমস্ত সংবাদ ও ঘটনা থেকে বোঝা যায়, রামমোহনের ‘আত্মীয় সভা’র কাল থেকে বিদ্যাসাগর কাল পর্যন্ত বিধবাবিবাহের সমস্যা সভাকক্ষের আলোচনা থেকে ক্রমে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের বিষয় হয়ে উঠছিল। এই সংস্কারকর্মের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার মতো ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৫ সালে জানুয়ারি মাসে ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা’—এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় মতামত উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ দেশের লোক যে কর্তব্য—অকর্তব্য শাস্ত্রবচন অনুযায়ী নির্ধারণ করেন, যুক্তি—বুদ্ধি—বিবেক অনুযায়ী করেন না, সে কথা পুস্তিকার প্রথমেই তিনি পরিষ্কার করে লেখেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁকে ঋষিবচনও সংগ্রহ করতে হয়েছিল। শাস্ত্রবচনের সাহায্যে বিদ্যাসাগর নবযুগের বাংলার মানবমুখী যুক্তিবাদের (Humanist Rationalism) ভিত গঠন করেছিলেন। তার আগে এ কাজ রামমোহন রায় করেছিলেন সহমরণ নিবারণের উদ্দেশ্যে পুস্তিকা রচনার সময়। রামমোহনের সামাজিক আদর্শের সুযোগ্য উত্তরসাধক হলেন বিদ্যাসাগর।
সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তিকা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ২০০০ কপি বই বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তী সংস্করণও ৩০০০ কপি অল্পদিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। উৎসাহিত হয়ে বিদ্যাসাগর পরে একসঙ্গে ১০০০০ কপি ছাপেন। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয় (ফাল্গুন ১৭৭৬ শক) :
”কয়েকবৎসরের মধ্যে বিধবাগণের পুনঃ সংস্কার প্রচলিত হইবার বিষয় এতদ্দেশে বারংবার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর এই বিষয় লইয়া যাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাদৃশ আন্দোলন অন্য কোনো বৎসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্বমাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত।”
বিধবাবিবাহ বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর তাঁর বিরোধী পক্ষের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা ও টীকা শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ খণ্ডন করেন। ”নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্য বিধীয়তে।।” পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মারা যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বা পতিত হয়, তাহলে এই পঞ্চপ্রকার আপদে নারীর অন্য পতিগ্রহণ বিধেয়। পরাশর—বচনের বিদ্যাসাগর—কৃত ওই ব্যাখ্যা ও যুক্তি খণ্ডন করে বিরোধী পণ্ডিতরা বলেন যে এখানে বিবাহিত পতির কথা বলা হয়নি, ভাবী পতির উক্ত পঞ্চপ্রকার আপদে পাত্রান্তরে কন্যাপ্রদান বিধেয়। বিদ্যাসাগর তার ব্যাখ্যার সমর্থনে বিরোধী পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। তার পরেও এ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ বহুদিন ধরে চলতে থাকে। চলা স্বাভাবিক। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে দেখা যায়, হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল ধারার পুনরুজ্জীবনকালে, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর অনেক বেশি তীব্র হয়ে ওঠে।
শুধু প্রচার সাহিত্যের সাহায্যে অথবা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়ে বিধবাবিবাহের মতো সংস্কারকর্ম যে সফল হবেন না, তা বিদ্যাসাগর বিলক্ষণ জানতেন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করা নয়। তাই বিধবাবিবাহের পক্ষে যাতে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা হয় তার জন্য ভারত সরকারের কাছে প্রায় ১০০০ গণ্যমান্য লোকের (৯৮৭) স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র তিনি পাঠান (৪ অক্টোবর ১৮৫৫)। ব্যবস্থাপক সভায় আইনের খসড়া নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন তার পক্ষে ও বিপক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক আবেদন ও প্রতিবাদপত্র ভারত সরকারের কাছে পৌঁছোয়।৬৪ রাজা রাধাকান্ত দেব অগ্রণী হয়ে ৩৬,৭৬৩ জন লোকের স্বাক্ষরসহ বাংলা দেশ থেকে প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ আইনের বিরুদ্ধে একটি আবেদনপত্র পাঠান (১৭ মার্চ ১৮৫৬)। এ ছাড়া নবদ্বীপ ত্রিবেণি ভাটপাড়া বাঁশবেড়িয়া কলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতরা সংঘবদ্ধ হয়ে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠান। প্রতিবাদীদের প্রধান যুক্তি ছিল, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ; বিধবাবিবাহের প্রচলন হলে বাংলা দেশের হিন্দুসমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কলহ হবে এবং তার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেবে। হিন্দুসমাজ শুধু যে ধর্মচ্যুত হবে তা নয়, ধনেপ্রাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উৎসন্নে যাবে।
বিদ্যাসাগরের সমর্থনেও বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক আবেদনপত্র ভারত সরকারের হস্তগত হয়। কৃষ্ণনগর বর্ধমান বারাসত মুর্শিদাবাদ মেদিনীপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার লোক সমর্থনপত্র পাঠান। কলকাতার মিশনারিরাও অনেকে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ইয়াং বেঙ্গল বা ডিরোজিয়ানরা একটি আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত আইন সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁরা বিধবাবিবাহ যাতে ‘রেজিস্ট্রেশন’ করা হয় সেই মর্মে আইনটি সংশোধন করতে সরকারকে অনুরোধ করেন। এই সময় রেজিস্ট্রেশনের পক্ষে আরও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন। ইয়াং বেঙ্গলের এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা বিদ্যাসাগর নিজেও, আইন পাশ হবার পরে, বিধবাবিবাহের শোচনীয় পরিণতির করুণ অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। পরে প্রধানত ব্রাহ্মদের আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ সালে Civil Marriage Act III পাশ হয়।
অবশেষে বহু বাদানুবাদের পর ২৬ জুলাই ১৮৫৬ বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। আইনটি পাশ হবার পর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেন—
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায়।।
মিছা—মিছি অনুষ্ঠান, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা।।
বোঝা যায়, বাঙালি চরিত্রের বাক্যবিলাসকে ব্যঙ্গ করে গুপ্ত কবি এই পদ্য রচনা করেন। তাঁর ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন যে ‘মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা।’ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এইটাই হল বড় বৈশিষ্ট্য। ‘সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?’ সাধারণ বাঙালি চরিত্র সম্বন্ধে গুপ্ত—কবির পক্ষে এই প্রশ্ন করাও স্বাভাবিক। তবে যে ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করে এই প্রশ্ন, বাঙালিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। বিদ্যাসাগরের প্রতিজ্ঞা ছিল পর্বতের মতো অটল, সাহসও ছিল দুর্জয়। জুলাই মাসে আইন পাশ হয়, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আইনসম্মত বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন। এই বিধবাবিবাহের প্রথম পাত্র হলেন খাটুরা গ্রামনিবাসী (২৪ পরগনা) বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন, এবং কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনা করে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। বিধবাবিবাহের প্রথম পাত্রী হলেন বর্ধমান জেলার পলাশডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। বিবাহের দিন স্থির হয় ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬, বঙ্গাব্দ ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৩। বাংলা দেশের, এবং ভারতের, সমাজসংস্কারের ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষ স্মরণীয়।
বিবাহের দিন স্বভাবতই কলকাতা শহরে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়, এবং কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য বহু লোক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। বিবাহের অনুষ্ঠান হয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে, ১২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে। বিবাহের জন্য প্রায় ৮০০ নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়। পণ্ডিত অধ্যাপকদের জন্য সংস্কৃত কবিতায় স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়েছিল। কলকাতার বিবাহের পরদিন পানিহাটিতে কুলীন কায়স্থ কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কলকাতার ঈশানচন্দ্র মিত্রর ১২ বছরের বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। কন্যার পিতাই কন্যাকে সম্প্রদান করেন। বিধবাবিবাহ যখন বাস্তবিক ঘটতে আরম্ভ করল, মুখে বলা আর কাজে করার মধ্যে প্রভেদ যখন ঘুচে গেল, তখন সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরের উপর অজস্রধারায় অভিসম্পাত—বর্ষণ আরম্ভ হল। কিন্তু বাধাবিপত্তি, অভিসম্পাত ও কটুবাক্যে বিচলিত হবার মতো ব্যক্তি ছিলেন না বিদ্যাসাগর। সামাজিক কর্তব্য স্থিরচিত্তে পালন করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য । বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ এই সময় লেখেন :
”এই মহৎ ব্যাপার যে ক’এক ব্যক্তি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে।”
রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘আত্মচরিত’—এ লিখেছেন যে তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ করেন তাঁর জ্যাঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর মনোমোহন বসু। কলকাতার দক্ষিণে বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর পৈতৃক বাস ছিল। ভাইদের বিধবাবিবাহের উৎসাহ তিনিই দিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁর খুড়োমশায় লেখেন যে বোড়ালের কায়স্থকুল থেকে বসু—পরিবার তাঁর এই কীর্তির জন্য বহিষ্কৃত হন। রাজনারায়ণ বসু তখন মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করতেন এবং সেখানে বিধবাবিবাহের আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। মেদিনীপুরের লোক তাঁর ঘর পুড়িয়ে দেবার ভয়ও দেখান।
বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান এরপর থেকে একটার পর একটা ঘটতে থাকে এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের উৎসাহও অনির্বাণ থাকে, যদিও বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য সেই উৎসাহের শিখা ধীরে ধীরে পরে ম্লান হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্ন বাংলা ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ খানাকুল কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। ১৮৭০—৭১ সালের কথা। এই বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে একখানি চিঠিতে লেখেন :
”আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক; আমি উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম।… বিধবাবিবাহ—প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এই বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।… আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।”
চিঠিখানি নানাদিক থেকে অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক। প্রথমত এই চিঠির মধ্যে বিদ্যাসাগর চরিত্রের মূল উপাদানটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ‘আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি’—এইটাই বিদ্যাসাগর চরিত্রের বড় কথা। নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য যা উচিত ও আবশ্যক বোধ করতেন, তা—ই তিনি করতেন, লোকনিন্দা অথবা আত্মীয়কুটুম্বের বিরাগের ভয়ে কখনো সংকুচিত হতেন না। সমাজ ও মানুষের জন্য তিনি জীবনে যত কাজ করেছেন, তার মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রবর্তনকে সবচেয়ে মহৎ কাজ বলে তিনি মনে করতেন।৬৫
১৮৫৭—৫৮
বাংলার সামাজিক জীবনের এই সচলতা ও চাঞ্চল্যের মধ্যে, ১৮৫৭ সালের গোড়ার দেশীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কলকাতার অনতিদূরে দমদম—ব্যারাকপুর অঞ্চলে এই বিদ্রোহ অগ্নিসংযোগ হয়, এবং ক্রমে সারা উত্তর ভারতে সেই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেনা বিদ্রোহ পরে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কারণে গণবিদ্রোহের আকার ধারণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের প্রেরণার মূলে সচেতন জাতীয়তাবোধ কতখানি সক্রিয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকরাও যথাসম্ভব তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পর এই সন্দেহ দূর করতে পারেননি। বিদ্রোহের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এই বিদ্রোহ আমাদের দেশের প্রথম ‘জাতীয় বিদ্রোহ’—কেউ বলেন আদৌ তা নয়, বিদ্রোহের এই ধরনের নির্দিষ্ট রূপ বলে তখন কিছু ছিল না। আপাতত এই বিতর্ক প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই আমাদের। তবে বিদ্রোহের স্তূপীকৃত ঘটনা ও তথ্য বিচার—বিশ্লেষণ করলে, ১৮৫৭—এর বিদ্রোহকে ‘জাতীয় বিদ্রোহ’ বলতে দ্বিধা হয়। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে অগাধ তথ্য—সমুদ্র মন্থন করে, এবং প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার—বিশ্লেষণ করে তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন : “On the whole, it is difficult to avoid the conclusion that the so called First National War of Independence of 1857, is neither the First, nor National, nor a War of Independence.”৬৬
বাংলা দেশ সম্বন্ধে উল্লেখ্য হল, এই বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের কণামাত্র সহানুভূতি ছিল না। কেন ছিল না, সে প্রশ্নও নিশ্চয় ঐতিহাসিকদের বিচার্য বিষয়। যদি কেউ বলেন যে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে দেশপ্রীতির অভাব ছিল বলে তাঁরা এই বিদ্রোহের স্বরূপ ও তাৎপর্য বুঝতে পারেননি, তাহলে তাঁর অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনার যোগ্য বলে মনে হয় না। রামমোহনের কাল থেকে ইয়াং বেঙ্গল, তত্ত্ববোধিনী ও বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজকর্ম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যেটুকু পরিচয় আমরা আগে দিয়েছি তা থেকে অন্তত তাঁদের সমাজচেতনা ও চলমান ইতিহাসবোধ যে যথেষ্ট সজাগ ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তা ছাড়া আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে ভাববার আছে। ‘সিপাহি বিদ্রোহ’ শেষ হতে না হতে বাংলা দেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং কৃষকরা শ্রেণিগতভাবে মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী হলেও, শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তরা দৃপ্তকণ্ঠে এই বিদ্রোহ ও কৃষকদের অভিযোগ সমর্থন করেন। প্রকৃত জাতীয় চেতনার প্রকাশ ও প্রসার এই সময় থেকে হয়, এবং তারপর ‘জাতীয় মেলা’ ‘ভারত সভা’ প্রভৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে ‘জাতীয় সম্মেলন’ ও ‘জাতীয় কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠার পথে ভারতের জাতীয় আন্দোলন অগ্রসর হয়। ‘সিপাহি বিদ্রোহ’—এর সময় যাঁদের জাতীয় চেতনা লুপ্ত অথবা সুপ্ত ছিল, তাঁদের সেই চেতনা নীল বিদ্রোহের সময়, এবং তারপরে, হঠাৎ সবলে আত্মপ্রকাশ করল, এরকম উদ্ভট ধারণা করার কোনও সংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না।
‘সিপাহি বিদ্রোহ’—এর সময় দেখা যায়, বাঙালি পরিচালিত বাংলা ও ইংরেজি সাময়িকপত্রে—সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রিকায়—বিদ্রোহের বিরুদ্ধে রচনা প্রকাশিত হতে থাকে।৬৭ অধিকাংশ রচনায় বিদ্রোহের সাম্প্রদায়িক রূপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ বিদ্রোহটা যে মূলত ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উদ্ধারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট, এ কথা বিশেষ জোর দিয়ে বাংলা পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে। অবশ্য বাংলা পত্রিকা ও বাঙালি—পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকাগুলিও তখন হিন্দুদেরই ছিল। কিন্তু শুধু সেই কারণে তাঁরা যে বিদ্রোহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ‘আবিষ্কার’ করেছিলেন, তা বলা যায় না, তা ছাড়া ভারতের হিন্দু সামন্তরাও অনেকে যে বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন, তা—ও তাঁদের অজানা ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা কেন ‘সিপাহি বিদ্রোহ’কে ভারতে মুসলমান রাজ্য পুনরুদ্ধারের একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি, সেটাও চিন্তার বিষয়। তার চেয়ে লক্ষণীয় হল, নতুন ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে পূর্বের মুসলমান রাজত্বের তুলনা করে প্রায় সকলে বলেছেন যে সেকালের মুসলমান শাসনে প্রত্যাবর্তন আধুনিক যুগ থেকে অতীতে ফিরে যাওয়ার মতোই কোনওমতেই কাম্য নয়। হিন্দু সামন্তরা স্বভাবতই সামন্ত যুগে ফিরে যেতে চান বলে তাঁরা মুসলমান শাসকদের চক্রান্তে যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। বিদ্রোহের এই স্বরূপ বিশ্লেষণ থেকে প্রথমে এই কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে বিদ্রোহের ‘জাতীয় রূপ’—এর বদলে ‘সাম্প্রদায়িক রূপ’ই শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় কথা, অতীতের মুসলমান শাসিত সামন্ত যুগকে শিক্ষিত হিন্দুরা ইতিহাসের পশ্চাদগতি বলে মনে করতেন। কোনও কারণেই, এমনকী ইংরেজ—বর্জনের বিনিময়েও, ঐতিহাসিক পশ্চাদগতি নব্যশিক্ষিত হিন্দু—মধ্যবিত্তদের কাম্য ছিল না। তাঁরা অগ্রগতির সমর্থক ছিলেন, তাই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন এবং তাকে ‘জাতীয় বিদ্রোহ’ অথবা ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’ বলে ভাবতে পারেননি।
সিপাহি বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া শুধু যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল তা নয়, ব্রিটিশ আমলের নতুন জমিদারশ্রেণিও রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ইংরেজের শাসনস্বার্থেই এই নতুন জমিদারশ্রেণি গঠিত হয়েছিল এবং বাংলা দেশে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ হয়েছিল তার প্রধান সহায় (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই নতুন জমিদারশ্রেণি স্বার্থ ইংরেজ শাসনের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে তাঁরা অন্য কোনও রাষ্ট্রীয় অবস্থান্তরের কথা চিন্তা করতে পারতেন না। বিদ্রোহের পরেই ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইংলন্ডের পার্লামেন্টে একটি আবেদনপত্র পাঠান এবং সেই পত্রে বাংলা দেশের মতো ভারতের সর্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ করেন :৬৮
“A comparison of the loyal and the disloyal throughout the late period of the crisis will, you petitioners submit, at least show a tendency of a Permanent Settlement to create a powerful class, who feel their interest as one with the ruling power and who are satisfied with their position.’’
(Emphasis added)
এই নতুন জমিদারশ্রেণির স্বার্থ এবং নতুন মধ্যবিত্তের স্বার্থ এক ছিল না। নতুন জমিদাররা নতুন মধ্যবিত্তদের জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তার যে আদৌ সুনজরে দেখতেন না, সে বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি (১৮০—৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কাজেই শ্রেণিস্বার্থের দিক দিয়ে বিচার করলেও নতুন জমিদারশ্রেণি ও নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির ‘সিপাহি বিদ্রোহ’—বিরোধিতার কারণ যে ভিন্ন ছিল, সে কথা মনে রাখা দরকার। উপরের নতুন জমিদার ও মধ্যের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির ভিন্ন দৃষ্টিতে বিদ্রোহের বিরোধিতা করলেও, বিদ্রোহকালে ইংরেজ শাসকদের নির্মম অমানুষিক অত্যাচার যে দেশের জনসাধারণের মনে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ইংরেজ—বিরোধী জাতীয় বিদ্রোহের ভাব সঞ্চারিত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। জনসাধারণের এই মনোভাবই পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এবং বাংলা দেশে ‘নীল বিদ্রোহ’ থেকে তার সূচনা হয়।
১৮৬০—১৯০০
১৮০০—৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারার সঙ্গে ১৮৬০—১৯০০—র ধারার পার্থক্য আছে। পতিত জমি আবাদযোগ্য করে তোলা এবং তাতে বীজ বপন করার সঙ্গে প্রথম ধারাকে খানিকটা তুলনা করা যায়। দ্বিতীয় ধারায় দেখা যায়, সেই বীজ অঙ্কুরে পরিণত হচ্ছে এবং সমাজজীবন ক্রমেই জটিল ও কলরবমুখর হয়ে উঠছে। রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা, ডিরোজিও এবং তাঁর ‘ইয়াং বেঙ্গল’ গোষ্ঠী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও তাঁদের অনুরাগীরা উন্নতিশীল ভাবধারা ও বলিষ্ঠ সংস্কারকর্মের ভিতর দিয়ে বাংলার সমাজমানসকে উজ্জীবিত ও প্রগতিমুখী করে তুলেছিলেন। অবশ্য অবাধে করতে পারেননি, বিপরীতমুখী ঐতিহ্যিক (হিন্দু) ভাবধারার প্রতিরোধের সম্মুখীন তাঁদের হতে হয়েছিল প্রতি পদক্ষেপে। এই দুটি ভাবধারার ঘাতপ্রতিঘাত উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলা দেশে তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং সংঘাতের ক্ষেত্রও ব্যাপক হয়। এই পর্বে বহু শাখাপ্রশাখায় ভাবসংঘাতের যে বিস্তার বাংলার সমাজজীবনে দেখা যায়, তার প্রধান ঐতিহাসিক কারণ হল—
ক। বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির দ্রুত প্রসার, বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর, শিক্ষিত বাঙালি মধ্যশ্রেণির (educated Bengali middle-class) বিস্তার।
খ। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থের সঙ্গে বিদেশি শাসকশ্রেণির স্বার্থের সংঘাত, এবং তার ফলে জাতীয়তাবোধের বেধবৃদ্ধি।
শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রসার প্রসঙ্গে পূর্বে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি (চতুর্থ অধ্যায়ে)। জাতীয় চেতনার বিকাশ প্রধানত ঐতিহ্যিক হিন্দু ভাবাশ্রয়ী (traditional Hinduism) হয়ে ওঠে—এবং তারও অন্যতম কারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হিন্দু প্রাধান্য—যার ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে নব্য—হিন্দুত্বের (neo-Hindusim) বেশে পুরাতন হিন্দু ভাব পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন বেশ প্রবল হয়। এই আন্দোলনের প্রাবল্যের আরও একটি বড় কারণ হল, পরিণত বয়স—বুদ্ধির জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেশ বড় একটা অংশের সমাজচিন্তায় এই সময় বৈপরীত্য (contradiction) ও অসংগতি দেখা যায় (যেমন দেবেন্দ্রনাথের যুগের আদি—ব্রাহ্মদের মধ্যে), এবং নবীন যুবক গোষ্ঠী (যেমন কেশবচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী নবীন ব্রাহ্মরা) এই চিন্তাবৈপরীত্যের বিরোধিতা করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন (যেমন ব্রাহ্মসমাজে বিভক্ত হয়ে যায় আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান গোষ্ঠীতে), উন্নতিশীল সমাজচিন্তাকে সুসংবদ্ধ ও সংহত করতে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার জন্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে চিন্তাসংকট গভীর হয়, উন্নতিশীল চিন্তাধারার গতি বিপর্যস্ত ও ব্যাহত হয়, নব্য—হিন্দু ভাবধারা প্রবল হয়ে ওঠে, এবং জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রিক চিন্তার তরঙ্গ অনেকটা সমাজচিন্তাকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু এই ভাবসংঘাতের ঐতিহাসিক সুফল ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালির মননের ফলে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের কর্ষণের পর বাঙালির মনীষা শতদলের মতো ফুটে ওঠে আধুনিক বাংলা কাব্যে, গল্প—উপন্যাস—কথাসাহিত্যে, নাটকে, রঙ্গালয়ের অভিনয়ে, সংগীতে ও চিত্রকলায়। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্য—সংস্কৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন এবং তার বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান দেন। সে ইতিহাস স্বতন্ত্র, শুধু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছাড়া তার বিস্তারিত আলোচনা আপাতত আমাদের সামাজিক ইতিহাসের ধারাবিশ্লেষণের গণ্ডি—বহির্ভূত।
বাংলার বাইরে ভারতবর্ষে একসময় কেশবচন্দ্র সেন ‘thunderbolt of Bengal’ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। মনে হয় যেমন ডালহৌসির আমলে যে রেলওয়ে—যুগের সূচনা হয়, সামাজিক জীবনে যে নতুন গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়, কতকটা তারই প্রতিমূর্তিরূপে কেশবচন্দ্র আবির্ভূত হন। ১৮৫৭ সালে ১৯ বছর বয়সে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ১৮৫৯ সালে তিনি স্টেজ—ম্যানেজার ও প্রযোজক হয়ে ‘বিধবাবিবাহ নাটক’ অভিনয় করেন চিৎপুরে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে। বিদ্যাসাগর একাধিকবার এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। সামাজিক রঙ্গমঞ্চে, বিদ্যাসাগরের পরে, তাঁরই আদর্শের উত্তরাধিকারীরূপে কেশবচন্দ্রর আবির্ভাব হয়।৬৯
১৮৫৯—৬০ থেকে ১৮৭০—৭২ সাল পর্যন্ত ‘কেশবচন্দ্রর যুগ’ বলা যায়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই সময়টাকে বলা হয় ‘নবোত্থানের যুগ’। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : ”এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান রবির ন্যায় বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মসমাজও সূর্যমণ্ডলের ন্যায় মানবচক্ষুর গোচর হইল।” তরুণ বাংলার কণ্ঠ হলেন কেশব, এবং সে কণ্ঠ যেমন দৃপ্ত তেমনি আবেগময়। ‘বাংলার বজ্র’ বলেই মনে হবার কথা। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে প্রবল বেগে কেশব “lecture, tractwriter, reformer, missionary and philanthropist” হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মসমাজ নবজীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত হল। একসময় ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ (১৮৩৯—৫৯) ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে, কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগীরা পরবর্তীকালে (১৮৫৯—৭২) অনুরূপ দায়িত্বই পালন করেন। কিন্তু কেশবের যুগের ভাবসংঘাতের গভীরতা ও ব্যাপ্তি অনেক বেশি। ওই সময়ের মধ্যে নীল বিদ্রোহ হয়, দীনবন্ধুর ‘নীল দর্পণ’ নাটক (১৮৫৯—৬০), মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ (১৮৬১), বঙ্কিমচন্দ্রর ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) ও ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২) প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১) ও বিবেকানন্দ (১৮৬৩) জন্মগ্রহণ করেন, ব্রাহ্মসমাজে প্রথম বিভেদের ফলে ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’—এ স্থাপিত হয় (১৮৬৬), ‘হিন্দু মেলা’র অধিবেশন আরম্ভ হয় (১৮৬৭), প্রথম ও দ্বিতীয় অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তরুণ ব্রাহ্মদের উৎসাহে (১৮৬২ ও ১৮৬৪), তিন আইনে অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ হয় (১৮৭২)। শুধু এই ঘটনাগুলির সংযোগ লক্ষ করলে বাংলার সমাজজীবনে নতুন চিন্তাবর্তের বেগ ও রূপ অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। বেগ প্রবল, আবর্তও জটিল। এই বেগবান জটিল চিন্তাবর্তের মধ্যে কেশব বিশিষ্ট নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এবং তাঁর পূর্বসূরি রামমোহন—ইয়াং বেঙ্গল—দেবেন্দ্রনাথ—বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীল সমাজচিন্তাকে কালোপযোগী নতুন স্তরে উত্তরণের কর্মে ব্রতী হন। কিন্তু এই কঠিন ব্রত উদযাপনের পথে কেশবের চরিত্রে ও কর্মে আদর্শগত অসংগতি দেখা দিতে থাকে, তার ফলে তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ও বিরোধ হয়, এবং নায়কের উচ্চাসন থেকে তিনি নামতে থাকেন। বাংলার আকাশে কেশবের উত্থান ও পতন হয় উল্কার মতো।
কেশবচন্দ্র ও তাঁর তরুণ অনুগামীরা প্রথম থেকেই সংস্কারকর্মে উৎসাহী হন। ব্রাহ্মধর্মের আচার্যদের ব্রাহ্মণত্বের সনাতন প্রতীক ‘উপবীত’ অর্জন তাঁরা দাবি করেন, ব্রাহ্মরীতি অনুযায়ী অসবর্ণ বিবাহে উদযোগী হন। তার সঙ্গে বিধবাবিবাহের উদ্যোগ, আয়োজন, অনুষ্ঠানও পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। মনে হয় যেন বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে কেশবচন্দ্রর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেন, এমনকী তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদেও অভিষিক্ত করেন (১৮৬২)। কিন্তু কেশবপন্থীদের সংস্কারের দাবি ক্রমে বাড়তে থাকে। উপাসনার সময় এবং বাইরের সমাজে চলাফেরার সময় তাঁরা পুরুষ—নারীর সমান অধিকার ও স্বাধীনতা দাবি করেন। কেশব নিজে আত্মীয়স্বজনের প্রবল বাধা উপেক্ষা করে সস্ত্রীক কলুটোলার পৈতৃক গৃহ থেকে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথের গৃহে যান, তাঁর আচার্য পদে অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় (১৮৬২)। বাংলার স্ত্রী—স্বাধীনতার ইতিহাসে এটি স্মরণীয় ঘটনা। ‘ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা’ গঠন করে কেশবপন্থীরা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনায় নবীনদের প্রত্যক্ষ দায়িত্বগ্রহণ দাবি করেন। মেয়েদের জন্য ‘ব্রাহ্মিকা সমাজ’ স্থাপিত হয় (১৮৬৫)। তার আগে ‘সঙ্গত সভা’র উদ্যোগে নারীপ্রগতির জন্য অন্তঃপুর শিক্ষা ও ‘বামবোধিনী পত্রিকা’ (১৮৬২—৬৩) প্রকাশ আরম্ভ হয়। নবীন ব্রাহ্মদের এইসব সামাজিক দাবিদাওয়ার সঙ্গে বেশি দিন আপস করে চলা প্রবীণ ব্রাহ্মণদের পক্ষে (দেবেন্দ্রগোষ্ঠী) সম্ভব হয় না। কেশবের আগে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তর (বিদ্যাসাগর সমর্থিত) একটি দেবেন্দ্র—বিরোধী গোষ্ঠী ছিল। অক্ষয়গোষ্ঠী ১৮৬৩—৬৪ সালেই দেবেন্দ্রনাথের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বতন্ত্র ‘উপাসনা সমাজ’ স্থাপন করেন এবং সেখানে নতুন পদ্ধতিতে উপাসনা পর্যন্ত আরম্ভ করেন। বিস্ময়কর হল, এই নতুন উপাসনাপদ্ধতি রচনায় নাকি বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন—“they began to conduct divine service according to a new form framed by themselves and revised by Pandit Iswar Chandra Vidyasagar.”৭০ কেশবচন্দ্রের আগে প্রথম বিচ্ছেদ ঘটে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের, এবং অক্ষয়—গোষ্ঠী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ গঠন না করে, নিভৃতে একটি ‘উপাসনা সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। এ হল ১৮৬৩—৬৫ সালের কথা।
১৮৬৪—৬৫ সালের মধ্যে নবীন কেশবগোষ্ঠীর কার্যকলাপ এমন স্তরে পৌঁছোয় যে প্রবীণ ব্রাহ্মগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ বিরোধ ও বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে, কেশব ও তাঁর সহকর্মীরা ব্রাহ্মধর্মের বাণী প্রচারে জয়যাত্রা করেন। ১৮৬৪ সালের মধ্যেই প্রচারের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। কেশবের তরুণ সহকর্মীদের মধ্যে প্রধান হলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্তী, অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অমৃতলাল বসু, কান্তিচন্দ্র মিত্র, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু। প্রচার ও কাজের ভিতর দিয়ে কেশবগোষ্ঠী ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। নবীন ব্রাহ্ম যুবকরা পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে, হিন্দুধর্মের প্রাণহীন আচার—অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকেন। সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে তাঁরা হিন্দু আচার ও দেবদেবীকে মানতে চান না। তাঁদের উপর পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন চলতে থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :৭১
“In Bengal the new ferment roused up the spirit of old Hinduism ‘put them down, put them down,’ was the cry raised everywhere by the leaders of orthodox Hinduism.”
তিরিশের ইয়াং বেঙ্গলের আন্দোলনের সঙ্গে এই নবীন কেশবগোষ্ঠীর আন্দোলনের অনেক সাদৃশ্য আছে। তরুণ ব্রাহ্মরা উনিশ শতকের ষাট—সত্তরে ‘ইয়াং বেঙ্গল’—এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবি ক্রমে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে। প্রবীণদের কানে নবীনদের এই স্বাতন্ত্র্যের সুর স্বভাবতই বেসুরো মনে হয়। কেশব Struggle for Religious Independence and Progress in the Brahmo Samaj সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন (জুলাই ১৮৬৫)। তারপর Jesus Christ–Asia and Europe বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা (মে ১৮৬৬) বোমার মতো বিস্ফোরিত হয়। প্রবীণ ব্রাহ্মরা পর্যন্ত রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদের বিচ্ছেদ হয়, কেশবগোষ্ঠী ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপন করেন (নভেম্বর ১৮৬৬)। নবগোপাল মিত্র নতুন সমাজগঠনে বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রবীণদের সমাজের নাম হয়—’আদি ব্রাহ্মসমাজ’।
এই সময় প্রবীণ ব্রাহ্ম নেতা রাজনারায়ণ বসু ‘জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা’ স্থাপনে অগ্রণী হন (১৮৬৬)। সভার অনুষ্ঠানপত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা, বাংলায় কথোপকথন ও বক্তৃতা, হিন্দু শাস্ত্রসম্মত সমাজসংস্কার, দেশীয় (হিন্দু) উৎসব—অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা, দেশীয় পোশাক পরিধান ইত্যাদির সংকল্প ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের এক বছরের মধ্যে নবগোপাল মিত্র উদ্যোগী হয়ে ‘হিন্দু মেলা’ প্রবর্তন করেন (‘চৈত্র মেলা’ বা ‘জাতীয় মেলা’ও বলা হত)। ১৮৬৭ সালে ‘হিন্দু মেলা’র প্রথম অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন : ”এই মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। …একদিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা ‘হিন্দু মেলা’ ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে।”
লক্ষণীয় হল, হিন্দু মেলার প্রেরণা দেন ও প্রবর্তন করেন দু—জন কেশবগোষ্ঠী—বিরোধী ‘আদি’ ব্রাহ্ম—রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র। শুধু তা—ই নয়, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বিভেদকালেই ‘হিন্দু মেলা’ সোৎসাহে প্রবর্তিত হয়। এ শুধু আকস্মিক ঘটনাসংযোগ নয়। এই ঘটনাপরম্পরার তাৎপর্য আছে এবং তার বিশেষ গুরুত্ব আছে সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে। নবীন ব্রাহ্মদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে প্রবীণ ব্রাহ্মরা যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে এ বেশি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন তা তাঁদের পরবর্তী কর্মধারায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। হিন্দু মেলার মধ্যে অবশ্য শুধু হিন্দুত্বের নয়, স্বাদেশিকতার প্রেরণাও ছিল। এই স্বাদেশিকতাবোধ সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী নীল বিদ্রোহের (১৮৫৯—৬০) ফল। নীলকরদের অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতনের কথা আগে আমরা বর্ণনা করেছি (পৃষ্ঠা ৩১—৩৬)। নীল বিদ্রোহ তারই প্রতিক্রিয়া। ১৮৫৯—৬০ সালে বাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষি ধর্মঘট করে নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। নদিয়া যশোহর পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। কারণ এই জেলাগুলিই ছিল নীলচাষের প্রধান কেন্দ্র। ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’—এ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহী চাষিদের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। দীনবন্ধু মিত্র ‘নীল দর্পণ’ নাটকে তার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। মাইকেল মধুসূদন এই নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, রেভারেন্ড জেমস লং তা প্রকাশ করেন। লং—এর কারাদণ্ড হয়, হরিশ্চন্দ্রেরও মৃত্যু হয়—
”নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম’ল, লঙের হল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।”
গভর্নমেন্ট যে নীল কমিশন (Indigo Commission) নিয়োগ করেন ১৮৬০ তার সুপারিশে অবশ্য প্রজারা বিশেষ উপকৃত হয়নি। কেবল নীলকরদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা কিছুটা সংযত হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ শাসকরা প্রজা বিদ্রোহের ভয়ে কিছুটা নীলকরদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তরা সিপাহি বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, তাঁরা নীল বিদ্রোহ মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করেন। হরিশ্চন্দ্র, দীনবন্ধু, মাইকেল তাঁদের নির্ভীক মুখপাত্র হন। এই সময়ে মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ প্রকাশও (১৮৬০) স্মরণীয় ঘটনা। রাবণ—সন্তান রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ মধুসূদনের কাব্যের নায়ক, জ্ঞাতিশত্রু বিভীষণ দেশদ্রোহিতার প্রতিমূর্তি। কাব্যের প্রতিপাদ্য, সুর ও নতুন ছন্দের মধ্যে আগাগোড়াই বিদ্রোহ। সনাতন ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে, গতানুগতিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ পেল মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’—এ। স্বাদেশিকতাবোধ, বীরত্ব ও বিদ্রোহের উজ্জীবন এই কাব্যের দানও উপেক্ষণীয় নয়।
জাতীয়তাবোধের নবজাগরণের এই পরিবেশে ‘হিন্দু মেলা’র উদ্ভব হয়। মেলার অনুষ্ঠানে যেমন জাতীয়তার সুর ধ্বনিত হয়—শুধু বাংলার নয়, সর্বভারতীয় জাতীয়তার—তেমনি তার হিন্দুত্বের প্রচারও বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। এই জাতীয়তার ধারা যেমন পরে ‘ভারত সভা’ ও জাতীয় কংগ্রেস’—এর মধ্যে হিন্দু বেশ অনেকটা ত্যাগ করে পূর্ণ রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে, তেমনি হিন্দুত্বের ধারাটিও ক্রমে প্রবল হয়ে ধর্ম ও সমাজসংস্কার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। রাজনীতির মধ্যেও হিন্দু ধারার মিলন—মিশ্রণ চলতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মন এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায় যদিও দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ধারা নয়, পাশাপাশি প্রবাহিত অথচ বহু শাখাপ্রশাখায় মিশ্রিত ধারা। অর্থাৎ জাতীয়তার ধারা হিন্দুত্বের পুনরভ্যুত্থান—ধারার সঙ্গে বরাবরই মিশ্রিত ছিল, যেমন হিন্দুত্ব ছিল জাতীয়তার সঙ্গে।
হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান—ধারাকে বেগবান ও শক্তিশালী করেছে ব্রাহ্মসমাজে প্রবীণ—নবীনদের আদর্শবিরোধ, অন্তর্বিরোধ, বিভেদ—বিচ্ছেদ, এবং উভয় গোষ্ঠীর পরবর্তী আদর্শচ্যুতি। দেবেন্দ্র—কেশবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম যে বিচ্ছেদ হয় তার মূল কারণ, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, দুটি : ৭২
“In reply to the Adi Brahmo Samaj cry of ‘Brahmoism is Hinduism’, the young reformers cried ‘Brahmoism is Catholic and Universal’, and on the question of caste they difinitely declared that its renunciation was as essential to Brahmoism as the renunciation of idolatry. These were the main issues upon which they parted.’’
বিচ্ছেদের পরে আদিমসমাজপন্থীরা ক্রমে হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। এই ঝোঁক দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল, উদার মধ্যপন্থাই তিনি শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করতেন। সামাজিক ও পারিবারিক আচার—অনুষ্ঠানে তিনি হিন্দুত্বের সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ কাম্য বলে মনে করতেন না। দেবেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেও শিবনাথ বলেছেন : ৭৩ “Devendra Nath who has justly acquired the title of Maharshi, a great seer, from his countrymen, was essentially a Hindu in all his spiritual aims and aspirations. He ever remained so.” কেশবপন্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে আদিসমাজ সামাজিক—পারিবারিক আচার—অনুষ্ঠান (অনুষ্ঠানপদ্ধতি)—যেমন ব্রাহ্মণের উপনয়ন, বিবাহে সপ্তপদী ইত্যাদি—হিন্দু—ঘেঁষা করে সংস্কার করেন।৭৪ নবীন ব্রাহ্মদের প্রগতিশীল সমাজসংস্কারের দাবির এই প্রতিক্রিয়া তাঁদের মধ্যে দেখা দেয়, হিন্দুসমাজের বিক্ষোভ প্রশমিত করার স্বার্থে। দুর্বলের নিরাপদ আত্মরক্ষা ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না। আত্মসমর্পণ যে আত্মরক্ষার প্রশস্ত পথ নয়, বিভ্রান্তি, বিচ্যুতি ও পরাজয়ের পথ, ক্রমেই উনিশ শতকের সত্তরের মধ্যে সামাজিক আন্দোলনের ধারায় ব্রাহ্মদের পরিণতিতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীরা ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নস্তূপের উপর বিজয়—পতাকা প্রতিষ্ঠা করেন।
সমকালের সাময়িকপত্রের আলোচনায় এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্রাহ্মদের অন্যতম মুখপত্র ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় দেওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার আলোচনাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।৭৫ দু—একটি নমুনা উল্লেখ করছি। ‘হিন্দু সমাজের সহিত ব্রাহ্মদিগের সংস্রব রাখা উচিত কি না?’ শিরোনামে ‘সোমপ্রকাশ’ লেখেন (২৯ মাঘ ১২৭০) :
”হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী ও স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, ব্রাহ্ম ও হিন্দু সেরূপ নহে। ব্রাহ্মেরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম। হিন্দুদিগেরও সেই আদি ধর্ম। জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন।… ফলতঃ ব্রাহ্মে ও হিন্দুতে বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ে এক জাতীয় ও এক ধর্মাবলম্বী, কেবল কিঞ্চিৎ প্রস্থান ভেদ এই মাত্র।”
১৮৬৭—৬৮ সাল থেকে ব্রাহ্ম বিবাহ আইনসংগত করার জন্য প্রধানত কেশবপন্থীরা আন্দোলন আরম্ভ করেন। তার কারণ ব্রাহ্ম বিবাহ পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিক হিন্দু বিবাহ নয় বলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা ব্রাহ্ম বিবাহ ‘অবৈধ’ বলে অভিযোগ করেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা স্বীকৃত না হলে পরে নানা রকমের সামাজিক ও পারিবারিক জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে। তার জন্য কেশবপন্থীরা ব্রাহ্ম বিবাহ আইন পাশ করার দাবি উত্থাপন করেন। প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্মদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়। অবশেষে আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ সালে তিন—আইনে রেজিস্টারি বিবাহের আইন পাশ হয়। ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতার এই আন্দোলনের সময় আদি সমাজপন্থী ব্রাহ্মরা দীর্ঘ ও দ্রুত পদক্ষেপে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের দিকে এগিয়ে যায়। রাজনারায়ণ বসু এই সময় (১৮৭২) ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা হয় ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ভবনে। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি। ‘আত্মচরিত’এ রাজনারায়ণ লিখেছেন : যেদিন ”বক্তৃতা করা হয়, সেদিন লোকে লোকারণ্য। বক্তৃতা করিবার সময় করতালি ঐ বাটীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই কেবল দিয়াছিলেন এমত নহে, বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান শ্রোতারা পর্যন্ত উহা দূর হইতে শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন।” সভার উপস্থিত ব্রাহ্মদের লক্ষ্য করে হিন্দুরা বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করতে থাকেন—”শুনলেন তো, এবার গোবর খেয়ে আবার হিন্দু হয়ে যান।” ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা মন্তব্য করেন—”হিন্দুধর্মে ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহা রক্ষা করিলেন।” কলকাতার সনাতন হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার মুখপাত্ররা রাজনারায়ণকে বলেন, ‘হিন্দুকুলচূড়ামণি।’ কেউ বলেন, রাজনারায়ণ ‘কলির ব্যাসদেব।’ ”কলিকাতার প্রগাঢ় সাকারবাদী হিন্দু বিখ্যাত শিবচন্দ্র গুহ বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণবাবুর একটি প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করা কর্তব্য।” সনাতনধর্মীরা তাঁকে হিন্দু সভার সভ্য হতে অনুরোধ করেন, ”কিন্তু সাকারবাদীদিগের সহিত একীভূত হইবার ভয়ে তাহা হইতে বিরত হই” (রাজনারায়ণ)। ত্রিবেণীর কাছে আকনা গ্রামের ‘গাঢ় সাকারবাদী হিন্দু’ দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ স্থানীয় লোকেদের কাছে রাজনারায়ণ বসুর পরিচয় দিয়ে বলেন ”ইনি অন্যরূপ ব্রাহ্ম নহেন। ইনি হিন্দু ব্রাহ্ম।” ‘ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া’র সম্পাদক জেমস রাটলেজ বক্তৃতার প্রশংসা করে বিলেতের ‘টাইমস’ পত্রিকায় লেখেন। প্রতিবাদ করেন বাঙালি খ্রিস্টান রেভারেন্ড লালবিহারী দে। তিনি বলেন যে শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর থেকে চুন আমদানি করে হিন্দুধর্মের কলি ফেরানো হচ্ছে। কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী এই বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়। সমাজের স্রোত তখন সবেগে হিন্দুমুখী হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের চরিতকার অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন :৭৪
‘দেশের স্রোত অন্যান্য খাত কাটিয়া বাহিয়া চলিল এবং ব্রাহ্মসমাজের নদী ক্রমশঃ মরা নদী হইয়া দাঁড়াল। এই বিখ্যাত ১৮৭২ সালেই বঙ্কিমের প্রতিভার নবরবি ‘বঙ্গদর্শনে’র ভিতর দিয়া দেশে এক নূতন প্রভাত উপস্থিত করিল। কিন্তু এই নূতন সাহিত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের ভাব ও আদর্শের কিছুমাত্র প্রভাব থাকিল না। তারপরে এই নূতন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকেও দেশের স্রোত ফিরিল। মনমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ইঁহারা ‘ভারত সভা’ স্থাপন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করিয়া দিলেন। ক্রমশঃ কনগ্রেস কনফারেন্সের আরম্ভ হইল। তখন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের যুগ গিয়া স্বাদেশিকতার যুগ এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ দেখা দিল। ক্রমে শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অলকট ব্ল্যাভাটসকির থিয়সফির আন্দোলন, অদৃশ্য মহাত্মা সূক্ষ্ম শরীর প্রভৃতি গুহ্য সাধনার ব্যাপার হিন্দুধর্মের সার বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা, রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের এক নূতন অদ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাসের আন্দোলন—এই সমস্ত পরে পরে উপস্থিত হইতে লাগিল। এ সমস্তের ভিতরকার কথা এই যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতা পাশ্চাত্ত্য দেশের ধর্ম ও সভ্যতার চেয়ে কোনো অংশে খর্ব নয়, চাই কি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।”
১৮৭০—৭২ সাল থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার সমাজজীবনের মূলধারাগুলি এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ—বিকার ও ক্রমিক অবনতি, জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় সাহিত্যের স্বাভাবিক স্বজাতি—ঐতিহ্যগৌরব, ক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীদের শক্তিশালী করে তোলে।
‘হিন্দু ব্রাহ্ম’ ছাড়া ব্রাহ্মদের মধ্যে যে ‘অন্যরূপ ব্রাহ্ম’রা ছিলেন, তাঁদের ব্রাহ্মত্বকে শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রই সংকটাপন্ন করে তোলেন। কেশব—চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ভাবাতিশয্য। এদিক থেকে তিনি খাঁটি বাঙালিই ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতায় শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতেন। ১৮৬০ সালের শেষদিক থেকে কেশবের মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও অবতারভাবের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তাঁর বিখ্যাত ‘Great Men’ বক্তৃতার মধ্যেই (১৮৬৬) অবতারবাদের বীজ রয়েছে দেখা যায় :
‘‘Great men are sent by God into the world to benefit mankind. They are his apostles and missionaries who bring to us glad tidings from heaven; and in order that they may effectually accomplish their errand they are endowed by him with requisite power and talents.’’
১৮৬৮ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, যদুনাথ চক্রবর্তী ও নীলকমল দেব একখানি পত্র প্রকাশ করে কেশবের অবতারভাবের প্রতিবাদ করেন :৭৭
”আমরা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে কতিপয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তিদাতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহার নিকট পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন এবং কেহ কেহ তাঁহার চরণধূলি লইলেন কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যে এখানে এই ভারতবর্ষে তাঁহার চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহার মুক্তি হইবে না। তিনি একজন ঈশ্বরাবতার। ঐ সকল ব্রাহ্মের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের পত্রে কেশববাবুকে ‘দয়াল প্রভু’ ‘পাপীর গতি’ প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন। কখন কখন তাঁহার কেশববাবুকে লইয়া কোন বিশেষ সঙ্গীত করিতে করিতে রাজপথে পরিব্রজণ করেন।”
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ‘সোমপ্রকাশ’ কেশবের অবতারভাবের কঠোর সমালোচনা করেন, যদিও ‘সোমপ্রকাশ’ ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজের সংশ্লিষ্ট পত্রিকা নয়। ‘সোমপ্রকাশ’ লেখেন (৫ পৌষ ১২৭৫) :৭৮
”বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণের ব্যবহারবিষয়ক বিস্তর পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। আরো অনেকগুলি দীর্ঘপত্র আমাদিগের হস্তে রহিয়াছে। এক বিষয় লইয়া অধিকতর আন্দোলন করা আমাদিগের ব্যবহারানুগত নহে। বিশেষতঃ কেশববাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বালকবৎ ব্যবহার করিতেছেন।… বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণ ভালরূপে লেখাপড়া জানেন বলিয়া অভিমান করেন। আমাদিগেরও এতদিন ঐ সংস্কার ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য দেখিয়া এখন বিপরীত জ্ঞান জন্মিতেছে। মানুষের চরণরেণু লেহন এটি কি কৃতবিদ্যের পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার নহে? কৃতবিদ্যের এত নীচ কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে, আমরা অগ্রে ইহা জানিতাম না। কেশববাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বিদ্যার অবমাননা করিবার নিমিত্ত কি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন।”
অবতারভাবোন্মাদ ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখে মুগ্ধ হন এবং ২৮ মার্চ তাঁর পরিচালিত The Indian Mirror পত্রিকায় সেই সংবাদ প্রকাশিত হয়। যত দূর জানা যায়, পত্রিকায় এই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণর সংবাদ প্রচারিত হয়। অতঃপর কেশবগোষ্ঠীর ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ ‘ধর্মতত্ত্ব’ ‘সুলভ সমাচার’ ‘The New Dispensation’ প্রভৃতি পত্রিকায় দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ—সংবাদ প্রচারিত হতে থাকে।৭৯ কেশবের খ্যাতি ও প্রতিভার দীপ্তি তখনও শিক্ষিত বাঙালির কাছে সর্বোজ্জ্বল। তাঁরা স্বভাবতই দক্ষিণেশ্বরমুখী হয়ে ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের অকৃত্রিম মাধুর্য, তাঁর ধর্মমতের উদারতা এবং পরে স্বামী বিবেকানন্দর মতো অনন্যসাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব ও সহযোগ শিক্ষিত—অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালির মন সহজেই আচ্ছন্ন করে ফেলে।
অবশেষে যে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন করে ‘তিন—আইন’ পাশ করান, সেই কেশবচন্দ্র নিজের কন্যার বিবাহ দেন কোচবিহার রাজ—পরিবারে হিন্দু মতে। ১৮৭৮ সালে বিবাহ হয়। তার ফলে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় বিচ্ছেদ হয় এবং ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৭৮ মে)। কেশব—অনুরাগীরা ‘নববিধান’ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দমোহন বসু হন ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে’র প্রথম সভাপতি, শিবচন্দ্র দেব প্রথম সম্পাদক এবং উমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম সহকারী সম্পাদক। কিন্তু তার ফলে ব্রাহ্মসমাজের মরা গাঙে আর জোয়ার আসেনি।* সমাজজীবনের স্রোত তখন অন্যান্য খাতে প্রবল বেগে বইতে আরম্ভ করেছে। শিবনাথ লিখেছেন :৮০
“The Brahmo Samaj rose with Keshub Chunder Sen; with him, perhaps, it has gone down in public regard, I say this with great very great, regret, and with a sense of shame, that we, the standard-bearers of the new faith, have not proved quite worthy of the trust reposed in us.
ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রর এই পরিণতি থেকে মনে হয়, বাঙালি চরিত্রে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও ভাবাবেগ কত গভীরে প্রসৃত। আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির কাছে বোধহয় কেশবচন্দ্রই প্রথম অবতারবাদের মোহজাল নতুন করে বিস্তার করেন, যে মোহজাল থেকে আজ পর্যন্ত, সাধারণ বাঙালি তো দূরের কথা, শিক্ষিত বাঙালিরাই মুক্ত হতে পারেননি। কেশব—পরবর্তীকালে বড় বড় অবতারের আবির্ভাব হয়েছে বাংলা দেশে। বিশ শতকের অপরাহ্ণেও দেখা যায়, বাংলা দেশে অবতারের সংখ্যা অগণিত, এবং তাঁদের অনুচরবর্গের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির সংখ্যাই বেশি। মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুসমাজের এই অবতার—উপসর্গ সমাজতাত্ত্বিকের কাছে প্রহেলিকা মনে হয়। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করলে এই প্রহেলিকা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়।
কেশবচন্দ্রর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার দীপ্তি যখন ব্যক্তিপূজা ও অবতারবাদের রাহু গ্রাস করতে উদ্যত হল, তখন বঙ্কিম—প্রতিভার নতুন সূর্যোদয় হল বাংলার আকাশে এবং তার বর্ণচ্ছটায় শিক্ষিত বাঙালি ও ভাবুক বাঙালি যেন বিমুগ্ধ হয়ে গেল। যদিও কেশবের পরে তৎকালের তরুণদের কাছে শিবনাথ—আনন্দমোহনের ব্রাহ্মধর্মের যুক্তিবাদিতা ও উদারতার খানিকটা আকর্ষণ ছিল, তাহলেও, ‘বঙ্গদর্শন’—যুগের বঙ্কিমের কাছে সে আকর্ষণ ম্লান হয়ে গেল। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন তরুণ ছাত্র। তিনি লিখেছেন :৮১
“Shivanath’s Brahmoism was more attractive to me than that of the Keshub… Social freedom and national emancipation were both organic elements of Shivanath’s religion and piety.”
শিবনাথ—আনন্দমোহনের ব্রাহ্মধর্ম যদিও সামাজিক ও জাতীয় মুক্তিচিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল, তাহলেও বঙ্কিমচন্দ্রর স্বাদেশিকতা, বিচারশীল ঐতিহ্যগৌরব, পাশ্চাত্য বিদ্যা ও প্রাচ্য বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য (রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে সে যুগের ‘শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ’ বলেছেন) এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যানুশীলনের ভিতর দিয়ে তার যুগান্তকারী রূপায়ণ খুব সহজেই বাংলার শিক্ষিত তরুণের মন ও জনমন জয় করে ফেলল। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন : “The generation of Bengalee youths to which I belonged came, however, in more direct contact with the ‘Bangadarshan’ than with the ‘Tattabodhini’ School”. তার কারণ বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র স্মৃতিকথায় লিখেছেন : ৮২
“The years 1875-1878… saw the birth of our new Nationalism. This new Nationalism had its origin in a renaissance in Bengalee literature brought about by our contact with modern European thought… Bankim Chandra was, in a special sense, the prophet of this renaissance… Bankim Chandra, combining in himself the novelist, the historian, the essayist, and the critic, was the centre and organising genius of this renaissance. The ‘Bangadarshan’ School did for contemporary Bengalee thought literature what the French Encyclopaedists did for 18th century European thought and French literature.”
রামমোহন—ইয়াং বেঙ্গল—তত্ত্ববোধিনী—বিদ্যাসাগরের যুগকে যদি উনিশ শতকের বাংলার প্রথম পর্বের নবজাগরণ বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রর যুগকে বলা যায় দ্বিতীয় পর্বের নবজাগরণ। দ্বিতীয় পর্বের নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রাচ্য—পাশ্চাত্যের আদর্শ—সমন্বয়ে গভীর স্বাজাত্যবোধের অনুরঞ্জন। এই স্বাজাত্যবোধের একটি ধারা, অলকট—ব্লাভাটস্কি প্রমুখ পাশ্চাত্য থিয়োজফিস্টদের প্রভাবে এবং তিরিশের ‘ধর্মসভা’র অন্তঃসলিলা রক্ষণশীল প্রবাহের উচ্ছ্বাসে হিন্দু—ঐতিহ্যমুখী হয়ে ওঠে। দেশের যা—কিছু সব ভালো, বিদেশের যা—কিছু সব খারাপ এবং প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম জ্ঞান—বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আকর, এরকম একটা মনোভাব ঐতিহ্যাবদ্ধ পুনরুত্থানবাদীদের মধ্যে প্রকট হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারার সমর্থক ছিলেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে তিনি স্বজাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অনুশীলন ও পুনর্মূল্যায়নের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ‘কৃষ্ণচরিত্র’ (১৮৮৬) তার সাক্ষী। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :
”বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনা বোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।” (আধুনিক সাহিত্য)
‘বঙ্গদর্শন’—এর যুগে (১৮৭২ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত বলা যায়) বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘সব্যসাচী’। ”সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে, এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।” (রবীন্দ্রনাথ)। জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনে, সাহিত্যসৃষ্টি ও সমাজসংস্কারকর্মে বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধ পাশ্চাত্যপন্থীদের ও অন্ধ দেশাচারপন্থীদের ”ধূম এবং ভস্মরাশি” দূর করার ভার নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে তাঁর ‘গঠনকার্য’ চলছিল প্রখর স্বাজাত্যবোধ ও দেশকাল—সাপেক্ষতার ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ মানবমুখী যুক্তিবাদ ও উদারতার অভিযানে—ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য—সংস্কৃতিক্ষেত্রে। সাহিত্য—বিজ্ঞান—দর্শন সমাজতত্ত্ব—ধর্মতত্ত্ব—ইতিহাস—অর্থনীতি—ভাষা—সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত অভিযান আরম্ভ হল ‘বঙ্গদর্শন’—এর যুগে এবং তার মধ্যে যে সুর সর্বোচ্চগ্রামে ধ্বনিত হতে থাকল, তা হল স্বাদেশিকতার সুর। এই সুরের ভাবোদ্দীপ্ত ঝংকার প্রথম শোনা গেল ‘কমলাকান্ত’ (১৮৭৫) : ”চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকা রূপিণী—অনন্তরত্ন—ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।” এই সুরের গম্ভীর পরিণতি হল ‘আনন্দমঠ’—এ (১৮৮২) ‘বন্দে মাতরম’ সংগীতে। নবজাতীয়তাবোধ—উদ্ভূত এই নবজাগরণের গুরু হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।
‘কমলাকান্ত’র দৃষ্টি দিয়ে নতুন করে আমরা চিনলাম আমাদের ‘জননী জন্মভূমি’কে। ‘কমলাকান্ত’র প্রকাশকালে, ‘বঙ্গদর্শন—এর মধ্যাহ্নে, ‘ভারত সভা’ (Indian Association) স্থাপিত হল (২৬ জুলাই ১৮৭৬)। নীল বিদ্রোহ, হিন্দু মেলা, বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’—এর ভিতর দিয়ে যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ও বিস্তার হচ্ছিল, তার প্রকাশ হল ‘ভারত সভা’ সংগঠনে। তার আগের বছর শিশিরকুমার ঘোষের উদযোগে ‘ইন্ডিয়ান লিগ’ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৫) স্থাপিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ও জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র এই সময় ‘বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন’ নামে একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। বাংলার তরুণদের মনে জাতীয়তাবোধ উজ্জীবনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, শিবনাথ ও তাঁদের সহকর্মীরা সচেষ্ট হন এবং ‘ছাত্রসভা’ (Students’ Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতায় (ম্যাৎসিনি, শিবাজি, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বিষয়ে) তরুণরা উদবুদ্ধ হন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : ৮৩
“I felt that the political advancement of the country must depend upon the creation among our young men of a genuine, sober and rational interest in public affairs. The beginnings of public life must be implanted in them…, They must, on the one hand, be stirred out of their indifference to politics, which was prevailing attitude of the student-mind in Bengal in 1875, and on the other, protected against extreme fanatical views which, as all history shows, are fraught with peril in their pursuit. I was resolved, so far as it lay in me, to foster a new spirit and to produce a new atmosphere. This was the underlying idea that prompted me to help in the organisation of the Students’ Association.
‘ভারত সভা’র ভিতর দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ এই রাজনৈতিক আদর্শ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অগ্রসর হন। ‘ভারত সভা’ দেশের একটি বড় রাজনৈতিক অভাব পূরণ করে। দেশের বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধিস্থানীয় কোনও রাজনৈতিক সংস্থা এতদিন পর্যন্ত ছিল না। “British Indian Association” বা ‘ভারতবর্ষীয় সভা’ ছিল মুখ্যত উচ্চশ্রেণির ও জমিদারদের সভা এবং তাঁরা মধ্যবিত্তশ্রেণির রাজনৈতিক—গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন (পৃষ্ঠ ২১৫—১৭ দ্রষ্টব্য)। ‘ভারত সভা’ রাজনীতিক্ষেত্রে বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তশ্রেণির সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়। সুরেন্দ্রনাথলিখেছেন :৮৪
“The Indian Association supplied a real need. It soon focussed the public spirit of the middle class, and became the centre of the leading representatives of the educated community of Bengal.”
ইতালির ম্যাৎসিনি হলেন সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শের প্রেরণাদাতা :৮৫
‘Mazzini had taught Italian unity. We wanted Indian unity. Mazzini had worked through the young. I wanted the young men of Benal to realize their potentialities and to qualify themselves to work for the salvation of their country…”
‘ভারত সভা’ প্রথমে ‘সিভিল সার্ভিস’ পরীক্ষায় ভারতীয় প্রতিযোগীদের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করে। লালমোহন ঘোষ সভার মুখপাত্র হয়ে বিলেত যান। সমগ্র উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারত সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবির কথা প্রচার করে জনচিত্তে বিপুল সাড়া জাগান। ‘ভারত সভা’ হয় ‘জাতীয় কংগ্রেস’—এর অগ্রদূত।
মধ্যবিত্ত—পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্রের ব্রিটিশ কুশাসনের সমালোচনা এই সময় তীব্রতর হতে থাকে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য Vernacular Press Act (১৪ মার্চ ১৮৭৮) পাশ করা হয়, ভারতীয়দের নিরস্ত্র করার জন্য Arms Act—ও বিধিবদ্ধ হয়। তার ফলে মধ্যবিত্তের জাতীয় চেতনা আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। জনমত গঠন ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে ‘ভারত সভা’র দ্রুত অগ্রগতি হতে থাকে। ১৮৭৯ সালে ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়ে (পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ) সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেন।
১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিলের (Ilbert Bill) আন্দোলন আরম্ভ হয়। রিপনের নির্দেশে তাঁর আইনসচিব ইলবার্ট বিচারবিভাগে ভারতীয়—ইংরেজের বর্ণবৈষম্যজনিত অধিকারভেদ দূর করার জন্য এই আইনের খসড়া করেন। ভারতের বিদেশি শ্বেতাঙ্গরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কবি হেমচন্দ্র এই সময় লেখেন :
”গেল রাজ্য, গেল মান, হাঁকিল ইংলিশম্যান
ডাক ছাড়ে ব্রানশন কেশুয়িক, মিলার—
নেটিবের কাছে খাড়া, ‘নেভার—নেভার”!
বিচারপতি নরিস হাইকোর্টে শালগ্রাম শিলা আনিয়ে এক মকদ্দমার বিচার করেন বলে বিভিন্ন পত্রিকায় সমালোচনা করা হয়, সুরেন্দ্রনাথও সমালোচনা করেন। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর কারাদণ্ড হয় (মে ১৮৮৩)। তার ফলে জনসমাজে বিক্ষোভ তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে, তরুণ ছাত্রসমাজ স্বভাবতই তার শীর্ষে থাকেন। এই ছাত্রবিক্ষোভ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন।৮৬
“In the demonstration that followed the passing of the sentence they took a leading part in a fashion common among young men all over the world, smashing windows and pelting the police with stones. One of those rowdy youths was Asuthosh Mukherjea…”
বিক্ষুব্ধ ‘rowdy’ ছাত্রদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও একজন ছিলেন।
ইলবার্ট বিল ও সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের আন্দোলনের ফলে (১৮৮২—৮৩) সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনা আরও ব্যাপক ও গভীর হয়। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রর ‘আনন্দমঠ’ প্রকাশিত হয় এবং তাঁর ‘বন্দে মাতরম’ সংগীত দেশবাসীর মর্মস্থল পর্যন্ত স্বজাতি অনুরাগে রঞ্জিত করে তোলে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিশ শতকের গোড়ায় ‘স্বদেশি আন্দোলন’—এর অভ্যুত্থান পর্যন্ত ‘বন্দে মাতরম’ হয় দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ধ্বনি, পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই ধ্বনির মাহাত্ম্য এতটুকু ম্লান হয়নি। স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতও আজ বঙ্কিমচন্দ্রর ‘বন্দে মাতরম’। ‘বন্দে মাতরম’ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :৮৭
“They cry, at one time banned and barred and suppressed, has become pan-Indian and national, and is on the lips of an educated Indian when on any public occasion he is moved by patriotic fervour to give expression to his feelings of joy… Its stately diction, its fine musical rhythm, its earnest patriotism, have raised it to the status and dignity of a national song…”
১৮৮২—৮৩ সালের মধ্যে সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়, সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায়। এর মধ্যে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ‘ভারত সভা’র যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হয়। সুরেন্দ্রনাথ কারাবাস থেকে মুক্ত হয়ে এসে তাঁর সহকর্মীদের প্রস্তাবে, ‘ভারত সভা’র আনুকূল্যে, কলকাতায় একটি ‘ন্যাশনাল কনফারেন্স’ আহ্বান করেন (ডিসেম্বর ১৮৮৩)। ২৮, ২৯,৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৩ কলকাতার ‘অ্যালবার্ট হল’—এ অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় ভারত ভ্রমণ করে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আহ্বান জানান (১৮৮৪)। ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৫ কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে ‘জাতীয় সম্মেলন’—এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন ও মহমেডান অ্যাসোসিয়েশনও যোগ দেন। ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫ বোম্বাই শহরে ভারতের ‘জাতীয় কংগ্রেস’—এর প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম অধিবেশনে যদিও সভাপতি হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহলেও বাংলার বিশিষ্ট নেতারা (সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখ) কেউ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি। তার কারণ বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের প্রথম উদ্যোক্তারা যতটা ইংরেজ রাজানুগত্যের ছায়ায় থেকে রাজনৈতিক দাবিদাওয়া—অভিযোগ জ্ঞাপন করতে চেয়েছিলেন, বাঙালি সুরেন্দ্রনাথ—আনন্দমোহন—শিশিরকুমার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঠিক ততটা ছায়ার নিচে থাকতে চাননি। মনে হয় এই কারণেই তাঁদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতায় (১৮৮৬), সভাপতি হন দাদাভাই নৌরজি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। সুরেন্দ্রনাথ—আনন্দমোহন—মতিলাল সকলে অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনের নিখুঁত বিবরণ দিয়ে ‘সোমপ্রকাশ’ লেখেন :৮৮
‘জাতীয় সভার সৃষ্টি দিবসে বোম্বাই নগরে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল বটে, কিন্তু জাতীয় সভার দ্বিতীয় বৎসরে কলিকাতা মহানগরীতে যে অপূর্ব দৃশ্য ভারতবাসীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বোম্বাই সভা স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ভারতবাসী যাহা স্বপ্ন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, গত ২৬শে ডিসেম্বরের রাত্রি প্রভাত হইলে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সে স্বপ্ন নহে প্রকৃত ঘটনা। কলিকাতার রাজপথ ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিতে পরিপূর্ণ, ঘোর কলরবে দিগদিগন্তর প্রকম্পিত, লক্ষ লক্ষ ধনী মানী দরিদ্র, রাজা প্রজায় রাজপথ অবরুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন, শকটে শকটে কলিকাতার বক্ষ প্রকম্পিত হইতেছে, আশায় উৎসাহে প্রফুল্ল নেত্রে ঊর্ধ্বমুখে, প্রাণের আবেগে ভারতবাসী লক্ষ লক্ষ প্রজা কোন ঐশী বলে বলীয়ান হইয়া একযোগে, এক পন্থার পথিক হইয়া যেন কোন অপূর্ব জগতে গমন করিতেছেন।…’
প্রত্যক্ষদর্শী ‘সোমপ্রকাশ’—প্রতিনিধির এই বিবরণ থেকে বাংলাদেশে কলকাতা শহরে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে জনসমাজে যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায়, এবং বোঝা যায় বোম্বাই এর সঙ্গে কলকাতার স্বাদেশিকতামুখী সামাজিক পরিবেশের পার্থক্য কত। কিন্তু কংগ্রেস—রাজনীতির তাৎকালিক লক্ষ্য ‘সোমপ্রকাশ’—এর এই বিবরণের কয়েকটি মন্তব্যের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন—”পার্সী জাতির শিরোমণি মিঃ দাদাভাই নাওরাজী জাতীয় সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন… এই মহাত্মা জাতীয় সভার উচ্চতম আসন গ্রহণ করিয়া প্রথমেই রাজভক্তির চূড়ান্তভাব প্রকাশ করিলেন।” ”যে সকল মুসলমান জাতীয় কনগ্রেসে যোগদান করেন নাই নবাব রেজা আলি তাঁহাদের নিন্দা করিয়া বলিলেন ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে কেবল এই কয়েকজন লোক ভিন্ন কনগ্রেস সভায় কাহারও বিরূপ দৃষ্টি নাই।” ”কন্গ্রেসের সকল সভ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে ভারতবাসী ইংরাজকে রাজ্য দিয়া সুখী হইয়াছেন।”
পরিষ্কার বোঝা যায়, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীনতার কথা তখনও চিন্তা করতে পারেননি। দেশের উচ্চশ্রেণি ও মধ্যশ্রেণির ঊর্ধ্বস্তরের মধ্যেই তখন কংগ্রেস গণ্ডিবদ্ধ ছিল এবং ব্রিটিশ শাসকদের কাছে, প্রধানত আবেদন—নিবেদনের ভিতর দিয়ে, তাঁরা শ্রেণিস্বার্থের আংশিক চরিতার্থতার জন্যই প্রথমে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে আমাদের জাতীয় আন্দোলন গণ—আন্দোলন ও পূর্ণ—স্বাধীনতার লক্ষ্যের পথে পৌঁছেছে প্রায় বিশ শতকের তিরিশে। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশেও কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এবং বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গবিভাগের (১৯০৫) ফলে জাতীয়তাবোধের এক বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস বাংলা দেশ থেকে সর্বভারতে উৎসারিত হয়।৮৯
জাতীয় আন্দোলনের এই ধারার পাশে সামাজিক আন্দোলনের যে ধারাটি প্রবলবেগে বাংলা দেশে বইছিল, সে সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :৯০ “Practically the whole decade, 1880 to 1890, was marked by a strong current of religious revival and social reaction which positively set back the movement of progress not only in Bengal but all over India.” এই সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল ধারার প্রবাহ শক্তিশালী করেছে “the revival of mediaevalism in the Brahmo Samaj itself” এবং থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির আন্দোলন—“which… was perhaps the most powerful of the forces that brought in this movement of Hindu religious revival and social reaction.” (বিপিনচন্দ্র)।৯১ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কীভাবে ক্রমে ম্লান হয়ে গেল, ১৮৭০—এর দশকের মধ্যে, সে কথা আগে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক মঞ্চে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে কেশবচন্দ্রর ব্যক্তিত্বের শেষ জ্যোতিটুকুও নিভে গেল। পৌরাণিক অবতারবাদের মোহাচ্ছন্নতা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাটল না, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মাহাত্ম্য প্রচার করেই প্রায় তাঁর বাকি জীবনটা কেটে গেল। অন্যদিকে প্রবীণ ব্রাহ্মদলের অন্যতম মুখপাত্র রাজনারায়ণ বসু ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ প্রতিপাদনের পর (১৮৭২—৭৩) ‘মহা হিন্দু সমিতি’ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ‘জাতিভেদ’ সম্বন্ধেও তাঁর মতামত প্রায় সনাতন হিন্দুপন্থী হয়ে ওঠে। রাজনারায়ণ বলেন :৯২ ”জাতিভেদ প্রথা কেবল ধর্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্বক লোক সমাজের উপকার সাধন করে এমত নহে; দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া আর এক প্রকারেও লোকসমাজের উপকার সাধন করে।” জাতিভেদের সমর্থনে রাজনারায়ণ সুজনবিদ্যার (Eugenics) সাহায্য নিয়েছেন। ‘বৃদ্ধ হিন্দুর আশা’র (১৮৮৬—৮৭) মধ্যে তিনি মহা হিন্দু সমিতির স্থাপনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন :৯৩
”মুসলমানদিগের যেমন National Mahommedan Association নামে জাতীয় সভা, ভারতপ্রবাসী ইংরেজদিগের যেমন Anglo-Indian Defence Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদের Eurasian and Anglo-Indian Association নামক যেমন জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটি জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়। যে প্রয়োজন দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া, ঐ ঐ জাতি ঐ ঐ জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ প্রয়োজন হিন্দুদিগের আছে। হিন্দুদিগের ধর্মসম্বন্ধে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে।… হিন্দুজাতির উন্নতি সাধনার্থ কোন সভা যদি ধর্মমূলক না করিয়া সংস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে বুনিয়াদশূন্য, ও গাঁথুনিশূন্য আলগা ইষ্টকের বাড়ী যেমন প্রবল বায়ুর প্রথম ঝটিকাতে পড়িয়া যায়, তেমনি সভা বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য মহা হিন্দু সমিতিকে ধর্মমূলক করা হইয়াছে। এইজন্য এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের স্তব করিয়া সভা আরম্ভ হইবে এবং কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্যন্ত দেবপূজা উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, কারণ ভারত মাতার হিতার্থ একত্রিত হওয়া অপেক্ষা কোন ধর্মক্রিয়া শ্রেষ্ঠতর?”
লক্ষণীয় হল, রাজনারায়ণ বসু এই ‘বৃদ্ধ হিন্দুর আশা’ ব্যক্ত করেন কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনকালে। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ রাজনারায়ণের প্রস্তাব সমর্থন করে লেখেন (কার্তিক ১৮০৮ শক, ১৮৮৬) : ”এখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বলে আমাদের অনেক উৎকর্ষ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন স্বদেশানুরাগী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার রক্ষা বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। …এই ঘোর বিপ্লবের সময় সভা সমিতি বা যে কোন উপায়েই হোক যিনি এই হিন্দু জাতির বিনাশোন্মুখ ধর্ম রীতি রক্ষার সূচনা করিবেন তিনি বাস্তবিক এদেশের একজন পরম বন্ধু।” রাজনারায়ণ ও তত্ত্ববোধিনীর ‘হিন্দু জাতির বিনাশোন্মুখ ধর্ম রীতি রক্ষা’র আবেদন একসুরে বাঁধা। এই ‘মহা হিন্দু সমিতি’র প্রস্তাবের ফলে যে আন্দোলন হয়, সে সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন :৯৪ ”আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশা সংবাদপত্রে আন্দোলন উৎপাদন দ্বারা বোয়ালিয়া ধর্মসভা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য ধর্মসভাকে প্রথমতঃ মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপন করিতে অভিলাষী ও তৎপরে [পশ্চিমের ‘ভারত ধরম’] মহামণ্ডলের সঙ্গে যোগ দিতে উত্তেজিত করে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।”
রামমোহনের কালে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ‘ধর্মসভা’ গঠিত হয়েছিল। পঞ্চাশ বছর পরে ব্রাহ্মসমাজের নীতিবিকৃতি ও বিচিত্র কার্যকলাপ হিন্দুধর্মসভার ভারতব্যাপী পুনরুত্থানে সহায় হয়। ইয়াং বেঙ্গল ও বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে ১৮৮০—৯০ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানসতার দোলন (swing) বিস্ময়কর মনে হয়। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন, পরাধীন দেশে স্বাদেশিকতাবোধ স্বভাবতই জাতীয় ঐতিহ্যমুখী হয়। কিন্তু স্বাদেশিকতার এই স্বাভাবিক ঐতিহ্যপ্রবণতা স্বীকার করেও পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালির মনের গতির প্রায়—বিপরীত বাঁক—পরিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়—পূর্ব যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডি ছিল সীমাবদ্ধ, এবং অভিজাত সমাজের মতো শিক্ষিতদের তখন একটা স্বতন্ত্র বিদ্যাকৌলীন্য ও চিন্তাভিজাত্য ছিল। সহজে তাঁদের চিন্তাজগতে সাধারণ স্তরের চিন্তার ছায়াপাত হত না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ—মারা বিদ্যা প্রচলিত হবার পর এবং সেই বিদ্যাশিক্ষার সুযোগবৃদ্ধির পর সমাজের সাধারণ স্তরভুক্ত অনেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কলেবর বৃদ্ধি করেন। শিক্ষার মান ও উদ্দেশ্যও আর্থিক পেশাগত হয়ে ওঠে, প্রকৃত বিদ্যা ও চিন্তার অনুশীলন, অথবা মনন—সাধনের সঙ্গে তার বিশেষ কোনও সম্পর্ক থাকে না। কাজেই সমাজের সাধারণ স্তরের চিন্তাভাবনা—আদর্শ এই সম্প্রসারণপর্বে শিক্ষিত বাঙালির মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেক পরিমাণে তাঁদের সুবুদ্ধি ও সুযুক্তিকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইম সমাজমানসের এই প্রকৃতি সম্বন্ধে বলেছেন :৯৫
“If a society in which various classes have very unequal standards of life, very unequal opportunities for leisure, and vastly dissimilar opportunities for psychological and critical development, offers the chances of cultural leadership to larger and larger sections of the population, the inevitable consequence is that the average outlook of those groups… tends more and more to become the prevalent outlook of the whole society… as a result of largescale ascent, the limited intelligence and outlook of the average person gains general esteem and importance and even suddenly becomes a model to which people seek to conform.”–(Emphasis added)
ম্যানহাইমের এই সামাজিক সূত্র বর্তমান জনতা—সমাজের (mass society) ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। বিশ শতকের অপরাহ্ণকালে বর্তমানে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে (এবং ভারতেরও, তবে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের স্বশ্রেণির তুলনায় বয়সে প্রবীণ বলে এই উপসর্গ তাঁদের মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রকট) যে ধর্মীয় (অবতারবাদ, গুরুবাদ, পৌত্তলিকতা, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি), সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রুচিবিকারের উপসর্গ দেখা যায় তা ম্যানহাইমের এই সমাজবিজ্ঞানের সূত্র দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই সূত্রের প্রাথমিক ক্রিয়া আরম্ভ হয় উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব থেকে (১৮৭৫—১৯০০)—শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রথম প্রসারণকালে (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তখন স্বাদেশিকতার জোয়ার ও জনসংখ্যার স্বল্পতা ব্যাপক নৈতিক বিকৃতি ও অবনতি অনেকটা প্রতিরোধ করে, কিন্তু সামাজিক চিন্তাস্রোত সাধারণ স্তরের ধ্যানধারণা—বিশ্বাসের খাতে বইতে থাকে। এই প্রবাহ পথেই হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের আন্দোলন বাংলা দেশে শক্তিশালী হয় এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশকে সেইদিকে আকর্ষণ করে।
‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’—এর সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে রাজনারায়ণ বসু একখানি চিঠিতে লেখেন (১৫ জুন ১৮৭৮) :৯৬ “…it is evident that the Brahmo movement is a superficial one, and has not penetrated into the very depths of Hindu Society. What is the cause of this? The cause is we do not know how to move Hindu Society. Hindu Society must be moved in a Hindu way.” (emphasis added) রাজনারায়ণ বসু সত্য কথাই বলেছেন, কিন্তু ‘Hindu way’—টা কী? হিন্দুসমাজ ‘must be moved’, কিন্তু কোন দিকে, তার ‘direction’ কী? এই ‘direction’—এর উপর নিশ্চয় ‘way’ নির্ভর করে। তা ছাড়া ‘Hindu way’ একটি নয়, অনেক। বৈষ্ণবের পন্থা ও তান্ত্রিকের পন্থা এক নয়, শংকরের পন্থা ও শ্রীচৈতন্যর পন্থাও এক নয়। রাজনারায়ণের ‘জাতিভেদ’ রক্ষা ও ‘মহা হিন্দু সমিতির’ গঠনের পন্থা এবং কেশবচন্দ্রর অবতার—মাহাত্ম্যের পন্থাও এক নয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত রাজনারায়ণ—কেশবচন্দ্র বা তাঁদের পরবর্তী ব্রাহ্ম নেতা কারও পক্ষে ‘Hindu way’ আবিষ্কার করে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হিন্দুসমাজের গভীরে প্রোথিত করা সম্ভব হয়নি। বরং আবিষ্কার করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীদের পথই তাঁরা প্রশস্ত করেছেন।
১৮৮০ সালের পর থেকে বাংলা দেশে ‘হরিসভা’র দ্রুত বিকাশ হতে থাকে। ‘ব্রাহ্মসভা’র নকল ‘হরিসভা’। খ্রিস্টানদের উপাসনাসভার অনুকরণে ব্রাহ্ম উপাসনাসভা স্থাপন করে যেমন ব্রাহ্মসমাজ একসময় খ্রিস্টান পাদরিদের ধর্মাভিযান প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন,৯৭ তেমনি হিন্দু রক্ষণশীলরা ব্রাহ্মদের ধর্মীয় প্রভাব নির্মূল করার জন্য ‘হরিসভা’ স্থাপনে উদযোগী হলেন। সমাবেশ উৎসব (congregational worship) বাংলা দেশে বৈষ্ণবরাই প্রবর্তন করেন, সংকীর্তন ও মহোৎসবের ভিতর দিয়ে, কিন্তু তাতে শিক্ষিত শ্রেণি প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করতেন না। আধুনিক মণ্ডলী—বা—সমাবেশ উপাসনা ব্রাহ্মসমাজ—প্রবর্তিত, প্রধানত শিক্ষিতরাই সেই মণ্ডলীভুক্ত। এই ব্রাহ্মমণ্ডলী—উপাসনাসভার মডেলেই হিন্দুদের ‘হরিসভা’ গঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :৯৮
“It was the Brahmo Samaj which first introduced congregational worship in modern India. With this Hindu revival and reaction, Hari Sabhas commenced to grow up everywhere which inaugurated a kind of congregational worship. At meetings of these Sabhas, Scripture texts were read and expounded by some Pandit and hymns or bhajans wre sung. All this was clearly a reproduciton of the Brahmo mode of worship.”
হিন্দুদের এই হরিসভার আন্দোলন এমন ব্যাপক রূপ ধারণ করে যে গোঁড়া হিন্দুসমাজেই রীতিমতো ত্রাসের সঞ্চার হয়। ‘সোমপ্রকাশ’ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র নয়, হিন্দুসমাজেরই মুখপত্র। তৎসত্ত্বেও ‘হরিসভা’র বিস্তার ও কার্যকলাপ প্রসঙ্গে ‘সোমপ্রকাশ’ যে আলোচনা করেন (১৮ শ্রাবণ ১২৯৩), তা নির্ভীক সাংবাদিকতা ও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ‘সোমপ্রকাশ’ লেখেন :৯৯
”ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয়কালে ব্রাহ্মের উপর লোকের যে বিদ্বেষ ভাব জন্মেছিল সেই ভাবের সহায়তায় স্থানে স্থানে হরিসভা স্থাপিত হইল। হরিসভা ব্রাহ্ম সমাজের বিদ্বেষ্টা। দেশের ভিতর স্থানে স্থানে যদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত না হইত, কোথাও কখনও বর্তমান পদ্ধতিক্রমে হরিসভা স্থাপিত হইত কি না সন্দেহ।* এই সকল হরিসভার অধিকাংশ সভ্য কাহারা? যাহারা ‘আর্যধর্ম’ সনাতন ‘হিন্দুধর্মে’র নাম ডাকিয়া এককালে বেদব্যাসের জন্ম দিতে চায়, পৈর্তৃক ধর্মত্যাগী অনাচারী বলিয়া ব্রাহ্মগণকে ঘৃণা করে, মস্তকের উপর শিখা রাখিয়া কুপ্নী ও জপের ঝুলি ধারণ করিয়া গৌর নাম জপ করিতে করিতে দোকানদারী করে, আদালতের আমলা হইয়া নিতাইয়ের নামে উৎকোচ গ্রহণ করে, রাধা নামে উন্মত্ত হইয়া বেশ্যার পদতলে আত্মসমর্পণ করে, আর রসকলি কাটিয়া প্রতিবাসীদিগের বৌ—ঝির সর্বনাশের চেষ্টায় বিচরণ করে। যাঁহারা বাস্তবিক বৈষ্ণব নামের অধিকারী আমরা তাঁহাদিগকে এই ঘৃণিত দলভুক্ত করিয়া পাপের ভাগী হইতে পারি না। যে সকল সভ্য বাস্তবিক ধর্মাত্মা তাঁহাদিগের চরণে একশতবার প্রণাম করিয়া দূরে রাখিয়া দি। কিন্তু একশতের মধ্যে একজনও যদি এইরূপ সাধু—হৃদয় ব্যক্তি থাকেন তিনিও এই দলে সারস বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। অবশিষ্ট নিরানব্বই জনের ধর্মের আড়ম্বর যেমনই অধিক তাহাদের পশুবৎ ব্যবহার কলঙ্কিত প্রবৃত্তি ও ভয়ানক অত্যাচারের কাহিনীও তেমনি বিচিত্র। পাঠক! হরিসভায় গিয়া ইহাদের প্রেমের ঢলাঢলি দেখিয়া আসিয়াছেন, যদি একবার এই পাশব বৃত্তিপরায়ণ পাষণ্ডদিগের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন এই পাষণ্ডেরাই প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বঙ্গদেশকে ছারখার করিয়া ফেলিতেছে।”
হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীরা, এমনকী তাঁদের মধ্যে অতিগোঁড়া যাঁরা, তাঁরাও নিশ্চয় ধর্মের নামে নৈতিক ব্যভিচারের স্রোত সমাজে প্রবাহিত হোক কামনা করেননি। কোনও যুগে, কোনও সমাজে, কোনও ধর্মপ্রবর্তকই তা কামনা করেন না। কিন্তু ধর্মান্দোলন যখন কোনও সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য লোকচিত্ত জয় করতে চায়, তখন তার মধ্যে আদর্শবিকার ও ব্যভিচারের একটা ঝোঁক দেখা যায়। ভণ্ড—ধার্মিকরা তার সুযোগ নিয়ে ব্যাভিচারের পথ আরও সুগম করে। সাধারণ জনস্তরে তখন, ম্যানহাইমের পূর্বোদ্ধৃত সমাজসূত্র অনুসারে, ব্যাভিচারনীতিই ধর্মনীতিরূপে প্রবল হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য—আদর্শপন্থী ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে নব্যহিন্দুধর্মবাদীদের ‘হরিসভা’ আন্দোলনের সামাজিক ফলও তা—ই হয়েছিল। শুধু ‘হরিসভা’ নয়, বাংলা দেশের বহু ধর্মসম্প্রদায় (বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি) এই সময় নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ‘গুরুবাদ’ পুনরুজ্জীবিত হয় :১০০
”…গুরু ব্যবসা আজকাল যেরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে আফ্রিকার দাসব্যবসা তাহার নিকট হার মানে। ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত কোন লোকে যদি আমাদের ধর্মের উপর একটুও বা কটাক্ষপাত করে অমনি আমাদের স্বধর্মপ্রিয়তার বৃদ্ধি হয়, সর্পের লাঙ্গুলে অমনি যেন পা পড়ে। বিলাতে গিয়া যদি কেহ কখনও অখাদ্য ভোজন করিয়া আসিয়া আবার হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চান, অমনি সংস্কারগণ সহস্র কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু স্বধর্মে থাকিয়া ধরাচূড়া পরিয়া মালা ঠুকিতে ঠুকিতে যাহারা… ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে সমাজের ভিতর তাহাদের একটা শাসন করিবার জন্য কাহারও চেষ্টা নাই।’
ধর্মের নামে অধর্মের স্রোত যখন সমাজে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন কারও তা শাসন করার চেষ্টা থাকে না, কোনও কালেই থাকে না, আজও নেই। তার কারণ, ধর্ম এমনই একটা জিনিস যা প্রকাশ্যে সমালোচিত হলে আজও সভ্য মানুষের মনে আদিম মানুষের প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। কাজেই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে যে—কোন প্রকৃত ধার্মিক, বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী ব্যক্তি নীতিভ্রষ্ট ধর্মাচরণের নীরব ও নির্বাক দর্শক থাকাই সমীচীন মনে করেন, প্রতিবাদ করে সাপের লেজ মাড়াতে চান না। ধর্মব্যবসায়ীরা তা জানেন বলেই ধর্মের নামে তাঁরা স্বেচ্ছাচার—ব্যভিচারের স্বাধীনতা পান। এই স্বাধীনতাও অনেক ক্ষেত্রে, উনিশ শতকের শেষে, বাংলার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতার ইন্ধন জোগায় এবং বৃহত্তর জনসমাজের মানসিক আবর্জনার তলানি উপরে গেঁজিয়ে তোলে।
সমাজের উপরের স্তরে নব্যহিন্দুধর্মের মননধর্মী আন্দোলনের মধ্যে (১৮৮০—১৯০০) দুটি ধারা লক্ষ করা যায়—একটিকে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র—প্রবর্তিত ধারা, আর—একটিকে বলা যায় শশধর তর্কচূড়ামণি—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রবর্তিত ধারা। শেষদিকে, ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ—আমেরিকা পর্যটন ও চিকাগো ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩) হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচারান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর, আর—একটি ধারা এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই বিবেকানন্দ—প্রবর্তিত ধারা, স্বামীজির তিরোধানের পর (১৯০২), স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ (মে ১৮৭৯, রেজিস্টার্ড এপ্রিল ১৯০৯) ও ‘বেলুড় মঠ’ (ডিসেম্বর ১৮৯৮) উনিশ শতকের মধ্যেই স্থাপিত হয়।
বঙ্কিমচন্দ্রর ‘প্রচার’ (১৮৮৪), অক্ষয়চন্দ্রর ‘নবজীবন’ (১৮৮৪) ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ‘বঙ্গবাসী’ (১৮৮১) নব্যহিন্দুধর্মের অনুশীলনে এবং ‘আলোচনা’ ও ‘সঞ্জীবনী’ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হয়। বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’—পর্ব ও ‘প্রচার’—পর্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। ‘প্রচার’—পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের বিচারশীল অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব এবং শশধরগোষ্ঠীর মনোভাব এক বা অভিন্ন ছিল না। বঙ্কিমের ‘অনুশীলনধর্ম’ ছিল যুক্তিবাদী ও মানববাদী ব্রাহ্মধর্মেরই হিন্দু—রূপায়ণ। বিপিনচন্দ্র বলেছেন :১০১ “Bankim Chandra’s Anusheelana Dharma was really the Brahmo Somaj ideal of… the harmionous development of all the faculties of man… through his personal and social life, and he preached it only without the unpopular Brahmo name.” শশধরগোষ্ঠীর নব্যহিন্দুধর্ম তা ছিল না। শশধর তর্কচূড়ামণি, বিপিনচন্দ্রর ভাষায়, “adopted a new line of interpretation seeking to reconcile ancient Hindu ritualism and mediaeval Hindu faith with modern science.” দেশে—বিদেশে জ্ঞান—বিজ্ঞানের যত উন্নতি হোক, একদল হিন্দু পণ্ডিত আছেন যাঁরা বলেন, ‘কিছুই নতুন নয়, সবই বেদে আছে, সবই শাস্ত্রে আছে।’ তর্কচূড়ামণি ছিলেন সেই পণ্ডিতগোষ্ঠীর অন্যতম। অক্ষয়চন্দ্রকে বিপিনচন্দ্র বলেছেন, “the most powerful opponent of progressive social views” এবং কৃষ্ণপ্রসন্নকে বলেছেন, “He had the power to rouse popular sentiments by vulgur witticism and through playing upon words.” ১০২ কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন জনসমাজে পণ্ডিত ও শিক্ষিত গোষ্ঠীর এই ধর্মান্দোলন যে শক্তিশালী হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই আন্দোলন লক্ষ্য করে ‘সোমপ্রকাশ’ মন্তব্য করেন :১০৩ ”অনেকে বলেন পুরাতন হিন্দুধর্ম শীঘ্র পুনরুজ্জীবিত হইবে। আবার হিন্দুগণ আর্য মুনিঋষির প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রানুসারে চলিবেন।… কিন্তু আমরা এই বেলা বলিয়া রাখিতেছি, যিনি যতই কেন চেষ্টা করুন না, খাঁটি হিন্দুধর্ম আর চলিত হইতে পারিবে না। সেদিন অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। আমাদেরও ইচ্ছা নয় যে আবার সমস্ত হিন্দুধর্মনীতি সমাজে অবিকল প্রচলিত হউক। তাহা প্রচলিত হইলে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই।” হিন্দুধর্মে একটু ভেজাল দিয়ে চালাতে হবে, কারণ ‘সোমপ্রকাশ’ বলেছেন যে ইংরেজদের শাসনকালে সমাজে বাস্তব অবস্থার ও লোকের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চাকরিবাকরি ব্যাবসাবাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা, এগুলি যথানিয়মে করতে হলে শাস্ত্রসম্মত হিন্দুধর্ম অনেকটা যুগসম্মত করতে হবে। খাঁটি হিন্দুধর্মের গোদুগ্ধে একটু জল না মিশিয়ে উপায় নেই। ‘সোমপ্রকাশ’—এর এই টিপ্পনী বাস্তব সত্য। আমরা দেখেছি, শুধু জল—মেশানো তরল হিন্দুধর্ম নয়, অনাচার—ব্যভিচারের গরল—মেশানো হিন্দুধর্ম কীভাবে সাধারণ জনস্তরে, পুনরুত্থানবাদীদের প্রচারের ফলে, বিস্তৃত হয়েছে।
প্রগতিশীল সমাজসংস্কারের ধারা, নব্যহিন্দুধর্মের এই আন্দোলনের ফলে, স্বভাবতই ব্যাহত হয়। বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী—স্বাধীনতার কঠোর সমালোচনায় পুনরুত্থানবাদীরা মুখর হয়ে ওঠেন। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে অক্ষয়চন্দ্র তাঁর পত্রিকায় ও বক্তৃতায় একরকম ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন।১০৪ বহুবিবাহ আইনত বন্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগরের শেষ প্রচেষ্টা (১৮৬৬) ব্যর্থ হয়। স্ত্রীশিক্ষা মন্থরগতিতে চলতে থাকে, তা—ও উচ্চশিক্ষা নয়, লিখন—পঠনশিক্ষা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার একুশ বছর পরে ১৮৭৮ সালে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হিন্দুসমাজ ভালো চোখে দেখেনি, এমনকী প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মরাও তার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ এ বিষয়ে লিখেছেন (চৈত্র ১৮০২ শক, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) :
”গত তিন বৎসরের মধ্যে পাঁচজন বঙ্গীয়া কুমারী প্রবেশিকা এবং দুইজন এল.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আর কয়েক বৎসরে বঙ্গীয়া নারীগণের মধ্যে অনেকে বি.এ, এম.এ পরীক্ষা দানে কৃতকার্য হইবেন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অনেকে প্রচলিত প্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ উন্নতি দেশের অতিশয় হিতকর শুভকর জ্ঞান করিতেছেন… কিন্তু আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার কি শুভকর ফল তাহা আমরা বঙ্গীয় যুবকগণের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইতেছি।… আমাদিগের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহারা ধর্মে বিশ্বাসশূন্য ও সুনীতিবিচ্যুত হইবেন।”
১৮৮০ সালে যদি প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মরাই প্রকাশ্যে এই ভাষায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করতে পারেন, তাহলে নব্যহিন্দুধর্মের প্রচারকরা তার প্রতি কীরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারেন তা সহজেই কল্পনা করা যায়। ১৮৯১ সালে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ ‘মনুসংহিতা’র আদর্শ স্ত্রীসমাজে প্রয়োগ করার জন্য ওকালতি করেন :১০৫ ”…জন সমাজে সুনীতি সদাচার ও ধর্মব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে স্ত্রীরক্ষা ও তন্নিবন্ধন প্রজাশুদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু স্ত্রীজাতি স্বাধীন থাকিলে ইহা আদৌ সম্ভবিতেই পারে না।” ‘সোমপ্রকাশ’ লেখেন :১০৬ ”দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যদ্যপি আমরা এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করি, তাহা হইলে পরে আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে।” উদারচিন্তার পোষক হয়েও ‘সোমপ্রকাশ’ অবরোধপ্রথা পর্যন্ত সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হননি :১০৭
”হিন্দুর সমাজবন্ধনী যেমন দৃঢ়, লোকের চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার পক্ষে যেমন অনুকূল তেমন আর পৃথিবীর কোন জাতিরাই নহে।… হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাপকেরা দেখিলেন স্ত্রীলোকের চরিত্র নির্মল রাখিতে গেলে তাহাদের কমনীয়কান্তি, সুন্দর বদনচন্দ্রিমা লোকলোচনের অন্তর্হিত করিয়া রাখা চাই; তাই সভ্য নীতিসঙ্গত অবরোধপ্রথা হিন্দুসমাজের ভিতর প্রবর্তিত করিলেন। এই অবরোধপ্রথার ফলে হিন্দুরমণীরা জগতের সম্মুখে সতীত্বের আদর্শস্বরূপে পরিচিতা হইয়াছেন।”
—১৮ শ্রাবণ ১২৯৩
লক্ষণীয় হল, এই ‘সোমপ্রকাশ’ হরিসভা, গুরুবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে তীব্র—কঠোর ভাষায় হিন্দুধর্মের ব্যভিচারের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু স্ত্রী—স্বাধীনতা প্রসঙ্গে, উনিশ শতকের প্রায় শেষ দশকের কাছাকাছি, অবরোধপ্রথার সঙ্গে সতীত্বের সম্পর্ক এবং হিন্দুদের সমাজবন্ধনের দৃঢ়তার প্রশংসায় বেসামাল হয়ে গিয়েছেন। এ প্রশ্ন ‘সোমপ্রকাশ’—এর মনে হয়নি যে হিন্দুদের সমাজবন্ধন যদি দৃঢ় হত, তাহলে সেকালের সমাজের ভিত্তি যে ধর্ম, সেই ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যভিচারের বন্যা বইত না, যে ব্যভিচারের বন্যায় তাঁরাও আতঙ্কে শিউরে উঠে আর্তনাদ করেছেন। তা যদি মনে হত, তাহলে একমাত্র পরদার অন্তরালে থাকলে অথবা ‘লোকলোচনের অন্তর্হিত’ করে রাখলে যে স্ত্রীলোকের ‘সতীত্ব’ রক্ষা হয়, এরকম হাস্যকর যুক্তির অবতারণা তাঁরা করতে পারতেন না। আসল কথা হল, ধর্মের চেয়েও হিন্দুসমাজের কাছে গুরুতর সমস্যা যে স্ত্রী—স্বাধীনতা, এই নিষ্ঠুর সত্যই ‘সোমপ্রকাশ’—এর উক্তি ও যুক্তি থেকে প্রমাণিত হয়। কাজেই ১৯০০ সাল পর্যন্ত যদিও তিনজন বাঙালি মহিলা এম.এ. এবং বাইশজন মহিলা বি.এ. পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হন, তাহলেও স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী—স্বাধীনতার আন্দোলন উনিশ শতকের শেষে যে পদে পদে ব্যাহত হয়েছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।১০৮ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও তাঁর সহযোগীদের স্ত্রীশিক্ষা—স্ত্রী—স্বাধীনতার সমর্থনে আন্দোলন সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এমনকী বিদ্যাসাগরও মনে হয় বার্ধক্যে নব্যহিন্দুধর্মের আন্দোলনে এবং বিধবাবিবাহ বাল্যবিবাহ প্রচলন (আইন সত্ত্বেও) ও বহুবিবাহ প্রতিরোধের সামাজিক ব্যর্থতার কিছুটা দেশাচার—সচেতন হয়েছিলেন। সহবাস সম্মতি আইনের প্রস্তাবের (Age of Consent Bill) বিরুদ্ধে অভিমত জানিয়ে তিনি মন্তব্য করেন (ভারত সরকারের কাছে লিখিত চিঠিতে) ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ :১০৯
“I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with any religious usage.”
অবশেষে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে বিদ্যাসাগরও ‘religious usage’—এ হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। যিনি আইনসম্মত বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, যিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তিনি প্রকারান্তরে ‘বাল্যবিবাহ’—র সমর্থন করেন শেষজীবনে। অথচ এই বাল্যবিবাহই স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় ছিল উনিশ শতকে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার। বাল্যবিবাহের সামাজিক কুফল নিয়ে তখনকার সাময়িকপত্রে আলোচনাও হয়েছে যথেষ্ট।১১০ কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু লোকাচারের বিরোধিতার ভয়ে কোনও সংস্কারক তার প্রতিকার করতে পারেননি। নব্যহিন্দুধর্মের আন্দোলন স্বভাবতই বাল্যবিবাহপ্রথা আরও দৃঢ়মূল করেছে। তার ফলে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী—স্বাধীনতার কোনও উল্লেখ্য অগ্রগতি বাংলা দেশে হয়নি।
উপরন্তু আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার ফলে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়োত্তর এন্ট্রান্স—এল.এ. এম.এ পাশ করা যুবক, ডাক্তার—উকিল—ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, বাংলার সামাজিক জীবনে নতুন একটি সমস্যা দেখা দেয়। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার ‘commercialisation’, অর্থাৎ বিদ্যাও বাজারের পণ্য এবং যার বিদ্যা যত বেশি (অবশ্যই লেবেল বা ছাপ—মারা বিদ্যা) তাঁর বাজারমূল্যও (market-price) তত বেশি। সমাজবিজ্ঞানী ফন মার্টিনের ভাষায় বলা যায়—‘‘the learned had to begin to work for a ‘free market’… there was a close correlation between the mercantile classes and the intelligentsia… by the inherent objective and stylistic relationship of money and intellect.’’ ১১১ কাজেই শিক্ষিতরা নতুন একটি শিক্ষা—বিদ্যাব্যবসায়ী শ্রেণিতে পরিণত হন। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য ‘free market’ যেহেতু খুবই সীমাবদ্ধ, তাই বিবাহ—বাজারে (matrimonial market) শিক্ষিতরা মূল্য—প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। বাঙালি হিন্দুসমাজে বিবাহ—পণপ্রথার (dowry) উদ্ভব হল। আধুনিক বাণিজ্যপ্রবণ শিক্ষার ভীতিপ্রদ সামাজিক অভিসম্পাত এই পণপ্রথা। ‘সোমপ্রকাশ’ এ বিষয়ে ‘বঙ্গদেশে পুত্র বিক্রয়’ শিরোনামে (১০ আষাঢ় ১২৯১) লেখেন :১১২
”পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার যে বিবাহ দেওয়া হয় তাহারই নাম আসুর। বঙ্গদেশে অনেকদিন অবধি এ—বিবাহটি চলিয়া আসিতেছে। কুলীন মৌলিক বংশজ প্রভৃতির ব্যবস্থাই এ কুৎসিত প্রথার কারণ।… একে এই প্রথার জ্বালায় বাঁচা যায় না, কত বৃদ্ধ ও গুণহীন কাপুরুষ গুণবতী ও রূপবতীর পাণিগ্রহণ করিতেছে। …এই জ্বালার উপরে আবার পুত্রবিক্রয়ের জ্বালা উপস্থিত। এই পুত্রবিক্রয়ের প্রথা উপস্থিত হওয়াতে সকল শ্রেণীরই, বিশেষতঃ কায়স্থশ্রেণীর কন্যার বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহার দুই তিনটি কন্যা জন্মে, তিনি অগাধ বিপদসাগরে নিমগ্ন হন। বরকর্তার চিত্তসন্তোষ সাধনার্থ তাঁহাকে ইটে—ভিটে বিক্রয় করিতে হয়। লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে বাসা বাঁধেন না। ছেলে যে পরিমাণে পাস দিতে আরম্ভ করে, সেই পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে।… একি সভ্য ব্যবহার?”
‘সোমপ্রকাশ’—সম্পাদক আলোচনার শেষে তৎকালের জনপ্রিয় লোককবি রূপচাঁদ পক্ষী রচিত একটি সংগীত (পণপ্রথা বিষয়ে) উদ্ধার করেছেন :
”আ মরি কি নাকাল, কন্যাবিবাহের কাল, আজ কাল
হচ্ছে বঙ্গদেশেতে।
মাতৃদায়, পিতৃদায়, এর আগে লাগে কোথায়, ভিটে
মাটি চাটি হয়, বিয়ের ব্যয়েতে।।…
বল্লালী বাধাকুল, প্রায় হলো নির্মূল, বিশ্ববিদ্যালয়
স্কুল, সুরু যে হতো।
এনট্রান্স একপেসে, এল এ দুপেসে, বি.এ
তেপেসে মান্য ভারতে।।…
চারিপেসের কর্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্বভক্ষ্য, যার ছেলে গণ্ডমূর্খ,
সে মরে দুঃখেতে।
ছেলে থাকিলে গুণবন্ত, একরাত্রে হতাম ভাগ্যবন্ত, পোড়াকপালী
ভেড়াকান্ত, ধল্লেন গর্ভেতে।।…
উচ্চশিক্ষার প্রভাবে, দেশের উন্নতি হবে, সমাজের কুক্রিয়া যাবে,
বিদ্যার জ্যোতিতে।
হিতে হলো বিপরীত, পাসকরা বাড়ায় কুরীত, এশিক্ষা কার মনোনীত
হয় অনিষ্ট যাতে।।…
বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজে ‘কন্যাদায়’ যে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার দান, এই সামাজিক সত্য অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। কন্যাদায়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হল সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীর অমর্যাদা ও অপমান। এই অমর্যাদার অভিশাপ নিয়েই বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে কন্যাসন্তানের জন্ম হয় এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই অভিশাপের বোঝা তাকে বহন করতে হয়। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সামাজিক প্রগতিবাদীদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষে একেবারে রুদ্ধ হয়নি—হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীদের গুরুগর্জনের মধ্যেও তাঁদের গুঞ্জন শোনা গিয়েছে, এমনকী সনাতন হিন্দুধর্মীরাও বহুবিবাহাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন১১৩—কিন্তু সমাজসংস্কারের ইতিহাসের নিষ্ঠুর প্রহসন হল ‘পুত্রবিক্রয়’ ও ‘কন্যাদায়’—এর ‘অসভ্য’ (‘সোমপ্রকাশ’—এর ভাষায়) প্রথা রহিত করার জন্য কোনও আন্দোলনে কোনও ফল হয়নি। স্ত্রীজাতির অমর্যাদা ছাড়াও, পণপ্রথার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্তের আর্থনীতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের সঞ্চিত মূলধনটুকু, স্বাধীন ব্যবসাবাণিজ্যের বা কর্মসংস্থানের শেষ সম্বলটুকু তাঁরা হারিয়েছেন, এবং বংশপরম্পরায় প্রধানত চাকরিরূপ দাসত্বের মুখাপেক্ষী হয়েছেন।
এই সময় বাংলার মুসলমানদের সমাজচিন্তার গতি কী ছিল তা না জানলে সমাজচিত্র সম্পূর্ণ হয় না। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি, সে কথা আগে বলেছি (পৃষ্ঠা ২১৭—২০)। উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই ‘ওয়াহাবি’ আন্দোলন বাংলার তথা ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মগোঁড়ামি নতুন করে জাগিয়ে তোলে এবং তার ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ তখন থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। যদিও আর্থনীতিক সংগ্রামে (যেমন বাংলার প্রজা বিদ্রোহে) দরিদ্র মুসলমান কৃষকরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদারদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্রোহ করেছে এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থসীমা লঙ্ঘন করে তারা হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে শ্রেণিস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে (‘‘In the peasant rising around Calcutta in 1831, they broke into the houses of Musalman and Hindu landholders with perfect impartiality’’–Hunter ১১৪) তাহলেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে শেষ পর্যন্ত তারা মুক্ত হতে পারেনি। ক্যান্টওয়েল স্মিথ তাই বলেছেন :১১৫
‘The Wahabi movement, therefore, did not set lower class Muslims against lower Hindus in open conflict, nor did it divert lower class Muslims from economic issues to a false solidarity with their communal ‘friends’ but class enemies. None the less it did encourage communal attitudes, especially in religious thinking, and left a considerable section of the Muslim masses more susceptible to later communalist, propaganda than they might otherwiese have been.’(emphasis added)
বাংলা দেশে ওয়াহাবিরাই প্রথম ‘সন্ত্রাসবাদী’ বলে পরিচিত হন, আবদুল্লার বিচারপতি নরম্যান—হত্যা (১৮৭১) এবং শের আলির বড়লাট মেও—হত্যার (১৮৭২) পর। কিন্তু তার ফলে কোনও অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ, অথবা রাজনৈতিক চেতনা মুসলমানদের মধ্যে জাগেনি! আধুনিক ইংরেজি—শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের যেটুকু বিকাশ হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত তা—ও নগণ্য। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে মুষ্টিমেয় মুসলমান যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, বৃহত্তর মুসলমান—সমাজের কাছে তাঁরা বিশ্বাসভাজন ছিলেন না। বাংলাদেশে মৌলবি আবদুল লতিফ ‘মহমেডান লিটারারি সোসাইটি’ স্থাপন করে (এপ্রিল ১৮৬৩) পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার প্রতি মুসলমানদের উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হন। আবদুল লতিফ নিজে লিখেছেন :১১৬
‘‘Being fully aware of the prejudice and exclusiveness of the Mahomedan community, and anxious to lmbue its members with a desire to interest themselves in Western learning and progress, and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual intercourse with the best representatives of English and Hindoo Society, I founded the Mahomedan Literary Society in April 1863…’’
আবদুল লতিফের এই প্রয়াস যে একেবারে ব্যর্থ হয় তা নয়। সৈয়দ আহমদের (১৮৭১—৯৮) আন্দোলনের ফলেও মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ১১৭ কিন্তু বাংলা দেশে যখন ধীরে ধীরে ইংরেজি—শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ হয় তখন থেকে আমরা দেখেছি, জাতীয়তাবোধের নবজাগরণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের কণ্ঠে ‘হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব’—এর সুরই ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত হতে থাকে। তার সঙ্গে নব্যহিন্দুধর্মের আন্দোলনও যুক্ত হয়। তার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে হিন্দু—মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ব্যবধান বিস্তৃত হতে থাকে। বাংলার মুসলমানরা তাঁদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির দাবিদাওয়া স্বতন্ত্রভাবে ঘোষণা করতে আরম্ভ করেন এবং ব্রিটিশ শাসকরাও কৌশলে তাকে সাম্প্রদায়িকতার খাতে চালনা করেন। তৎকালের সাময়িকপত্রের আলোচনা থেকেও তার পরিচয় পাওয়া যায়।১১৮ কংগ্রেসের আন্দোলন এই সাম্প্রদায়িকতার প্রবাহ প্রতিরোধ করতে পারেনি। ১৮৯১ সালে সৈয়দ আমির আলির বিখ্যাত গ্রন্থ Spirit of Islam প্রকাশিত হয়। ১১৯ এই গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ এবং কেবল বাংলার বা ভারতের নয়, ভারতের বাইরের সমগ্র মুসলমান—সমাজের মনে এই গ্রন্থ অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্মের কঠোর সমালোচনা করে আমির আলি ইসলামধর্মের অতুলনীয় মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। এমন একসময়ে করেন যখন এ দেশে আর্যধর্ম (দয়ানন্দ) ও নব্যহিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উচ্চশিক্ষিতদের কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে। কাজেই আমির আলির ইসলামধর্মগ্রন্থ এ দেশের উদীয়মান শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের কাছে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের আকর হয়ে ওঠে।১২০ সৈয়দ আহমদের প্রভাবও তার ফলে কিছুটা শেষদিকে ম্লান হয়ে যায় এবং তিনি শুদ্ধ—সদাচারী ইসলামপন্থী হয়ে ওঠেন, জাতীয় জীবনে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হন।
অতঃপর এই ‘Spirit of Islam’ কার্জনের শাসনকালে (১৮৯৯—১৯০৫) বাংলা দেশে প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বঙ্গবিভাগের ফলে (১৯০৫)। ১৯০৫ সালেই স্থাপিত হয় ‘মুসলিম লিগ’। ‘The partition struck at the root of the Bengali nation, and at the nationhood of the Indian Motherland’১২১—এবং তার ফলে স্বদেশি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের অভ্যুদয় হয় বিশ শতকে। সে ইতিহাসের ছন্দ ও আবর্তের সঙ্গে উনিশ শতকের পার্থক্য আছে, কিন্তু তবু ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় বলতে হয়—‘‘In everything the old overlaps the new’’ এবং সামাজিক ইতিহাসের ধারায় ‘‘There is never any clear cut’’—সমাজ ও জীবন একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। তাই বিশ শতকের বাংলার আবর্তসংকুল সামাজিক জীবনের সংঘাত ও বিক্ষোভের মধ্যে সন্ধান করলে দেখা যাবে, অনেক স্রোত ও তরঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে উনিশ শতকে—হয়তো বা তার আগে, আরও দূরে অতীতে।
নির্দেশিকা
বন্ধনীর মধ্যে সূচকসংখ্যা
(১) Lewis Mumford : The culture of Cities, London Reprint 1944, p. 98
(২) Quoted in Mumford, op cit. p. 72
(৩) H.J. Rainey : Historical and Topographical Sketch of Calcutta, Calcutta 1876, p. 118 : “1802 : On the 20th August, a Regulation was passed prohibiting Hindu parents from casting their children off Sagar Island.”
(৪) The Calcutta Monthly Journal : December 1801 : “Gangasagar Child Throwing Ceremony”
(৫) G.M. Trevelyan : English Social History, London 1948, pp. 495-96
(৬) H.L.V. Derozio : Poems, Calcutta 1827
(৭) Trevelyan, op. cit. p. 96
(৮) Trevelyan, op. cit, pp. 96-97
(৯) Bengal Hurkaru : ‘Lal Bazar Revelries,’ September 24, 1842
(১০) Karl Mannheim : Essays on the Sociology of Culture, London 1956, pp. 137-39
(১১) জয়গোপাল গুপ্ত : গীতরত্ন, কলকাতা ১২৬৩, পৃষ্ঠা ৭—৮
(১২) রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সংগৃহীত : রাজা রামমোহন রায়—প্রণীত গ্রন্থাবলি কলকাতা ১৭৯৫ শক, পৃষ্ঠা ৮
(১৩) Lewis Mumford : Technics and Civilisation, London 1934, p. 136
(১৪) Mumford, op. cit. p. 134
(১৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রামমোহন রায় (সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১৬) : রামমোহনের গ্রন্থাবলির তালিকা দ্রষ্টব্য।
(১৬) Johnson’s England : An Account of the Life and Manners of his age : ed by A. S. Turberville (Oxford 1933) : Vol. I, pp. 210-11
(১৭) The Calcutta Journal, Vol. 3, May 18, 1819, No. 89 (লাইন ২৩)
(১৮) Karl Mannheim : Man and Society, London 1940, p. 84 fn.
(১৯) F Parkes : Wanderings of a Pilgrim etc. London 1850E. Roberts : Scenes and Characteristics of Hindostan, London 1835 ইত্যাদি।
(২০) শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০; বিষ্ণু চক্রবর্তীর জীবনী : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৩৭ শক, ৮৭১ সংখ্যা; সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮০—৬৮৪
(২১) Parliamentary Papers (London) Vol. XVIII, 1821
(২২) Parliamentary Debates (London)1821-April-July, Vol. V, Cols 1217-221823-May-July, Vol. IX, Cols 1017-10211825-April-July, Vol. XIII, Cols 1043-1047সতীদাহের সংখ্যা বিষয়ে তথ্যাদি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই রিপোর্ট থেকে গৃহীত।
(২৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০—০৭ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৫—৭৮
(২৪) Human Sacrifices in India : Substance of the Speech of John Poynder, on the 21st and 28th Days of March 1827, London 1827
(২৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য়, পৃষ্ঠা (২৭১—২৭২), ২৭৪, ৫৮০—৮১
(২৬) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, পৃষ্ঠা ১৪—১৫
(২৭) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : পঞ্চবিংশতি, পৃষ্ঠা ১৬
(২৮) Kisory Chand Mitra : ‘The Hindoo College and its Founder’–a lecture, printed in App. B. Peary Chand Mitra’s A Biographical Sketch of David Hare, Calcutta 1877ডিরোজিও সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদের উক্তিগুলি এই বক্তৃতা থেকে গৃহীত।
(২৯) Peary Chand Mitra : op. cit.
(৩০) Rev. Lal Behari Dey : Recollections of Alexander Duff, London 1879, Ch. III, pp. 27-36
(৩১) India Gazette : ১৮৩১—৩২ সালের পত্রিকায় ‘এনকোয়্যারার’ পত্রিকার অনেক উদ্ধৃতি আছে।
(৩২) Rev. Alexander Duff : India and India Missions, Edin. 1840, Appendix, pp. 631-708–ডাফের উক্তিগুলি ও ‘এনকোয়্যারার’ পত্রিকার মন্তব্যগুলি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে উদ্ধৃত।
(৩৩) L. B. Day : op. cit. lbid
(৩৪) Hindu College MS Proceedings, 1831 (unpublished)বিনয় ঘোষ : বিদ্রোহী ডিরোজিও
(৩৫) Baboo Krishna Mohana Banerjea : The Persecuted or Dramatic Scenes Illustrative of the Present State of Hindoo Society in Calcutta, Lal Bazar 1831
(৩৬) Alexander Duff : op. cit. p. 673.
(৩৭) Duff : op. cit. p. 679-80
(৩৮) S.N. Eisenstadt : From Generation to Generation : Age Groups and Social Structure, Free Press, New York 1964, p. 318
(৩৯) Eisenstadt, op. cit. pp. 313-14
(৪০) Eisenstadt. op. cit. p. 311
(৪১) Encyclopaedia of Social Sciences (1951 print), Vol. 6
(৪২) A. S. Turberville edited : Johnson’s England : An Account of the Life and Manners of His Age (Oxford 1993), Vol I, pp 210-11
(৪৩) Duff : op. cit. pp. 637-38
(৪৪) Duff : op. cit. p. 640
(৪৫) Selections from Discourses delivered at the Meetings of the society for the Acquisition of General Knowledge, Vol. I. (1840), Vol. II (1842), Vol. III (1843)
(৪৬) Sivnath Sastri : History of the Brahmo Samaj, Vol. I, Calcutta 1919, pp. 86-88
(৪৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য়, পৃষ্ঠা ৪৭৭—৯৭ : ‘ডাফের প্রতিবাদ’, আশ্বিন ১৭৬৬ শক; ‘Vaidantic Doctrines Vindicated.’ ১ ফাল্গুন ১৭৬৬ শক
(৪৮) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বাল্যকথা
(৪৯) শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃষ্ঠা ২০০
(৫০) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী : ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
(৫১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৭ শক, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা
(৫২) আত্মজীবনী : পৃষ্ঠা ৬৫
(৫৩) রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ৪৬
(৫৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম, পৃষ্ঠা ১৮১, ২য়, পৃষ্ঠা ৫৫৯—৬৩, ৩য়, পৃষ্ঠা ৫৭৬—৭৮
(৫৭) J.A. Richey : Selections from Educational Records, Part II (1840-59), pp 52-56
(৫৬) সম্বাদ ভাস্কর, ১২ জুন ১৮৪৯’সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রচনাগুলি ‘সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র’ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৭—৪২৬ দ্রষ্টব্য।
(৫৭) ভূদেব মুখোপাধ্যায় : বিবিধ প্রবন্ধ ২য় খণ্ড, ১৩২৭—’রাজা রামমোহন রায় ও তন্ত্রশাস্ত্র’, পৃষ্ঠা ১৪৩—৪৯দিলীপকুমার বিশ্বাস : ‘রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র’—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৬ খণ্ড, ৪ সংখ্যা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৮৮২ শক’রাজা রামমোহন ও তন্ত্র’—দেশ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২, পৃষ্ঠা ১৬৩—৬৭
(৫৮) Speeches of Ram Gopal Ghose etc. Calcutta N.D. p. 65
(৫৯) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৩য়, পৃষ্ঠা ৩৪৯—৫০, ৩৬০—৬১, ৩৬৩—৬৪
(৬০) Transactions of the Bethune Society 1859-60
(৬১) বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ ৩য় খণ্ড, ৪ অধ্যায়
(৬২) Widow Remarriage Papers, Manuscript Records, National Archives, Delhi : Letter dated Fort William, the 24th July 1837
(৬৩) দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : ক্ষিতীশবংশাবলি চরিত, ২৪ অধ্যায়
(৬৪) Widow Remarriage Manuscript Records : National Archives, Delhi
(৬৫) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাঁর সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের ‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ’ তিন খণ্ড দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪, ১৯১, ১৯৭, ২১৬—২০সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১—৭০, ১৯৬—২০১, ২০১—০৪সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭—৮০, ৯০—৯২, ১৩০—৩১, ২৯০—৯১, ৩০০—০১, ৩০৩—০৫, ৩১৩—১৪, ৩২৯—৩০, ৩৩৮—৩৯, ৩৪৩—৪৭, ৩৫২—৫৮, ৩৭৭
(৬৬) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, ড. শশিভূষণ চৌধুরী ও ড. হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছেন। এ ছাড়া আরও অনেক রচনা এ বিষয়ে ১৯৫৭—৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহের ‘স্বরূপ’ বা ‘প্রকৃতি’ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বর্তমান লেখকের কাছে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিশ্লেষণ ও মতামত অনেক বেশি ইতিহাস—বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয় :Dr. R.C. Majumder : The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, Second edition, Calcutta 1963এই গ্রন্থের চতুর্থ বিভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘The Character of Outbreak of 1857’ (pp. 383-432) দ্রষ্টব্য।বিদ্রোহের প্রতি বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভাব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য :Benoy Ghose : ‘Bengali Intelligentsia and the Revolt’ in Rebellion 1857, A symposium, People’s Publishing House, New Delhi 1957
(৬৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চার খণ্ড দ্রষ্টব্য।
(৬৮) British Indian Association Reports, 1859-60
(৬৯) কেশবচন্দ্রর জীবনের ঘটনাবলি প্রধানত P. C. Mozoomdar—এর The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen (Calcutta 1931) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
(৭০) Sivnath Sastri : History of the Brahmo Samaj, Calcutta 1919, Vol. I, pp. 146-47
(৭১) Sivnath Sastri : op. cit. p 148
(৭২) Op. cit. P. 189
(৭৩) Op. cit. P. 187
(৭৪) Op. cit. P. 190
(৭৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ পৃষ্ঠা ২০৩—১১
(৭৬) অজিতকুমার চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : এলাহাবাদ ১৯১৬, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৫০৪—৩০সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য়, ‘প্রাসঙ্গিক তথ্য’
(৭৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ২১৫—১৬
(৭৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ২১৬—১৭
(৭৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস : শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে) কলিকাতা ১৩৫৯
(৮০) Sivnath Sastri : op. cit. p. 306
(৮১) Bipin Chandra Pal : Memories of My Life and Times, Calcutta 1932, p. 309
(৮২) op. cit. pp. 226-27
(৮৩) Surendranath Banerjea : A Nation in Making : Oxford University Press 1925, p. 38
(৮৪) op. cit. p. 42
(৮৫) op. cit. p. 43
(৮৬) op. cit. p. 76 (pp. 76-79)
(৮৭) op. cit. Chapter XX, pp. 205-6
(৮৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৪৭১—৭৩
(৮৯) S.N. Banerjee : op. cit. Ch. XVIII ‘The Partition of Bengal’.
(৯০) B.C. Pal, op cit. p. 433
(৯১) op. cit. pp. 424-25
(৯২) রাজনারায়ণ বসু : বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ২৮৮২—’জাতিভেদ বিষয়ে বর্তমান আন্দোলন’।
(৯৩) রাজনারায়ণ বসু : বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (১৮৮৭), ভূমিকা
(৯৪) আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ৯৮
(৯৫) Karl Mannheim : Man and Society, London 1954, p. 102
(৯৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য়, পৃষ্ঠা ৩৩৭—৩৯
(৯৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য়, সম্পাদকীয়, পৃষ্ঠা ২৯—৩০
(৯৮) B.C. Pal : op. cit. p. 428
(৯৯) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩৬৪—৬৭
(১০০) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩৬৭
(১০১) op. cit. p. 427
(১০২) op. cit. pp. 438-39
(১০৩) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩১৮—২২
(১০৪) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩৩১—৩৪৩
(১০৫) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য়, পৃষ্ঠা ৩৫১—৫৮
(১০৬) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ পৃষ্ঠা ২৭৬—৭৮
(১০৭) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩৬৮—৬৯
(১০৮) Calcutta University Calendar upto 1900
(১০৯) বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩—৪
(১১০) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২য়, পৃষ্ঠা ৫৩৫—৪১, ৪র্থ, পৃষ্ঠা ২০৬—০৭, ২১২—১৫, ২৫৯—৬৯, ২৮৫—৯৩, ৩২৩—২৪, ৩৬২—৬৩, ৩৬৯—৭০
(১১১) A.V. Martin : Sociology of the Renaissance, London 1945, p. 41
(১১২) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩১২—১৫
(১১৩) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ, পৃষ্ঠা ২৩৭—৩৯
(১১৪) W.W. Hunter : The Indian Mussalmans, pp. 106-7
(১১৫) W. Cantwell Smith : Modern Islam in India–A Social Analysis, Lahore 1943, pp. 189-90
(১১৬) Abdul Luteef : A Short Account of My Public Life, Calcutta 1885–Thacker Spink & Co—র প্রকাশিত আবদুল লতিফের কর্মজীবনের ঘটনাবলির সংকলনগ্রন্থে (১৯১৫) সন্নিবেশিত।
(১১৭) W. Cantwell Smith, op. cit. Ch IG.F.I. Graham : Life and Work of Syed Ahmed Khan, London 1885
(১১৮) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র পৃষ্ঠা ২৩৪—৩৭, ২৬৭—৬৯, ৩৪৩—৪৪, ৩৫৯, ৪০৩—০৬, ৫৬৩—৬৪, ৫৬৯—৭১
(১১৯) Syed Ameer Ali : The Life and Teachings of Mohammed, or The Spirit of Islam, 1891– পরবর্তী সংস্করণে (১৯২২) নাম দেওয়া হয় The Spirit of Islam
(১২০) Cantwell Smith, op. cit. Ch. II
(১২১) Valentine Chirol : India Old and New, P. 115
* মার্শম্যান ও রামমোহন রায়ের দু—খানি অপ্রকাশিত চিঠির প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত হল
(লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ)।
* ব্রাহ্মসমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবন কাটে। ব্রাহ্মধর্ম, হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবোধের উপাদান—মিশ্রিত ‘গোরা’ উপন্যাস রচনার প্রেরণা তিনি এই পরিবেশ থেকে পেয়েছেন মনে হয়। ১৯০৭—০৮ সালে ‘প্রবাসী’তে এবং ১৯০৯—১০ সালে পুস্তকাকারে ‘গোরা’ প্রকাশিত হয়।
* বিপিনচন্দ্র পালের ব্যাখ্যার সমর্থন ‘সোমপ্রকাশ’—এর এই উক্তিতে পাওয়া যায়।
