জন্মদ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর
সম্পাদনা – দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক
প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
.
উপক্রমণিকা
১৮২৮ সালে গ্রামের পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করে পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র মাত্রই আট বছর বয়সে যখন তৎকালীন হুগলি জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রাম থেকে লেখাপড়ার কারণে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজধানী কলকাতা শহরের উদ্দেশে যাত্রা করেন, আমরা জানি, যাত্রাপথে মাইলফলক দেখতে দেখতেই শিখে নিয়েছিলেন ইংরিজি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি। সেই শেখার পদ্ধতিটি ছিল ব্যতিক্রমী— নয়, আট, সাত হয়ে বিপরীতক্রমে নেমে এসেছিল দুই, এক-এ। বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁর ‘আত্মচরিত’-এ সে কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন:
… প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটিতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে, দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম (The Golden Book of Vidyasagar, All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee, Calcutta, 1993, p. 24)।
পথের ধারের মাইলস্টোন পুঁতে দূরত্ব সূচিত করাকে এক অর্থে আধুনিক নগরসভ্যতার একটা সূচক বলে অবশ্যই ধরে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু যে-দেশের মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় মধ্যযুগীয় স্তরে পড়ে, অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই, সেদেশে ইংরিজি সংখ্যা খুদে নিশ্চয় ঔপনিবেশিক শাসকেরা সাধারণের মধ্যে সেই আধুনিকতার আলো পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন এমন ভাবার অবকাশ নেই। কিছু ব্যতিক্রম বাদে বরং তাঁরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশ শাসনের প্রয়োজনে নিজেদের যতটুকু বাংলা শিখলে হয় তেমন কাজ চালানোর মতো বাংলা ভাষা রপ্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অন্য দিকে হতদরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত পণ্ডিত ঘরের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্রই পরবর্তীতে গোটা বাঙালি সমাজের মধ্যে যাতে আধুনিক শিক্ষার আলো গিয়ে পৌঁছায় তারজন্য আমৃত্যু অমানুষিক পরিশ্রম করে গিয়েছেন। এ যেন ওই উলটো দিক থেকে অঙ্ক শেখার মতোই ব্যতিক্রমী এক প্রব্রজ্যা।
১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভারতে আসেন এবং তার পরের বছর, ১৮২৯-এ, রাজা রামমোহন রায় ও বেন্টিঙ্ক সাহেবের বিশেষ উদ্যোগে আইন করে সতীদাহ প্রথা রদ হয়, এবং সে বছরই ঈশ্বরচন্দ্র ভরতি হন সংস্কৃত কলেজে। লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় বড়সড়ো এক রদবদল ঘটিয়ে ইংরিজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিলেন। মেকলে-অকল্যান্ড ছিলেন তাঁর সহচর। হিন্দু কলেজ হয়ে উঠল সেই নব্য ইংরিজি শিক্ষার আঁতুড়ঘর, যেখানে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছাড়া পড়াশুনা করা দুষ্কর, কেননা মাসিক বেতন ছিল পাঁচ টাকা।
যে সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যালাভ সেখানে প্রধানত সংস্কৃতই পড়ানো হত, ইংরিজি পড়ানোর উপযুক্ত শিক্ষক ছিল না। পরবর্তী কালে তাই যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড পণ্ডিতের চাকুরিতে বহাল ছিলেন তিনি, নিজের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে শিখেছিলেন ইংরিজি ও হিন্দি ভাষা, এবং সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও অসম্ভব মেধাশক্তির বলে দু’টি ভাষাকেই প্রায় মাতৃভাষার মতো আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন।
ইংরেজ মহলে ও সেইসঙ্গে ইংরিজি শিক্ষিত তৎকালীন বাঙালি সমাজে তাঁর মতো একজন গ্রাম্য, খেটো ধুতি পরিহিত ‘আউটসাইডার’কে স্থান করে নিতে হলে যে ইংরিজি রপ্ত করে নিতে হবে এই ‘প্র্যাগমাটিজম’, ‘বাস্তবধর্মিতা’ ঈশ্বরচন্দ্রের পুরো মাত্রায় ছিল। সংস্কৃতবিদ্যায় ব্যুৎপত্তির কারণে ইতিমধ্যেই তিনি ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে স্বীকৃত হয়েছেন হিন্দু শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডলে। ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি তাঁর আগে-পরে আরও অনেকেই পেয়েছেন কিন্তু নাম-পদবি মিলেমিশে বিদ্যাসাগর হয়েছেন একজনই। এই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য কখনওই ছিল না শুধু জ্ঞানার্জনের; অধিগত বিদ্যাকে কাজে লাগানো, তার যথার্থ প্রয়োগই ছিল ধ্যানজ্ঞান। ১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে বহাল তিনি, ‘কাউন্সিল অব এডুকেশন’-কে একটি চিঠি লিখলেন। তাতে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োগভাবনার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়।
… What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of vernacular schools, let us prepare a series of vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. (ইন্দ্রমিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, পৃ. ৬৬১)
চিঠিটির উদ্ধৃতাংশ থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট—
১. শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বসাধারণের মধ্যে;
২. মাধ্যম হবে মাতৃভাষা;
৩. শিক্ষকদের মাতৃভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে পর্যাপ্ত, প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে তাঁরা হবেন তথ্যাভিজ্ঞ এবং সেইসঙ্গে অবশ্যই কুসংস্কারমুক্ত।
অর্থাৎ, বেন্টিঙ্ক-মেকলে-অকল্যান্ড প্রণীত শিক্ষা কর্মসূচির থেকে বিদ্যাসাগর মশাই শত যোজন দূরে। একদিকে ইতিমধ্যে ‘We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern;…’ এই চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত সরকারি জেলা স্কুলগুলি ছাত্রাভাবে মুখ থুবড়ে পড়ছে; এবং অন্যদিকে, সংস্কৃত কলেজের পঠনপাঠনে বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাভাবনার প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন। আবার অনেকসময়ই এক কদম আগে, দু’ কদম পিছনে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছিলেন পায়ের তলার মাটিকে আলগা হতে না দিয়ে। তড়িঘড়ি ছিল না, কেননা তিনি এই দেশ, দেশবাসী, এর গ্রাম-মফস্সল-নগরকে চিনতেন জানতেন হাতের তালুর মতো, ‘ইয়ং বেঙ্গল’-এর সোৎসাহী সংস্কারবিরোধী ডিরোজিয়ো-শিষ্যদের অনেকেই তাঁর বন্ধু-সুজন হলেও তাঁদের ‘র্যাডিকাল’ পথ তিনি মাড়াননি। এখানে উল্লেখ করতে চাইব ১৯০৪ সালে লেখা লেনিন-এর বিখ্যাত One Step Forward, Two Steps Back বইয়ের ভূমিকা থেকে একটি অংশ, প্রেক্ষিত আলাদা হলেও যার সঙ্গে আমরা কাজের পদ্ধতিগত একটা মিল খুঁজে পেতে পারি:
When a prolonged, stubborn and heated struggle is in progress, there usually begin to emerge after a time the central and fundamental points at issue, upon the decision of which the ultimate outcome of the campaign depends, and in comparison with which all the minor and petty episodes of the struggle recede more and more into the background. (সূত্র: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1904/onestep/preface.htm)
ঔপনিবেশিক ভারতে যতদূর সম্ভব আরও আরও মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো ছিল বিদ্যাসাগরের কাছে যথার্থই এক আন্দোলনের শামিল। এ ব্যাপারে সরকারি সাহায্য নিতে যেমন তিনি পিছপা ছিলেন না, তেমনই ধনী জমিদার থেকে শুরু করে বিত্তশালী মানুষের সহায়তা গ্রহণেও আপত্তি ছিল না। আর স্বোপার্জিত অর্থ তো বিলিয়েছেন অকাতরে।
বাংলা সরকারের কনিষ্ঠ সচিব রিভার্স টমসন-কে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তির জবাবে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ বিদ্যাসাগর মশাই জানিয়েছিলেন:
বাংলায় শিক্ষা প্রবর্তনের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে, যদি-না সেটি একমাত্র উপায় হয় তবে, উচ্চতর শ্রেণিগুলিকেই পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে সরকারের নিজেকে আবদ্ধ রাখা উচিত। একশো জন শিশুকে শুধু পড়তে, লিখতে ও অল্প কিছু পাটিগণিত শেখানোর চেয়ে একটি ছেলেকে যথাযথ রীতিতে শিক্ষিত করে সরকার যা করবে, প্রকৃত জনশিক্ষার অভিমুখে তা অনেক বেশি কাজে লাগবে। সমগ্র জনগণকে শিক্ষিত করা নিশ্চয়ই খুব বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এ কাজ আদৌ কোনো সরকার গ্রহণ করতে পারবে কি না সন্দেহ। এও বলা যেতে পারে যে, ইংল্যান্ডে সভ্যতার উঁচু অবস্থা সত্ত্বেও শিক্ষা বিষয়ে সেখানকার জনসাধারণও এদেশে তাঁদের ভাইদের চেয়ে ভালো অবস্থায় নেই।
বিদ্যাসাগর মশাই আরও জানান, সরকার যদি জনশিক্ষা নিয়ে পরখ করে দেখার কথা ভাবে তবে পুরোপুরি অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে। তিনি এও মনে করেন, খেটে-খাওয়া শ্রেণিগুলির অবস্থা এতই নিচু স্তরে যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের কাজ করার উপযুক্ত বয়স হলে যেকোনও কাজে তাদের ঢুকতে হবে; অভিভাবকরা বিলক্ষণ জানেন লিখতে পড়তে শিখলেই তাঁদের অবস্থার উন্নতি হবে না। কতই ব্যাবহারিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর। এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখছেন:
পুরো বিষয়টিকে তিনি [বিদ্যাসাগর] দেখেছেন প্রয়োগ (practice)-এর নিরিখে। নীতিগতভাবে তিনি জনশিক্ষার বিরোধী নন, বরং তাকে খুবই বাঞ্ছনীয় (very desirable) বলেই মনে করেন। কিন্তু বাস্তববুদ্ধি বলে দেয়: এখুনি তা করা যাবে না (বিদ্যাসাগর : নানা প্রসঙ্গ, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১৩০-৩১)।
স্বাধীনতার এত বছর পরে, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের সর্বজনীন শিক্ষার হাল কি চোখে আঙুল দিয়ে সেটাই দেখিয়ে দেয় না? ইদানীং মিড-ডে মিল কর্মসূচি সেই অবস্থার উন্নতি কিছুটা ঘটাতে পারলেও পরিসংখ্যানগতভাবে এখনও তা যথেষ্ট অগৌরবেরই।
বড় কথা হল, নিজস্ব শিক্ষাভাবনার প্রয়োগ নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কাউকেই রেয়াত করেননি। আপস যেটুকু যা করেছেন তা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে। তাই, মনে-প্রাণে চাইলেও সংস্কৃত কলেজে শূদ্রদের ভরতির ব্যবস্থা সাময়িকভাবে চালু হয়তো করতে পারেননি তিনি, কিন্তু কায়স্থদের বেলা সেটা করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর সরকারের সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে কোনও কাজে তাঁর পক্ষে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন হয়ে পড়ে, সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত ব্যয়সংকোচ করতে থাকেন। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছিলেন তিনি, কাজের পরিবেশ-পরিস্থিতিই আর ছিল না। অগত্যা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা। এরপর বিস্তর টালবাহানা শেষে ১৮৫৮ সালের ৩ নভেম্বর মিলল অব্যাহতি এবং তার পরে তিনি আর কখনও সরকারি কোনও চাকুরিতে যুক্ত করেননি নিজেকে। কিন্তু সরকার কোনও পরামর্শ চাইলে বা কোনও উদ্যোগে তাঁর যোগদান কামনা করলে তিনি তাঁদের ফিরিয়ে দেননি। কেননা শিক্ষা সংস্কার ও প্রসার ছিল তাঁর ‘prolonged, stubborn and heated struggle’ এবং ‘the minor and petty episodes of the struggle recede more and more into the background’।
১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের চিঠি থেকে যে তিনটি বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীনই সেই সেই বিষয়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন, বিশেষত বাংলায় গ্রন্থ রচনার কাজ। এ ব্যাপারে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন তাঁর একান্ত সহচর। মদনমোহনকে সঙ্গে করে ‘সংস্কৃত যন্ত্র’ নামে ছাপাখানা, প্রকাশনালয় ও পুস্তক ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছেন। একের পর এক ভাবানুবাদ করে গিয়েছেন শেক্সপিয়র-এর Comedy of Errors অবলম্বনে ভ্রান্তিবিলাস, মহাকবি কালিদাস রচিত অভিজ্ঞানশকুন্তল-এর ‘উপাখ্যানভাগ’ অবলম্বনে শকুন্তলা, সেইসঙ্গে সীতার বনবাস যার ‘প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক সঙ্কলিত হইয়াছে’। অনুবাদ করেছেন Æsop’s Fables থেকে কথামালা, কিছু কিছু মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের কাহিনি অবলম্বনে জীবনচরিত, যার ‘প্রথমবারের বিজ্ঞাপন’-এ ঈশ্বরচন্দ্র জানাচ্ছেন, ‘রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স, বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া, ইঙ্গরেজী ভাষায় যে জীবনচরিতপুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইল, এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে এই আশয়ে আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।’ এ ছাড়া বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ তো কিংবদন্তি। বর্ণপরিচয় প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন অনেকের মনেই হয়তো উঁকি দেয়, বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত শিশুশিক্ষা-র মতো বহুল প্রচারিত বাংলা প্রাইমার থাকা সত্ত্বেও কেন বিদ্যাসাগর বইটি লিখতে গেলেন, এবং কালে কালে জনপ্রিয়তায় শিশুশিক্ষা-কে পিছনে ফেলে আপামর বাঙালির কাছে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগই কেন হয়ে গেল প্রধান প্রাইমার গ্রন্থ। এর কারণ, আমাদের মনে হয়েছে, বিদ্যাসাগরের বাস্তবতাবোধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি জানতেন শিশুদের সহজসরল ভঙ্গিতে বর্ণের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোই প্রাইমারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের চালু বিন্যাসে মৌলিক পরিবর্তন ঘটালেন, যে কথা স্পষ্ট করে জানিয়েও দিলেন বই দু’টির বিজ্ঞাপনে। এ হল এক নম্বর, এবং মোক্ষম দুই নম্বরটি হল— শুরু শুরুতে শিশুদের পাঠাভ্যাসে অত্যন্ত জরুরি যে ছবির আভাস (পাঠকের মনে উদিত হতে পারে বিখ্যাত সেই পিকাসো-বচন: ‘Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up.’) সেই ভাব ফুটিয়ে তুলতে প্রথম থেকে অন্তিম পাঠ অবধি তিনি লেখাগুলিকে ধীর লয় ও ছন্দের মাত্রায় বেঁধে রাখলেন, যেন শব্দ-বাক্য পাঠের মধ্যে দিয়ে বিমূর্ত হতে থাকে ছবি। ছবির কথা যখন উঠলই তখন কীভাবে অনুল্লেখ রাখা সম্ভব মুদ্রণ সৌকর্য নিয়ে বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী ভূমিকা? শ্রীপান্থ তাঁর যখন ছাপাখানা এল (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৭৭) বইটিতে এই প্রসঙ্গ টেনে লিখেছেন, ‘স্কুলের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত হরফের মান স্থির করার জন্য তাঁর (বিদ্যাসাগরের) চেষ্টার কথা… তিনি নাকি সেজন্য শ্রীরামপুরের একটি ঢালাই কারখানায় পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন’ (পৃ. ১৪৩)। বিহারীলাল সরকার রচিত বিদ্যাসাগর-জীবনী উল্লেখ করে শ্রীপান্থ আরও লিখেছেন: ‘কম্পোজিটারের সুবিধার কথা ভেবে বিদ্যাসাগর মশাই খোপে খোপে অক্ষর সাজিয়েছিলেন নতুনভাবে। তাকে বলা হয় “বিদ্যাসাগর সাট” (পৃ. ১৪৩)।’ মুদ্রণ ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে পেট আর পকেট ভরে তোলার উপায় ছিল না, এর উন্নতি ও বিকাশের ব্যাপারে এতটাই গভীরভাবে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন তিনি যে মুদ্রণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল উপযোগী এক শিল্পকলা। শিশুদের বইয়ে মানানসই টাইপোগ্রাফিও অতএব তাঁর কাছে বই রচনার পাশাপাশি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
প্রধানত পাঠ্যপুস্তক ও সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থরচয়িতা বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যের ধরনে বিশদভাবে চারটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এক, জীবনচরিত, কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী ইত্যাদি শিশু/কিশোরদের জন্য ঋজুপাঠ; দুই, শকুন্তলা, সীতার বনবাস ইত্যাদি সাহিত্য পাঠ; তিন, বাল্যবিবাহের দোষ, বিধবাবিবাহ (প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক), বহুবিবাহ (প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক) ইত্যাদি সামাজিক প্রবন্ধ পুস্তিকা এবং চার, অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা ইত্যাদি যুক্তিনিষ্ঠ, তার্কিক, ব্যঙ্গাত্মক গদ্য। বাংলায় আলাদা আলাদা গদ্য রীতির এই আবিষ্কার যে তাঁরই, সেটা বলা এমন নতুন কিছু নয়, যেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন, ‘বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।’ আর, শিল্পীই তো আবিষ্কার করবেন বিষয়ভেদে নতুন নতুন আঙ্গিক। তিন ও চার, এই দুই প্রকার গদ্য প্রসঙ্গে চমৎকার কথা বলেছেন দেবেশ রায়, তাঁর সাম্প্রতিক একটি লেখায়—
বিদ্যাসাগর মশায়ের বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক বাংলা লোকগদ্যের এক মহানিদর্শন। লোকগদ্য বলতে বোঝাচ্ছি ‘পাবলিক প্রোজ’। গদ্য হিসেবে মিলটন-এর অ্যারিওপ্যাগিটিকা-র সমতুল্য। বাংলায় লোকগদ্যের কোনো ঐতিহ্যই ছিল না ও বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজ-এর ছাত্র ছিলেন না। অথচ তিনি কাশ্যপ প্রমুখ শাস্ত্রকারদের যুক্তি খণ্ডন করছেন ও এই দ্বিতীয় পুস্তক যতই উপসংহারের দিকে এগোচ্ছে ততই যে শাণিত হয়ে উঠেছে, তা সম্ভব হয়েছে— ভারতচন্দ্র থেকে কবিগান পর্যন্ত ব্যবহৃত বাংলা ভাষার উদাহরণে ও অভিজ্ঞতায়। এই নির্ভেজাল বাংলা গদ্য ইংরেজি-প্রভাবহীন সচ্ছলতায় ‘রত্নপরীক্ষা কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য প্রণীত’ রচনাটিতে প্রখর প্রকট আক্রমী ও জঙ্গি হয়ে উঠেছে (স্বরান্তর, ‘ছোটো পত্রিকা, নতুন লেখা, অচেনা পাঠক’, বর্ষ ৫ সংখ্যা ১০, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৯০)।
‘বিদ্যাসাগর-রচনাবলি: না-পড়া অংশ’ নামে দু’পাতার একটি লেখায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আমাদের বিদ্যাসাগর রচিত নানা বইয়ের ‘বিজ্ঞাপন’ অংশে মনোযোগী করে তোলেন: ‘কিন্তু মন দিয়ে এই ছোটো ছোটো লেখাগুলি পড়লে বিদ্যাসাগরের ধ্যান-ধারণা, পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে নিজেদের বোধ-বিবেচনা আরও স্পষ্ট হয়। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতামত আরও ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়।’ (বিদ্যাসাগর : নানা প্রসঙ্গ, পৃ. ১৭৬)। অতএব দু’-একটি নমুনা নেয়া যাক (স্থানে স্থানে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে বাঁকা হরফ ব্যবহৃত হল):
পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া ইহার রচনা অতি সরল। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ সরল গ্রন্থ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।… মধ্যে মধ্যে অনেক দীর্ঘ সমাস আছে, অনেক অসার ও অসম্বন্ধ কথা আছে, এবং কয়েকটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। ইহাতে, অধুনাতন গ্রন্থের ন্যায়, রচনার মাধুর্য্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য্য নাই। (‘বিজ্ঞাপন’, ঋজুপাঠ, প্রথম ভাগ)
শেক্সপীর পঁয়ত্রিশখানি নাটকের রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।… অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, এরূপ নহে; এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাতবিবর্জ্জিত কি না মাদৃশ ব্যক্তির তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতাপ্রদর্শন মাত্র। (‘বিজ্ঞাপন’, ভ্রান্তিবিলাস)
বিষ্ণুপুরাণ অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত গ্রন্থ; পাঠমাত্রেই অর্থপ্রতীতি হয়।… এই পুরাণ অন্যান্য যাবতীয় পুরাণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।… যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না।…
বিষ্ণুপুরাণের রচনা যেরূপ প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত, মহাভারতের সেরূপ নয়। আবৃত্তিমাত্র সকল স্থলের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। অনেক স্থল এরূপ দুরূহ অথবা অস্পষ্ট যে কোনওক্রমেই অর্থপ্রতীতি হয় না। (‘বিজ্ঞাপন’, ঋজুপাঠ, তৃতীয় ভাগ)
নিজের লেখা বইয়ের পাশাপাশি বেশ কিছু বই সম্পাদনা যেমন করেছেন, তেমনই কিছু কিছু সাময়িক পত্রর সম্পাদনার কাজেও বিদ্যাসাগরের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল প্রধানত ব্রাহ্ম-ধর্মীদের নিয়ে গঠিত ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’-র মুখপত্র গোছের, হিন্দু হয়েও বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন সেই সভার শেষ সম্পাদক। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সরাসরি সম্পাদনা না করলেও বিদ্যাসাগর তার পেপার কমিটির সদস্য ছিলেন। এই পেপার কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমতিসাপেক্ষে পত্রিকাটিতে লেখা প্রকাশিত হত এবং কোনও কোনও রচনার অদলবদলেও কমিটির অধিকার ছিল। ১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর সোমপ্রকাশ নামে একটি সাপ্তাহিকপত্র প্রথম প্রকাশ পায়। এটি প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে, ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধে কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ হাজার টাকায় তার স্বত্ব কেনেন। কিন্তু পত্রিকা চালানো হবে কী করে। বিদ্যাসাগরই সে দায়িত্ব পালন করেছেন।
গ্রন্থ সম্পাদক হিসেবে তাঁর সম্পাদিত বইগুলির ‘বিজ্ঞাপন’ থেকে আমরা সবিশেষ আন্দাজ করতে পারি এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল কতই প্রগাঢ়। দু’-একটি নমুনা:
পাঠবৈলক্ষণের ন্যায়, মেঘদূতে শ্লোকসংখ্যারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।… এরূপ সংখ্যাবৈলক্ষণ্যের কারণ এই বোধ হয়, কোন কোন ব্যক্তি, ক্ষমতাপ্রদর্শনবাসনায়, দুই একটি শ্লোক রচনা করিয়া মেঘদূতে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই প্রক্ষেপক্রিয়া এক দেশে বা এক সময়ে সম্পন্ন হয় নাই; তত্ প্রযুক্তই, সকল পুস্তকে সমস্ত শ্লোকের প্রক্ষিপ্ত সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। (‘বিজ্ঞাপন’, মেঘদূত, ১৮৬৯)
ভবভূতি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কবির কাব্যে গিরি, নদী, অরণ্য প্রভৃতির প্রকৃতিরূপ বর্ণনা নিতান্ত বিরল। অন্যান্য কবিরা, অনাবশ্যক হইলেও, আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু ভবভূতি সে দোষ দূষিত নহেন।… ইঁহার যেমন অসাধারণ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই অসাধারণ দোষও লক্ষিত হইয়া থাকে।… মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে, যে তদ্দ্বারা অর্থবোধ ও রসগ্রহ বিষয়ে, বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। নাটকে, কথোপকথনস্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাস অবলম্বন নিরতিশয় দোষাবহ, তাহার সন্দেহ নাই। (‘বিজ্ঞাপন’, উত্তরচরিত, ১৮৭০)
‘বাল্যবিবাহের দোষ’ শিরোনামে একটি ছোট লেখা বিদ্যাসাগর লেখেন সর্ব্বশুভকরী (১৮৫০, সম্পাদক: মতিলাল চট্টোপাধ্যায়) পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। বিশেষত হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদের উদ্যোগেই এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ এবং তাঁদের বিশেষ অনুরোধেই তাঁর এই লেখা। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক নিবন্ধগুলির মধ্যে এটিই যে প্রথম তা বলা যায়। এই রচনাটিতে বিধবাবিবাহ ও বিবাহব্যাপারে প্রণয়ের স্থান নিয়ে তাঁর বক্তব্য ও মন্তব্য থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসে যে, শিক্ষাসংস্কারের পাশাপাশি তিনি এবার নিজের কর্মশক্তি সংহত করে আনবেন সমাজসংস্কারের কাজে।
মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে।
…
এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অস্মদ্দেশীয় বালক-বালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত।… সন্তানের হৃদয়ে জননীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই,…
…
… বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার।… বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপকার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ‘বাল্যবিবাহের দোষ’, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৫-৯)।
ভাই শম্ভুচন্দ্রকে চিঠি লিখে ‘বিধবাবিবাহ প্রবর্তন’-কে যে-ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ‘জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম’ বলে উল্লেখ করেছিলেন, বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আর্থিক দেনায় জর্জরিত হয়েছিলেন, সেই তিনিই আবার বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, ‘আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম।’ (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, পৃ. ৪৮২)। এ থেকে স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি বিদ্যাসাগর ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন?
আমরা তাঁর জীবনের কাহিনি থেকে জেনেছি, স্ত্রী-পুত্র-মাতা-পিতা-পরিজন, এমনকী চিরদিনের মতো বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এ কি শুধুই তাঁর আপসহীন মানসিকতা, কোনও অন্যায় মেনে না নেবার প্রবল জেদ মাত্র? না কি তাঁর মধ্যে মানিয়ে নিতে না-পারার ব্যাপার ছিল? বারবার তাই বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, সভা বা সমিতি থেকে পদত্যাগ করেছেন। এমন কথা কারও কারও বিচার-বিশ্লেষণে উঠে এলেও মেনে নেয়া কঠিন। কেননা কোনও কাজ অসম্পূর্ণ রেখে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি, এমন উদাহরণ নেই। দুর্গাচরণের কাছে বিধবা বিবাহ নিয়ে ওই আক্ষেপের পরেও সাধ্যমতো তিনি বিধবা বিবাহের আয়োজন-অনুষ্ঠানে শুধু উপস্থিতই থাকেননি, যতদূর সম্ভব সাহায্য করে গিয়েছেন। খাঁটি স্বদেশি উদ্যোগে ও পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। এর সমতুল্য, গোটা ভারতে এমন আর একটিও ইন্স্টিটিউশন সে যুগে দেখানো যাবে না, যার শিক্ষকেরা ছিলেন সকলেই ভারতীয়। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে এমন অভিযোগ অনেকে করেছেন যে, শ্রেণি অবস্থানের কারণে তিনি তাঁর মধ্যবিত্ত সমাজের ঘেরাটোপ ও ইংরেজ-প্রীতি বা নির্ভর অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, অর্থাৎ কিনা তাঁকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান নিতে খুব-একটা দেখা যায়নি। কথাটা অর্ধসত্য। সমাজসংস্কারের অনেক বিষয়েই তাঁকে ইংরেজদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়ার পর বহুবার সরকারি চাকুরির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি তিনি। কে না জানে সেসময় ব্রিটিশরাজের অধীনে চাকরির বলে কতদূর ক্ষমতার অধিকারী হতে পারা যেত। তা ছাড়া, মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা কি প্রমাণ করে না তাঁর স্বাধীনচেতা মানসিকতার? একেও কি ইংরেজ-প্রীতি বলব?
বিদ্যাসাগর যে-সময় জন্মেছিলেন সেই সময়ের সমাজচিত্রর বেশিরভাগটাই আমরা পাব বাংলা সাময়িকপত্রগুলির বিবরণ থেকে, এবং ইংরেজ ও ইংরিজি-শিক্ষিত বাঙালি রচিত কিছু কিছু রিপোর্ট আর ইতিহাসগ্রন্থ থেকে, যেগুলির সিংহভাগই ছিল ইংরিজিতে লেখা। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ ‘শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্বক, সঙ্কলিত’ করেছিলেন। লন্ডনে বসে সেসময় কার্ল মার্কস এরকম নানা তথ্য ঘেঁটে ভারতবর্ষর তৎকালীন অবস্থা বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। এখানে সেইসব চিঠির একটি (লিখিত হয়েছিল ২২ জুলাই ১৮৫৩ এবং মুদ্রিত হয়েছিল ৮ আগস্ট ১৮৫৩) থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরা যাক:
দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রম-জাতিভেদে; এমন একটা স্থিতিসাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়ে উঠেছিল যা এসেছে সমাজের সভ্যদের মধ্যস্থ একটা পারস্পরিক বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা থেকে;— এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের এক অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না? হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই?…
ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলন্ডকে, একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক— পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক [material] ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।
… কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণি গড়ে উঠছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। (সূত্র: https://www.marxists.org/bangla/archive/marx-engels/1853/indianwar/indian-war-independence.pdf)
মার্কস লক্ষ করেছিলেন নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, যাঁরা আলোকপ্রাপ্ত, ‘ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে’ যাঁরা ‘সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন’। বিদ্যাসাগরও তেমনই একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তিনি ইংরেজ শাসকদের সাহায্য নিয়ে চেয়েছিলেন, মার্কস-এর মতে যা ছিল ‘ইংলন্ড’-এর ‘কর্তব্য পালন’, ‘পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক [material] ভিত্তির প্রতিষ্ঠা’, সেই কাজে এগিয়ে যেতে। কিন্তু হায়, ইংরেজরা সেই ‘দ্বিবিধ’ বুর্জোয়া ‘কর্তব্য’ থেকে নিজেদের সরিয়েই রাখলেন এবং ভারতীয় সমাজে ধনী ভারতীয়রা হয় তাঁদের জমিদারি নিয়ে অথবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টের ভূমিকা নিয়ে রসেবশেই থেকে গেলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজকল্যাণে নিজেদের যুক্ত করে নিলেও একটা শ্রেণি হিসেবে উদ্যোগপতি হওয়ার মতো জোটবদ্ধ কর্মশক্তি দেখাননি। পুরনো সামন্তব্যবস্থাটা অতএব থেকেই গেল। যে-সমাজ এমন স্থিতাবস্থা নিয়ে চলে, সেখানে পরিবর্তন, বিশেষত রাজনৈতিক পরিবর্তন খুব কঠিন। এক-আধজন ব্যক্তির পক্ষে, সে তাঁরা যতই উদারনীতিক হন, সেই পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভবই নয়। কেননা কাজটা ছিল শ্রেণিগতভাবেই উদ্যোগপতি তথা পুঁজিপতিদের— পুরনো সামন্তব্যবস্থাটা ভেঙে ফেলা ও সেইসঙ্গে জাতপাত ও ধর্মীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটানো।
ভারতের মাটিতে বুর্জোয়া ‘কর্তব্য’-পালনে ব্রিটিশ শাসকদের নিস্পৃহতা-প্রসঙ্গ এনে অশোক সেন তাঁর Iswarchandra Vidyasagar and His Elusive Milestones (Riddhi-India, Calcutta, 1977) বইয়ে জানাচ্ছেন, ‘Time and again, Vidyasagar was a victim of… British policy.’ (p. 91) শ্রীসেন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন না করা এবং সেইসঙ্গে বহুবিবাহ রদে আইন প্রণয়ন থেকে বিরত থাকার বিষয়কে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি অত্যন্ত যথার্থভাবে এও জানিয়েছেন, ‘Admittedly, the Bengali middle class had no strength of an economic role to fulfill the sufficient conditions of progressive social leadership.’ (p. 93)
অতএব আমরা দেখলাম, শিক্ষাই হোক বা সমাজ সংস্কার, যেদিকেই এগিয়েছেন বিদ্যাসাগর, কি তথাকথিত প্রগতিশীল ইংরেজ শাসক, কি দেশীয় শিক্ষিত-পণ্ডিত মধ্যবিত্ত সমাজের বেশিরভাগ অংশ, তাঁর কাজের পাশে দাঁড়ানোর বদলে বরং বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্ধৃত করেই বলি:
সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন (রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৭৮২)।
কিন্তু এই ‘নির্বাসন’ তিনি নিয়েছিলেন নিজের মধ্যবিত্ত সমাজের থেকে, নিজের আত্মীয়-পরিজনের থেকে। এমনকী মাতা-পিতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের থেকেও যে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করে নিয়েছিলেন সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ক্রমশ ‘কৌম’ বা প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যর ভাষায় ‘বেসরকারি’ সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে নিচ্ছিলেন নিজেকে (প্রদ্যুম্নবাবুর একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধর নামই হল ‘বিদ্যাসাগর ও বেসরকারি সমাজ’। দ্র. টীকাটিপ্পনী, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮)। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে তাঁর কর্মকাণ্ড বা ১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া মহামারি শুরু হলে হিন্দু-মুসলমান চাষিদের মধ্যে তাঁর সেবাকর্ম অথবা কার্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের পরমাত্মীয় করে নেবার খবর তো সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁর ওই স্বেচ্ছা নির্বাসন ছিল স্ব-শ্রেণির মানুষজনের থেকে, কাজের থেকে নয়। বিশেষত ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশনের মতো স্বশাসিত বিদ্যালয়টিকে কঠিন পরিশ্রমে ধাপে ধাপে কলেজে পরিণত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখব একেবারে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর নিজেকে যুক্ত করে নেবার মানসিকতা, শিক্ষায় দীক্ষায় তাঁদের তিনি স্বদেশিয়ানায় গড়ে তুলছিলেন। ছাত্রদের মারধর করা বা শাস্তি দেয়া একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। ভাবতে অবাক লাগে, এমন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি পেয়েছিলেন কোথায়? ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল এ নিয়ে করুণাসাগর বিদ্যাসাগর থেকে একটি কাহিনি উদ্ধার করি:
মেট্রোপলিটানের ছাত্রেরা একবার বিদ্যাসাগরের কাছে পৌষ-পার্বণের ছুটি চাইল। ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন বিদ্যাসাগর। তারপর ছাত্রদের বললেন— তোমাদের অনেকের তো বিদেশে বাড়ি। কলকাতার বাসায় পিঠে পাবে কোথায়?
ছাত্রেরা বলল— আপনার বাড়িতে।
বিদ্যাসাগর বললেন— ভালো। তাই হবে।
তাই হল। বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ছেলেদের জন্য বিস্তর পিঠের ব্যবস্থা হল। (পৃ. ৩৬৯)
কালের নিয়মে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনেক কাজই ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে, আবার যে-বর্ণপরিচয়-এর মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া শুরু হত, সেই বই আর পড়ানো হয় না প্রাথমিকে। কিন্তু এই মানুষটি তাঁর সময়ের ঊর্ধ্বে উঠে একের পর এক যেসব কাজ প্রায় একক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন, তার তুলনা ভূভারতে নেই। এশিয়াটিক সোসাইটি-র উদ্যোগে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পুথি থেকে সায়ণ-মাধব (‘মাধবাচার্য’) রচিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-র পাঠ উদ্ধার ও সম্পাদনা করে তার অনুবাদের ব্যবস্থা করা (বইটির অনুবাদক ছিলেন তাঁর শিক্ষক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন), যে-বইয়ের দৌলতে সারা পৃথিবী ভারতে বস্তুবাদচর্চার ইতিহাস অবগত হলেন। আবার, শিক্ষা পাঠ্যক্রম নিয়ে ব্যালান্টাইন-এর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মতামত জানাতে গিয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য দু’টি কথা বললেন। এক, ‘কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় নেই।… বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নেই।… সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতে হবে, এদের প্রভাব কাটিয়ে তুলতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজিতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার।’ (দ্র. গোপাল হালদার-কৃত ‘ভূমিকা’, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ষোলো) এবং দুই, সংস্কৃত ও ইংরিজি দু’ ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য পড়ে যে যথার্থরূপে ধারণা করেছে, তার কাছে সত্য— সত্যই। সত্য দু’রকম— এ ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। অর্থাৎ, বিদ্যাসাগর কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্যবিদ্যাকে জোর করে গুঁজে মেলানোর পক্ষপাতী নন, কেননা তা বিভ্রান্তিমূলক। বরং তুলনামূলক পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সত্যকে চিনে নেবার যথার্থ বিদ্যা রপ্ত করার সুলুকসন্ধান দিতে চাইছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ব্যালান্টাইন যখন সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনশেষে বিশপ বার্কলে-র Inquiry (মূল গ্রন্থ: Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, 1710) বইটিকে ভারতীয় সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের পাশাপাশি পড়ানোর প্রস্তাব করেন, বিদ্যাসাগর শিক্ষাদপ্তরকে লিখিত আকারে (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩) তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন: ‘Bishop Berkeley’s Inquiry, which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of philosophy, will not serve the purpose.’ (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, পৃ. ৬৫৯)। এটা ভাবতে তখন কি আমাদের একটু অবাকই লাগে না যে, কত বলিষ্ঠ ভাবেই না ভাববাদী দর্শনগুলিকে তিনি নাকচ করে দিচ্ছেন! ১৯০৯ সালে রাশিয়ার মাটিতে মাখ-পন্থীদের বিরুদ্ধে কলম ধরে লেনিন যখন লিখছেন তাঁর গ্রন্থ বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ (Materialism and Empirio-criticism) তখন এই বিশপ বার্কলে-র প্রত্যক্ষ ভাববাদী দর্শনকে, যার মূল কথাই হল আমাদের মনোজগতের বাইরে বহির্জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ অসম্ভব, তাকেই খণ্ডন করতে হচ্ছিল। বিদ্যাসাগর বার্কলে-কে বাতিল করছেন সাংখ্য ও বেদান্তর সঙ্গে তুলনা করে, আর লেনিন মাখ-পন্থী ভাবনাকে বাতিল করছেন বার্কলে-র সঙ্গে তুলনা টেনে। এটা অবশ্যই কোনও প্রতিতুলনা নয়, তবু পঞ্চাশ বছরেরও বেশি ব্যবধানে ঘটা এই দু’টি ঘটনাকে একপ্রকার সমাপতন বলাটা কি বাচালতা হবে? বিদ্যাসাগর বিষয়টাকে দেখেছেন শিক্ষাসংস্কারক মন নিয়ে, লেনিন দেখেছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কিন্তু যুক্তিবাদিতা ও প্রয়োগের দিক থেকে উভয়ের মননেই কাজ করেছিল তাঁদের সামাজিক সত্তা। আর, এই ২০২০-তে একজনের বয়েস হল ২০০ এবং অন্যজনের ১৫০।
রামায়ণ, মহাভারত-কে কোথাও বিদ্যাসাগর ধর্মগ্রন্থ বলে উল্লেখ করেননি, এমনকী মহাভারত-এর কিছু অংশ অনুবাদ করে যখন বই আকারে বের করছেন তখনও তার ভূমিকায় তেমন উল্লেখ নেই। ধর্ম তাঁর কাছে ছিল একটি ব্যক্তিগত আচরণ মাত্র। তাঁর ‘অজেয় পৌরুষ’, ‘অক্ষয় মনুষ্যত্ব’ তাঁকে সেই যুক্তিবোধ ও কাণ্ডজ্ঞানে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রেখেছিল স্থিতপ্রজ্ঞ।
যেমন কর্মবুদ্ধি তেমনি ধর্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। (‘বিদ্যাসাগরচরিত’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৮০)
যে সময়ের ভিতর দিয়ে চলেছে আমাদের দেশ, ধর্ম-জাতপাত নিয়ে অমানবিক ও প্রতিহিংসার রাজনীতি যেভাবে মানবিকতা বা মনুষ্যধর্মকেই কবরে পাঠাবার সব রকমের আয়োজন করে চলেছে, একটা ভয়, দমনপীড়নের এমন এক আবহ বিরাজ করছে যে, ‘গোটা সমাজ পরিণত হয়েছে আলুর বস্তায়, সকলেই যেখানে ব্যক্তিমাত্র, আকার নেই এমন এক দল বা গোষ্ঠী যারা একসঙ্গে কোনও কাজ করতেও অক্ষম’ সেরকম একটা সময়ে বেশি বেশি করে আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে প্রাসঙ্গিক তো মনে হবেই, যিনি সামাজিক সত্তার ওপরে কখনও ব্যক্তিসত্তাকে স্থান দেননি, এই ইতিহাসজ্ঞান তাঁর দস্তুরমতো ছিল। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে ‘এই বঙ্গদেশে একক’ বলেছেন, সেই মানুষটির একাকিত্ব তাই তাঁর সামাজিক সত্তার আপসহীন ‘অক্ষয় মনুষ্যত্ব’র ‘নির্বাসিত’ নিঃসঙ্গতা, এক সৃষ্টিশীল মানুষের নিঃসঙ্গতা।
বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন, সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন, কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। (‘বিদ্যাসাগরচরিত’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৮২।)
জন্মদ্বিশতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে এই প্রবন্ধ সংকলনের পরিকল্পনার পিছনে স্বভাবতই আমাদের লক্ষ্য ছিল এই সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষটির প্রাসঙ্গিকতার নানা দিক তুলে ধরা। সেইমতোই বিন্যস্ত হয়েছে লেখাগুলি। নিবন্ধকারেরা নানা সময় নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন যেমন, তেমনই তাঁদের মননঋদ্ধ লেখা এই সংকলনের জন্য সময়মতো প্রস্তুত করে দিয়ে আমাকে ও আমাদের নিজ গুণে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় বেঁধে নিয়েছেন। এই উপক্রমণিকায় আমার উচ্চারিত কথার ভিতরে ভিতরে তাঁদেরই ভাবনাসূত্রগুলি রয়েছে উল্লেখে-অনুল্লেখে। এমন একটি সংকলন প্রস্তুত করার নেপথ্যে অনেক কিছু ঘটতে থাকে, অনেক টানা-পোড়েন, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব; তার প্রতিটি পর্যায়ে আনন্দ পাবলিশার্সের কমিশনিং এডিটর মলয় ভট্টাচার্য সবসময় আমার পাশে থেকেছেন, নানা পরামর্শ ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। তাঁকে ও সেইসঙ্গে আনন্দ পাবলিশার্সকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এমন একটা কাজে আমাকে আনন্দের ভাগী করে নিয়েছেন বলে। এইসঙ্গে যে কথা না বললেই নয় সেই কথাটা জোর দিয়ে বলি, এই গ্রন্থের যা-কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি, সবই এই সংকলকের, এবং নিজেকে সম্পাদকের পরিবর্তে সংকলক ভেবে নিতেই আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করব। সবশেষে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন একটা কাজ শেষাবধি কতটা সার্থক হতে পারল তার বিচার করবেন পাঠক।
দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক
খড়দহ, ফেব্রুয়ারি ২০২০


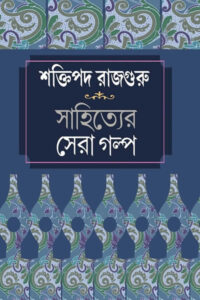
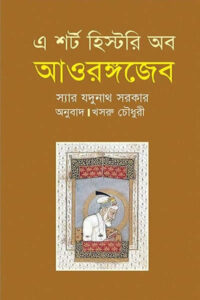

Leave a Reply