এক. ঋগ্বেদ সংহিতা প্রসঙ্গে
চার বেদের প্রত্যেকটিই চারটি অংশে বিন্যস্ত: সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ আক্ষরিক অর্থে সংহিতা ভিন্ন ভিন্ন বেদে আলাদা আলাদারূপে গৃহীত: ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের ক্ষেত্রে ‘আবৃত্তিযোগ্য’; সামবেদে ‘গেয়’ এবং যজুর্বেদে ‘জপনীয়’ মন্ত্রসমূহের সংকলন। ঋক্, সাম ও অথর্ববেদের একটি করে সংহিতা রয়েছে; এদের প্রত্যেকটির এক বা একাধিক পাঠভেদ আছে; অন্য দিকে যজুর্বেদের দুটি সংহিতা— শুক্ল ও কৃষ্ণরূপে পরিচিত। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে একাধিক ব্রাহ্মণ যুক্ত রয়েছে; শুধু অথর্ববেদের একটি মাত্র ব্রাহ্মণ। আবার চারটি সংহিতার প্রত্যেকটিরই একাধিক আরণ্যক ও উপনিষদ আছে, তবে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যবর্তী ভেদরেখা খুব স্পষ্ট নয়। সংহিতাগুলির রচনাশৈলী ও রচনাকাল স্পষ্ট, কিন্তু প্রায়শই রচনাশৈলী ও রচনাকাল স্পষ্ট হলেও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলি প্রায়শই পারস্পরিক সীমা লঙ্ঘন করেছে; তাই একই ধরনের রচনা কোনও শাখার কাছে ব্রাহ্মণ, আবার অন্য শাখার কাছে আরণ্যক বা উপনিষদ রূপে পরিচিত। কিংবা কোনও ব্রাহ্মণের হয়তো এমন উপসংহার অংশ রয়েছে, যাকে ওই ব্রাহ্মণটি কখনও আরণ্যক কখনও বা উপনিষদ বলে উল্লেখ করছে অথবা একই সঙ্গে দুটোই।
বেদের সংহিতা পাঠ প্রচলন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বিন্যস্ত হয়েছিল। এই পাঠ আবার শাখা বা চরণে বিভক্ত। প্রতিটি শাখায় একটি একটি সংহিতা রয়েছে, অন্য দিকে চরণগুলির সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত আছে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ও সূত্র; এই পার্থক্য সাধারণ ভাবে আঞ্চলিক ভেদজনিত বলেই ধরা যায়। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে এক যুগ থেকে অন্য যুগে আনুক্রমিক এবং এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশের সঞ্চরণের ফলে মৌখিক সাহিত্যের বিশুদ্ধ পরম্পরা কিছু না কিছু পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এটাও সম্ভব যে, কিছু কিছু বিকল্প পাঠের প্রতি আঞ্চলিক পক্ষপাতের ফলেই রচনার স্থানে-স্থানে পাঠভেদ তৈরি হয়েছে, যদিও সমগ্র সাহিত্যকে ঐশী প্রেরণালব্ধ ও অপৌরুষেয়— আর সেই জন্যে আবহমান কাল ধরে সমরূপ ও অপরিবর্তনীয়— বলে দাবি করা হয়ে থাকে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বেদের এই পাঠভেদগুলি যে এত বিরল ও তাৎপর্যহীন, সেটাই বরং বিস্ময়ের। এতে আমরা যেমন চিরায়ত ভারতীয় রক্ষণশীলতার পরিচয় পাই, তেমনি উচ্চারিত শব্দকে অপরিমেয় তাৎপর্যপূর্ণরূপে গ্রহণ করার মৌলিক প্রবণতা সম্পর্কেও অবহিত হই।
পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বেদের বহু প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায়: শ্রুতি, অনুশ্রব, আন্নায়, ত্রয়ী, ছন্দঃ, স্বাধ্যায়, আগম এবং নিগম। সংহিতা অনেক শিথিল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্ত্রের সঙ্কলন। ঐতিহ্য অনুযায়ী এই সব মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ ‘বিভাজন’। এটাই এর তাৎপর্য। অঞ্চলভেদে সংহিতার বিভিন্ন বিভাগের একটি সাধারণ ছক দেখা যেতে পারে:
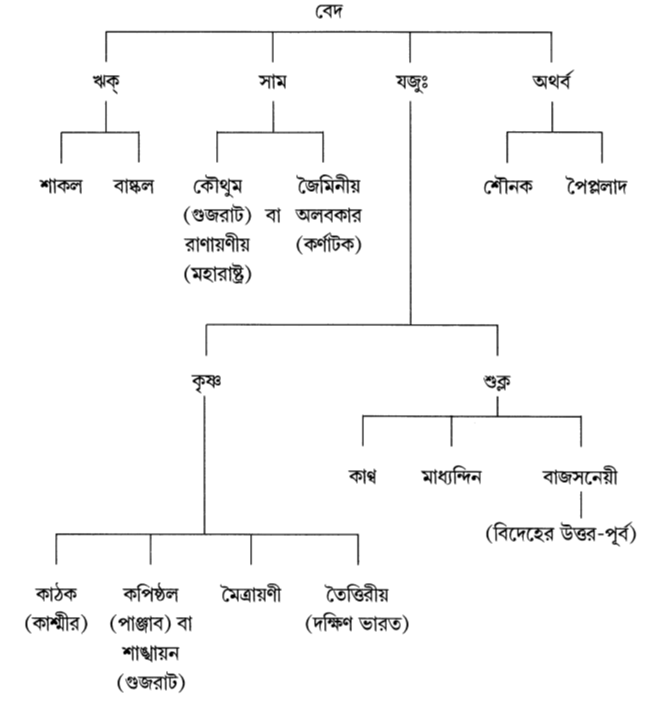
ঋগ্বেদের বিভাগ
আনুমানিক ৯০০–৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাভারতের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় (যদি তা সত্যিই ঘটে থাকে) ঋগ্বেদ তার বর্তমান আকৃতি ধারণ করেছিল বলে মনে হয়। মহাভারতের রচয়িতা ব্যাস সম্ভবত ঋগ্বেদের নবম খণ্ড অর্থাৎ সোম মণ্ডলের প্রণেতা ছিলেন; এই মণ্ডলের মধ্যে স্পষ্ট সম্পাদকীয় প্রয়াস থেকে এমনটা মনে হয়। পূর্বতন নয়টি মণ্ডলের তুলনায় দশম মণ্ডল অনেক পরের রচনা। বৈদিক সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টিধর্মী পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে চারটি সংহিতা। ঐতিহ্যগত ভাবে ঋগ্বেদ দশটি খণ্ড বা মণ্ডলে বিভক্ত; এই মণ্ডলগুলি আবার বিভিন্ন অনুবাক-এ বিভক্ত; প্রতি অনুবাকে অনেক সূক্ত এবং প্রতি সূক্ত কিছু মন্ত্ৰ বা শ্লোকের সমষ্টি। শাকল শাখা মণ্ডলক্রম বিভাগকেই অনুসরণ করেছে ও বালখিল্য সূক্তগুলি সংকলন করেছে। প্রখ্যাত টীকাকার সায়ণ খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে এই শাখাকেই অনুসরণ করেছিলেন। মণ্ডল বিভাগের প্রাচীনতম উল্লেখ রয়েছে ঐতরেয় আরণ্যকে। মণ্ডল বিভাগের তুলনায় যান্ত্রিকক্তর বিভাজন রয়েছে বাঙ্কল শাখায়; সেখানে সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতাকে পরিমাণগত ভাবে সমান আটটি খণ্ড বা অষ্টকে বিন্যাস্ত করা হয়েছে; প্রতি অষ্টকের আটটি করে অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায়ের মোটামুটি ভাবে তেত্রিশটি করে বর্গ রয়েছে; আবার প্রতি বর্গই কিছু শ্লোকের সমষ্টি।
শাকল: ১০ মণ্ডল, ৮৫ অনুবাক, ১০১৭ (+ ১১ বালখিল্য) সূক্ত, ১০৮৫০ ঋক্, ১৫৩৮২৬ পদ
বাঙ্কল: ৮ অষ্টক, ৬৪ অধ্যায়, ২০০৬ বর্গ, ১০৪১৭/১০৬১৬/১০৬২২ সূক্ত
বৈদিক শাখা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থ চরণব্যূহ অনুযায়ী ঋগ্বেদ সংহিতার পাঁচটি বিভিন্ন পাঠভেদ ও সমপরিমাণ শাখা ছিল। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের অধিকতর সমীপবর্তী বাঙ্কল শাখা বর্তমানে অপ্রচলিত। পরবর্তী ঋগ্বেদ-সাহিত্যের দুটি প্রধান শাখা: ঐতরেয় এবং কৌষীতকি।
ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের মধ্যে প্রত্যেকটির রচনাকাল ভিন্ন; এর মধ্যে অন্তত তিনটি প্রধান পর্যায় সহজেই আবিষ্কার করা যায়। প্রাচীনতম বা মূল পর্যায়ে রচিত হয় ‘পারিবারিক মণ্ডল’ রূপে পরিচিত দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল; গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ— এই ঋষি-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কবিরাই মণ্ডলগুলির রচয়িতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে মূলত কাণ্ব পরিবারভুক্ত কবিদের রচনা: অষ্ট মণ্ডল, এবং এই মণ্ডল বিন্যাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী সঙ্কলিত প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অংশ, ৫১ তম থেকে ১৯১ তম সূক্ত। তৃতীয় পর্যায়ে, সম্ভবত সোমযাগের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের জন্য, আটটি মণ্ডল থেকে সোমদেবতার উদ্দেশে রচিত সমস্ত সূক্ত একটি পৃথক মণ্ডলে সঙ্কলিত হয়। এটিই হল নবম বা সোমমণ্ডল। আরও অন্তত দুই শতাব্দী পরে চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে রচিত হয় দশম মণ্ডল এবং প্রথম মণ্ডলের প্রথম অংশ, ১–৫০ সূক্ত।
সংহিতায় শেষ দুটি পর্যায়ের সূক্তসমূহ বিষয়বস্তু অনুযায়ী সঙ্কলিত; প্রথম দুটি পর্যায়ের মতো কবি-পরিবারের পরিচয় অনুযায়ী নয়।
সুতরাং আমরা ঋগ্বেদের চারটি ভিন্ন রচনাস্তরের একটি রৈখিক বর্ণনা করতে পারি :
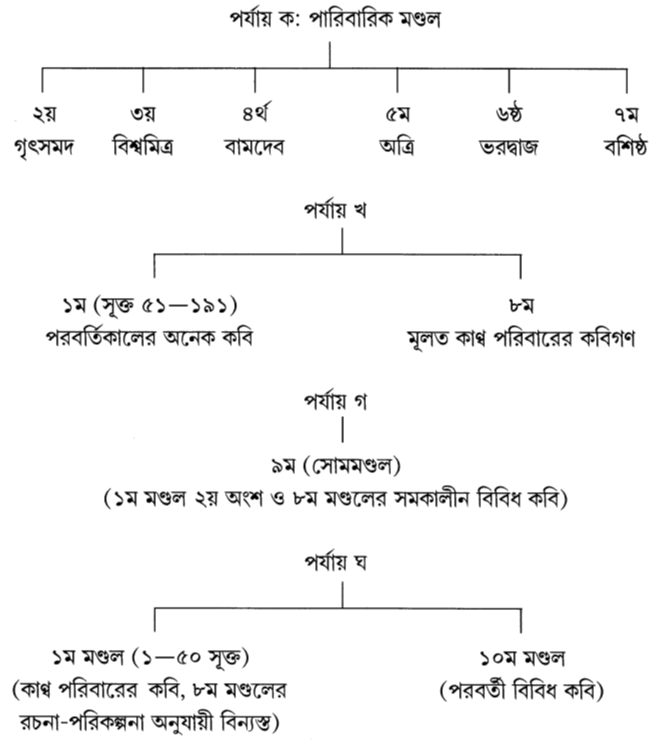
প্রাচীন ভারত বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেন, দশম মণ্ডলের ১৫১টি কবি-নামের মধ্যে মাত্র ৭৮টিই নির্ভরযোগ্য, অন্য ৭৩টি কাল্পনিক।
মন্ত্র-বিন্যাসের পদ্ধতিতে কিছুটা অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়; পারিবারিক মণ্ডলগুলির প্রত্যেকটির প্রথম সূক্ত অগ্নির প্রতি নিবেদিত, আবার নবম মণ্ডলে একমাত্র সোমদেবতাই স্তুত হয়েছেন। মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণত ছন্দঃক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত। বেদ ঐশীপ্রেরণাজাত, বোধিলব্ধ ও অপৌরুষেয় এবং নিশ্চিত ভাবেই প্রত্যাদেশ রূপে বৰ্ণিত হওয়ায় বৈদিক সাহিত্য বিশুদ্ধ ও অখণ্ডনীয়, অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছে। উল্লেখনীয়, বাইবেল ও কোরান এ রকম ঐতিহ্য অনুসারী। তবে এর অন্যবিধ তাৎপর্যও রয়েছে। দৈব প্রেরণা মন্ত্রপ্রণেতাকে এতটা আলোড়িত করত যে, তিনি শিহরিত হতেন (তুলনীয় ‘বিপ্র’, বিপ্ ধাতু, শিহরণ অর্থে)। সেই প্রেরণার ফলেই দৈনন্দিন সাধারণ ভাষা থেকে মন্ত্রগুলির ভাষা খানিকটা পৃথক হয়ে পড়ত। এই পার্থক্যের মূলে আছে কাব্যিক ভাষায় উপলব্ধিগত তুরীয়তার প্রতিফলন। তাই ঋষিগণ ‘মন্ত্র রচয়িতা’ নন, এই বিশ্বাস দৃঢ় ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে, এবং তাঁদের বলা হল ‘মন্ত্রদ্রষ্টা’। এমনটা না হলে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, সাধারণ মানুষই এই সর্বজনস্বীকৃত অতিমানবিক সাহিত্যের প্রণেতা। তাই মন্ত্র হয়ে উঠল প্রত্যাদেশ, আর ঋষি-কবি হলেন দ্রষ্টা। খুবই যথার্থ অর্থে সমস্ত মহৎ কবিতাই প্রত্যাদেশ, কেননা মুষ্টিমেয় মহৎ কবিই তা রচনা করতে পারেন; আর, এই অনন্য অন্তর্দৃষ্টি ও যথাযোগ্য ভাষায় তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতাই তাঁদের সাধারণ জনপ্রবাহ থেকে পৃথক করে রাখে। সাধারণ মানুষও এই অসামান্য সৃষ্টিপুঞ্জকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়রূপে গ্রহণ করে বিশেষ মর্যাদা দিতে চাইল।
বহুপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত পরিবারসমূহের কবি ছাড়াও আমরা কয়েকজন মহিলা কবি বা ঋষিকার সন্ধান পাই: লোপামুদ্রা, (১:১৭৯), অপালা মৈত্রেয়ী (৮:৯১), যমী (১০:১০), বসুক্রের পত্নী (১০:২৮), কাক্ষীবতী ঘোষা (১০:৩৯-৪০), সূর্যা (১০:৮৫), ঊর্বশী (১০:৯৫), অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ (১০:১২৫), ব্রহ্মজায়া (১০:১৩৯), বিবস্বৎ-কন্যা যমী (১০:১৪৫), ইন্দ্ৰাণী (১০:১৪৫), শ্রদ্ধা কামায়নী (১০:১৫১), পৌলোমী শচী (১০:১৫৯) এর উদাহরণ। এই সমস্ত সূক্তের নাম ও বিষয়সূচি, অর্থাৎ প্রার্থনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা রচয়িতাদের সামাজিক পশ্চাৎপট সম্পর্কে অবহিত হই; এই সব কবিদের তৎকালীন সমাজের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা চলে। কোনও মহিলা কবিই অন্য কারও সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয় নন, তবুও সামগ্রিক ভাবে বৈদিক সমাজের নারীজগৎ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়েই আমরা পাই। যে সব কবি অনেক শ্লোক জানতেন কিংবা রচনা করেছিলেন, তাঁদের ‘বহুবচ’ (বহু + ঋচ্) বলে উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন কবির মধ্যে চারণকবিসুলভ প্রতিযোগিতার লক্ষণও আমরা দেখতে পাই। বিশেষত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রায় সমতুল্য মর্যাদাদানের মধ্যে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। পরবর্তী জনশ্রুতি অনুযায়ী এই দুই ঋষির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। কিছু কিছু সূক্তে কবি পরিচয় অত্যন্ত যান্ত্রিক ভাবে নির্ধারিত হয়েছে; দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনারত ঋষির নাম অনুসারে সংবাদ সূক্তগুলির প্রতি শ্লোকে সেই পরিচয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ যাঁর উদ্দেশে কিছু বলা হয়েছে তিনি তখন দেবতা এবং যিনি তা বলছেন তিনি ঋষি। তাছাড়া এমন কিছু সুক্তও রয়েছে যেখানে কবির পরিচয়ে কোনও দেহধারী মানুষের ইঙ্গিত নেই; যেমন মন্যু বা ক্রোধ (১০:৮৩) এবং অর্বুদ নামে সর্প। (১০:৯৪)
পুরোহিত-পরিবারগুলি বিশেষ ভাবে কৌতূহলজনক: যখন কোনও অনুপ্রাণিত কবি কাব্যিক বা অনুষ্ঠানগত ভাবে তাৎপর্যময় গীতিরচনায় সফলকাম হতেন, সম্ভবত তখনই তিনি তাঁর সৃষ্টির দীর্ঘায়ু কামনা করে স্বাভাবিক ভাবে সন্তান বা শিষ্যদের তা কণ্ঠস্থ করতে শিক্ষা দিতেন। নিরক্ষর সমাজও স্মরণীয় শ্লোক রচনায় সমর্থ ছিল, কিন্তু সংরক্ষণই ছিল তার সমস্যা; অতএব স্বাভাবিক ভাবেই সংরক্ষণ-বিষয়ে কবির নিকট-আত্মীয় বা শিষ্যগণই ছিলেন সর্বাধিক আগ্রহী এবং নির্ভরযোগ্য আধার। সম্ভবত তাঁরা মৌখিক সাহিত্য রচনার প্রক্রিয়াকে খুবই নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করে থাকবেন এবং ক্রমশ আবেগের সংবেদনশীল মুহূর্তগুলিকে বাচনিক অভিব্যক্তিদানের রহস্যেও দীক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। এ ভাবেই কিছু কিছু পরিবারের সদস্যরা অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ-ক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে এক একটি কবি-পরিবাররূপে সম্মানিত হয়েছিলেন; কখনও কখনও পাঁচ প্রজন্ম ধরে এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। আধুনিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে চৌষট্টি প্রজন্ম ধরে ঋগ্বেদের প্রকৃত রচনা অব্যাহত ছিল।
পুরোহিত, চারণ-কবি এবং ঋষি-কবিদের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকরা শিল্প-চাতুর্য্যের জন্য কবিদের রচনার পুরস্কার দিতেন। কেউ কেউ মনে করেছেন যে নববর্ষ উৎসবে চারণকবিরা পুরস্কারের আশায় রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন; তা হয়ে থাকলে, খুব সম্ভবত এটি ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য, গ্রিসের ট্রাগোইডিয়াতে যেমনটা হত বলে জানা যায়। যজ্ঞানুষ্ঠান যখন পরবর্তিকালে বহুমাত্রিক ও জটিল হয়ে উঠেছিল তখন ক্রমেই কবি-পরিবারগুলি বিশেষ মর্যাদার আসনের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তাই ঋগ্বেদের প্রতি সূক্তেই ছন্দ, দেবতা ও যজ্ঞবিষয়ক বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিকবির নামও উল্লেখিত থাকে। এ নামের উল্লেখে রচনাটির ওপারে স্বত্বাধিকারের স্বাক্ষর রয়ে গেছে। এমনকী, তিন হাজার বছরেরও আগে রচিত এই স্তোত্রগুলি যে কবিনামবিহীন নয়, তাতেই বৈদিক জনসাধারণের কবিতা বা স্তোত্রবিষয়ক মনোভাবটি চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।
ঋগ্বেদের রচনাকাল
মৌখিক কাব্যের ভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সমসাময়িক প্রতিশব্দ ও বাগ্বিধিকে গ্রহণ করে অব্যবহার্য্য ও প্রাচীনতর প্রকাশরীতিকে পরিত্যাগ করা হয়। তাই আদি বাসভূমি থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিকে যাত্রার পূর্বে যে ইন্দো-ইয়োরোপীয় মূল ভাষাটির প্রচলন ছিল তা আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বেই পথিমধ্যে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ এবং স্বাভাবিক সময়-বাহিত ধ্বনিগত ও শব্দার্থগত বিবর্তনের ফলে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকী ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়ে ঋগ্বেদের প্রাথমিক সূক্তগুলি যখন তাঁরা রচনা করলেন, তারপরেও কথ্যভাষা স্থিতিশীল রইল না। লিখিতরূপের অভাবে আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অর্থাৎ ভারতভূমিতে আর্যরা পদার্পণ করবার আগেকার রচনার ভাষাকে নিরন্তর সমসাময়িক লক্ষণযুক্ত করে তোলা হচ্ছিল। সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রচিত সমস্ত সূক্তে এই ভাষা সংস্কারের প্রবণতা অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষোক্ত সময়সীমাতে সংহিতা- -রচনার ধারা তুলনামূলক ভাবে ক্ষীণ হয়ে সম্পাদনকর্ম বেড়ে ওঠায় ভাষা কিছুটা স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল। ফলে সেই যুগের ভাষার সূক্তগুলিকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা একটি পবিত্র দায়িত্বরূপে গণ্য হয়েছিল। ভাষাগত পরিবর্তন থেমে যাওয়ার আরও একটি কারণ হল সেই সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সাহিত্যরীতি অর্থাৎ গদ্যে ব্রাহ্মণসাহিত্যের সূত্রপাত। সংহিতা রচনার প্রেরণাময় ও সৃষ্টিশীল পর্যায়টি তত দিনে শেষপ্রান্তে; ক্রমশই, অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ভাষ্যমূলক গদ্য রচনার দিকে বিবর্তিত হচ্ছিল।
ইদানীং ঋগ্বেদ রচনার কাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) শতক থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ধার্য করা হয়ে থাকে, যদিও সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কালসীমা সম্পর্কে গবেষকদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতরা সাধারণ ভাবে অনেক বেশি প্রাচীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সমসাময়িক গবেষকদের মধ্যে কোনও কোনও ভারতীয় পণ্ডিত এখনও প্রাচীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু সাধারণ ভাবে ভারতীয় ও বিদেশি বিদ্বৎসমাজের অভিমত এই যে, ঋগ্বেদ-রচনা আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ বা ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিত টি. বারো-র মতে প্রাচীনতর বৈদিক বা পূর্ব-বৈদিক সাহিত্য (অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম থেকে নবম মণ্ডলের সূক্তগুলি) ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল, আর উত্তর-বৈদিক সাহিত্য (অর্থাৎ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে উপনিষদ পর্যন্ত) ১০০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক সুকুমার সেন কতকটা পরবর্তিকালে রচনার সীমানিরূপণের পক্ষপাতি (অর্থাৎ সূচনাকাল আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ); ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায় বৈদিক ভাষার তুলনায় অবেস্তা কিছুটা পরের অর্থাৎ ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ: অতএব এই দুটি ভাষার সাধারণ উৎসটি অর্থাৎ ইন্দো-ইরাণীয় সাহিত্যের আদিপর্ব ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পিছিয়ে যাবে। তাঁর মতে ঋগ্বেদ খ্রিস্টপূর্ব একাদশ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়ে গিয়েছিল। আবার কিছু কিছু গবেষক সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের রচনাকালের নিম্নতম সীমা ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধার্য করেছেন, অবশ্য পণ্ডিতমহলে এ মত গৃহীত হয়নি।
ঋগ্বেদ-রচনার সর্বাধিক কালগত ব্যবধান রয়েছে প্রথম নয়টি মণ্ডল থেকে দশম মণ্ডলের মধ্যে। যেহেতু সামবেদ একমাত্র দশম মণ্ডল থেকেই কোনও উদ্ধৃতি দেয়নি, এতেই প্রমাণিত হয় যে দশম মণ্ডল সামবেদের পক্ষপাতী। ভাষাগত দিক দিয়েও এই মণ্ডলের অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত: শব্দ-ভাণ্ডার, ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ, বাক্যগঠন রীতি, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, সমস্তই এখানে ভিন্ন। অনেক প্রাচীনতর বাক্রীতি অপ্রচলিত হয়ে গেছে এবং বহু নূতন বাক্পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে; বাগ্ভঙ্গি, ক্রিয়াপদের গঠন, শব্দরূপ ও ধাতুরূপের সীমাবদ্ধ বৈচিত্র্য সঙ্কুচিত ও বহু পূর্বপ্রয়োগে অচলিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। প্রত্নকথা, দেবকল্পনা, ভৌগোলিক সংস্থান ও দার্শনিক প্রতীতির দিক দিয়েও দশম মণ্ডলকে বহু পরবর্তী রচনারূপে চিহ্নিত করা যায়। যদিও এতে কিছু কিছু প্রাচীনতর সূক্ত সন্নিবেশিত হয়েছে, আমাদের মনে হয় যে, সামূহিক স্মৃতি সম্পূর্ণ ক্ষয় হওয়ার পূর্বে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প তাৎপর্যপূর্ণ সূক্তকে সংরক্ষণ করার একটা চেষ্টা হয়েছিল। স্বভাবতই এই প্রবণতা সেই সময়ের দিকেই সংকেত করছে যখন মন্ত্ররচনার সৃষ্টিশীল পর্যায় অবসিত হয়ে সংরক্ষণ, পুনরাবৃত্তি ও সংশ্লেষণের পর্যায় আরম্ভের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাই দশম মণ্ডলকে সাধারণ ভাবে পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্য সূচনার প্রথম সৃষ্টিরূপে গ্রহণ করা হয়।
ঋগ্বেদের ভাষ্যকার
প্রাথমিক স্তরে বৈদিক সাহিত্যের ভাষা ছিল মৌখিক: আচার্য ও শিষ্যের আলাপ; এই জন্যই সেগুলি সংরক্ষিত হয়নি। বেদের সূক্তগুলি অধিকাংশ আর্য বালকের শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যতালিকা ছিল; যেহেতু দেবতারা সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন এবং প্রায়ই সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে যজ্ঞ আয়োজিত হত আর সমগ্র সমাজ এতে অংশগ্রহণ করত, তাই ভাষ্যের প্রয়োজন সম্ভবত খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠান যতই বিরল ও দীর্ঘ ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও আনুক্রমিক যুগবাহিত নূতন অধ্যাত্মবিদ্যার মধ্য দিয়ে নূতন নূতন চিন্তার প্রচলন হতে লাগল, প্রাচীন সাহিত্যের ততই সংরক্ষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হল; ফলে নানা রকম ভাষ্যও রচিত ও সংরক্ষিত হল। এদের মধ্যে আদিতম হচ্ছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি; পরবর্তিকালে আরণ্যক ও উপনিষদ সাহিত্যে যজ্ঞ প্রতীকী ভাবে ব্যাখ্যাত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কোনও ভাষা আমরা পাইনি, সম্ভবত সেগুলি থাকলেও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।
যে সমস্ত ভাষ্যকারদের রচনা আমাদের কালে এসে পৌঁছেছে তাঁদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে খ্যাতকীর্তিরা হলেন, স্কন্দস্বামী, নারায়ণ, উদগীথ, হস্তামলক, উবট (১১শ শতাব্দী), বেঙ্কটমাধব (১২শ), আনন্দতীর্থ (১২-১৩শ), আত্মানন্দ (১৩শ), সায়ণ (১৪শ) রাবণ (১৬শ), দেবস্বামী, ভট্টভাস্কর, হরদত্ত, সুদর্শনসুরি, ভবস্বামী, রহুদেব, শ্রীনিবাস, ভাস্করমিশ্র, মাধবদেব ও মাধবাচার্য। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ঋগ্বেদ সাহিত্য ভাষ্যের বিবিধ প্রবণতার প্রেরণাস্থল হয়েছে: কিছু কিছু ব্যাখ্যা যজ্ঞানুষ্ঠানকেন্দ্রিক, কিছু বা দুরাবগাহী ভাবনাকেন্দ্রিক, কিছু কিছু আবার প্রত্নকথা ও কাল্পনিক উপাখ্যানের অনুগামী। ভাষ্যকারদের আপন প্রবণতা অনুসারেই ভাষ্যগুলির চরিত্রে এই পরিবর্তন।
সূক্ত: প্রকৃতি ও গঠন
ঋগ্বেদে কাব্যসাহিত্য সাধারণত একটি স্তবকের মধ্যেই কোনও ভাব হিসাবে সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। কয়েকটি স্তবক একটি সাধারণ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই একটি সূক্তে সংকলিত হয়; সচরাচর একজন দেবতাকে সম্বোধন করা হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে বহু দেবতা একটি সূক্তে সামগ্রিক ভাবে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে স্তুত হয়েছেন। একই সূক্তের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তুও সন্নিবিষ্ট হয়েছে: দৃষ্টান্ত বেশ কিছু সূক্তের দানস্তুতি অংশগুলি এবং আপ্রীসূক্তের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-অসংলগ্ন অংশগুলি বা সূর্যাসূত (১০:৮৫) কিংবা বহু সংবাদ-সূক্তকে স্তোত্রগীতির প্রতি ঋগ্বেদের কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সেই সঙ্গে সূক্তসমূহের তথাকথিত ঐন্দ্রজালিক শক্তি দিয়ে দেবতাদের অনুকূল করার প্রচলিত বিশ্বাস, এবং সূক্তগুলিতে অভিব্যক্ত সাধারণ মানুষের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে আমরা ঋগ্বেদের কাব্য-মহিমা আরও ভাল ভাবে উপলব্ধি করতে পারব।
স্তোত্রগীতি বিষয়ে দৃষ্টিকোণ
সম্ভবত ঋগ্বেদের কবিদের রচনায় কিছু কিছু আদিম বিশ্বাস কাব্য-রূপ পরিগ্রহ করেছে, বিশেষত ঐন্দ্রজালিক সম্মোহন সম্বন্ধে আদিম জাদুকর বৈদ্যের মনোভাব এতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, দেবতাদের ক্ষমতা ও মহাজাগতিক ক্রিয়াকলাপকে পরিপুষ্ট করেই সূক্তগুলি ঐন্দ্রজালিক আবেশ তৈরি করতে সমর্থ: ঠিক যে ভাবে আহুতিরূপে অর্পিত খাদ্য দেবতাদের পরিপুষ্ট করে, স্তুতিও সে ভাবেই দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন করে। স্তুতি রণক্ষেত্রে ইন্দ্রের যোদ্ধা চরিত্রের উৎকর্ষ ত্বরান্বিত করে, এটা অতি প্রচলিত ধারণা, কেননা ইন্দ্র প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে আর্যদের জয়, সমৃদ্ধি, শান্তি, স্বাস্থ্য ও সম্পদবৃদ্ধিকে নিশ্চিত করে তোলেন। যজ্ঞের সবচেয়ে প্রীতিকর উপকরণই হচ্ছে মন্ত্র; একটি শক্তিশালী মন্ত্র যজ্ঞের মান বাড়িয়ে দিতে পারে। মন্ত্রগুলির মধ্যে শব্দের ইন্দ্রজাল নিহিত থাকে এবং যথার্থ স্বরন্যাস, উচ্চারণ, সুর ও অনুষ্ঠানসহ যজ্ঞে প্রযুক্ত হলে সেই সব শব্দ রহস্যময় অলৌকিক ক্ষমতা উৎপন্ন করে। মন্ত্রগুলি ঋষিকবিকে অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিতে ভূষিত করেছিল; এমনকী সূর্যও নিজেকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কাছে প্রকাশ করেছিলেন, এমন কথা সূক্তে শুনি।
এটা অনুধাবন করার জন্য উচ্চারিত শব্দের প্রতি আর্যদের অদ্ভুত শ্রদ্ধাবোধের তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন। তাঁদের কাছে বাক্ (গ্রিক ‘লোগস’) হল সেই বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ যা মানুষকে প্রাণিজগতের বহু ঊর্ধ্বে উন্নীত করে; এমন একটা স্তরের কাছাকাছি নিয়ে আসে যেখানে তার সঙ্গে দেবতাদের অবারিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুপ্রযুক্ত স্তোত্র শতবর্ষব্যাপী পরমায়ুর আশ্বাস দেয়। যে ব্যক্তি দেবতাদের স্তুতিগান করে না, জীবনে তার কোনও উন্নতি হয় না। মন্ত্রের সাহায্যে ঋষিকবি পাপ ও দুর্ভাগ্য অতিক্রম করে নিরাপত্তার বেলাভূমিতে উপনীত হওয়ার প্রত্যাশা করেন; এই রকম মন্ত্রই মানুষের সকল বন্ধন-শৃঙ্খল শিথিল করে দেয়।
অতিলৌকিক অর্থেও স্তোত্রগীতি সৃজনধর্মী হতে পারে। অঙ্গিরা বংশের ঋষিরা ছিলেন দেবতাদের প্রতিবেশী ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রকৃত কবি; সেই পূর্বসূরিগণ গোপন নিগূঢ় জ্যোতি জয় করেছিলেন; নিজেদের স্তোত্রের সাহায্যে তাঁরা ঊষাকে অর্জন করেছিলেন। এই বক্তব্যের মূলগত তাৎপর্য এই যে, দেবতাদের প্রতিবেশী সত্যভাষী অঙ্গিরা ঋষিরা যদি যথার্থ প্রশস্তি না গাইতেন, তা হলে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত। অতএব মন্ত্রের অতিজাগতিক ভূমিকা স্পষ্ট; তাদের মাধ্যমেই মানুষ ঐহিক সীমিত স্তর থেকে উৎক্রমণ করে বিশ্বস্রষ্টার স্তরে উন্নীত হয়।
স্তুতি শুধুমাত্র কাব্যিক আবেগ-উন্মাদনার অভিব্যক্তি নয়; বারবার এর দ্বারাই প্রার্থিত বরলাভের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নূতন মন্ত্ররচনা করে সম্পদ ও বলদায়ী অন্ন দান করার জন্য বিভিন্ন দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়, প্রশস্তির বিনিময়ে দৈব অনুগ্রহ ও প্রাণ-প্রাচুর্য কামনা করেন ঋষি-কবি। উপাসনার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ হল স্তোত্রপাঠ। সূক্তরচনার আরও একটি কারণ এই যে, দেবতারা তাঁদের মাধ্যমে নন্দিত হতে ভালবাসেন; এই জন্য বারবার তাঁদের উপস্থিত হয়ে মন্ত্রের স্তুতি উপভোগ করার আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়েছে যে, বিপ্ররা অর্থাৎ ঐশী প্রেরণা-ধন্য কবিরা ঋভুদের জন্য স্তোত্র রচনা করেছেন।
ঋগ্বেদের প্রধান দুই দেবতার অন্যতম অগ্নিকে দেবতাদের কবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর প্রতি নিবেদিত স্তুতি দিয়েই প্রাচীনতর মণ্ডলগুলির প্রারম্ভিক সূক্তসমূহ গঠিত হয়েছে; এর অন্যতম কারণ সম্ভবত অগ্নির কবিসংজ্ঞা। কবিদের হৃদয়েই স্তোত্রের জন্ম; রথনির্মাতা যে ভাবে তার শিল্পকলাকে ধৈর্য ও শ্রমের সাহায্যে প্রকাশ করে তেমনই কবিও শব্দের মাধ্যমে অনুরূপ ভাবে অনুভূতিকে অভিব্যক্ত করেন। সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের উপমা দিয়েও এই একই বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। জনৈক কবি নিজেকে শব্দের কারিগর বলে অভিহিত করেছেন, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি সচেতন শিল্পী এবং কাব্যের শিল্পকর্মটিও যত্নসাপেক্ষ ধীর নিষ্ঠার সম্পাদিত বস্ত্রবয়ন শিল্পের মতোই। আর একজন কবি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের নূতন ভাষা দিয়েই দেবতারা কাব্যের প্রধান উপাদান সৃষ্টি করেছিলেন: মনোরমা বাক্ যদি যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তা হলে অন্ন ও ওজস্বিতা উৎপাদন করে; তাই বাক্ প্রকৃতপক্ষে কামধেনু। মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পূর্ববর্তী বিনিময়ভিত্তিক প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যে গাভী মুদ্রার মতোই ব্যবহৃত হত; এ কথা মনে রাখলে কামধেনুর চিত্রকল্পটি বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। অন্যত্র বলা হয়েছে, প্রেমময়ী সুসজ্জিতা নববধূ তার দয়িতের কাছে যে ভাবে নিজেকে উন্মোচিত করে, তেমনই বাক্ও কবির কাছে আপন সৌন্দর্য প্রকাশ করে। প্রেরণা ও ছন্দোযুক্ত হওয়ার পরই সাধারণ বাক্ নবরূপে অপৌরুষেয় হয়ে ওঠে।
অধিকাংশ কাব্যশিল্পবিষয়ক যে মন্ত্র আমরা প্রথম (৫১–১৯১ সূক্ত) ও দশম, অর্থাৎ কালগত ভাবে দুটি নবীনতম মণ্ডলে পাই, তা খুবই কৌতুহলপ্রদ। সৃষ্টিশীল রচনাপ্রবাহে যখন ভাঁটার টান শুরু হয়েছে, তখন পরবর্তী প্রজন্মগুলি সম্ভবত নিরাসক্ত দূরত্ব থেকে সৃষ্টির রহস্যকে বিশ্লেষণ করে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চাইছিল। নবম মণ্ডলে আমরা প্রায়ই ‘প্রত্নমন্ম বা পুরাণীগাথা’ অর্থাৎ পুরাতন প্রশস্তি বা পুরাতন গীতির কথা শুনি। বস্তুত, নূতন রচনা কবির গভীর শ্রদ্ধাবোধেরই পরিচায়ক— এর প্রভাবে তিনি উদ্দিষ্ট দেবতার জন্য নূতন রচনার অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। অন্যান্য মণ্ডলেও পুরাতন ও নূতন গীতিকে একই সঙ্গে এমন ভাবে প্রশস্তি করা হয়েছে যাতে মনে হয়, এদের গুণগত মাত্রা প্রতি সূক্তেই ভিন্ন। প্রায় কুড়িটি নূতন বা ‘নব্য’ সূক্তের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের নিজস্ব সময়ের বহু পূর্ব থেকেই ঋগ্বেদের সূক্ত-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল, বৈদিক কবিরা এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।
সূক্তের বিন্যাস
ঋগ্বেদের প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ একক; অধিকাংশ সূক্তই একটিমাত্র ছন্দোরীতি অনুসরণ করে, যদিও অন্তিম বা উপসংহারের কয়েকটি শ্লোক কখনও কখনও ভিন্ন ছন্দে রচিত হয়। পরবর্তী মহাকাব্যগুলিতেও সর্গের সমাপ্তি বোঝাতে এই রীতিই ব্যবহৃত হত। মাঝে মাঝে একই সূক্তে দুটি ভিন্ন ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। গঠনকৌশলের দিক দিয়েও যে কোনও সূক্ত সাধারণত একটি মাত্র বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই রচিত; তবে প্রসঙ্গ-বিচ্যুতি ও বিষয়গত প্রক্ষেপ বহু স্থানেই পাওয়া যায়।
ঋগ্বেদের সূক্তগুলিকে পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: ১. ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ক: বিবাহ, অন্তিম সংস্কার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যে সব ব্যবহৃত; ২. প্রার্থনা বিষয়ক: আশীর্বাদ, প্রায়শ্চিত্ত, ইত্যাদি; ৩. প্রত্নকথা বিষয়ক: প্রত্ন উপাখ্যান-সূচক সেই সব সূক্ত যেখানে অনুষ্ঠানসমূহে এদের প্রাসঙ্গিকতা নিহিত; ৪. আনুষ্ঠানিক উৎসর্গমূলক: যজ্ঞের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সমস্ত সূক্তের যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে; ৫. যজ্ঞে প্রযুক্ত হলেও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে সমস্ত সূক্তের যোগ নিতান্ত শিথিল।
আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য অবশ্য আমরা সূক্তগুলির বিষয়বস্তুর স্বভাববৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণি-বিভাগ করছি। যেহেতু অধিকাংশ মন্ত্রই প্রশস্তি বা প্রার্থনা জাতীয়, আলোচনার শুরুতেই আমরা সর্বপ্রথম তাদেরই গ্রহণ করছি। সাধারণত কোনও দেবতাকে আহ্বান করে বিভিন্ন অর্ঘ্যের উপচার স্তব দ্বারা তাঁর বন্দনা করা হয়। দেববন্দনায় তাঁর অবয়ব, পোশাক, অলঙ্কার, আয়ুধ, রথ ও অশ্বের উল্লেখ করে তারপর সাফল্য এবং পূর্ব প্রার্থীদের প্রতি প্রদত্ত দানের বর্ণনা করা হয়; অনেক ক্ষেত্রেই এই সব প্রার্থীদের নামে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয়ও নিহিত। এ ধরনের সূক্ত সমস্ত বৈদিক দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছে।
প্রশস্তি অংশের পরে আসে প্রার্থনা; এর বিষয়বস্তু সাধারণত আহুত দেবতার চরিত্র এবং দেবকল্পনায় তার ভূমিকার দ্বারা নির্ধারিত। স্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, আরোগ্য, শক্তি, জয়, পরমায়ু, জীবনীশক্তি, সম্পদ, স্বর্ণ, গবাদি পশু, উর্বরতা, দাম্পত্য সুখ ও সন্তানের জন্য সৌর দেবতাদের নিকট প্রার্থনা জানানো হয়। মৃত্তিকার উর্বরতা, বিপদে সুরক্ষা ও দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয় পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের কাছে। প্রার্থনাগুলি শুনে প্রায়ই মনে হয় যে, দেবতা ও তাঁর উপাসকদের সম্পর্ক শুধু দাতা ও গ্রহীতার। দেবতাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করে মূল্যবান দানসামগ্রীর কথা, কখনও বা পরিমাণ উল্লেখ করেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে এই তথ্যও জানিয়ে নেওয়া হয় যে, প্রার্থিত প্রাপ্তি যেন দানের সমানুপাতিক হয়। কবি ও সূক্তভেদে প্রার্থনার ভঙ্গি ভিন্ন: কিছু সূক্ত প্রসন্নতা ও শান্তি কামনায়, কিছু কিছু আবার অনুনয় ও স্তাবকতায় পূর্ণ। আবার কোথাও বা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, উপাসক যদি নিজে দেবতা হতেন, তা হলে সমস্ত প্রার্থনাই তিনি যথাযথ ভাবে পূরণ করতেন।
প্রশস্তি ও প্রার্থনামূলক বিষয়বস্তু ছাড়াও ঋগ্বেদের মধ্যে বহু বিচিত্র বিষয়বস্তুর সমাহার লক্ষ্য করা যায়। এ সবের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র ধরনের গীতিকবিতা, বহু বীর ও বীরত্বের উপাখ্যান সম্বলিত গীতিকা, প্রণয়সঞ্চারী সম্মোহন ও উর্বরতাবর্ধক ইন্দ্রজাল বর্ণনা, অলৌকিক কাহিনি, বন্দনা-গীতি, নিসর্গকাব্য (যেমন রাত্রি সূক্ত বা অরণ্যানী সূক্ত), দানবিষয়ক গীতি, প্রেম-সঙ্গীত, শোক-গাথা, বিবাহ-গীতি এবং আক্ষেপ-গীতি ও অন্যান্য বহু বিষয়ে রচিত সূক্ত। বহু স্তোত্রকেই আমরা যুদ্ধগীতি রূপে চিহ্নিত করতে পারি, যেখানে আদিম জনগোষ্ঠীর উপর আর্যদের জয় বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের মধ্যেও এই জাতীয় স্তোত্র লক্ষ্য করা যায়, যেমন দেবোরার গান ও বিজয়গীতি। বৈদিক যুদ্ধগীতিগুলির মধ্যে উৎসাহ ও আড়ম্বরের একটা বিশেষ বাতাবরণ রয়েছে; এ ছাড়া, এতে শত্রুর উল্লেখ, ইন্দ্রের বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা, ইত্যাদি বার বার উল্লিখিত হয়েছে। এ ধরনের রচনায় আমরা এক দিকে আক্রমণকারী আর্যজাতির সেনাপতিরূপে বন্দিত ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সোম, মরুণ ও বিষ্ণু এবং অন্য দিকে বৃত্র, অহি, নমুচি, ধুনি, চুমুরি এবং অন্যান্য প্রাগার্য জাতির গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক সংগ্রামের আভাস পাই। প্রতিটি পক্ষেই অনুগামী সৈন্যদল বর্ণিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ইন্দ্ৰ প্রাচীর-বেষ্টিত বসতিগুলির দুর্গ-প্রতিরোধ ভেদ করে বিজিত জাতির গবাদি পশু ও স্বর্ণ সম্পদ লুণ্ঠন করেন। বিজিত বন্দি শত্রুদের দাস ও দস্যু বলে অভিহিত করে আর্য দেবতার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাও উল্লিখিত, তবু শত্রুর শক্তিকে প্রায়ই ‘মায়া’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইন্দ্রের বীরত্ব ছাড়াও আর্যপক্ষের জয়কে যা নিশ্চিত করেছে তা হল বজ্ৰ।
এর ঠিক পরেই রয়েছে আনন্দ অভিব্যক্তির মন্ত্র। যাযাবর আক্রমণকারীরা বসতি বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজনে ভূমি অধিকারের জন্য নির্মম ও নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। আক্রমণকারীদের ক্রোধ উদ্রেক করার জন্য আদিম অধিবাসীরা যদিও কোনও অপরাধই করেনি এবং নিজেদের গোষ্ঠী ও বসতিকে রক্ষা করার জন্যই তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, তবু তারাই পাপ ও অমঙ্গলের প্রতীক বর্বর জাতিরূপে অকারণে নিন্দিত। কিন্তু যুগে যুগে অনিবার্য ভাবেই আক্রমণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি এ রকমই হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত যুদ্ধগীতিগুলিতে ইন্দ্র ও তাঁর সহায়কদের সম্পর্কে অসংখ্য গৌরবসূচক বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং অন্য দিকে অনার্যজাতি মাত্রকেই অন্ত্যজ ও ঘৃণ্যরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইন্দ্রের বজ্রই সম্ভবত ভারতবর্ষে ব্যবহৃত প্রথম লৌহ-নির্মিত অস্ত্র। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের কাছে এই ধাতুটি ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত; প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন, মোটামুটি ভাবে খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে তা সম্ভবত প্রথম ব্যবহৃত হয়।
সংলাপসূক্ত বা সংবাদসূক্ত
ঋগ্বেদে প্রায় কুড়িটি সংলাপ সূক্ত বা সংবাদ-সূক্ত রয়েছে; যদিও এগুলিতে প্রকৃত সংলাপের মতোই প্রকাশরীতি রয়েছে, তবু বক্তাদের নাম উল্লিখিত নেই বলে প্রকরণ থেকেই সেগুলি অনুমান করে নিতে হয়। অনেকগুলি সূক্ত পড়ে মনে হয় যেন সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এও মনে হয় যেন প্রচলিত পাঠ থেকে ব্যাখ্যামূলক গদ্য অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বহু গবেষক এই সব সূক্তের মৌলিক স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা রকম অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত করেছেন। এদের খণ্ডিত অবস্থা বিচার করে কেউ কেউ এদের আখ্যান বা গীতিকা-ধর্মী সূক্ত রূপে চিহ্নিত করেছেন। এঁদের মতে, শুধুমাত্র শ্লোকাংশই স্মৃতিতে গ্রহিত করা হত বলেই ব্যাখ্যামূলক ও সংযোজক গদ্য অংশগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে, প্রতিটি অনুষ্ঠানেই গদ্যাংশগুলি নূতন করে পরিমার্জিত হত, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি প্রকৃতপক্ষে সেই সব বিলুপ্ত অংশ-সমূহের সম্পূরণ করত। সিলভ্যা লেভি জানিয়েছেন যে, সংবাদ-সূক্তগুলি নাটকেরই বিশিষ্ট একটি ধরন। এই সব সূক্তের প্রকৃত চরিত্র বা মৌলিক উদ্দেশ্য নির্ণয় করার মতো কোনও উপায় আমাদের নেই, তবে যজ্ঞীয় বিনিয়োগের অনুপস্থিতি থেকে পণ্ডিতরা নানাবিধ অনুমান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সাধারণ ভাবে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি যদিও প্রথাগত ভাবে কবির নাম, ছন্দ ও দেবতার নাম এবং যজ্ঞীয় বিনিয়োগের নির্দেশ দিয়ে থাকে, সংবাদ-সূক্তগুলি কিন্তু সে দিক থেকে প্রচলিত নিয়মের অন্যতম ব্যতিক্রম। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কোনও কোনও পণ্ডিত বলেছেন যে সংবাদ-সূক্তগুলি সম্ভবত সমাজ-মানসে ভাসমান গীতিকা-র অংশ ছিল, যে সব উপাদান পরবর্তিকালে বিভিন্ন মহাকাব্য, পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য এবং এমনকী ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের নাটকগুলিতেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে তা প্রকৃতই সংবাদ-সূক্তের কোনও সহগামী গদ্য অংশ ছিল কিনা, নিশ্চিত ভাবে এখন বলা সম্ভব নয়। তৎকালীন শ্রোতার কাছে এই প্রকাশারীতিই সম্ভবত পর্যাপ্ত ছিল, কেননা উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ প্রত্নকথা ও উপাখ্যান যেমন শ্রোতৃ-সমাজের কাছে পরিচিত ছিল তেমনই সর্বজনসম্মত প্রকাশরীতি ও উপযুক্ত স্বরন্যাস ও ইঙ্গিতপূর্ণ প্রত্যক্ষ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সম্ভবত শ্রোতা ও দর্শকের কাছে অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করত।
সংবাদ-সূক্তগুলির মধ্যে ঊর্বশী ও পুরূরবার সংলাপই (১০:৯৫) সর্বাধিক পরিচিত। রাজা পুরূরবার অপ্সরা-বধূ ঊর্বশী চার বছর তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। পুরূরবা ঊর্বশীকে তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে অন্বেষণ করে শেষ পর্যন্ত একটি সরোবরে অন্য অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত হংসীরূপে দেখতে পেলেন। রাজা ঊর্বশীকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আকুল অনুরোধ করে ব্যর্থ হলেন। ঊর্বশী দৃঢ় ভাবে পুরূরবাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। দুজনের সংলাপ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী: এক দিকে রয়েছে বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় কাতর মর্ত মানুষের আর্তি ও আকৃতি, অন্য দিকে আছে অপ্সরার স্পষ্ট হৃদয়হীন ঔদাসীন্য। এর সঙ্গে তুলনীয় ব্যাবিলনের গিল্গামেশ মহাকাব্যের সেই সংলাপমূলক অংশটি যেখানে দেবী ইস্টার মরণশীল গিলগামেশকে তাঁর প্রণয়ী হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন, কিন্তু মর্ত নায়ক দেবীর প্রণয় প্রত্যাখ্যান করছেন।
এই বিষয়বস্তুর সামান্য ভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি ঘটেছে আর একটি সংবাদসূক্ত— যমযমী সূক্ততে। (১০:১০) পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত সৃষ্টিবিষয়ক প্রত্নকথাগুলির সঙ্গেই এই সূক্তের আত্মীয়তা, কেননা এই ধরনের রচনায় এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় যে, মনুষ্যসৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে ভ্রাতা ও ভগিনীর মিলনের ফলেই মানবজাতির প্রথম সৃষ্টি। পরবর্তী সমাজে অজাচার নিষিদ্ধ হওয়ার পরে স্বাভাবিক ভাবে অবাধ যৌনতার উপর যে নিষেধ আরোপিত হয়, সম্ভবত তারই ফল হিসাবে আলোচ্য সংবাদসূক্তের উপসংহারটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সূক্তটি আকস্মিক ভাবে সমাপ্ত হয়। এ ছাড়া বৃষাকপিসূক্তে (১০:৮৬) ইন্দ্রাণী, ইন্দ্র ও তার পোষ্য বৃষাকপির মধ্যে একটি কৌতূহল-ব্যঞ্জক সংলাপ দেখা যায়। বৃষাকপি অর্থাৎ হনুমানের প্রতি ইন্দ্রের মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় ইন্দ্রাণী মেনে নিতে পারছেন না। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত ও পরবর্তিকালে সবিশেষ জনপ্রিয় হনুমান-উপাসনা পদ্ধতির প্রতি প্রথম ইঙ্গিতরূপে এই সূক্তটিকে গ্রহণ করা যায়। বৈদিক যুগের ইন্দ্র-চর্চাকে যে সমস্ত লোকচর্যা পরবর্তিকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হনুমান-উপাসনার সূত্রপাত, বৈদিক যুগের অনার্য সংস্কৃতিতে। অন্যান্য সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্দ্র, বসুক্র ও তাঁর স্ত্রীর সংলাপ (১০:২৮), অগ্নি ও দেবতাদের সংলাপ (১০:৫১-৫৩), ইন্দ্র ও মরুতের সংলাপ (১০:৬৫), ইন্দ্র ও অগস্ত্যের সংলাপ (১:১৭০), অগস্ত্য, তাঁর শিষ্য ও অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার সংলাপ (১:১৭৯); আরও একটি বিখ্যাত সংলাপ হয়েছে সরমা ও পণিদের মধ্যে। (১০:১০৮)
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অধিকাংশ সংবাদসূক্তই রয়েছে সংহিতার অন্তিম পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম ও দশম মণ্ডলে। কারণ সম্ভবত এই যে, সৃষ্টিশীলতার পর্যায় সমাপ্ত হওয়ার পরে যখন সংকলন ও সম্পাদনার প্রক্রিয়া চলছিল তখন জনপ্রিয় গীতিকাগুলিরও আহরণ করা হচ্ছিল। সম্ভবত যজ্ঞীয় বিনিয়োগ না থাকায় এই সব গীতিকা পূর্বে সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
দানস্তুতিসুক্ত
অন্য যে ধরনের সূক্ত বা সূক্তাংশ ঋগ্বেদে অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়, তা দানস্তুতি। এই শব্দটি বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। অতএব বৃহদ্দেবতা রচিত হওয়ার পূর্বেই দানস্তুতিগুলি বহুপরিচিত হয়ে ছিল; এটা সহজেই বোঝা যায়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত অনুক্রমনী গ্রন্থ দানস্তুতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে— ‘রাজ্ঞাঞ্চ দানস্তুতয়ঃ’। (২:২৩) অর্থাৎ এগুলি রাজাদের দানের স্তুতি। প্রকৃতপক্ষে নামটি অসার্থক, কেননা এই সব সূক্ত সরাসরি দানকর্মকে প্রশংসা করে না; বরং তার স্তুতির লক্ষ্য প্রাচীনকালের সেই সব দাতা রাজাদের দান, যাঁরা তাঁদের যজ্ঞ-নির্বাহক পুরোহিতদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিতেন। সমসাময়িক পৃষ্ঠপোষকরা যাতে পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্ররোচিত হন, এই জন্য প্রাচীনকালে প্রদত্ত দানসামগ্রীর আনুপুঙ্খিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ এই সব দানস্তুতিতে রয়েছে। কোনও দানস্তুতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ সূক্ত নয়; কোনও দেবতার মহিমা বিবৃত করার জন্য প্রচলিত প্রার্থনা ও প্রশস্তিসহ রচিত একটি সাধারণ সূক্তের পরিপূরক রূপে এই শ্রেণির কয়েকটি ঋক্ এই সূক্তগুলিতে সংযোজিত হয়েছে। কোনও এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে এই জাতীয় সুক্ত আকস্মিক ভাবে প্রাচীনকালের কোনও সম্পৎশালী দাতার বদান্যতার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। অনিবার্য ভাবেই এই সব সূক্তের দানস্তুতি অংশটি সাহিত্যের বিচারে নিম্নমানের ও দীন, স্পষ্টতই এই অংশের রচয়িতাও ভিন্ন। সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের শ্লোক আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না, অথচ পূর্বদাতাদের দানের প্রশংসা সমকালীন রাজাকে অনুরূপ দানে ও দক্ষিণায় অনুপ্রেরিত করবে বলেই পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত কোনও সূক্তে তাদের সংলগ্ন করে রাখতে হত।
বালখিল্যসূক্ত
অষ্টম মণ্ডলের সমাপ্তি-অংশ, ৪৯–৫৯ সূক্ততে তথাকথিত বালখিল্যসূক্তগুলি ঋগ্বেদের সমগ্র সম্পূরক বিভাগের সর্বাধিক পরিচিত অংশরূপে পরিগণিত। স্পষ্টতই এই সূক্তগুলি মিশ্র রচনার প্রমাণ নিয়ে পরবর্তিকালে সংযোজিত হয়েছিল এবং এ জন্যই এরা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সায়ণ এই সূক্তগুলির কোনও ভাষ্য রচনা করেননি। আটটি সূক্তের মধ্যে যে পুনরাবৃত্তি দেখা যায় সে সম্পর্কে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৬:২৮) এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (৩০:৪) সচেতন ছিল। অধিকাংশ সূক্তই ইন্দ্রের উদ্দেশে নিবেদিত; কিছু কিছু সূক্ত অগ্নি, সূর্য, বরুণ ও অশ্বীদেরও আহ্বান করেছে।
খিলসূক্ত
আপাতদৃষ্টিতে বহু পরবর্তী সম্পূরক সূক্তসমূহের আরও একটি গুচ্ছ সংহিতার শেষ ভাগে সংস্থাপিত হয়ে খিলসূক্ত রূপে পরিচিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে নিবিদ্, পুরোরুচ্, প্রৈষ এবং কুত্তাপ-সূক্ত— একত্রে এই সমগ্র সম্পূরক অংশ ঋক্-পরিশিষ্ট রূপে বিখ্যাত। শৌনকের রচনারূপে প্রচারিত আর্যানুক্রমণী ও অনুবাকাক্রমণী গ্রন্থেই ‘খিল’ নামটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। যাস্ক খিল থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করলেও তিনি তাদের ‘নিগম’ বলেই উল্লেখ করেছেন। স্পষ্টতই অনেক দেরিতে সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলেই খিলসূক্তের চরিত্রে বিষমতা দেখা গেছে; সংহিতার মূল ধারায় গৃহীত হওয়ার পরিবর্তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে সম্পূরক অংশে। তবে এই বিলম্বিত অন্তর্ভুক্তি কিন্তু তাদের রচনাকালকে প্রতিফলিত করেনি, কেননা এই সব সূক্তের বেশ কয়েকটি মন্ত্রই সংহিতার প্রধান ভাগের চেয়েও প্রাচীনতর। খিলসূক্তগুলি যে পরবর্তিকালে সঙ্কলিত হয়েছে তার আরও একটি প্রমাণ হল মূল ঋগ্বেদ থেকে এগুলিতে শ্বাসাঘাতের চিহ্নের পার্থক্য।
বাস্কল শাখার পাঠে খিলসূক্তগুলিকে ঋগ্বেদের অংশরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল বলেই মনে হয়; যদিও এদের অধিকাংশই শাকল পাঠের পূর্ববর্তী। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, খুব সম্ভবত খিলসূক্তগুলি ঋগ্বেদে সংহিতার সামান্য পরবর্তী। তবে সাম্প্রতিক রচনার সমকালীন বত্রিশটি সূক্তের মধ্যে সব খিলসূক্তগুলি হয়তো একই পর্যায়ে রচিত হয়নি। এই সব সম্পূরক সূক্তের মধ্যে প্রয়োগ যৎসামান্য; কখনও কখনও যদিও বা সংযোগসূত্র দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষীণ। এদের বিষয়বস্তুতে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য— যেমন স্বস্তিবচন, বিবাহ-অঙ্গীকার, অভিশাপ, জাদুবিদ্যা, স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা, ধীশক্তিবর্ধনের কামনা, সপত্নীদলন, গবাদি পশুর কল্যাণ এবং উত্তম সঙ্কল্প; এরা প্রায়শই খণ্ডিত, কখনও কখনও গূঢ়ার্থবহ এবং সংহিতার মূল অংশ থেকে প্রায়ই কিছু কিছু শ্লোক ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা বলে বিষয়গত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। খিলসূক্তগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হল লক্ষ্মীসূক্ত ও শিবসঙ্কল্পসূক্ত দুটি।
অন্যান্য সূক্তাবলি
পুরোরুচ্, নিবিদ ও পৈষন সূক্তগুলি সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর পর্যায়ে রচিত হয়েছিল কিন্তু বালখিল্য, মহানাম্নী এবং কুন্তাপ-সূক্তগুলি স্পষ্টতই পরবর্তিকালের রচনা। এগারোটি গদ্যসূক্তসম্বলিত নিবিদ্ অংশে বিভিন্ন দেবতা কিংবা একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য স্তুত হয়েছে; এই অংশই ঋগ্বেদীয় কালের প্রাচীনতম গদ্য এবং নিশ্চিত ভাবেই প্রচলিত ঋগ্বেদসংহিতার চেয়ে প্রাচীনতর। এই নিবিদ সূক্তগুলির অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত, বিশুদ্ধ জাদুবৈশিষ্ট্যযুক্ত কয়েকটি মাত্র অক্ষরে বিধৃত সম্মোহনমন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রই এই সব নিবিদের ছন্দোবদ্ধ রূপ। খুব সম্ভবত প্রৈষ অংশ ঋগ্বেদের সমাপ্তি পর্বের রচনা; আপ্রীসূক্তগুলির মতো এখানেও অগ্নিকে বহু নামে বন্দনা করা হয়েছে। কুন্তাপ অংশে রয়েছে বিচিত্র চরিত্রের বারোটি সূক্ত। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে মানব প্রশংসা এবং কামনা ও উর্বরতা- -সূচক গীতি, তেমনই রয়েছে দুর্বোধ্য বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রলাপ। এটি আপাতদৃষ্টিতে অপরিমার্জিত যৌনকামনার তাৎপর্যযুক্ত সূক্ত যার সঙ্গে তৎকালীন কোনও উর্বরতাচর্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়।
নিবিদ্
হ্রস্ব-কলেবর নিবিদ মন্ত্রগুলি আদিতে গদ্যে রচিত হয়েছিল বলে যে অনুমান করা হয় তার কারণ, এগুলি সাধারণ ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলির মতো ছন্দোবদ্ধ রচনা নয়, তবু এদের মধ্যে অদ্ভুত তাল ও লয়ের প্রবাহ রয়েছে। কোনও কোনও গবেষকের মতে ঋগ্বেদে নিবিগুলি প্রয়োগিক কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। অবেস্তা গ্রন্থে আমরা ‘নিবেদয়েম্’ শব্দটি পেয়েছি, কিন্তু সেখানে তার অর্থ আলাদা। ব্রাহ্মণগ্রন্থ অনুযায়ী নিবিসূক্তে সেই সব দেবতাদের আহ্বান করা হয় যাঁরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে সোমযাগে হবি গ্রহণ করেন। নিবিক্তে কোনও শ্বাসাঘাত নেই এবং উচ্চাবচতাহীন সুরে অর্থাৎ একশ্রুতির মধ্য দিয়ে এদের আবৃত্তি করা হয়, সম্ভবত এ ধরনের উচ্চারণে এদের ঐন্দ্রজালিক গাম্ভীর্য বর্ধিত হয়। নিবিদের মধ্যে মাত্র একজন পুরোহিত অর্থাৎ হোতাই উল্লিখিত হয়েছেন। আহুতির মধ্যে সোমকে উপাদানরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে, দেবতারূপে নয়। এতে নিবিদের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত, অর্থাৎ সোম দেবত্বে উপনীত হওয়ার পূর্বেই নিবিগুলি রচিত হয়েছিল। সম্ভবত যাযাবর আর্যজাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আদিম পর্যায়ের যজ্ঞে এগুলি প্রযুক্ত হত। তাছাড়া ভাষা বিশ্লেষণ করে নিবিগুলির বিশেষ প্রাচীনতা, এমনকী ইন্দো-ইয়োরোপীয় পর্যায়ের নিকটবর্তী অবস্থানই প্রমাণ করা যায়। প্রাথমিক স্তরে নিবিদ্ সংক্ষিপ্ত ঐন্দ্রজালিক সূত্ররূপে থাকলেও ক্রমশ এগুলিকে কেন্দ্ৰ করে দীর্ঘ প্রার্থনা সূক্ত রচিত হতে থাকে। সম্ভবত বৈদিক যুগে অসংখ্য নিবিদ্ প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের কালে এর সমস্ত অংশ এসে পৌঁছয়নি।
আপ্রীসূক্ত
মোট দশটি আপ্রীসূক্তর প্রত্যেটিরই পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপ্রী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— সকলের মনোরঞ্জনকারী (আ = সমন্তাৎ, প্রীণয়ন্তি ইতি আপ্রী)। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী বিভিন্ন বৈদিক শাখার আপ্রীসূক্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন। যজ্ঞে আহুতি অর্পণের পূর্বে আপ্রীসূক্তগুলি গীত বা আবৃত্ত হয়। আপ্রীসূক্তগুলির বিষয়বস্তু ও চরিত্র-লক্ষণের মধ্যে প্রীতিদায়ক ভাবটি পরিস্ফুট। যজ্ঞানুষ্ঠানের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা অগ্নির প্রীতি উৎপাদনের জন্য তার বিভিন্ন নাম ঘোষণা করে প্রশংসা করা হয়েছে: সমিদ্ধ, ই তনূনপাৎ, নারাশংস, ইল, দেবীদ্বারঃ, বা দ্বারো দেব্যঃ, ঊষাসানক্তা, দেব্যৌ হোতরৌ এবং হব্যবহ। মৌখিক সাহিত্য রচনার যুগে কবিরা শব্দের স্বল্পতার জন্য সচেষ্ট থাকতেন; তাই দেবতার বিভিন্নমুখী দক্ষতাকে প্রশংসা করার প্রয়োজনে পূর্বোক্ত বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হত। আপ্রীসূক্তগুলি যজ্ঞের প্রাচীনতম ধারা অর্থাৎ পশুযাগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল; স্পষ্টতই এগুলি প্রাচীনতর যুগের রচনা, তখনও পশুপালন-নির্ভর যাযাবর সমাজে অঞ্চলগত ভাবে গোষ্ঠী ও পরিবারের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সেই জন্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক নীতিকে কঠোর ভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা হত।
সোমমণ্ডল
ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলই সোমদেবতার প্রতি নিবেদিত। এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সম্পাদনার প্রক্রিয়া অনেক বিলম্বে ঘটেছিল; পূর্ববর্তী মণ্ডলগুলি থেকে একজন নির্দিষ্ট দেবতা অর্থাৎ সোমের প্রতি নিবেদিত সূক্তসমূহ একটি পৃথক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট করার মধ্যেই এ-প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল। এই সম্পাদনা কর্মের পশ্চাৎপটে সক্রিয় অনুপ্রেরণার সন্ধান করতে গিয়ে আমরা এই বিশেষ তথ্যের সম্মুখীন হই যে, বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রীয় ও সর্বাত্মক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে সোমযাগ ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সোমদেবের মধ্যে রাজধর্ম প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছিল; এই রাজধর্মের মধ্য দিয়েই একজন ক্ষত্রিয় সোমদেবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতেন। রাজপদে সোমের উন্নয়ন সোমচর্যার গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। অভিষেকের সময় সোমদেবকেই ব্রাহ্মণদের রাজারূপে বর্ণনা করা হয়; এতেও তাঁর আধিপত্য ও আনুষঙ্গিক জাদুশক্তি প্রমাণিত।
সন্দেহ নেই যে, সোমরসের মধ্যে যে মাদকতাময়, উল্লাসজনক ও ভ্রম-উৎপাদক বৈশিষ্ট্য ছিল, তারই ফলে যজ্ঞানুষ্ঠানে এর গুরুত্ব ক্রমশ বর্ধিত হয়। দীর্ঘায়ু লাভের জন্যও এই পানীয় ব্যবহার করা হত। ঋগ্বেদের সোমের মতোই অবেস্তার ‘হওম’, যা স্বর্গ থেকে উচ্চ পর্বতে একটি বিপুলকায় পক্ষী দ্বারা আনীত হয়েছিল। ব্যাবিলনীয় প্রত্নকথাতেও রয়েছে, সূর্যদেব শামসের নিকট পবিত্ররূপে গৃহীত ও দীর্ঘায়ুপ্রদ একটি জাদুকরী লতা পর্বতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি সাধারণ ভাবে পবমান সোম অর্থাৎ পশমের চালুনির মধ্যে দিয়ে ছেঁকে-নেওয়া সোমরসের প্রতি নিবেদিত। শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় রস ‘দ্রোণ’-কলস-এ রক্ষিত হওয়ার সময়ে যে ধ্বনি নির্গত হত পানকারীদের কানে তা অতি মধুর ঠেকত। ঋগ্বেদীয় প্রত্নকথা অনুযায়ী সোম মূলত দৈব সম্পদ; পক্ষী দ্বারা পৃথিবীতে আনীত হয়ে তা পার্বত্য অঞ্চলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বহুবিধ বাস্তব, আনুষ্ঠানিক ও প্রতীকী বিঘ্ন অতিক্রম করে সেই সোম সংগ্রহ করতে হত। সোমলতা থেকে নিষ্কাশিত রসের সঙ্গে নানা রকম দুগ্ধজাত দ্রব্য, মধু ও ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত করে তার মাদক-শক্তি বর্ধিত করা হত। আনুষ্ঠানিক ভাবে সোমরস প্রস্তুতির সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন সূক্তে বারেবারে বিবৃত হয়েছে। এমনকী প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন পাত্র, কলস, হাতা, পেষণ-প্রস্তর (শিল-নোড়া), ছাঁকনি, প্রভৃতিও উল্লিখিত ও প্রংশসিত হয়েছে।
সোমযাগ সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী; সমস্ত বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে দীর্ঘতম হল ‘সত্র’, এটি একাদিক্রমে দ্বাদশ বর্ষ ধরে অনুষ্ঠিত হত। কিছুকাল পরে চারজন পুরোহিত সম্বলিত একদিবসীয় যজ্ঞও এতই সম্প্রসারিত হল যে, যজ্ঞনির্বাহক পুরোহিতদের সংখ্যা এবং আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খ অনেক বেড়ে গেল; বস্তুত সোমযাগ যজ্ঞশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত যজ্ঞের সরল কাঠামোয় সম্ভ্রম-উৎপাদক উপাদান, ইন্দ্রজাল ও রহস্য নিরন্তর সংযোজিত হয়ে চলেছিল। পরে সোমযাগের অনুষ্ঠানগত তাৎপর্য বিশেষ ভাবে বর্ধিত হয়ে যখন তার নিজস্ব অতীন্দ্রিয় রূপকর্ম গড়ে উঠল এবং সংহিতার পূর্বতন অংশ থেকে যখন নবম মণ্ডল পৃথক হয়ে গেল তখন বহু সংখ্যায় রচিত ও পরিমার্জিত হয়ে সোমগীতি প্রভূত ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক তাৎপর্যবহ সূক্তসমূহে সন্নিবেশিত হল।
প্রাথমিক পর্যায়ে সোম পার্থিব উদ্ভিজ্জ; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দৈব সত্তায় উন্নীত এবং রাজা, সম্রাট ও ব্রাহ্মণদের অধিপতিরূপে অভিহিত। লক্ষণীয় যে, তৎকালীন ভারতবর্ষে রাজকীয় পদবি যখন প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দৃঢ় রূপ পরিগ্রহ করছিল, সে সময়েই রাজার সঙ্গে প্রতীকী ভাবে সোমের সমীকরণ ঘটে এবং এর দ্বারা তার গুরুত্বও বহুগুণ বেড়ে যায়। এতে আনুষ্ঠানিক ও ঐন্দ্রজালিক তাৎপর্য যেমন কালক্রমে সমন্বিত হয়েছে, তেমনই আনুষ্ঠানিক পানীয় ও দেবতার মধ্যে ব্যবধানও ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া, সোমের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক যেহেতু ঘনিষ্ঠ, নবম মণ্ডলের অনেক মন্ত্র প্রাথমিক ভাবে সোমসম্বন্ধীয় হয়েও ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
নবম মণ্ডলের প্রধান কবিরা— কাণ্ব, ভৃগু ও অঙ্গিরা— পুরোহিত-পরিবারের সদস্য; এঁরা যথাক্রমে আট, বারো ও তেইশটি সূক্ত রচনা করেছিলেন। এঁরা এবং অন্যান্য কবিরা সোমকে লতা, দেবতা ও আকাশবিহারী চন্দ্ররূপে বন্দনা করেছেন। সমস্ত বৈদিক ছন্দই এই মণ্ডলে ব্যবহৃত হয়েছে; তবে মোট সূক্তের অর্ধেকেরও বেশি রচিত হয়েছে গায়ত্রী ছন্দে। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অধিকাংশ সোমসূক্ত আমাদের হতাশ করে; কাব্যগত ভাবে স্পষ্টতই এগুলি নিম্নমানের রচনা। এই মণ্ডলের বেশ কিছু সূক্ত অন্যান্য প্রাচীন কাব্যে প্রচলিত মদ্যপান-গীতির মতো; পানীয় ও তজ্জাত মাদকতার অবস্থা এ সব রচনায় বর্ণিত হয়েছে। অতিদীর্ঘায়িত ও পুনরাবৃত্তিময় যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে এদের নিবিড় সম্পর্ক স্পষ্ট; প্রসঙ্গ থেকে শ্লোকগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও কাব্যিক সৌন্দর্য প্রায় কোথাওই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মণ্ডলের শেষ সূক্তটি একটি চমৎকার ব্যতিক্রম।
সর্বেশ্বরবাদ: সংশয় ও প্রত্যয়
সামগ্রিক বিচারে ঋগ্বেদ নিশ্চিত ভাবেই সর্বেশ্বরবাদী। তবু, অন্তিম পর্যায়ের রচনায় পুরনো বিশ্বাসের কিছু কিছু চিহ্ন এমনকী একেশ্বরবাদের প্রতি সুস্পষ্ট ঝোঁকও কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের এত দিনকার তর্কাতীত প্রাধান্য এখন আর বিনা বাক্যে গ্রহণীয় নয়। পারিবারিক মণ্ডলগুলির একটি সূক্ত (২:১২)-তে যুদ্ধবিজয়ী ও অলৌকিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে ইন্দ্র স্পষ্ট ভাবে বন্দিত হয়েছেন, তবু তার মধ্যেও কয়েকটি মন্ত্রে যেন সংশয়ের ছায়াও ফুটে উঠেছে। পরবর্তী একটি সূক্ত (৮:১০০)-তে সংশয়ের ছায়া আরও স্পষ্ট ও ঘনীভূত। অবশ্য সংশয়ের এই তীক্ষ্ণ সুরকে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে দেওয়া হয়নি; দেবতা এখানে যেন স্বয়ং যজমানকে নিজ গৌরবের কথা জানিয়ে আশ্বস্ত করেছেন, অবিশ্বাসীর সন্দেহ দূর করে তাঁর প্রতি আস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।
ইন্দ্ৰ বা অন্যান্য দেবতার অস্তিত্ব বা পরিচয় সম্পর্কে সরাসরি অবিশ্বাস প্রকাশ না করেও হয়তো বা এই সব মন্ত্র যথার্থই সংশয় ব্যক্ত করেছিল। ঋগ্বেদের আদিপর্বেই মানুষ প্রশ্ন করছে ‘কে জানে কে দেখেছে’: অর্থাৎ সংশয় ও প্রত্যয় একই যুগে দেখা দিয়েছে। বহু সংখ্যক দেবতা সম্ভবত সাধারণ মানুষের পক্ষে বিভ্রান্তিজনক বলে প্রতিভাত হয়েছিল এবং যাঁরা চিন্তা বা বিশ্বাসের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মনেও এই বিশাল দেব-সঙ্ঘের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সাহসী ও স্পষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল। বৈদিক ধর্মীয় ভাবনার ইতিহাসের কোনও এক অজ্ঞাত সন্ধিক্ষণে সর্বেশ্বরবাদ সম্পর্কিত সংশয় একেশ্বরবাদী প্রবণতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ধীর কিন্তু নিশ্চিত ভাবে সহায়তা করেছিল; এই প্রক্রিয়ায় অস্পষ্টতা ও প্রচুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ছিল, প্রাথমিক ভাবে যে বিশুদ্ধ প্রত্নপৌরাণিক একেশ্বরবাদের জন্ম হয়েছিল তাতে দেবতাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব অন্তরালে রয়ে গিয়েছিল। একটা দেশজ অনার্য প্রভাব কিংবা আর্য ধর্মীয় চিন্তার দ্বন্দ্ব নিরসনের মধ্য দিয়ে অথবা, কোনও আকস্মিক সামাজিক বিপ্লবের ফলে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল। আবার এও হতে পারে যে, পূর্বোক্ত উপাদানগুলি এক সঙ্গে এমন এক নব্য প্রবণতায় শক্তি জুগিয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদে পরিণত হয়। উৎস যাই হোক না কেন, সংহিতা-রচনার শেষ পর্বে আমরা একেশ্বরবাদের স্পষ্ট লক্ষণ যথার্থই দেখতে পাই।
একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা
সর্বেশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে রূপান্তর কোনও ক্রমবিবর্তনের ফলে ঘটেনি। ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা একেশ্বরবাদী চিন্তাকে দৃঢ়প্রোথিত অবস্থায় দেখতে পাই। অবশ্য অনত্র্যও এমন কথা পাই যাতে মনে হয় অস্পষ্ট ভাবে হলেও একেশ্বরবাদের দিকে ঋষিদের প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। কিছু কিছু নূতন দেবনাম প্রবর্তিত হয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতার পদবিতে উন্নীত হয়েছে এবং বিমূর্ত সৃষ্টিতত্ত্বরূপে গৃহীত হয়েছে। এই সংশয়ের তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আমরা স্মরণে রাখি যে প্রচলিত ধর্মীয় বাতাবরণ প্রত্নকথা ও অনুষ্ঠান-চর্যার উপর নির্ভরশীল ছিল। সেই সময়ে কোনও পথসন্ধানী একেশ্বরবাদীর পক্ষে প্রত্নকথা ও রহস্য-নিষ্ণাত পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা অত্যন্ত কঠিন; তাই কিছু কিছু বহুদেববাদী ও প্রত্ন-পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান একেশ্বরবাদী ভাবনার সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছিল।
যদিও ঋগ্বেদের সমস্ত প্রধান দেবতাকেই কোথাও না কোথাও সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সংহিতার শেষ পর্যায়ে জগৎ স্রষ্টা রূপে সম্পূর্ণ নূতন কয়েকটি দেবনাম প্রবর্তিত হয়: প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মণস্পতি, পুরুষ ও পরমাত্মা এর উদাহরণ। কোনও কোনও সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গেই তাদের সম্পর্কিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হল ভাবসূক্ত (১০:১৯০), নাসদীয় সূক্ত (১০:১২৯) এবং অস্যবামীয় সূক্ত। (১:১৬৪) অধিকাংশ অধ্যাত্মবিদ্যা ও সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক সূক্তে অতীন্দ্রিয়বাদী উপাদান স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়; এর কারণ হিসাবে আমরা আদিম দার্শনিকের দৃষ্টিতে দুর্জ্ঞেয়তার অভিব্যক্তি এবং বিষয়বস্তুর নিজস্ব অন্তর্নিহিত রহস্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই সব রহস্যময় অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির ব্যাখ্যা প্রকৃত তাৎপর্য করতে পরবর্তী ভাষ্যগুলি সর্বদা সমর্থ হয়নি।
সৃষ্টিরত পরমেশ্বরকে সাধারণত ধ্যানরত যোগী রূপে কল্পনা করা হয়, পরবর্তী বৈদিক সমাজের ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি যে দেখা দিয়েছে, তার একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। এমনকী দিকসমূহ এবং যে সমস্ত দেবতার সঙ্গে নিদানবিদ্যাবিষয়ক প্রত্নকথা সম্পৃক্ত, তাঁদের উত্তানপাদ যোগী রূপে বর্ণনা হয়েছে। সেই সঙ্গে সৃজন-প্রক্রিয়ায় নিরত স্রষ্টা দেবতাদের ‘তপস্’-এর উল্লেখ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে ‘স্রষ্টা যোগী’ একটি নূতন সামাজিক ধারণা রূপে বৈদিক সাহিত্যের শেষ অংশে দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ধ্যানমগ্ন দেবতার মূর্তির কথা আমাদের মনে পড়বে। সম্ভবত যোগী দেবতার এই আদিমতম রূপটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল রচিত হওয়ার সময়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় ধর্মীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছিল।
নাসদীয় সূক্ত (১০:১২৯)-তে অসৎ বা অনস্তিত্ব থেকে সৎ বা অস্তিত্বের সৃষ্টি কল্পনা। কবি তাঁর কল্পনাকে মহাসময়ের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যখন সৃষ্টির সূচনাও হয়নি। অনস্তিত্বের আদিতম অন্ধকার এবং সময় ও পরিসরের সার্বিক শূন্যতা তাঁর কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবি-দৃষ্টির এই উদ্ভাসনেই সূক্তটির গৌরব নিহিত। আধ্যাত্মিক ভাবনা এতে অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল। প্রজাপতি মাত্র চারবার উল্লিখিত হয়েছেন, যদিও পরবর্তী সাহিত্যে তাঁকে শক্তিমান স্রষ্টার ভূমিকায় দেখা গেছে। স্রষ্টারূপে তিনি কালের প্রতীক; অন্য দিকে সর্বাতিগ আকাশ দেবতারূপে পরিকল্পিত মহাপরিসরের মানবায়িত রূপ আমরা বৃহস্পতির মধ্যে দেখতে পাই। আবার ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, বৃহস্পতি, প্রমুখ প্রধান দেবতাদের বিশ্বস্রষ্টার ভূমিকায় বিমূর্তায়িত প্রকাশ লক্ষ্য করি বিশ্বকর্মার মধ্যে। এছাড়া, হিরণ্যগর্ভ স্বর্ণোজ্জ্বল অন্ত বা সৃষ্টি আদিকণিকারূপে জগৎপ্রক্রিয়ার একটি বিশেষ স্তরের প্রতিভূ।
যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে দর্শনে উত্তরণের স্তরের প্রামান্য রচনা হল পুরুষসূক্ত। (১০:৯০) এই সূক্তে পুরুষ স্রষ্টারূপে প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করেননি; দেবতারা তাঁকে যজ্ঞে হব্যরূপে অর্পণ করেছিলেন; তাঁর সেই বলিপ্রদত্ত শরীর থেকে ক্রমে ক্রমে সমগ্র সৃষ্টি উদ্ভূত হয়েছিল। অধিবিদ্যার স্তরে পুরুষসূক্ত যজ্ঞের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির চূড়ান্ত প্রতীকী বিবরণ দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানকে মৌলিক আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে ভূষিত করেছে, যা আরণ্যক ও উপনিষদের স্তর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সূক্তের ষোড়শ মন্ত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য, কেননা, সেখানে পুরুষের মুখ, বাহু, ঊরু ও চরণ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চার বর্ণের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র ঋগ্বেদে এটাই একমাত্র নিদর্শন যেখানে সামাজিক শ্রেণিভেদের ইঙ্গিত-সহ চতুবর্ণ উল্লিখিত, যদিও ‘বর্ণ” শব্দটি এখানে উচ্চারিত হয়নি।
অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্-বিরচিত পরতাত্ম-সূক্ত (১০:১২৫) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এখানেই প্রথম এক নারী কবি সমস্ত দেবতার সঙ্গে আপন সত্তার একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী বহু ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে একাত্মতা ঘোষিত হয়েছে তার প্রথম উচ্চারণ যেন এই নারী কবিটির রচনায়। উপনিষদ ও বেদান্তে অভিব্যক্ত দার্শনিক ভাবনার উৎস রূপে একে গ্রহণ করা যায়। রচয়িতা বাক্ যেহেতু নারী এবং তিনি উত্তম পুরুষের বাচনিকভঙ্গিতে নিজের সঙ্গে দেবসঙ্ঘ ও বিশ্বজাগতিক তাবৎ উপাদানকে একাত্মীভূত করে কাব্য প্রণয়ন করেছেন, তাই এই সূক্তকে পরমাত্মার সমতুল্য আদ্যাশক্তির প্রতি নিবেদিত প্রথম স্তোত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়। পরবর্তিকালে তাই এর জনপ্রিয় নামান্তর হল দেবীসূক্ত।
উপাখ্যান ও প্রহেলিকা
এই সব সূক্তে ক্রমাগত কিছু প্রহেলিকাধর্মী অংশ পাওয়া যায় এখনও যাদের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। এটাই বিস্ময়জনক যে, সাধারণ ভাবে ধর্মীয় কাব্য বলে পরিচিত বৈদিক সংহিতায় এ জাতীয় প্রহেলিকা সন্নিবিষ্ট, এমনকী সংরক্ষিত হয়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে, সত্রের মতো দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হয়ে পড়ত, সেই একঘেয়েমির অবসাদ দূর করার জন্য পুরোহিতরা হয়তো এই সমস্ত প্রহেলিকা ও নানা উপাখ্যান বিবৃত করতেন। হয়তো বা বৈদিক জনসাধারণের মগ্ন স্মৃতিতে এই সব প্রহেলিকার কোনও গূঢ় বা অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য প্রোথিত ছিল; কিন্তু পরবর্তিকালে তা সময়ের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আদিম মানুষের কাছে সৃষ্টির মতো রহস্যোদ্দীপক আর কিছুই ছিল না; তাই সৃষ্টিবিষয়ক একটি সূক্তের মধ্যে যে আলোচ্য প্রহেলিকাগুলি সংরক্ষিত হয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কখনও কখনও প্রহেলিকার আপাত কিছু সমাধান দেওয়া হয়েছে; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রকৃত উত্তর অদীক্ষিতদের কাছ থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে।
সূর্যাসূক্ত
অনন্য বিষয়গৌরবের জন্য কিছু কিছু সূক্ত আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। মোট সাতচল্লিশটি মন্ত্রসূক্ত (১০:৮৫) রূপে পরিচিত বিবাহ সূক্তটি বেশ আগ্রহোদ্দীপক। যদিও এতে মূলত সবিতৃকন্যা সূর্যার পতিগৃহে যাত্রার বর্ণনা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত তা বিবাহ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আশীর্বাদ ও মাঙ্গলিক আচার এবং তৎসহ ঐন্দ্রজালিক ও আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খসমূহের প্রামাণিক বিবৃতিপূর্ণ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের একটি আদর্শ বিবাহ-সূক্তে পর্যবসিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে সাধারণত শীত-প্রধান অঞ্চলেই সূর্য নারী বা দেবী রূপে কল্পিত, যেমন প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের দেবী আরিন্না। জার্মান ভাষায়ও সূর্য স্ত্রীলিঙ্গ। আলোচ্য সূক্তে সূর্যাকে বধূরূপে পাওয়ার জন্য দেবতারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সূর্যার পিতা তাঁকে তাঁর প্রেমিক সোমদেবের কাছে অর্পণ করতে উদ্যত ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অশ্বীরা রথে করে তাঁকে হয়তো সোমের কাছেই নিয়ে যান। সূক্তের শেষ ভাগে নবদম্পতির জীবনকে নির্বিঘ্ন করার জন্য অশুভ জাদুশক্তি ও অধিদৈবিক আধি-ব্যাধিকে মন্ত্রবলে বিতাড়িত করার কথা পাই। সবশেষে রয়েছে বিখ্যাত আশীর্বাণী: বধূ যেন শ্বশুরালয়ে সম্রাজ্ঞী হতে পারে।
দ্যূতকরের অনুশোচনা
বিখ্যাত অক্ষসূক্ত (১০:৩৪) অর্থাৎ পাশা খেলোয়াড়ের মর্মন্তুদ স্বগতোক্তির এই সূত্রটি সম্পূর্ণই ভিন্ন ধরনের এক রচনা। পাশা খেলার প্রলোভন দুর্নিবার, অন্তহীন তার আমোদ, সোমরস পানের মতো যা উল্লাসজনক ও মানুষের চিত্তকে অধিকার করে সম্মোহিত রাখার জাদুশক্তি যাতে নিহিত, সেই পাশা খেলার প্রশস্তি দিয়েই এই সূক্তটির সূচনা। কিন্তু তার পরই দ্যূতাসক্ত ব্যক্তির মর্মান্তিক করুণ অবস্থা, তার পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় অত্যন্ত সংযত ভাষায় বর্ণনা করেছেন কবি। সূক্তের সমাপ্তিতে পরিস্ফুট হয়েছে অনুশোচনা এবং অন্য দ্যুতকরের প্রতি উপদেশ, যাতে তারা পাশার মারাত্মক আকর্ষণ প্রতিরোধ করে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকার্যে নিরত হয়।
যমসংহিতা
যমসংহিতা বলে পরিচিত সূক্তগুচ্ছে রয়েছে অন্ত্যেষ্টিবিষয়ক মন্ত্রসমূহ। এগুলি যদিও দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত তবু শুধু এই তথ্য দিয়ে এদের অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত হবে না। কেননা মৃত্যু ও প্রখ্যাত পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান ও প্রত্নকথা ছাড়া কোনও প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বই সম্পূর্ণই অকল্পনীয়। আলোচ্য অন্ত্যেষ্টিসূক্তগুলিতে যম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অগ্নি এবং পিতৃগণ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছেন। বিচিত্র ধরনের আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি এদের মধ্যে অভিব্যক্ত হলেও অপরিচয়ের স্বাভাবিক অবিশ্বাসজনিত মৃত্যুভীতিই এতে সবচেয়ে মৌলিক। ইহজীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই ভয় দূরীকরণের পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়, তাই প্রাচীন মানুষ বিচিত্র আবেগের দ্বারা আলোড়িত হত; মৃতমানুষেরা এক সময় জীবিতের প্রিয় পরিজন ছিল, অতএব অচিরেই তাদের জীবিত মানুষের পক্ষে অনিষ্টকারী হয়ে ওঠার আশঙ্কা নেই, তবুও অতৃপ্ত সুখতৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রসন্ন আত্মাকেও হয়তো বা ভীতিপ্রদ করে তুলতে পারে, এমন বিশ্বাস ছিল, এবং উপযুক্ত অর্ঘ্য নিবেদন করে সে আতঙ্কিত সম্ভাবনাকে ঠেকাবার চেষ্টা করা হত। জীবিতদের মধ্যে প্রথম যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন, সেই যম নিশ্চয়ই বিদেহী প্রিয়জনকে মরণোত্তর কোনও জগতে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং অঙ্গিরা, মাতলি ও ভৃগুর সাহচর্যে আমোদ-প্রমোদে কালযাপনে সাহায্য করবেন। মৃত আত্মীয়ের মরণোত্তর ভবিষ্যৎ জীবিতদের কাছে অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়; তাই যাতে প্রিয় পরিজন পরলোকে সুখেস্বাচ্ছন্দে ও আনন্দে থাকে এই ঐকান্তিক কামনা ও তাদের মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠা ও আকুতি এই সূক্তগুলিকে একটি করুণতায় মণ্ডিত করেছে। এইখানেই এদের কাব্যমূল্য। অন্তেষ্টিক্রিয়ার বিষয়ে এই সব সূক্তের সঙ্গে তুলনীয় রচনা অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়।
মণ্ডূকসূক্ত
‘সংবাদ সূক্ত’গুলির মতো মণ্ডূকসূক্ত বা ভেকগীতির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে; কারও মতে এটি বৃষ্টির আবাহন, বর্ষণের জন্য ভাবগম্ভীর একটি জাদুগীতি, আবার কারও মতে এতে রয়েছে বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সম্বন্ধে একটি অন্তর্লীন ব্যঙ্গ। প্রথম মন্ত্রে সম্ভবত এই দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে।
রাত্রিসূক্ত ও অরাণ্যানীসূক্ত
প্রাচীন ভারতীয়দের অরণ্যবেষ্টিত বসতিতে ঘনকৃষ্ণ রাত্রি যে রহস্য ও ভীতি সঞ্চার করত, তারই সজীব অভিব্যক্তি ঘটেছে রাত্রিসূক্ত (১০:১২৭)-তে। অন্ধকারের শক্তি যেহেতু অনতিক্রম্য, কবি তাই রাত্রির কাছে রাত্রিকালীন বিভিন্ন বিপদ— নেকড়ে বাঘ, চোর-ডাকাত ও আকস্মিক মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। আদিম মানুষ যখন মূলত প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল, অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় যখন সে নিরন্তর কম্পমান থাকত, তখনকার উদ্বেগের সুন্দর প্রতিফলন রয়ে গেছে এই সূক্তে।
অরণ্যানীর প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্ত (১০:১৪৭)-টিও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এর সঙ্গে তুলনীয়। নূতন আর্য বসতিগুলির চতুষ্পার্শ্বের নিবিড় অরণ্য ছিল একই সঙ্গে জীবনধারণের উৎস ও বহুবিধ সমাধানহীন রহস্যের আকর। এই সূক্তেও বৈদিক কবির কল্পনাশক্তি ও বর্ণনাচাতুর্য স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে।
ঋগ্বেদ: লোকায়ত না ধর্মসাহিত্য?
ঋগ্বেদের চরিত্র সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে বাদানুবাদ চলে আসছে: উৎপত্তি ও অন্তর্বস্তুর বিচারে তা ধর্মসাহিত্য না লোকায়ত গ্রন্থ? কোনও কোনও কবি তাঁদের রচিত সূক্তে যজ্ঞের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রায়ই সংহিতা-পাঠের সঙ্গে যজ্ঞীয় বিনিয়োগের সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। স্পষ্টতই এই সব সূক্তের যজ্ঞীয় বিনিয়োগ পরবর্তিকালে যান্ত্রিক ভাবে পর্যালোচনাপ্রসূত পুনর্ভাবনার ফলে ঘটেছিল। লুই হ্রেনু তাঁর একটি গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ‘প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বেদে লোকায়ত কাব্য রয়েছে। যথার্থ বিচারে অবশ্য এ রকম নিদর্শন পাওয়া যায় না; শুধু কিছু কিছু লোকায়ত বিষয়বস্তু, গান, ধ্রুবপদ ও কৌতুককর আখ্যানকে ধর্মীয় উদেশ্যে বিশেষ ধরনে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বেদের সমস্ত কিছুই ধর্মীয় বিধিরই অধীন। এর লক্ষ্য দ্বিবিধ: এক দিকে পর্যাপ্ত অলঙ্কৃত ভাষায় দেবতার স্তুতি এবং অন্য দিকে পুরোহিতের ক্রিয়াকলাপের পার্থিব দাবিসমূহ পরিপূর্ণ করা।’ অর্থাৎ বিভিন্ন সূক্তে মাঝে মাঝে লোকায়ত বিষয় প্রবর্তিত হলেও ঋগ্বেদ মূলত ধর্মীয় সাহিত্য।
বস্তুত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাচীন সাহিত্যরূপে আমাদের কাছে যা কিছু এসে পৌঁছেছে তার অধিকাংশই নিছক শিল্পবোধপ্ৰণোদিত সৃষ্টি নয়, বরং সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবনের আয়তনের মধ্যে এদের একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগিক দিক ছিল। তাদের যথোপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত করে, শুধু সাহিত্যরীতি হিসাবে বিচার না করে, বিশেষ অভিব্যক্তি রূপেই গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত সংহিতার যে যজ্ঞীয় বিনিয়োগ পাওয়া যায় তা সায়ণ কর্তৃক ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র থেকে সঙ্কলিত হয়েছিল। কারও মতে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে এবং ভারতীয় আর্যদের নিরাপত্তা ও বিজয় বিধানের জন্য দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক সূক্তগুলি থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে রচিত হয়েছিল; পরবর্তিকালে সূক্তগুলির উপযোগিতা ব্যাপকতর করার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রই কেবলমাত্র সংহিতায় পাওয়া যায়; এতে প্রমাণিত হয় যে, যজ্ঞে এদের প্রয়োগ ছিল না। এই বাদানুবাদকে আমরা তিনটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি; যেমন ঋগ্বেদে (১) প্রাথমিক ভাবেই যজ্ঞীয় আচার-বিধিমূলক, (২) এটি ধর্মসাহিত্য অর্থাৎ দেবকল্পনার বিবরণ, (৩) এটি লোকায়ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সাহিত্য।
সংহিতাপাঠের প্রমাণ থেকে সম্ভবত নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অধিকাংশ সূক্তই দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনারূপেই রচিত এবং সমস্ত সংহিতাটি প্রাথমিক ভাবেই একটি স্তোত্র-সংগ্রহ। ধর্মনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ লোকায়ত রচনা প্রাচীন মানুষের পক্ষে অকল্পনীয়, যেহেতু তাদের বিশ্ববীক্ষা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক ও অনুষ্ঠাননির্ভর এবং তাদের জগৎ রহস্য-নিয়ন্ত্রিত। ঋগ্বেদের সূক্ত শুধুমাত্র দেবতার প্রশস্তিবাচক গান নয়, কোনও রাজকীয় শাসককে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনে রচিত বিশেষ ধরনের কাব্য, সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী ও ঐতিহ্যনিয়ন্ত্রিত বিশেষ শৈলীতে সেই কাব্য রচিত হত। যজ্ঞীয় বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কহীন মন্ত্র যেমন রচিত হয়েছিল, তেমনই বিনিয়োগসূক্তর কিছু কিছু মন্ত্র সম্ভবত রচনা-মুহূর্তে কোনও যজ্ঞের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল না। কাব্যসৌন্দর্য বা রচনাশক্তির জন্যই পরবর্তিকালে এগুলি যজ্ঞের অংশ হয়ে পড়ে।
নিরুক্তে প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কিছু কিছু মন্ত্র নিরর্থক অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে তাৎপর্যহীন। আরও কিছু মন্ত্রের যজ্ঞীয় উপযোগিতা সম্পর্কে সায়ণ বলেছেন, অনুষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী মন্ত্রগুলি প্রযোজ্য। যজ্ঞ যখনই প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতি অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সর্বজনগ্রাহ্য উপায় হয়ে উঠল, সম্ভবত তখন থেকেই আনুষ্ঠানিক বিনিয়োগের প্রয়োজনে বিভিন্ন সূক্তের রচনায় নূতন একটি পর্যায়ের সূচনা হল, অর্থাৎ বিশুদ্ধ যজ্ঞেরই উদ্দেশ্যে সূক্ত রচিত হতে শুরু হল। অবশ্য, বিশ্লেষণে দেখা যায় এ
জাতীয় সূক্তের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বিবিধ লক্ষ্যযুক্ত মন্ত্র রচনার বিভিন্ন স্তরগুলি আমরা হয়তো কতকটা নির্ধারণ করতে পারি। সম্ভবত প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ প্রেরণায় কিছু কিছু সূক্ত রচিত হয়েছিল, যদিও এখনকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবীক্ষা প্রাচীন মানুষের ছিল না। বলা চলে সেগুলি ছিল নিতান্তই অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কোনও প্রকাশ্য অভিব্যক্তি ছিল না। পরবর্তিকালে যজ্ঞানুষ্ঠান যখন অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করল তখন স্পষ্ট আনুষ্ঠানিক প্রযোজনে সূক্ত রচনার সূত্রপাত হল; সেই খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য কবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল। অনুমান করা যায় যে, রাজকীয় পরিবারগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারণকবিরা লোভনীয় পুরস্কারের আশায় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। প্রতিযোগিতার আবেগ-মথিত উদ্যমে চারণকবিদের পরিবারে যে মৌলিক কাব্যপ্রক্রিয়ার স্ফুরণ ঘটেছিল পণ্ডিতরা তাকে “চারণকবিদের পর্যায়’ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।
কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন, সুসমৃদ্ধ রাজন্যবর্গের তুষ্টির জন্য অধিকাংশ সূক্তই পরস্পর প্রতিস্পর্ধী চারণকবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত খুব একটা যুক্তিসংগত নয়। আর্যদের ইতিহাসে আদিম ইয়োরোপীয়, প্রথম বাসভূমি থেকে বেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ইরান হয়ে এ দেশে এসে পৌঁছে এখানকার আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করা, তাদের বাসভূমি দখল করে বসবাস, প্রাগার্য ঐশ্বর্য লুণ্ঠন ও ক্রমে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার অভ্যাস, রাজ্যবিস্তার ও সমৃদ্ধিলাভ— এই দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমার ইতিহাসের বহু স্মরণীয় অধ্যায় নানা বংশের নানা কবির প্রেরণায় সূক্তরূপে ব্যক্ত ও রচিত হয়েছিল। স্থানে কালে তার ব্যাপ্তি যেমন সুদূরপ্রসারিত, তেমনই উদ্দেশ্যে ও সিদ্ধিতে বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। সম্ভবত বহু সূক্তই আক্রমণকারী আর্যদের যাযাবর জীবনেই গ্রথিত হয়েছিল। যদিও অধিকাংশ মন্ত্র ভারতভূমিতে আর্যবসতি স্থাপিত হওয়ার পরই রচিত, তবুও তাদের মধ্যে অনিশ্চিত বাতাবরণের একটা দ্যোতনা রয়ে গেছে। রাজন্যদের সন্তুষ্টিবিধানের প্রয়াস সম্পর্কে বহু মন্ত্রই প্রত্যক্ষ কোনও ইঙ্গিত বহন করে না, যদিও পরবর্তী সূক্তগুলিতে তেমন অনেক দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পেয়েছি। সূক্ত রচনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অভিমত অনুযায়ী প্রথম পর্যায় ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, দ্বিতীয়টি নিশ্চিত ভাবে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানমূলক এবং তৃতীয়টি মৌল প্রেরণাগত বিচারে ধর্মনিরপেক্ষ, দর্শন-অভিমুখী।
ঋগ্বেদের ভাষা
সাধারণ বিচারে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত ভাষা সর্বত্র সমান নয়; সতর্ক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, জাতিগত ও ভাষাগত সংমিশ্রণ এবং বহু শতাব্দীব্যাপী রচনা, গ্রন্থনা, সম্পাদনা ও আঞ্চলিক বৈষম্যের ফলে ভাষা প্রয়োগে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা দিয়েছে। শৈলী ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে কতকটা কৃত্রিম ভাবেই সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে, তাতে শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত বৈচিত্র্য ও কথ্য ভাষার উপযোগী ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যকে নূতন তাৎপর্যে অন্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত শব্দ নির্বাচনের দিকটিও পরিস্ফুট হয়েছে। বৈদিক সংস্কৃত ভাষা তৎকালীন উপভাষাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় একটি বিশেষ কথ্যভাষাকে অধিক গুরুত্ব দিলেও বিভিন্ন উৎস থেকে যে উপাদান সংগ্রহ করছিল, তার বহু চিহ্নই ঋগ্বেদের মধ্যে রয়ে গেছে। ঋগ্বেদের ভাষা মূলত কবিদের সচেতন প্রয়াসে নির্মিত একটি সাহিত্যিক ভাষা— কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর বা কোনও অঞ্চলের কথ্যভাষার সম্পূর্ণ অনুগামী নয়। তখনকার চারণকবিদের কাছে এই ভাষাটিই আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছিল। যখন বৈদিক সংস্কৃত কথ্যভাষা রূপে প্রচলিত ছিল, সেই সুদূর অতীতেই প্রাক্-পালি এক প্রাকৃত ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। সামাজিক অবচেতনায় তার নিগূঢ় প্রভাবের সঙ্গে বিভিন্ন উপভাষার সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গভীর সংযোগের ফলে ধীরে ধীরে বৈদিক চারণকবিদের কথ্যভাষা গড়ে ওঠে। বৈদিক ভাষা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সেই প্রত্নরূপ যা পরবর্তী নব্য আর্যভাষাগুলির জন্ম দিয়েছে। ভারতীয় আর্যগণ যখন এ দেশে এসেছিলেন ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা-ভাণ্ডারের উত্তরাধিকার ছাড়াও তাঁরা দীর্ঘ পথ অতিবাহনের ফলে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত শব্দাবলি সংগ্রহ করতে করতে এসেছিলেন। পরবর্তিকালে প্রাচীন ব্যাবিলন ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে তাঁদের ভাষার কিছু কিছু বিদেশি শব্দের প্রভাবও দেখা গিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব ভাষা যেমন বিবর্তিত হয়েছিল তেমনই ভারতীয় অনার্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক ও দৈনন্দিন নানান আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে স্থানীয় ভাষাও গঠনমূলক প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু তাই নয়, অবৈদিক আর্যভাষার শব্দও যে ঋগ্বেদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, এমন অনুমানেরও যথেষ্ট হেতু আছে।
অধিকাংশ শব্দ কৃষি-সভ্যতার দৈনন্দিন জীবন থেকেই ঋণ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, কেননা গ্রামনিবাসী আর্যদের পক্ষে নাগরিক জীবনের কোনও অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব ছিল না। ভারতভূমিতে যখন ঋগ্বেদের সূক্তসমূহ রচিত হচ্ছিল, অস্ট্রিক এবং হয়তো অল্প কিছু দ্রাবিড় উৎসজাত শব্দ তখনই আর্য শব্দ-ভাণ্ডারে প্রবেশ করে। যেহেতু ঋগ্বেদের সূক্তগুলি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং বহু শতাব্দী ধরে রচিত ও সঙ্কলিত হয়েছিল, সে কারণে বৈদিক ভাষা শব্দ-ভাণ্ডারে অনেকগুলি কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল; কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কোনও নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর কথ্যভাষার পরিধির মধ্যে তা কখনওই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংহিতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষিত হয়, কেননা অনেক শব্দ, বিশিষ্ট বাক্যাংশ বা বাগ্বিধির গুচ্ছ ও বাচনিক সঙ্কেতসূত্রকে প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে উত্তরাধিকার রূপে আহরণ করে বৈদিক কবি বিভিন্ন সময়ে শূন্যস্থান পূরণের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট ভাষা সঙ্কেতরূপে প্রয়োগ করেছিলেন; অথচ তত দিনে এই সব বাচনিক উপাদান দৈনন্দিন ব্যবহারের অভাবে অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।
ঋক্সংহিতা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার পদান্বয়রীতি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন, যেহেতু কাব্যরচনায় কখনও নির্দিষ্ট পদান্বয় রীতি অনুসৃত হয় না। তাছাড়া, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় গদ্য পদ্য নির্বিশেষে বাক্যের অর্থ পদক্রমের ওপর নির্ভরশীল নয়। সংহিতা যেহেতু মৌখিক সাহিত্য বা শ্রুতিকাব্য, ছন্দ ও শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য সেখানে তর্কাতীত এবং পদান্বয়ে তাদের ভূমিকাই নির্ধারক। বস্তুত, যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের গদ্যভাষার সঙ্গে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা বৈদিক ভাষার পদান্বয়-রীতি সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণাই অর্জন করতে পারি না। সাধারণ গদ্য ভাষায় বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হলেও পদ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; কেননা ছন্দ ও শ্বাসাঘাতের নিজস্ব প্রয়োজনে বিশেষণ বাক্যের যে-কোনও স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে। অক্ষরজ্ঞান আবিষ্কৃত হওয়ার পূববর্তী পর্যায়ে ভাষা যখন বিভিন্ন প্রজন্মের দ্বারা কেবলমাত্র মৌখিক ভাবেই সংরক্ষিত হত, তখন শব্দব্যবহারে চূড়ান্ত মিতব্যয়িতা ও তজ্জনিত সংহতি এবং সংক্ষেপীকরণ অনিবার্য ছিল। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে এই অনুমান করতে পারি যে, সংহিতায় প্রযুক্ত বিশেষণগুলি সম্পূর্ণ যথাযথ, অপরিহার্য ও অ-পরিবর্তন সহ-ই কবির পরিকল্পিত ভাবনার অনুগামী সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম অভিব্যক্তিরই নিদর্শন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেবতাদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষণসমূহ তাঁদের প্রত্নপৌরাণিক কার্যকলাপ বা প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিতবহ। হোমারের ইলিয়াড ও অডিসিতেও বিশেষ প্রয়োগের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; অবেস্তাতেও তাই। প্রাক্-লিখন যুগে শব্দব্যবহারের অপরিহার্য একটি লক্ষণ হল যে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কোনও শব্দই প্রযুক্ত হত না; অতএব প্রত্যেকটি শব্দই সুপ্রযুক্ত এবং কবির একান্ত অভীষ্ট। ব্যতিক্রম শুধু কিছু কিছু পাদপূরণার্থক অব্যয়, যেগুলি ছন্দের অনুরোধে ব্যবহৃত। তাই ইন্দ্রকে যখন পুরন্দর বা বৃত্রহা বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে, তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আর্য সেনাপতি ইন্দ্ৰ কর্তৃক প্রাগার্য বসতিগুলির প্রাচীরসমূহ চূর্ণ করার ইঙ্গিত বা অনার্য কোনও প্রবল পরাক্রান্ত গোষ্ঠীপতিকে হত্যার আভাস। আবার তাঁকে যখন অংহোমুক বা পাপক্ষালনকারী কিংবা ওজস্বৎ বা শক্তিশালী অভিধায় বর্ণনা করা হচ্ছে, তখন এই জাতীয় নিহিত বিশেষণে বিশেষ বিশেষ প্রত্নবিশ্বাসের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।
বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, সংহিতার ভাষার অধিকাংশেই সাংস্কৃতিক সমরূপতার প্রবণতা বিদ্যমান। তাই এই সাহিত্য এমন করে বহু বিশিষ্ট সর্বজনীন অভিজ্ঞতার সামূহিক প্রত্নস্মৃতির অমেয় ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। ‘বৃত্রাতুর্থ’-র মতো বিশেষণ-প্রয়োগ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে মন্ত্রের শ্রোতা আর্যদের প্রাচীন সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত, অর্থাৎ সে জানে ওই বিশেষণের মধ্যে ইন্দ্রের বৃত্রধরের কাহিনির একটি অধ্যায় বিধৃত আছে। সামুহিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ অতীত বৃত্তান্তগুলির প্রতি তর্জনিসঙ্কেত করে বলেই এই ধরনের বিশেষণ জাতি-গোষ্ঠী-বহির্ভূত ব্যক্তির কাছে অর্থাৎ আর্যসংস্কৃতির পরিমণ্ডলের বাইরের ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ও অর্থহীন প্রতিভাত হবে। পরবর্তী ধ্রুপদী সংস্কৃতের তুলনায় সংহিতায় ব্যবহৃত সমাসগুলি সবলতর, প্রায় কখনওই দুয়ের বেশি শব্দ সমাসবদ্ধ হয়নি এবং সমাস সত্যই সংক্ষেপকরণের এবং সুখশ্রুতির জন্যেই ব্যবহৃত। মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যে যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তিই প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাই সেখানে সমাস-ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বিরল। সংক্ষিপ্ততা, পরিচ্ছন্নতা ও যথার্থতা— অর্থাৎ যে সমস্ত গুণ শ্রুতিকাব্যের পক্ষে অপরিহার্য, বিশেষত পরবর্তী অলংকার সাহিত্য যাকে ওজঃ ও প্রসাদ গুণ বলেছে, সেটাই এর বৈশিষ্ট্য। সমাস-প্রয়োগে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় গাঢ়তা ও বহুমুখী ব্যঞ্জনা। যেমন— ইন্দ্র হচ্ছেন শতক্রতু ও পুরন্দর; সৌরদেবতারা হিরণ্যবাহু; মিত্র ও বরুণকে বলা হচ্ছে ঋতাবৃধা; অগ্নিকে জাতবেদা, গৃহপতি ও রত্নধাতম, পুরুষকে সহস্রশিরাঃ, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাৎ, নারী অরণ্যানী, অঞ্জনগন্ধী, বৃহন্না ও অকৃষীবলা। গ্রিক প্রত্নকথায় পাচ্ছি একই ধরনের দেবনামগত বিশেষণ (যথা আপোল্লো লুকোকটোনোস, স্মিনথিওস, পার্নোপিওস ও নোমিওস কিংবা জিউস অ্যালেক্সিকাকোস, এফেস্টিওস, প্যামেলিওস ও অ্যাগারাইয়োস, ইত্যাদি)। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ভাষায় যে সমৃদ্ধি দেখা যায়, মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগত কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তিতেই তার উৎস।
ধ্বনিগত বা রূপগত দিক দিয়ে বৈদিক ভাষা অনড় স্থানুপদার্থ নয়; বহতা নদীর মতো নিজস্ব গতিতে সেই ভাষা ক্রমশ বিবর্তিত ও সরলীকৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত যে ধ্রুপদী সংস্কৃতের সমীপবর্তী হয়েছে তার বিভিন্ন পর্যায় ঋসংহিতার মধ্যেই স্পষ্ট। প্রাচীনতর পর্যায়ে বৈদিক ভাষায় ব্যাকরণগত বৈচিত্র্য ও বিকল্পের সংখ্যা যে অনেক বেশি, তার কারণ সম্ভবত এই যে, বহু কৌম ও জনগোষ্ঠী উপভাষাগুলির সংমিশ্রণে গঠিত একটি সর্বজনবোধ্য বাচনিক কাঠামোকে ভিত্তি করেই ঋক্সংহিতা রচিত। প্রতি গোষ্ঠীরই একটা নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র শব্দভাণ্ডার ছিল; সর্বজনীন রূপটি কালের নিয়মে বিবর্তিত হলেও কিছু কিছু অংশ আবার সেই নিয়মকে অস্বীকার করেই প্রাচীন বাগ্বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে ব্যবহৃত ভাষা তাই স্বভাবতই পূর্ববর্তী মণ্ডলগুলির তুলনায় অনেকাংশে ভিন্নপথগামী হয়ে পড়েছে। প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্যের অধিকাংশই খ্রিস্টপূর্ব একাদশ ও দশম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। সূক্তসমূহের ভাষা বিশ্লেষণ করে যেহেতু প্রাকৃত ভাষাগুলি থেকে ঋণগ্রহণের বহু দৃষ্টান্ত প্রমাণ করা যায়, তা থেকে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় যে, কোনও এক সময়ে সাধারণ জনতার ভাষা ও আনুষ্ঠানিক সাহিত্যের ভাষার মধ্যে কোনও একান্ত বা অলঙ্ঘ্য বিচ্ছেদের প্রাচীর বিদ্যমান ছিল না। কাব্যের প্রয়োজনে প্রচলিত বাচনিক কাঠামোকে কখনও কখনও কৃত্রিম ভাবে পরিমার্জিত করার ফলেই ঋগ্বেদের ভাষা তার নিজস্ব পরিশীলিত অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। ঋগ্বেদ সংহিতা যখন সম্পূর্ণ ভাবে দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াসের ফলে সংকলিত হল, তার মধ্যে রয়ে গেল প্রাচীন অলৌকিক আখ্যানের ভগ্নাবশেষ, মহাকাব্যের লক্ষণযুক্ত স্তর যা পরবর্তিকালে কখনও পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যে পরিণত হল না, এবং সেই সঙ্গে রইল জাদুরীতি ও কিছু বিরল গীতিকবিতার অংশ। ঋক্সংহিতা বহু শতাব্দীব্যাপী এমন এক ধরনের প্রয়াসের ফসল যার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তির অবকাশ খুব কমই ছিল; অভিজাত ও যুদ্ধনিপুণ সভ্যতা সুসংগঠিত ও বিবিধ শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যে বিশেষ সাংস্কৃতিক মননের পরিবেশ রচনা করেছিল ঋক্সংহিতা তারও ফল বটে। বহু প্রজন্মের চেষ্টায় যে সৃষ্টি গড়ে উঠেছে তাতে চিত্রধর্মিতার চেয়ে নানা বর্ণের প্রস্তরখচিত কারুকার্যই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে বেশি। এই সাহিত্যে পরিশ্রমসাধ্য যান্ত্রিক পরিশীলনের অভিব্যক্তি আছে বলেই কোনও কোনও সমালোচকের মতে তাতে সুখী ও ধর্মভীরু আদিম সমাজের কোনও যথার্থ প্রতিফলন নেই। যে নগর-সভ্যতাগুলিতে লিখনপদ্ধতি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, সাধারণ ভাবে ইন্দো-ইয়োরোপীয় জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ ভাবে বৈদিক আর্যরা এই পরিধির বাইরে থাকায় এক দিকে যেমন এদের মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, অন্য দিকে তেমনই গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানেরও প্রচলন হয়েছিল। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মৌখিক সাহিত্য ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল, তারই অনিবার্য ফল হিসাবে যে কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার বাতাবরণ ও রক্ষণশীলতার প্রবণতা দেখা দেয় তাতেই বৈদিক ভাষা বিদ্বৎসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে দৈনন্দিন কথ্য ভাষা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
মৌখিক সাহিত্যরূপে ঋগ্বেদ
প্রাচীনতম মৌখিক সাহিত্যের নিদর্শনগুলির মধ্যে যে সমস্ত রচনা পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষিত হয়েছিল, ঋগ্বেদসংহিতা তাদের অন্যতম। হোমারের দুটি মহাকাব্য এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ঋগ্বেদ গড়ে উঠেছে গীতিকবিতা, গীতিকা ও সূক্তের সংকলনরপে এবং মহাকাব্যের পূর্ববর্তী মৌখিক কবিতার রূপ ও চরিত্র অনুশীলনের একটি বিরল সুযোগ আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। মৌখিক কাব্যের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ে প্রশস্তি ও স্তুতিগানের সরল পদ্ধতিরূপে ছন্দোরীতির উৎপত্তি হয়েছিল; কালের গতিতে ছন্দের জটিলতা ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই ‘গায়ত্রী’ (গান করা অর্থে ‘গৈ’ ধাতু থেকে উদ্ভুত ছন্দের নাম) নামের মধ্যে রয়েছে গানের অনুষঙ্গ, তেমনই ‘প্রগাথ’ কথাটির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে গীত। স্তভ্-ধাতু নিষ্পন্ন ‘ত্রিষ্টুভ্’ ও ‘অনুষ্টুভে’র মধ্যে রয়েছে প্রশস্তির দ্যোতনা, কেননা এই দুটি নামের তাৎপর্য যথাক্রমে ‘তিনবার স্তুতি’ ও ‘পরবর্তী স্তুতি’। লক্ষণীয় যে, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্ ও অনুষ্টুভ্ প্রাচীনতম ছন্দরূপে পরিগণিত।
পৃথিবীর প্রাচীনতম মৌখিক রচনারূপে ঋগ্বেদ আমাদের সামনে এমন কিছু লক্ষণ তুলে ধরেছে যা অক্ষর বা লেখা আবিষ্কারের পরবর্তী সাহিত্যের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। যুগোস্লাভিয়ার মৌখিক মহাকাব্য সম্পর্কে অসামান্য গবেষণা করে বিদগ্ধ সমালোচক মিলম্যান প্যারি ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র-সহকর্মী এ বি লর্ড কাব্যের মৌখিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং হোমার ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনার আলোচনায় সেই সব সিদ্ধান্ত সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্যের লিখিত রূপে প্রত্যেকটি শব্দই মৌলিক এককরূপে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু মৌখিক ভাবে রচিত সাহিত্যে সাধারণত শব্দগুচ্ছই মূল ও ন্যূনতম উপাদান। কখনও কখনও মৌখিক সাহিত্যেও একক শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু রচনার প্রধান প্রবণতা সে দিকে থাকে না। সুদূর অতীতের প্রাচীন কবিরা যে সব শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে গেছেন, পরবর্তী কবিদের দ্বারা তা অক্ষয় উত্তরাধিকাররূপে সাদরে নিরন্তর গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। লেখা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বকালে বারংবার ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ স্মৃতিতে ধারণ করার পক্ষে যেমন সহজতর তেমনই নির্দিষ্ট ছন্দোগত কাঠামোয় সংস্থাপিত করার পক্ষেও সহজসাধ্য। মৌখিক সাহিত্যের চারণকবি যেহেতু বিচিত্র ধরনের ঐতিহ্যগত কাঠামোর সীমার মধ্যে কাব্যরচনা করতেন, তাই ভাষাগত অনুপুঙ্খের সাধারণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজস্ব রীতিতে কাব্যভাষাকে প্রয়োজন মতো নমনীয়তা-যুক্ত করতেও কোনও বাধা ছিল না। এ কারণে, মৌখিক ঐতিহ্যের কবি একই সঙ্গে স্বাধীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। ঋগ্বেদের পুনরাবৃত্ত অংশগুলিকে গভীর ভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলে মৌখিক কাব্যের নানা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মন্ত্রের সূচনায় ও সমাপ্তিতে কখনও সম্পূর্ণ চরণ, কখনও বা বাক্যাংশ পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এ ছাড়াও পুনরাবৃত্তির সূক্ষ্মতর কিছু পদ্ধতিও রয়েছে— চরণের মাঝামাঝি পুনরাবৃত্তি, পরবর্তী স্তবকের সূচনায়ও পূর্ববর্তী স্তবকের শেষাংশের পুনরাবৃত্তি, কোনও স্তবকের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দের বারংবার আবৃত্তি, সুপরিচিত, প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় চরণ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি, ইত্যাদি। এই জাতীয় বাচনিক পদ্ধতির মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট কবি কখনও বা কবি-পরিবারের নিজস্ব ঘরানার ছাপও স্পষ্ট ভাবে রয়ে গেছে। অধিকাংশ সূক্তই যেহেতু যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় সমবেত জনতা কিংবা পুরোহিত ও তাঁর সহকারীদের দ্বারা গীত হত, তাই কোনও একটি চরণকে ধ্রুবপদ রূপে বারবার আবৃত্তি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে কোনও চরণ পুনরাবৃত্ত হওয়ার পিছনে সম্ভবত এই বিশ্বাস সক্রিয় ছিল যে, এই সমস্ত চরণে ঐন্দ্রজালিক শক্তি নিহিত রয়েছে।
পুনরাবৃত্ত চরণে আর্যদের প্রার্থনার গুরুত্ব প্রতিফলিত; আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সঙ্কট থেকে রক্ষিত হওয়ার জন্য দেবতার প্রসন্ন অভিব্যক্তি যে তাঁদের প্রার্থিত, তা বোঝানোর জন্য এবং সেই সঙ্গে অন্তর্নিহিত জাদুকরী শক্তি উদ্বোধনের জন্য মন্ত্রের নির্দিষ্ট কোনও অংশ বারবার আবৃত্তি করা হত। কখনও কখনও একাধিক দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে একটি চরণ অনুরূপ ভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এতে যে অতিজাগতিক শক্তির স্ফুরণ প্রত্যাশিত ছিল, খুব কম ক্ষেত্রেই তা শুধুমাত্র নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; খুব সম্ভবত ঐন্দ্রজালিক শক্তি উদ্রেকের জন্যে এক প্রত্যয় কবি ও তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর অবচেতন মনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করত। সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম পর্বে বিশেষ ভাবেই শব্দের মধ্যে নিহিত এক অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল কবি মনীষীর ক্ষমতা আছে এই শক্তিকে মন্ত্রের দ্বারা সমষ্টি বা ব্যষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করার। এ বিশ্বাস সব প্রাচীন সমাজেই ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান ছিল। আবার কোনও স্তবকে যখন একটিমাত্র শব্দ বহুবার পুনরুক্ত হত, তখন তা যেন তার নিজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করে সেই স্তবকে বিধৃত ভাব-বিন্যাসের তীক্ষ্ণ একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠত। ফলে সেই স্তবকের অন্য শব্দগুলি তুলনামূলক ভাবে গৌণ হয়ে বাক্যের পশ্চাৎপটে অপসারিত হত। তা ছাড়া, পুনরুক্ত শব্দটি শ্রোতার মনে এমন মোহময় বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি করত যাতে সেই শব্দাশ্রিত ভাবনা মনে সুদৃঢ় ভাবে নিবিষ্ট হয়ে অন্য সমস্ত চিন্তাকে গৌণ ও নিষ্প্রভ করে দেয়। সংক্ষেপে বলা যায়, এই রচনা-পদ্ধতি এমন সম্মোহনকারী শাব্দিক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করত যার প্রতি সমগ্র সমাজের অনুমোদন অভিব্যক্ত হওয়াকে কবি তাঁর কাব্যের ব্যবহারিক কার্যকারিতার প্রমাণ হিসাবে ধরে নিতেন।
আবার কোনও সূক্তে যখন একটি বিশেষ চরণ পুনরাবৃত্ত হয়, তখন তা মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী রচয়িতা ও স্তুত দেবতার সাময়িক ঐক্য বা একাত্মতা সূচিত করে। দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রত্যেকটি ঋক্ই সমাপ্ত হয়েছে ‘স জনাস ইন্দ্রঃ’ দিয়ে। এই পুনরুক্তি একটি সঙ্গে দুটি ভূমিকা পালন করছে: এক দিকে এই শব্দগুচ্ছ অলৌকিক ঘটনার স্রষ্টারূপে ইন্দ্রের গৌরব দৃঢ় ভাবে প্রচার করছে এবং অন্য দিকে দেবতার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন মন থেকে সমস্ত রকম সম্ভাব্য সন্দেহও দূর করছে। আর্যদের প্রথম বিজয়ী সেনাপতি ইন্দ্ৰ একদা নিশ্চিতই রক্তমাংসের মানুষই ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের স্মৃতিতে তিনি অমর দেবত্বে মণ্ডিত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ইন্দ্র হয়তো সামূহিক জীবনে চূড়ান্ত সাময়িক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অধিকার করে গিয়েছিলেন; ফলে প্রথম ইন্দ্র সম্পর্কে যত দৈব ও অলৌকিক শক্তিসম্ভূত কীর্তিকলাপ প্রচারিত হয়েছিল, সেই সবই সংশয়ের বিষয় হয়ে উঠল। আলোচ্য পুনরুক্তি ইন্দ্রের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও তাঁর সাম্প্রতিক প্রত্নপৌরাণিক দৈবস্বভাবকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
পৃথিবীর বহু স্থানেই এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ঐন্দ্রজালিক শক্তিযুক্ত; এগুলি বহুবার পুনরুক্ত হলে শ্রোতার মনে একটি সম্মোহনী বাতাবরণ নির্মিত হয়, বিশেষ ভাবে দেবনামে রয়েছে পবিত্রভাবের দ্যোতনা ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার আভাস। বহু ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি যে, আহূত দেবতাকে বিবিধ বিভক্তিযুক্ত শব্দরূপের মাধ্যমে উল্লেখ করা হচ্ছে; প্রশস্তির প্রতি দেবতার মনোযোগ আকর্ষণ করা কবির সাধারণ উদ্দেশ্য হলেও, দেবনামে অন্তর্নিহিত ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে উদ্বোধিত করাও নিঃসন্দেহে তাঁর অভিপ্রেত। আবার কখনও কখনও পুনরুক্তির মধ্যে নান্দনিক আবেগও প্রচ্ছন্ন থাকে— ধ্রুবপদ জাতীয় চরণে উপমা ও অনুপ্রাসের প্রয়োগ ছাড়াও অনুকার ধ্বনির ব্যবহারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে কবি আত্মসচেতন শিল্পীর মতো সূক্ষ্ম প্রয়োগ নৈপুণ্যের অধিকারী; রচনারীতির প্রতি তাঁর এই বিশেষ মনোযোগের মধ্য দিয়ে তিনি একই সঙ্গে তাঁর অভীষ্ট দেবতা ও সমসাময়িক জনসাধারণের তৃপ্তি বিধান করতে চান।
মৌখিক সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ, অর্থাৎ শব্দগুচ্ছ, পুনরুক্তি, অনুপ্রাস, সমধ্বনিযুক্ত অক্ষর এবং অন্যান্য স্মৃতিসহায়ক বাচনিক উপাদান, ইত্যাদির উপস্থিতি লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলে। লেখন-পদ্ধতির বিস্তারের পরে লেখকরা বাচনিক এককরূপে একটি মাত্র শব্দকে ব্যবহার করতে সমর্থ হলেন। ফলে অন্যান্য উপাদানের আর কোনও প্রয়োজন রইল না। মৌখিক সাহিত্য সর্বতোভাবে স্মৃতিবাহিত বলেই বাচনিক উপাদানরূপে পুনরুক্তি এতে অপরিহার্য; এগুলির কিছু প্রার্থনাসূচক, কিছু বা আহ্বানমূলক আর কিছু অপেক্ষিত জাদুশক্তি-উদ্বোধক; শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে আবেগ সঞ্চার করার প্রয়োজনে শব্দগুচ্ছগুলি সামগ্রিক ভাবে ব্যবহৃত হয়। সে সমস্ত পুনরুক্তি সম্মোহনসঞ্চারী, অন্তর্বস্তু, চিত্রকল্প, ছন্দ ও অনুপ্রাসের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করে যেখানে সামুহিক অনুষ্ঠানে নিষ্ক্রিয় ভাবে যোগদানকারী জনতার সমস্ত বিচারবুদ্ধির ক্রিয়া সাময়িক ভাবে স্থগিত হয়ে যায়। প্রখ্যাত সমালোচক জি এস কার্ক নিয়মতান্ত্রিক সাহিত্যের পরিধিতে সন্নিবিষ্ট স্বাভাবিক রচনা এবং নিয়মতান্ত্রিক সাহিত্যশৈলীতে অভিব্যক্ত ইচ্ছাকৃত আত্মসচেতন রচনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যথার্থ মৌখিক সাহিত্যের পরিচয়জ্ঞাপক নিম্নোক্ত তিনটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন: ১. সংক্ষেপীকরণের আদর্শ অনুসরণ; ২. সূত্রবদ্ধ শব্দাবলির পরিবর্ধন ও উচ্চারিত গ্রন্থনীর স্বাভাবিকতা এবং ৩. ছন্দ, তাল বিষয়ে ঐতিহ্যগত অনুপুঙ্খ। তবে উক্ত সমালোচক যেহেতু হোমারের মহাকাব্যই বিশ্লেষণ করেছেন তাই তাঁর নির্দেশিত সমস্ত লক্ষণ নির্বিচারে বৈদিক কাব্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, কেননা ঋগ্বেদ প্রাক্-মহাকাব্য যুগের রচনা এবং চরিত্রগত ভাবে বহুলাংশে আনুষ্ঠানিক। কার্ক- আলোচনা থেকে এইটুকু গ্রহণীয় যে, নিয়মতান্ত্রিক শৈলীতে রচিত যথার্থ মৌখিক সাহিত্যের চরিত্রবৈশিষ্ট্য লিখিত সাহিত্যের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। সম্ভবত লেখনপদ্ধতি ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু সাহিত্য-রচনায় তা ব্যবহৃত হত না; এমন এক যুগে অনুকরণশীল মৌখিক রচনায় নিশ্চিতই পূর্ব কবিদের রচনা থেকে প্রভূত পরিমাণ ঋণ-গ্রহণের চিহ্ন থাকাই স্বাভাবিক।
দশম-মণ্ডলের সূক্তগুলি পূর্ববর্তী মণ্ডলের অন্তত দুই শতাব্দী পরে সঙ্কলিত হয়েছিল, পূর্ববর্তী রচনা থেকে ঋণরূপে কাব্যিক উপাদান আত্মীকরণের চিহ্নও তাই এতে অধিকতর পরিমাণে ও স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান এবং সহজেই আবিষ্কারযোগ্য। বস্তুত ঋগ্বেদের গঠনগত উপাদানসমূহ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে সংবর্ধিত হয়েছিল; সম্ভবত, সেই সঙ্গে, বিচিত্র সামাজিক ক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাসের ফলশ্রুতি, বেদ ও সুদীর্ঘকালীন শৈলীগত পরিমার্জনের ফসল, এর কাব্যভাষাও অনুরূপ কাব্যিক প্রক্রিয়ার ও পরিণতি চূড়ান্ত এক অভিব্যক্তি। বিশাল কাব্যভাণ্ডারের বহু প্রজন্মব্যাপী স্রষ্টাদের স্মৃতি যাতে অবাঞ্ছিত ভাবে পীড়িত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য কোনও অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ যুক্ত না করার প্রতি কবিগণ যত্নশীল থাকতেন। মৌখিক সাহিত্যের প্রধান চারিত্র্যলক্ষণ হল অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কঠোর মিতভাষিতা। এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, অদৃশ্য দেবতার সন্তুষ্টি মূলত অনুমাননির্ভর হলেও সম্পৎশালী রাজাদের বদান্যতাটা কিন্তু সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর এবং কিছু কিছু নির্দিষ্ট কবিতা রাজকীয় দাতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক আনুকূল্য লাভ করত বলে এই সব গানের গৌরব সমাজে যেন তর্কাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়ে যেত। বিভিন্ন কবিদের মধ্যে দান-সামগ্রী লাভের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল বলেই মন্ত্রে তার উপযোগী অংশের পুনরুক্তির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কেননা, নান্দনিক ভাবে তৃপ্তিকর কোনও চিত্রকল্প জনগোষ্ঠীর সাহিত্যভাণ্ডারে সতর্ক সংরক্ষণের যুগে নিশ্চয়ই একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বর্জিত হতে পারে না। বরং উপযুক্ত অবকাশে এই জাতীয় উপকরণ বারংবারই ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। মৌখিক সাহিত্যের কবিগণ উত্তরাধিকার সূত্রে সামাজিক প্রত্নস্মৃতি থেকে বাচনিক আঙ্গিকসমূহ আহরণ করে, সামান্য পরিমার্জন করে নিজস্ব এক কাব্যরচনার শৈলী নির্মাণ করতেন। এই পদ্ধতি কেবলমাত্র অধিকতর নির্ভরযোগ্যই ছিল না, একই সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিল। এ কথা বলা যায় যে, কবিদের প্রথম প্রজন্মকে অর্থাৎ যাঁরা কাব্যের প্রাথমিক উপাদানরূপে মূল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিৰ্মাণ করেছিলেন তাঁদেরই প্রধান অনুপ্রাণিত কবি রূপে চিহ্নিত করা যায়, কেননা প্রাথমিক পথ-প্রদর্শক রূপে তাঁদের সম্মুখে সূত্রবদ্ধ তেমন কোনও বাক্যাংশের দৃষ্টান্ত ছিল না, যা থেকে তাঁরা অনায়াসে ঋণগ্রহণ করতে পারতেন। পরবর্তী প্রজন্মের কবি, শিষ্যবর্গ বা উত্তরাধিকারীরা প্রাগুক্ত অনুপ্রাণিত কবিদের রচনা থেকে যথেচ্ছ মন্ত্রাংশ বা চরণ গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে এলেন স্বল্পমেধা কবিরা, অকটু অনুকারক এবং নিছক আবৃত্তিকারেরা। এদের কোনও রকমা কাব্যপ্রতিভা বা নান্দনিক উপলব্ধি বা প্রকাশক্ষমতা ছিল না বলেই উত্তরাধিকাররূপে গৃহীত বাক্যাংশকে যথাযথ প্রসঙ্গ অনুযায়ী ব্যবহার করতে এঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, ফলে এঁদের রচনা ত্রুটিযুক্ত ও কাব্যমূল্যে দীন।
ঋগ্বেদে চিত্রকল্প
মৌখিক কাব্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বাক্সংযম। যদিও এটি বিবিধ উপায়ে সাধিত হত, তবু বাস্বল্পতা অর্জনের প্রয়াস শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিক সঙ্কেতসূত্রেই পর্যবসিত হয় না— যে কোনও মানদণ্ডেই ঋগ্বেদীয় সূক্তের অনেক সূক্তই কাব্যপদবাচ্য।
বহু-কবি-বিরচিত এই জাতীয় বিপুল সাহিত্যে, খুব স্বভাবিক ভাবেই, কাব্যবিচারে বেশ কিছু অংশ উৎকৃষ্ট আবার অনেক অংশই নগণ্য হয়। প্রাচীন কাব্যে যে ধরনের প্রচলিত রীতি রয়েছে, সে সমস্তই বৈদিক সূক্তে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক সূক্তের বহুলাংশই অনলংকৃত এবং সম্ভবত তৎকালীন সাধারণ বাগভঙ্গির খুবই নিকটবর্তী; তবু এর বহুস্থানে চিত্রকল্প প্রযুক্ত হয়েছে এবং তা সার্থক ভাবেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন সাহিত্য চিত্রকল্প শুধুমাত্র শোভাবর্ধক নয়, এর একটি কার্যকর ভূমিকাও রয়েছে, কেননা অলংকৃত কাব্যে শব্দনির্ভর এক ইন্দ্রজাল রচনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান। বৈদিক চিত্রকল্পের অধিকাংশই নির্মিত হয়েছে উপমা, রূপক, সমাসোক্তি ও অনুপ্রাসের প্রয়োগের দ্বারা। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা যাকে চিত্রকল্প বলে মনে করছি, বৈদিক কবিদের বা তাঁদের শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তার তাৎপর্য সম্ভবত অনেকটাই ভিন্ন ছিল, কেননা তথাকথিত চিত্রকল্পগুলি ছিল তাঁদের দৈনন্দিন বাগ্যবহারের সাধারণ অঙ্গ। কিন্তু ভাষাগত অভ্যাস ও শৈলীগত প্রকরণের দিক দিয়ে বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যুগের যে স্পষ্ট ব্যবধান এসে গেছে, তার ফলে আমাদের পক্ষে পূর্বপরিকল্পিত আলংকারিক রীতির সঙ্গে সাধারণ ভাষার বিশেষ ভঙ্গির পার্থক্য নিরূপণ করা আজ খুবই কঠিন।
বৈদিক উপমা প্রধানত তিন ধরনের: স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাব্যিক, পরিকল্পিত ভাবে আলংকারিক ও স্পষ্টতই ঐন্দ্রজালিক। সংহিতায় নিছক শোভাবর্ধক উপমা প্রকৃতপক্ষে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যিক ও ঐন্দ্রজালিক উপমাই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য এই দুই জাতীয় উপমা পরস্পর ভিন্ন নয়। অন্য ভাবে বলা যায়, উপমা কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বা দেবতা ও মানুষের নিকট আরও প্রীতিকর করে তোলে বলেই কবি তার প্রয়োগ করেন, তাই একই সঙ্গে তাঁর অবচেতনায় এই উপলব্ধিও রয়েছে যে, উপমা সূক্তটিকে অনুষ্ঠানগত ভাবে অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক দিক দিয়ে আরও নিশ্চিত ফলপ্রদ করে তুলবে। যজমানের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রয়োজনে দেবতাকে তাঁর প্রার্থনা পূরণের অনুকূল করে তোলার জন্য কবি যে সমস্ত অনুষ্ঠানগত ভাবে কার্যকর সূক্ত রচনা করতেন, তাতে উপমার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই বাচনিক উপাদান সূক্তকে অধিকতর মনোমুগ্ধকর ও জাদুশক্তিতে সমৃদ্ধতর করে তুলত। বৈদিক উপমা দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত গণ্ডি থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছে। মোটামুটি ভাবে সেই সব উপমানকে নিম্নোক্ত ভাবে বিন্যস্ত করা যায়: (ক) প্রকৃতি— নদী, বৃক্ষ, লতা, ইত্যাদি (খ) প্রাণীজগৎ— যেখানে পরিচিত প্রাণীদের মধ্য থেকে মানবিক গুণাবলির সাদৃশ্য সন্ধান করা হত; (গ) বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক— অপত্যস্নেহ, দাম্পত্য প্রেম, প্রতিবেশীপ্রীতি ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের অনুভূতি; (ঘ) বিবিধ বৃত্তি; (ঙ) দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উপকরণ বস্তু এবং (চ) মহাজাগতিক।
অভিব্যক্তির কার্যকারিতাকে তীক্ষ্ণতর করে তোলার জন্যে মানুষ বহু প্রাচীন কালেই প্রতীক বা বস্তুর সমান্তরাল বিকল্প অর্থাৎ প্রত্নকথার সন্ধান ও প্রয়োগ করতে শিখেছিল। সুসংহত প্রত্নকথা থেকেই প্রথম পর্যায়ের উপমার সৃষ্টি এবং আরও বেশি সংহতি ও শব্দসংকোচের পর্যায়ে তা রূপকে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন কবিতায় এই সব চিত্রকল্পের নিজস্ব বাস্তব জীবন ছাড়াও তাৎক্ষণিক সৌন্দর্য সৃষ্টির অতিরিক্ত কিছু বিশেষ ধরনের ক্ষমতাও ছিল। কবির কল্পনা ও প্রতিভা অব্যবহিত পরবর্তী প্রসঙ্গ গভীরতর জীবনাবেগ যুক্ত করার জন্যই তাকে জীবনের অন্য কোনও সমান্তরাল দিকের সঙ্গে তুলনা করত। প্রত্যক্ষ যে জগৎ, অথবা পরম্পরাক্রমে আগত দেবপুরাণের যে জগৎ, তার থেকে তুলনীয় উপাদান আহরণ করে বর্ণিত বস্তুটিকে স্পষ্টতর ও দৃঢ়তর করার প্রয়াসেই প্রথম ব্যবহৃত হল উপমা। এর ফলে মন্ত্রের ব্যঞ্জনাশক্তি বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও অনুষ্ঠানের ঈপ্সিত ফল উৎপাদনে সমর্থ বলে উপস্থাপিত করল। চূড়ান্ত বিচারে চিত্রকল্প বিষয়বস্তুর গৌরব বৃদ্ধি করে ফললাভের সম্ভাবনাকেই সুনিশ্চিত করে। বৈদিক উপমাগুলির শক্তি ও কার্যকারিতা সমান নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি অত্যন্ত সতেজ ও সজীব। অনুমান করা যায় যে, বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হওয়ার বহু পূর্ব হতেই শ্লোক রচনার একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল; এমনকী সংহিতাতেও কিছু কিছু উপমাকে গতানুগতিক ও বিধিবদ্ধ মনে হয়; আবার একই সঙ্গে কিছু কিছু উপমা নবীন ও প্রাণবন্ত।
উপমা ও রূপকের তুলনায় অতিশয়োক্তি কিছু অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়; শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রভাবিত করার জন্য চূড়ান্ত আতিশয্যের আশ্রয় নেওয়ার পদ্ধতি সাধারণ ভাবে প্রাচীন ও অর্বাচীন সব সাহিত্যেরই বিশিষ্ট চারিত্র্যলক্ষণ। ঋগ্বেদে পড়ি, ‘সমুদ্র যে ভাবে জল ধারণ করে, ইন্দ্রের পাকস্থলীও তেমনই সোমরসে পূর্ণ’। (১:৮:৭) বস্তুত ইন্দ্রের কীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গেই সর্বাধিক অতিশয়োক্তি ব্যবহৃত হয়েছে; এ ছাড়া, বায়ুবাত, দেবতাদের শক্তি, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও দেবতার বিশ্বজাগতিক কার্যকলাপ এবং আর্যদের শত্রুবাহিনীর অত্যাচার ও বৈরিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রচুর অতিশয়োক্তি প্রযুক্ত হয়েছে। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রশস্তি ও প্রার্থনা এই অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। বিশেষত যখন সদ্য ফললাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল এবং অভীষ্ট পূরণে সূক্তের ক্ষমতা সম্পর্কে বিপুলসংখ্যক প্রত্যাশী শ্রোতৃমণ্ডলীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রভাবিত করা প্রয়োজন।
বৈদিক কবিতায় অতিশয়োক্তির ভূমিকা নিছক আলংকারিক নয়, তার একটা ধর্মীয় ও প্রত্নপৌরাণিক কার্যকারিতাও রয়েছে। দেবতাদের ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন রূপে উপস্থাপিত করার অর্থ তাদের অতিমানবিক গৌরব প্রতিষ্ঠা; কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে অভীষ্ট বস্তুদানের ক্ষমতা সম্পর্কে দেবতাদের উপর বিশ্বাস জাগাবার জন্য কবি তাঁদের ক্ষমতা ও কীর্তিকাহিনিকে মাত্রাহীন আতিশয্যে মণ্ডিত করতে চেয়েছেন। দেবতাদের অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্তমানে কোনও প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন নেই; সমাজের গোষ্ঠীগত প্রয়োজন নির্বাহের জন্য দেবতাদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা লাভের গৌরবজনক অতীত কাহিনি বর্ণনা ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা হত। শ্রোতাদের জানানো হত, তাঁদের পূর্বপুরুষের জন্য দেবতারা কত কিছু করেছিলেন— যথোপযুক্ত ভাবে সন্তুষ্টি বিধান করা হলে তাঁদের জন্যও তাঁরা একই রকম উদার বদান্যতায় দান করবেন। এই উদ্দেশ্যেই অতিশয়োক্তি প্রযুক্ত হত, যাতে আকাঙ্ক্ষা ও তার পূর্ণতা, এবং সম্ভাব্যতা ও বাস্তবের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মধ্যে সেতু নির্মাণ করা যায়। অর্থাৎ তাদের প্রয়োগ নিছক আলংকারিক নয়, একই সঙ্গে প্রত্নপৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক।
অতএব আমরা দেখছি যে, বৈদিক কবিতায় শুধুমাত্র শোভাবৃদ্ধির জন্য অলংকার ব্যবহৃত হয় না, তার কিছু সাহিত্যাতিরিক্ত উদ্দেশ্যও রয়েছে। কবি তাঁর নিজের জন্য, গোষ্ঠীর জন্য এবং দেবতার জন্যই রচনা করতেন; কিন্তু অধিকতর প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি রচনা করতেন পুরোহিতের জন্য, যাতে সেই পুরোহিতরা গোষ্ঠীর প্রয়োজনটা দেবতার নিকট আরও ভাল ভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন এবং দেবতা তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। এই পার্থিব প্রয়োজনের আবেগ অবশ্য কবির সমুন্নত দেবস্তুতিতে কোনও হানি করেনি, বস্তুত গোষ্ঠীর প্রয়োজনে কবির আবেগ পরিশীলিত হওয়াতে তাঁর প্রার্থনার গৌরব বৃদ্ধি হত। এই জন্য কবি উপমা, রূপক, অনুপ্রাস এবং অতিশয়োক্তির মতো যে সমস্ত অতিরিক্ত শিল্প প্রকরণের আশ্রয় নিতেন, দেবতাদের নিকট প্রশস্তি তাতে আরও রমণীয় হত এবং দেবতারা তাতে যেন আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠতেন, ফলে প্রার্থনার সাফল্য তাঁদের কাছে নিশ্চিততর হয়ে প্রতিভাত হত এবং সেই সঙ্গে তাদের কল্পনায় যজ্ঞও হয়ে উঠত আশু ফলপ্রদ।
চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ফলে এ ধরনের চিত্রকল্প নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল বলেই ঋগ্বেদীয় চিত্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সজীবতা ও স্পষ্টতা। এটা অনস্বীকার্য যে, কিছু কিছু সূক্ত কিছু স্বল্পধী উচ্ছ্বাসপ্রবণ চারণকবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল; প্রতিভার দৈন্যে এঁরা প্রাচীনতর কবিদের রচনা নির্বিচারে আত্মসাৎ করে প্রায়শই বিচিত্র উৎস থেকে সঙ্কলিত ও বহুব্যবহৃত চিত্রকল্প তাঁদের কাব্যে সরাসরি ব্যবহার করতেন। তবে সংহিতার বহু সূক্তই প্রকৃত শিল্পীর সৃষ্টি: সেখানেও শুধুমাত্র শোভা বর্ধনের জন্য চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়নি; অভিজ্ঞতার অনিবার্য প্রেরণার ফলেই এবং অনুষ্ঠানের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এদের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব। চিত্রকল্পপ্রয়োগের পশ্চাতে এই দৃঢ়বিশ্বাস সর্বদাই সক্রিয় ছিল যে, সার্থক বর্ণনা অনুষ্ঠানগত ভাবেও অধিকতর ফলপ্রসূ।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, শ্লোক রচনার আঙ্গিকটি শুধু বৈদিক কাব্যের সঙ্গেই সহব্যাপ্ত নয়, কেননা স্তবস্তুতি ছাড়াও আনুষ্ঠানিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যে কোনও বস্তুই সংহিতার উপজীব্য। যজ্ঞে ব্যবহারের উপযোগী বস্তুসমূহের আনুষ্ঠানিক পবিত্রীকরণের প্রয়োজনে যেখানে সূক্তগুলিতে সেই সব বস্তু উল্লিখিত হয়েছে, জনসাধারণের স্মৃতিতে তাদের ওপর অলৌকিক মহিমা আরোপ করার একমাত্র উপায়ই ছিল শ্লোক রচনার প্রচলিত আঙ্গিক। নিরক্ষর সমাজে যেহেতু সমস্ত কিছুই মৌখিক ভাবে রচিত ও সংরক্ষিত হত, তাই একমাত্র শ্লোকের আঙ্গিকই কোনও রচনাকে স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারত। সাহিত্যগত ভাবে সংরক্ষণযোগ্য সমস্ত কিছুই যেহেতু শুধু পদ্যেই রচিত হতে পারত, কারণ প্রাক্-লেখন যুগে ছন্দোবদ্ধ রচনাই কণ্ঠস্থ করা সহজ ছিল, তাই বিশুদ্ধ কাব্যের তুলনায় তার ক্ষেত্র ছিল ব্যাপকতর। বস্তুত, সংহিতার বহু অংশ প্রাথমিক ভাবে কাব্যিক রচনা নয়, আনুষ্ঠানিক কারণে কণ্ঠস্থ করার সহায়ক; তাই বহু স্থানেই আমরা প্রকৃত কাব্য খুঁজে পাই না, এমনকী প্রত্যাশাও করি না। তা ছাড়া চারণকবিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। লুই হ্রেনু যেমন বলেছেন, বিভিন্ন পুরোহিত পরিবারের প্রতি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা একটি সামাজিক রীতি ছিল, তাই কার্যকর ও শক্তিশালী সূক্ত রচনার জন্য পুরোহিতরা পরস্পর প্রতিস্পর্ধায় প্রবৃত্ত হতেন। নিঃসন্দেহে প্রেরণাই কাব্যচর্চার প্রধান উৎস ছিল, কিন্তু সে প্রেরণা গীতিকবি কিংবা মহাকাব্যিক চারণ কবি বা গীতিকা রচয়িতার বিমূর্ত ও নিরাসক্ত কাব্যরচনার সমগোত্রীয় নয়। পুরোহিতরা যখন সচেতন ভাবে অনুষ্ঠান উপযোগী শ্লোক রচনার চেষ্টা করতেন তখন বহু স্বতঃস্ফূর্ত গীতিকবিতাই আনুষ্ঠানিক প্রয়োগের জন্য গ্রহণ করা হত। কবিরা সম্ভবত তাঁদের রচনার এই জাতীয় প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সক্রিয় ভাবে যজ্ঞের প্রয়োজনে তৎকালীন সামাজিক দাবি ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার চেষ্টা করতেন।
ঋগ্বেদের বহু অংশেই গীতিকা বা আখ্যানে কাব্যের লক্ষণযুক্ত রচনা পাওয়া যায়, চরিত্রগত ভাবে ধর্মীয় আবেদনযুক্ত মৌখিক সাহিত্যের পক্ষে তা-ই স্বাভাবিক। যুদ্ধগীতি, অলৌকিক আখ্যান ও প্রত্নকথা, প্রহেলিকা, রহস্যপূর্ণ এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ স্বাভাবিক ভাবেই বিবৃতিধর্মী আখ্যানকাব্যের উপযোগী আঙ্গিকের জন্ম দিয়েছিল। ফলে যদিও ঋগ্বেদের অধিকাংশ রচনা ধর্মীয় চেতনা থেকেই হয়েছে এবং চরিত্রগত ভাবে এগুলি অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক, তবু বহু সূক্ত আঙ্গিকের দিক থেকে আখ্যানকাব্যের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যের চিহ্ন বহন করে। বস্তুত, কাব্য হিসাবে ঋগ্বেদের বহু সূক্তই মানবিক আবেগের উত্তাপে আতপ্ত, কোথাও বা এগুলি আড়ম্বরপূর্ণ ও রহস্য-দ্যোতক ভাবনা উপস্থাপিত করে; সেই সঙ্গে এগুলি সমুন্নত আদর্শ, স্পষ্ট বর্ণনা ও বিচিত্র ভাবাবেগের কাব্যিক অভিব্যক্তি।
ঋগ্বেদে বর্ণনা
ঋগ্বেদের কবির বিস্ময়বোধ যখন নিবিড় এবং বর্ণনীয় বিষয় সাধারণ গণ্ডির বহির্ভূত, সেই সব ক্ষেত্রে বর্ণনা বহুলাংশে উদ্দীপক হয়ে উঠেছে। ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, অগ্নি, মরুৎ ও আদিত্যগণের বর্ণনায় কবিত্বশক্তি বিশেষ ভাবে উচ্ছ্বসিত; সোমমণ্ডলে বিশ্বজগতের কেন্দ্রবিন্দুরূপে সোমদেবের বর্ণনায় ঋষিকবি অনুরূপ মুগ্ধতার সঞ্চার করেছেন। ইন্দ্র এবং সোমদেবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে অতিশয়োক্তির বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সমস্ত অংশে উন্নত আদর্শ অভিব্যক্ত, সেগুলিতে কাব্যিক সমৃদ্ধির প্রকাশ স্পষ্টতর; বিশেষত সৃষ্টিতত্ত্ব ও দর্শনবিষয়ক সমস্ত সূক্তে এই জাতীয় চিন্তার পরিপূর্ণ ও মনোজ্ঞ প্রকাশ ঘটেছে। বিখ্যাত মধুসূক্তটি (১:১৮:৬-৮) সমগ্র বিশ্বজগতের সঙ্গে পরিপূর্ণ একটি হৃদয়ের বিমুগ্ধ উৎসা-র প্রকাশ করে বৈদিক কবির মানসিক প্রবণতার ধ্রুপদী অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে।
সোমমণ্ডলের কিছু কিছু অংশে কবিরা যেহেতু দৈনন্দিন জীবনের উপাদান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাদের চিত্রকল্প ও বিশিষ্ট উল্লেখের মৌল রূপটি আহরণ করেছেন, তাই এই সমস্ত সূক্তে আমরা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষাংশে প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক অবস্থার পরিচয় লাভ করি। যখন কোনও কবি নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমেই দারিদ্র্য বর্ণনা করেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই বিরল এক সাফল্য অর্জন করেন। নবম মণ্ডলের একটি সূক্তে সমাজে অনুসৃত বিভিন্ন বৃত্তিধারী শ্রেণিগুলির বাস্তবনিষ্ঠ ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় বর্ণনা রয়েছে। মিশরের ঊনবিংশতিতম রাজবংশের (১৩৫০-১২০০ খ্রি. পূ.) আমলে লেখা একটা রচনা, ইংরেজি তর্জমায় স্যাটায়ার্স অন দি ট্রেডস নামে প্রকাশিত। এটি প্রহসন হিসাবে যথার্থ সার্থক এবং মিশরের তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিরও উজ্জ্বল নিদর্শন।
রাত্রি ও অরণ্যানীর প্রতি নিবেদিত সূক্তে নিসর্গের সম্ভ্রম-উৎপাদক মহিমার ও সৌন্দর্য্যের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগের পরবর্তিকালের দেবী লক্ষ্মীর বর্ণনাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। (খিল ২:৬:৫) দেবী ঊষার প্রতি নিবেদিত বিখ্যাত সূক্তগুলিতে দৈনন্দিন প্রত্যক্ষগোচর জীবনের অভিজ্ঞতার অনুরণন অত্যন্ত স্পষ্ট। অনুরূপ ভাবে মরুৎদের প্রতি নিবেদিত সূক্তে বাস্তবের সেনাবাহিনীর বর্ণনার প্রতিধ্বনি মেলে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ সেনা অভিযানের বর্ণনার গৌরব অনুভূত হয় এবং একই সঙ্গে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নৈসর্গিক দৃশ্যও বিশেষ ভাবে অনুভূতিগোচর হয়ে ওঠে। কিছু কিছু সূক্ত আবার উন্নত ভাবনা ও বিশ্বজগতে অন্তর্নিহিত রহস্যের বোধ প্রকাশ করে সাধারণ মানের অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছে। শেষ পর্যায়ের রচনা, অর্থাৎ প্রথম ও দশম মণ্ডলে এই জাতীয় অধিকাংশ সূক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের অব্যবহিত নিকটবর্তী প্রসঙ্গ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জনসাধারণের অন্তর্লীন স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলেছে। একই সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে বিবর্তনের যে পর্যায় কিছু কিছু মন্ত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাতে বর্ণনার অভিনবত্ব ও ভাষাগত পরিবর্তন বেশ সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়।
ইন্দো-ইয়োরোপীয় প্রত্ন-পুরাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা দেবতাদের মানুষের চেয়ে সর্বতোভাবে ভিন্ন বা অলঙ্ঘ্য দূরত্বে নির্বাসিত বলে মনে করে না। অন্য ভাবে বলা যায়, ইন্দো-ইয়োরোপীয় বিশ্ববীক্ষায় মানুষ দেবতাদের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী; এমনকী মানুষ ও দেবতারা পরস্পর নির্ভরশীল। তাই বৈদিক কবি উচ্চারণ করেন: “হে বৃত্রঘাতী ইন্দ্ৰ! তুমি আমি একত্রে চেষ্টা করব, যতক্ষণ না আমরা ধন লাভ করছি’। (৮:৬২:১১) শেষ পর্যায়ের আরও কিছু সূক্তে ইন্দ্রকে সমস্ত সৃষ্টির মর্মমূলে নিহিত মৌলিক আদিশক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে; পার্থিব ও অতিজাগতিক বহু কীর্তিরই তিনি অধিনায়ক, দেবতাদের মধ্যে তিনি শুধু শ্রেষ্ঠই নন, সর্বদেবের প্রতিনিধিও। স্পষ্টতই ইন্দ্রের এই চরিত্রগত রূপান্তর সর্বেশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে বিবর্তিত হওয়ার স্তরেই সম্ভবপর; কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি বিমূর্ত সৃষ্টির প্রেরণার উৎস ব্রহ্মের প্রায় সমগোত্রীয়। একটি বিবৃতিকে নির্লজ্জ আত্মপ্রশস্তি বলে ভ্রম হয়; এটি হল ইন্দ্র যখন চরম বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত মূল শক্তিরূপে বন্দিত হন তখন তাঁর সেই চূড়ান্ত রূপান্তরের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তের ইঙ্গিত বহন করে তাঁকে সর্বদেবতার প্রতীকরূপে দেখা। বৈদিক দেবসঙ্ঘে যাঁর বিলম্বিত প্রবেশ, সেই বিশ্বকর্মাও দশম মণ্ডলে এই গৌরবের অধিকারী।
অগ্নির প্রতিশব্দ ‘বৈশ্বানর’ পৃথক নাম রূপে সূর্য ও আগুন— এই উভয়ের দ্যোতক বিশ্বজাগতিক আলোক সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে। এই আলোক যখন প্রথম আবির্ভূত হল, সমগ্র সৃষ্টি, দেবগণ, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং উদ্ভিদজগৎ আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল, কেননা তার পূর্বে সমস্তই ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়ের বহু সূক্ত অনুরূপ উন্নত ভাবনায় পূর্ণ। প্রজাপতিসূক্ত (১০:১২১; ১০:১৩০); বাগাম্ভৃণীয় বা পরমাত্মা সূক্ত (১০:১২৭) এবং মুখ্যত নাসদীয় সূক্ত (১০:১২৯)-তে অত্যন্ত উচ্চমানের দার্শনিক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সময়ে বিমূর্ত শ্রদ্ধাও যে দৈবীকরণ প্রক্রিয়ায় পৃথক দেবতা হয়ে উঠেছেন, তার কারণ সম্ভবত এই যে, বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে প্রচলিত ধর্মবিধি সম্পর্কে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা কালের বাতাবরণে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল। এই সময়কার নবোদিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির মতাদর্শ মানুষকে যজ্ঞের তাৎপর্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করতে প্রবৃত্ত করছিল। ফলে শ্রদ্ধার নতুন মূল্যায়ন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।
ঋগ্বেদীয় বহু সূক্ত আবেগ-গাঢ় ও বিষয়গৌরবে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ, যদিও অধিকাংশ সূক্তই উৎস ও প্রেরণাগত বিচারে স্পষ্টতই আনুষ্ঠানিক। তবে সূক্তগুলির যথার্থ মানবিক অভিজ্ঞতার উৎসমূলের গভীরে অবগাহন করে আমরা বুঝতে পারি, এ ব্যাপারটাও খুবই স্বাভাবিক। কবি যখনই প্রশস্তি ও প্রার্থনার পরিমার্জনার পূর্ববর্তী পর্যায়ের শেষ দিকে শিল্প-ক্রিয়ার স্তরে প্রবেশ করেন তখন আপন অভিজ্ঞতাই তিনি প্রকাশ করতে চান; তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির মধ্যে সেই সব অভিজ্ঞতার ছাপই ফুটে ওঠে। ভীতি ও উদ্বেগ ঋগ্বেদের বহু কবিতার উৎস। বিস্তীর্ণ স্থলভাগের উপরে সুদীর্ঘ প্রবাস ও পরিক্রমার পরে আর্যরা যখন ভারতে উপস্থিত হলেন, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের জনগোষ্ঠী এবং অপরিচিত নৈসর্গিক দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা দেখলেন তাঁদের ভাবী বসতিস্থল আদিম অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত। তাঁদের দৃষ্টিতে তাই এই সব জনগোষ্ঠী তাঁদের যজ্ঞানুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়ে সর্বপ্রকার ঐহ্যিক কল্যাণলাভের সম্ভাবনাকে বিড়ম্বিত করেছে। এই রকম বিপর্যয়ের আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে আর্যদের প্রধান মানসিক অবস্থাই ছিল ভীতি, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় কণ্টকিত। আর্যরা তাঁদের আত্মীয়-পরিজন ও গোসম্পদের জন্য যখন নিরাপত্তার প্রার্থনা করতেন, সেই সব সূক্তে তাই বহু স্থানেই পূর্বোক্ত মানসিকতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা গেছে। শত্রুদের পরাজিত করার জন্য এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রকম অমঙ্গল ও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যে সমস্ত প্রার্থনা সূক্তগুলি রচিত হয়েছে, তা গভীরতম আবেগের অন্তঃস্থল থেকে উৎসৃত বলে যথার্থ মর্মভেদী আবেগের সৃষ্টি করেছে। সাম্যবোধের জন্য যে প্রার্থনা অথর্ববেদে মাঝে মাঝেই আছে, ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়েই তাদের প্রথম বার লক্ষ্য করা যায়। সাম্যবোধ ও সমন্বয়ের জন্য এই যে আকাঙ্ক্ষা ঋগ্বেদ রচনার উপসংহারে আমরা লক্ষ করি তা অবশ্যই এই সুদীর্ঘ সংঘাতেরাই সমাপ্তি সূচনা করছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষে উপনীত হওয়ার জন্য যে অকথিত অস্পষ্ট প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়, তারই ফল হিসাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সংমিশ্রণে ও সমবেত প্রচেষ্টায় বহুবিধ গঠনমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বহুগোষ্ঠীভূক্ত ভারতীয় সভ্যতার জন্ম হয়।
পরাজিত আদিম জনগোষ্ঠীর নিরবচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্ন শত্রুতা থেকে পরিত্রাণ লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় দূরদর্শী ঋষিকবিগণ শক্তির সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সম্ভবত আদিম জনগোষ্ঠী ছাড়াও অবৈদিক আর্যগোষ্ঠী এবং আর্য শ্রেণিভুক্ত বিবদমান শাখাগুলির মধ্যেও শান্তিস্থাপন বিশেষ ভাবে জরুরি হয়ে উঠেছিল। তাই এই সমস্ত প্রার্থনাকে নিছক ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষারূপে বিচার না করে সেই সময়ের সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ প্রয়োজনের অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন; কেননা তখনকার কলহদীর্ণ পরিবেশে যে কোনও জনগোষ্ঠীর বিকাশের পক্ষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অপরিহার্য ছিল। এ ছাড়াও সূক্তগুলিতে জীবনের অন্ধকার দিকেরও অভিব্যক্তি রয়েছে। সমৃদ্ধির প্রার্থনা তাই প্রায়শই শত্রুর প্রতি ঈর্ষাকাতর আর্যের প্রার্থনা, যাতে তার দেবতা শত্রুর সর্বপ্রকার অমঙ্গল সাধন করেন। ভিন্ন গোত্রজাত ও কৌমসমাজগত প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াও আদিম জনগোষ্ঠীভুক্ত যে সমস্ত মানুষ পরাজিত হয়েও বশ্যতা স্বীকার করেনি বা পর্যুদস্ত হয়ে যায়নি— তারাই ছিল শত্রুপদবাচ্য। বৈদিক কবি শুধু তাদেরই ধ্বংস ও মৃত্যুর জনে উদগ্র কামনা ব্যক্ত করেননি, তাদের আত্মীয়-পরিজন এবং শেষ সম্পদের সর্বনাশও চেয়েছেন।
এরই পাশাপাশি সরল সংশয়ও বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। সর্বজনগ্রাহ্য উপাসনা-পদ্ধতি রূপে সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান যখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হল, জনসাধারণের ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তা যজ্ঞের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যও দাবি করেছিল। তখন কিছু কিছু সূক্ষ্মতর অনুভূতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে এই জীবনবীক্ষার মৌল বিধিগুলির ভিত্তিভূমিকে অপসারিত করে অর্চনীয় দেবসঙ্ঘের গুরুত্ব খর্ব করে দিতে চাইল। সম্ভবত বিমূঢ় বিস্ময়বোধেরই প্রকাশ ঘটেছিল দশম মণ্ডলের দুটি সূক্তের অন্তর্গত (১২১ ও ১২৯) কিছু প্রখ্যাত মন্ত্রে; এর মধ্যে আছে অন্যতম সেই বহু পরিচিত ধ্রুপদ: ‘কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম’। মৌলিক সংশয়সূচক মন্ত্রগুলিতে এক ধরনের জরুরি ও আন্তরিক তাড়নার আভাস রয়েছে; এদের মধ্যে আমরা আত্মিক আলোড়ন ও গভীর অন্তর্লীন আন্দোলন অনুভব করি; বুঝতে পারি যে, অনুষ্ঠাননির্ভর জগতে প্রচলিত সংস্কারের প্রতি অভ্যস্ত বিশ্বাসের চেয়ে সহজ সংশয়ের যৌক্তিকতা অধিক। ঋগ্বেদের বহু স্থানে যেহেতু প্রেরণাশূন্য অনুষ্ঠানমূলক সাহিত্যের নিদর্শন রয়েছে, তাই বেশ কিছু শুষ্ক ও নীরস মন্ত্র খোলাখুলি ও নির্লজ্জ ভাবে রাজা ও দাতাকে পুরোহিতদের বদান্য ভাবে দান করতে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছে। এ জন্যে প্রাচীন দাতা ও দানের নজির উল্লেখ করে তারা যুক্তিজাল বিস্তার করেছে। এ সমস্তই ঋগ্বেদের অন্তিম পর্যায়ভুক্ত এবং এতেই একটি সমৃদ্ধ কাব্যিক ঐতিহ্যের ক্ষয় ও ধ্বংসের বীজ নিহীত রয়েছে।
ধর্ম ও দর্শন
যখনই আমরা ঋগ্বেদের ধর্ম ও দর্শনের কথা চিন্তা করি তখন বহুজাতিক সাংস্কৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত ও অন্তত এক সহস্রাব্দব্যাপী ইতিহাসের বিবর্তনের পরিশীলিত বিচিত্র একটি জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আচার আচরণের জটিল আয়তন সম্বন্ধে সচেতন হই। এই সময়ে বৈদিক সাহিত্য বিবর্তনের পথে সম্পূর্ণ পরিণতরূপে কখনও নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির থাকেনি। ফলত, প্রত্নপুরাণ ও অধ্যাত্মবিদ্যার ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির বিবিধ পর্যায়ের অবশেষ-চিহ্ন এতে খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে ধর্ম বলতে আমরা বুঝি প্রত্নকথা, অনুষ্ঠানচর্যা, ইন্দ্রজাল ও নীতিবোধ; অন্য দিকে দর্শন বলতে বুঝি একটি আধ্যাত্মিক উপগঠন— যাকে হয়তো জনসাধারণ স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেনি, কিন্তু তাদের সামূহিক জীবনদৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত আচার-আচরণে তার নিগূঢ় ও নিয়ন্ত্রক ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঋগ্বেদসংহিতা অবশ্য এই সম্পর্কে আমাদের সরাসরি বেশি কিছু জানায় না, কেননা অনার্য উপাদানের সঙ্গে নিরন্তর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ও সমন্বয়-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা মূলগত ভাবে নিরঙ্কুশ আধিপত্যশীল আর্য জনগোষ্ঠীর এক প্রায়-অখণ্ড সংস্কৃতির প্রতিনিধি। ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা প্রত্নকথাগুলিকে সম্পূর্ণত বা সুশৃঙ্খল ভাবে বিবৃত হতে দেখি না; বরং এমন ভাবে সেইগুলি উল্লিখিত এবং মাঝেমাঝে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বিবৃত হয়েছে যে, আমাদের মনে হয়, তৎকালে প্রচলিত প্রত্নকথাগুলির সঙ্গে পরিচিতি এই আপাত-সরল ভঙ্গির কারণ। সেই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, সামূহিক অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে পরিচিতি ও সে সম্বন্ধে প্রায়োগিক জ্ঞান এবং সেই সঙ্গে যজ্ঞে যথোপযুক্ত সূক্তগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত থাকার ফলে সংহিতা তার প্রচলিত রূপটি ধারণ করতে পেরেছিল।
যজুর্বেদে আমরা যজ্ঞানুষ্ঠানের কিছু কিছু বিবরণ পাই। তবে এই সব বিবরণ শুধু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীচক্রের জন্যেই সংরক্ষিত ছিল; ফলে এগুলি গূঢ়ার্থবাহী ও সংক্ষিপ্ত, যাতে অনুষ্ঠান-চর্চায় নিষ্ণাত ব্যক্তিদের মধ্যেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে যজুর্বেদেরই এক নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তর, সর্বপ্রথম তাদের মধ্যেই যথার্থ অনুষ্ঠানের উদ্দেশে গ্রথিত প্রত্নকথাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাওয়া যায়। প্রত্নকথাগুলির এইরূপ সারাংশ প্রণয়নের উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠান-চর্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যাদান এবং সেই সঙ্গে যজ্ঞের প্রত্নপৌরাণিক তাৎপর্য নির্ণয়।
বৈদিক জনসাধারণের চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও কার্যাবলির আধ্যাত্মিক কাঠামোটি যদিও সংহিতা ও ব্রাহ্মণ থেকে অনুমানলব্ধ সিদ্ধান্তরূপে আবিষ্কার করা সম্ভব, তবু এই ধরনের আনুমানিক সিদ্ধান্তের যোগফল পর্যাপ্ত হয় না। এর একটি কারণ এই যে, প্রাচীন গ্রিকদের মতো বৈদিক আর্যরাও আরও অনেক দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত বিশ্বাসের একটি স্পষ্ট রূপ দিতে আগ্রহ বোধ করেননি। অন্য ভাবে বলা যায়, তখনও তাঁদের ধর্মীয় ধ্যানধারণাগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। সমাজ হয়তো বা কতকটা অজ্ঞাতসারেই সেই সব গ্রহণ করে তার অংশভাক্ হয়েছিল, যদিও সমস্তই তখনও সামূহিক অবচেতনের স্তরে নিমজ্জিত। কালক্রমে আরও নানা উপাদান এর সঙ্গে যুক্ত হল। কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরই তা সচেতন স্তরে উন্নীত হয়ে আধ্যাত্মচিন্তার প্রণালীবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করল। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে অর্থাৎ দশম মণ্ডল ও প্রথম মণ্ডলের শেষাংশ রচিত হওয়ার সময়ে দার্শনিক ভাবনার প্রথম স্ফূরণ হয়; নবীনতর ব্রাহ্মণ ও প্রাথমিক উপনিষদগুলিতে তারই পরিণত রূপ পরিগ্রহণ।
নীতিবোধ
প্রত্নকথাগুলিতে এই বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়েছে যে, সৃষ্টিতে কোনও নীতিহীন বিশৃঙ্খলা নেই; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মে শাসিত। বিশ্বজগতের অন্তলীন সাম্যবোধ বিপর্যস্ত করার জন্য কিছু কিছু শক্তি সক্রিয়; বিধ্বস্ত ঐক্যবোধকে পুনর্বিন্যস্ত করার অনিবার্য আবশ্যিক প্রেরণা থেকে প্রত্নকথাগুলির জন্ম। সৃষ্টির মূলগত ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেবতারা মানুষের ওপর অর্পণ করেছিলেন বলেই মানব জীবন একটি কেন্দ্রীভূত বিশ্ববোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই আধ্যাত্মবাদী প্রবণতা থেকেই এক মহৎ নীতিবোধের জন্ম হয়েছিল; তাই অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক মানসিকতাই তৎকালীন সমাজে একমাত্র স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠল এবং প্রত্যেক তাৎপর্যপূর্ণ মানবিক কার্যই হয়ে উঠল ধর্মাচরণের অঙ্গ। যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রত্যেক অনুপুঙ্খ প্রত্ন-পৌরাণিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে নীতিবোধের বিচিত্রগামী অভিব্যক্তিতে নূতন একটি মাত্রা যোগ করল। ঋগ্বেদের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশদ তথ্য সেই সমস্ত সূক্তে পাওয়া যায় যেখানে দেবতা এবং মানুষকে ধৈর্য, দান, ঋজুতা, দয়া, অতিথিপরায়ণতা ও সহযোগিতা জাতীয় গুণাবলির জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র কিংবা অশ্বীদের মতো দেবতারা পূর্বোক্ত গুণগুলির জন্যই মহৎ; বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে জীবনকে সার্থক ভাবে সমন্বিত করার প্রেরণা তাঁরা দিয়েছেন; সেই সঙ্গে বিপদ, ক্ষুধা, ব্যাধি, অন্ধকার ও মৃত্যুর কবল থেকে জীবনকে মুক্ত করার যথার্থ পথও তাঁরা নির্দেশ করেছেন। বিশেষত ঋগ্বেদে আলোর জন্য নিরন্তর তৃষ্ণা বারে বারে ব্যক্ত হয়েছে, কেননা, বৈদিক আর্যদের নিকট এই আলো একই সঙ্গে জ্ঞান, উপলব্ধি, আনন্দ ও জীবনের প্রতীক। ঋগ্বেদের সেই বিখ্যাত প্রার্থনা স্মরণীয়: ‘উদয় সূর্যকে যেন অমরা চিরদিন দেখতে পাই’। ঋগ্বেদের নীতিবোধের মূল প্রেরণাই এই যে, জীব অমূল্য এবং মূলত কল্যাণময়, মধুর ও উপভোগ্য বলেই এই আশ্চর্য রহস্যময় জীবনকে যতদিন পর্যন্ত সম্ভব, উপভোগ করাই বাঞ্ছনীয়।
প্রত্নকথা
মহাসময়ের যে ঊষাকালে সৃষ্টির উৎস হয়েছিল, প্রত্নকথাগুলিতে তারই প্রতীকী বিবৃতি। বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডের তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধানের ফলেও কিছু কিছু প্রত্নকথা উদ্ভূত হয়েছিল। সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য দেবতারা যে সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, সমাজের প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করার জন্য সেই সমস্ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানই পুনরায় যজ্ঞের মধ্যে প্রবর্তন করে। প্রত্নকথাগুলির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্নপৌরাণিক সময়ে পার্থিব জীবন ছিল বিঘ্ন-সঙ্কুল, তাই দেবতারা নানা যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত অমঙ্গলকে দূর করতেন। অনুরূপ বিপদের আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েও মানুষ পুনরায় নূতন করে প্রাচীন দৈব যজ্ঞগুলি অনুষ্ঠান করে।
বেদের ধর্ম স্পষ্টতই বহু দেববাদী; ক্ষমতার ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত এই সব দেবতাদের প্রত্যেকেই কখনও না কখনও শ্রেষ্ঠ দেবরূপে বন্দিত হয়েছেন। বৈদিক জনগণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য থেকে কয়েকজন দেবতাকে আহরণ করে সঙ্গে এনেছিলেন; ভারতে উপনীত হওয়ার পথে নানা জনগোষ্ঠী থেকেও কিছু কিছু দেবতাকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং এই উপমহাদেশে বসতি স্থাপনের পরে এখানকার প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলে আরও কিছু দেবতাকে সৃষ্টিও করেছিলেন। যেহেতু প্রথম দুটি স্তরে তাদের জীবন ছিল মূলত পশুচারী, তাই ঐতিহ্যগত অধিকাংশ দেবতাই পশুপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত আকাশদেবতা ও সূর্যদেবেরই বিভিন্ন রূপ। পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে মধ্যবর্তী স্তর ছিল নিরন্তর সংগ্রাম ও পরিক্রমার কর্মবহুল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁরা তখনও পশুচারী; কিন্তু তখন ধন আহরণের আর একটি নূতন উপায়— লুণ্ঠন— তাদের জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে। যাত্রাপথে যত কৌম ও গোষ্ঠীকে তাঁরা পর্যুদস্ত করেছিলেন, তাঁদের ধন আত্মসাৎ করেই নূতন ভূমি অন্বেষণে তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন।
ভারতবর্ষে বসতি স্থাপনের পরে প্রাগার্যদের কৃষিকর্মের প্রভাবে ধীরে ধীরে আর্যরা কৃষিজীবী হয়ে উঠলেন এবং পশুপালন হল তাদের ধন ও খাদ্য সংগ্রহের পরিপূরক উৎস। যাস্ক যে ত্রিবিধ দেবতার কল্পনা করেছিলেন, তার সঙ্গে উপরোক্ত আলোচনায় মোটামুটি একটা ঐক্য রয়েছে। আপাতত বলা যেতে পারে যে, আকাশদেবতা ও প্রাচীনতর সৌরদেবগণ বৈদিক আর্যদের সামূহিক জীবনের সেই স্তরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন তাঁরা পিতৃভূমি ত্যাগ করে নিশ্চিন্তে পশুপালনের জীবনে অভ্যস্ত। তার কিছু পরে কিছু বর্ষণ ও বজ্রের দেবতা নিরন্তর সংঘর্ষমুখর সেই জীবনে উদ্ভূত হয়েছিলেন, তখন দীর্ঘতম যাত্রাপথে তাঁরা ইয়োরোপীয় ভূখণ্ড থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে আবির্ভূত হলেন শস্যের ও পাতালের অধিষ্ঠাতা দেবগণ; অবশ্য, প্রাচীনতর পর্যায়েও কোনও না কোনও আকারে তাঁদের উপস্থিতি আভাসিত হয়েছিল; বিশেষত অন্তিম সংস্কার ও পরলোক বিষয়ক দেবতারা প্রাচীনতর পর্যায়ে উপস্থিত থাকলেও কৃষিজীবী রূপে আর্যদের প্রতিষ্ঠা লাভের পরেই তাঁরা নতুন এক তাৎপর্য নিয়ে অভিনব সজীবতার সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৈদিক দেবসঙ্ঘে অধিকাংশ প্রাচীনতর দেবতাদের অবস্থান সুরক্ষিত হলেও তাঁদের মধ্যে গৌরবের আসনগুলি প্রায়শই বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল। কৃষিজীবী জনতারূপে তাঁরা বিশেষ ভাবে শস্য সমৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই শস্যের ও পাতালের দেবতা এবং পিতৃলোকের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক, কেননা তাঁরা কৃষির জন্য উপযোগী ভূমির উর্বরতাকে নিশ্চিত করতে উৎসুক ছিলেন। সব প্রাচীন সভ্যতাতেই ভূমির উর্বরতা বিধান করেন ভূমির অধিষ্ঠাতা দেবতা, পরলোকগত আত্মারা ও পাতালের অধিষ্ঠাতা দেবতারা। অগ্নির সঙ্গেও এঁদের একটি প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। পশুচারী আদিযুগে তাই দ্যৌঃ ও সূর্যই প্রধান দেবতা, পথপরিক্রমা এবং যুদ্ধের যুগে ইন্দ্ৰ, বায়ুবাতাঃ, পর্জন্য, এঁরাই প্রধান এবং স্থিতিশীল কৃষিজীবী যুগে অগ্নি, নিঋতি, ভূমি, প্রজাপতি, যম ও পাতালবাসী কিছু দেবতা প্রাধান্য লাভ করেন। কৃষিজীবী স্তরে আর্যরা নির্দিষ্ট সময় মতো বৃষ্টি এবং আবহাওয়াজনিত বিপত্তি নিবারণের জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষ ভাবে উদ্ভিদজগতের অধিষ্ঠাতা দেবতা, সৌর ও বর্ষণের দেবতাদের প্রয়োজনও তাঁদের পক্ষে এখনও ছিল অপরিহার্য; এঁরা শুধুমাত্র অঙ্কুরোদগমের পক্ষে প্রয়োজনীয় উত্তাপই দান করবেন না, মেঘ ও বৃষ্টি সৃষ্টি করে পরোক্ষ ভাবে বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণও করবেন।
পশুপালক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত আকাশের দেবতারা ছিলেন মূলত নিষ্ক্রিয়। সম্ভবত, এই পর্যায়েও কোনও ধরনের পিতৃদেব-পূজা বৈদিক আর্যদের ধর্মচর্যার অঙ্গ ছিল, কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সামান্য, শুধু কিছু পরোক্ষ প্রমাণই রয়েছে। একই ভাবে মাতৃকাদেবী এবং পাতাল ও শস্য অধিষ্ঠাতা দেবতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমরা অনায়াসে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি, যদিও তা শেষ পর্যন্ত অনুমান-নির্ভরই থেকে যায়। যাযাবর জীবনের বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতারা যুক্ত হয়েছিলেন পূর্বপ্রতিষ্ঠিত দেবসঙ্ঘের সঙ্গে। তাঁদের উপর প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারী আর্যদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় প্রত্ন-পৌরাণিক রূপান্তরের ছায়াপাত ঘটেছে। ভূমির উর্বরতা, পশুপ্রজনন ও সন্তান-বৃদ্ধির পরিপোষক উর্বারতাবিধায়ক দেবতারা এবং সেই সঙ্গে মাতৃকাদেবী, পাতাল ও শস্য অধিষ্ঠাতা দেবতারা ও আঞ্চলিক জীবনের অভিভাবক দেবতারা একত্র সম্মিলিত হয়ে বৈদিক দেবসঙ্ঘকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋগ্বেদে নৈসর্গিক উপাদানসমূহের উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে প্রত্নপৌরাণিক পদ্ধতিতে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেবগোষ্ঠীর মতো বৈদিক দেবতাদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির উপদেবতাদের অস্তিত্বও লক্ষ করা যায়, যেমন, অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, প্রভৃতি। নৈসর্গিক উপাদানের উপর দেবত্ব আরোপিত করে বৈদিক আর্যরা যাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরাই ঋগ্বেদের দেবগোষ্ঠীর প্রাচীনতর স্তর; পরবর্তিকালে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচিত্র চরিত্র ও ভূমিকাযুক্ত দেবতাদের সৃষ্টি হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের অনিবার্য পরিবর্তনশীল প্রয়োজনে দেবতাদের নিরন্তর উত্থান ও বিলয় ঘটেছে। বস্তুত জনসাধারণের সামাজিক অর্থনৈতিক ও অস্তিত্বের নিগূঢ় স্তরে অনুভূত প্রয়োজনের প্রেরণাতেই দেবতাদের সৃষ্টি।
ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়ে এমন কিছু দেবতার উৎপত্তি ঘটেছিল যাঁরা কোনও প্রকৃত ধর্মচর্যা বা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ভাবে যুক্ত ছিলেন না; বিমূর্ত আদর্শায়িত রূপেই শুধু তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। যদিও যজ্ঞের সঙ্গে সম্পূর্ণত সম্পর্কহীন কোনও দেবতা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, তথাপি ঋগ্বেদ রচনার শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপিত না হয়ে নিতান্ত বিমূর্ত ধারণার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে।
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত তাত্ত্বিক ও নিরুক্তকার যাস্ক বৈদিক দেবতাদের বাসস্থান অনুযায়ী তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করেছিলেন: পৃথিবী নিবাসী, অন্তরীক্ষ নিবাসী ও দ্যুলোক নিবাসী। তবে মনে হয় যে, যাস্কেরও অগোচরে এই শ্রেণিবিন্যাসের পশ্চাতে বর্ণভেদগত ধ্যানধারণাও সক্রিয় ছিল। সামূহিক আযমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণের ভিন্নমুখী ভূমিকা অনুযায়ী দেবতাদেরও শ্রেণিবিন্যাস কল্পনা করেছিল। ব্রাহ্মণশ্রেণি সমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন না, তাঁরা যাজকতান্ত্রিক গ্রন্থরচনা ও যজ্ঞকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই, সমাজের প্রতি তাঁদের অবদান ছিল মুখ্যত আধ্যাত্মিক সমগ্র গোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা পুরণে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মহান আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ও সর্বজনকল্যাণকর ‘তপঃ’ সৃষ্টি ও স্থিতির প্রতিভূ হয়ে উঠল এবং ব্রাহ্মণ বর্ণটিও দেবতাদের পার্থিব প্রতিরূপ হয়ে উঠলেন।
ঋগ্বেদে যে সমস্ত দেবতা প্রাচীনতম স্তরের প্রতিভূ এবং ইন্দো-ইয়োরোপীয় দেবগোষ্ঠীর প্রভাবজাত, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, দ্যৌঃ, সূর্য, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ঊষা, যম, ভগ, অংশ, দক্ষ, অর্যমা, বিবস্বান, মার্তণ্ড, অশ্বীরা, অদিতি, প্রভৃতি। ইন্দো-ইয়োরোপীয় আকাশের দেবতাদের মদ্যে দৌঃ-ই প্রাচীনতম এবং সর্বত্রই পশুপালক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক; কেননা সভ্যতার ঊষাকালে সেই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ আকাশের অনন্ত বিস্তার ও সর্বব্যাপিতা অবলোকন করে গভীর বিস্ময় ও আতঙ্কে নিমগ্ন হত। পৃথিবী আকাশদেবের পত্নীরূপে পরিকল্পিত। সৌরদেবগণ যে আদিত্য বা অদিতি-পুত্র রূপে কল্পিত হয়েছেন তারও মূলে আছে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য। তাঁদের মধ্যে মুখ্যতম হলেন সূর্যদেব; ইনি স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও উর্বরতা দানের জন্য বন্দিত হয়েছেন। এ ছাড়াও সাধারণ মানুষ সৌরদেবতাদের নিকট ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, শস্য, আরোগ্য, পরমায়ু, জ্ঞান ও আত্মিক উন্মেষ প্রার্থনা করত।
প্রথম পর্যায়ে বরুণও ছিলেন আকাশেরই দেবতা; পরবর্তী স্তরে তিনি হলেন নৈশ আকাশের অধিষ্ঠাতা, নক্ষত্রপুঞ্জ যাঁর চোখ। এই স্তর পর্যন্ত প্রত্ন-পৌরাণিক স্বরূপের চেয়েও তাঁর নৈতিকতার দিকের প্রবলতর অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। নক্ষত্ররূপ চক্ষু দ্বারা মানুষের গোপন পাপ তিনি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন এবং প্রয়োজন মতো শাস্তিবিধানও করেন। মানুষের আচার-আচরণের প্রতি এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত এবং বিচারক ও শাস্তিদাতার ভূমিকায় বরুণদেব ভীতি ও সম্ভ্রম উৎপাদন করেন; বস্তুত তিনিই একমাত্র দেবতা যাঁর ভাবমূর্তিতে একটি নৈতিক মাত্রা যুক্ত হয়েছে। পরবর্তিকালে তিনি সৌরদেবমণ্ডলী অর্থাৎ আদিত্যগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। গ্রিক দেবতাদের মধ্যে তাঁর প্রতিরূপ পাই উরানস-এ এবং নীতিবিদ বিচারকের ভূমিকায় প্রাচীন পারসিক পরম দেবতা অহুর-মজদার সঙ্গেও তিনি তুলনীয়। প্রায়শ মিত্রদেবের সঙ্গে দ্বৈরথরূপে মিত্রবরুণ দিন ও রাত্রির আকাশের অধিষ্ঠাতা। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে পড়ায় তিনিই প্রথম কল্পিত এবং পরে সাধারণ ভাবে সমুদ্রের অধিদেবতা হয়ে ওঠেন। বরুণদেবের শারীরিক বর্ণনা অস্পষ্ট ছিল বলেই তাঁর ভূমিকার এই কৌতূহলজনক রূপান্তর সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। যথাক্রমে রাত্রিকালীন আকাশ, অস্তায়মান সূর্য, দৈব জলরাশির অধিরক্ষক এবং সমুদ্রের অধিষ্ঠাতা রূপে তাঁর বিবর্তন ক্রমে সম্পূর্ণ হয়েছিল। পশুপালক সমাজের স্বাভাবিক দেবতা থেকে কৃষিনির্ভর সমাজোর দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাসই এর মধ্যে বিধৃত আছে। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় কৃষিজীবী আর্যদের পক্ষে আর্থিক ভাবে কল্যাণপ্রসূ ভূমিকা নিয়েই বরুণ আপন ক্ষমতা অটুট রেখেছিলেন; আর্যদের কল্পনায় দৈব জলরাশির রক্ষক রূপে উপযুক্ত ঋতুতে তিনি ছিলেন বৃষ্টিপাতের নিয়ন্তা। তেমনই পরবর্তী বাণিজ্যিক উদ্যোগের যুগে সমুদ্রযাত্রী বণিকদের কল্পনায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সপ্তসমুদ্রের অধিপতি।
এক দিক দিয়ে দেখলে সমগ্র ঋগ্বেদীয় কাব্যের ভাবকেন্দ্রে রয়েছে সূর্য ও সৌরদেবগণের বন্দনা। সূর্যরূপে আদিত্য আলো, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির উৎস, সবিতারূপে ধীশক্তির প্রেরয়িতা ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের মোচনকারী। মিত্ররূপে আদিত্যের বন্ধুত্বের ভূমিকা লক্ষণীয়। এ ছাড়া রয়েছে, ভগ, অর্যমা, অংশ ও দক্ষের মধ্যে আদিত্যদের অধস্ফুট ভাবমূর্তি। সম্ভবত, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে আর্য দেবগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের স্পষ্টতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ অটুট ছিল। দাম্পত্যজীবনের শান্তি ও জন্মপ্রক্রিয়া ছাড়াও পত্নী এবং মাতারূপে মহিলাদের ভূমিকার সঙ্গে ভগদেবের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। দক্ষের ভূমিকা খুব স্পষ্ট নয়, তিনি হয়তো বা কারুজীবীর ইষ্টদেবতা ছিলেন। তেমনই অংশ দেবতারূপে সম্পূর্ণ ছায়াবৃত: ভগ, দক্ষ ও অর্যমার সঙ্গে সামূহিক ভাবেই শুধু তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণকারী দেবতা রূপে তখনই অর্যমার উদ্ভব ঘটেছিল, যখন অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে আর্যরা বসতি স্থাপন করছিলেন। অদিতিকে পাওয়া যায় সৌরদেবতাদের আদিমাতারূপে। বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপের বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও পর্বতনিবাসী দেবতারূপে ঋগ্বেদে তিনি নিতান্তই গৌণ দেবতা: তাঁর উদ্দেশে মাত্র তিনটি সূক্ত নিবেদিত। তবে তাঁর মধ্যে সূর্যের ত্রিবিধ গতির প্রকাশ ঘটছে। ধাতা ও বিবস্বান সৌরদেবরূপে অ্যন্ত অস্পষ্ট; তবে সম্ভবত ধাতা সূর্যদেবের সৃজনশীল দিক এবং বিবস্বান তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে প্রকাশের প্রতীক। অন্য দিকে মার্তণ্ড সম্ভবত অস্তায়মান সূর্যের প্রতিনিধি। যাই হোক, আর্যদের সৌর দেবমণ্ডলীর মধ্যে আদিত্যরাই প্রাচীনতম গোষ্ঠী; ভারতবর্ষে প্রবেশ করার সময় এঁদের অধিকাংশই আর্যমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্পষ্টতই আদিত্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে মাস ও ঋতুভেদে এবং উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সূর্যের বিভিন্ন অবস্থানের অভিব্যক্তি ঘটেছে।
পূষা নিতান্ত পরোক্ষ ভাবে সৌরদেবমণ্ডলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত; আর্যরা যখন যাযাবর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল, ভূমির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না থাকার ফলে বৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের জন্য উর্বরতার অন্য স্থায়ী উপাদান অর্থাৎ সূর্যের উত্তাপের উপরই তাদের নির্ভর করতে হত। আর্যসভ্যতার যাযাবর পশুপালকস্তরে গো-সম্পদের রক্ষকরূপেও পুষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পূষাকে ‘অঘৃণি’ অর্থাৎ জ্বলন্ত বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে, তাতেই সূর্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আভাসিত। অবয়বগত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্যও পূষা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। কেননা, তিনি রথের পরিবর্তে ছাগবাহন, তাঁর চুল বেণীবদ্ধ, ‘করম্ভ’ অর্থাৎ যবচূর্ণমিশ্র তাঁর খাদ্য। এতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার পথে আর্যরা খুব সম্ভবত মোঙ্গোলিয়ার মধ্যে দিয়ে যখন এসেছিলেন সেই সময়ে মোঙ্গোলীয় আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভাসযুক্ত বিশিষ্ট কোনও দেবতার কল্পনা তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন। সুদীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন দুর্গম ভূমিতে পথভ্রষ্ট গো-সম্পদের পুনরুদ্ধার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই গোসম্পদের পুনরুদ্ধারকারী দেবতারূপে পূষার আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কালক্রমে তিনি পথিক মানুষ ও বিচরণশীল পশুর পথপ্রদর্শক দেবতার ভূমিকাও গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তা মৃত্যুলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মরণোত্তর লোকে প্রয়াত আত্মা যাতে পথভ্রষ্ট না হয়, তার জন্যও পূষার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।
ঊষা ঋগ্বেদে সবচেয়ে সুললিত বর্ণনায় সমৃদ্ধ কিছু সূক্তের উদ্দিষ্ট দেবী। প্রতিটি প্রভাতই স্বভাবত অতিসূক্ষ্ম ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের আভাস আনে। দেবী ঊষা তাই ঋষিকবিদের বর্ণনায় পরমা সুন্দরী, সজীব ও চিরতরুণী; রক্ত পরিচ্ছদে তাঁর যৌবন সঞ্জীবক ও দ্যুতিময়। তিনি জীবজগৎকে প্রতিদিন সকালে নিদ্রা থেকে জাগরিত করে দৈনন্দিন কর্তব্যে প্রেরণা জোগান। ঊষা নিজের চিরতারুণ্য অক্ষুণ্ণ রেখেও মানুষকে দিনে দিনে বার্ধ্যক্যের অভিমুখে প্রেরণ করেন। ঊষাকে সূর্যের মাতা, কন্যা বা পত্নীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবীর সক্রিয় ভূমিকা অপেক্ষা তাঁর কাব্যিক ভাবমূর্তি সূক্তগুলিতে অধিক অভিব্যক্ত। নূতনতর তৃণভূমির সন্ধানে সতত বিচরণশীল পশুপালক জনগোষ্ঠীর জন্য নিসর্গদৃশ্য স্বাভাবিক ভাবেই ছিল এক পরিবর্তনশীল উপাদান; একমাত্র স্থায়ী উপাদান হল আকাশ, বায়ু ও সৌরদেবমণ্ডলী। তাই মনে হয় যে, আর্যদের সামূহিক জীবনের প্রাচীনতর পর্যায়েই ঊষাসূক্তগুলি রচিত হয়েছিল; সম্ভবত ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার সময় আর্যরা এই সব রচনা সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন প্রাথমিক স্তরে ঊষাসূক্তগুলির কোনও যজ্ঞীয় প্রয়োগ ছিল না।
সোমদেব চন্দ্র রূপে অন্তরীক্ষে বিরাজিত এবং উজ্জ্বল ও জ্যোতিষ্মান রূপ ছাড়া তাঁর দেবত্ব নিতান্তই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। উদ্ভিদ সোম বর্ণনায় কোনও দেবত্ব আরোপ করা সম্ভব নয়। যদিও ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে সোমরসের মাদকতাই যেন উদ্ভিজ্জ সোমের উপর আরোপ করেছে। এখানে সোম থেকে রস নিষ্কাশনের যে বর্ণনা সোমপায়ীর দীপ্ত কল্পনা তাকে এক তুরীয় লোকে নিয়ে গেছে।
যম প্রেতলোকে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার হিতকারী অভিভাবক। তিনি মৃত ব্যক্তিদের দেবতা; পরবর্তী সাহিত্যে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অধিদেবতা রূপে যমের যে ভাবমূর্তি, তা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে তিনিই প্রথম মৃত্যুলোকে প্রয়াণ করেছিলেন। বস্তুত ঋগ্বেদে তাঁর প্রসন্ন ও আনন্দময় অভিব্যক্তিই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। পার্থিব জীবনের দীর্ঘায়িত প্রতিরূপ হিসাবেই কল্পিত হয়েছে পরলোক, তবে এ সংক্রান্ত কাহিনিগুলিতে এই কল্পনার প্রকাশ অস্পষ্ট ও পারম্পর্যহীন, কেননা ঋগ্বেদের সর্বত্রই পার্থিব জীবনই একান্ত ভাবে আকাঙ্ক্ষিত। যাই হোক, তখনও পর্যন্ত পরলোক কোনও যন্ত্রণার ক্ষেত্র নয় এবং যমদেব প্রয়াতদের সদয় সত্ত্বাধিকারী ও তাদেরই পূর্বপুরুষ। যমযমীর সংলাপমূলক বিখ্যাত সংবাদসূক্তটি (১০:১০) সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক: যমী তার যমজ ভ্রাতা যমকে প্রণয় নিবেদন করছেন এবং যম তা প্রত্যাখ্যান করছেন। দশম মণ্ডল রচনার সময়ে অজাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক বিধিনিষেধ যেহেতু অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়েছিল তাই যম ও যমীর দীর্ঘ বাদানুবাদের অতি সামান্য অংশই সংরক্ষিত হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত এই জাতীয় প্রত্নকথাগুলির সঙ্গে তুলনায় আমরা বুঝতে পারি যে, আদিম মানুষের মধ্যে অজাচার মানবজাতির সৃষ্টির আবশ্যিক পূর্বশর্ত রূপেই বিবেচিত হত।
অশ্বীরা যমজ দেবতা। এই দুই ভ্রাতা নাসত্য ও দস্র নামেও পরিচিত। এই নাসত্য নামটিও খ্রিস্টপূর্ব চতুদর্শ শতকের মিতান্নি ও হিট্টাইটদের সন্ধির সমকালীন কেননা তৎকালীন বোঘাজকোঈ থেকে প্রাপ্ত সেই বিখ্যাত সন্ধিপত্রে মিত্র বরুণ ও ইন্দ্রের সঙ্গে নাসত্যের নামও উল্লিখিত হয়েছে। গ্রিক প্রত্নকথাতেও এই যমজ দেবতার প্রতিরূপ লক্ষ করি ক্যাস্টর ও পলিডেউকিস-এর মধ্যে; আবার রোমান প্রত্নকথায় তাঁরা ক্যাস্টর ও পোলাক্স নামে বিখ্যাত। উত্তর ইয়োরোপের পুরাণে এঁরা দিবো দিওয়ালি বা দিবো সুনেলেই নামে পরিচিত। আদিত্যদের মধ্যে একমাত্র অশ্বীরাই বিভিন্ন সংকট, অসুস্থতা, অগ্নিকাণ্ড ও জলনিমজ্জন-এর মতো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে শারীরিক ভাবে মানুষের সহায়তা করে থাকেন। তাঁদের রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা প্রত্যক্ষগোচর; অন্যান্য সৌরদেবরা সাধারণত উদ্যমহীন, শুধুমাত্র অশ্বীরা প্রবল ভাবে সক্রিয়। তাঁরা সূর্য এবং মধুকে রথে বহন করে নিয়ে আসেন। অশ্বীদের পরিচয়বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যাস্ক বলেছেন যে, বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের কাছে এই যুগলদেবতা দিন ও রাত্রি, আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিনিধি; আবার যাস্ক বলেছেন যে, তাঁরা পুণ্যকৃৎ নৃপতি; অর্থাৎ জনকল্যাণকারী ঐতিহাসিক রাজাদেরই দেবত্বে উপনীত রূপ। সম্ভবত তাঁদের মানবিক পরিচয় স্পষ্ট হওয়ার জন্যই পরবর্তী প্রত্নকথাগুলিতে দেবভোগ্য সোম থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (অশ্বের অধিকারী) বিশ্লেষণ করে মনে হয়, আর্যদের মধ্যে তাঁরা ছিলেন প্রাচীনতম অশ্বারোহী।
অন্তরীক্ষের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই প্রধান; বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহে বীরত্ব প্রদর্শনের দ্বারা তিনি স্পষ্টতই ক্ষত্রিয় সেনাপতির দেবরূপ। অন্তরীক্ষ বিষয়ক দেবতাদের মধ্যে তাঁর সহায়ক বায়ুবাতাঃ, পর্জন্য, রুদ্র ও মরুৎগণ। তাদের প্রত্যেকেই যোদ্ধা, শত্রু-ধ্বংসকারী বিজয়ী; তাঁরা ক্ষমতাশালী ও বীর, ভীতি-উৎপাদক ও পৌরুষদীপ্ত। বীরত্বের জন্য এই সব দেবতা প্রশংসিত; সেই সঙ্গে জয়লাভের জন্যও তাঁদের নিকট প্রার্থনা জানানো হয়। বায়ুবাতাঃ ও পর্জন্য যথাক্রমে বাতাস, ঝড় ও বজ্রপাতের দেবায়িত রূপ। বৈদিক বায়ু দেবতার মধ্যে এক দিকে যেমন আছে প্রাণধারণের অপরিহার্য উপাদান বায়ু, অন্য দিকে তেমনই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের শক্তিও। প্রকৃতপক্ষে বায়ুবাতাঃ শব্দবন্ধে এই দুটি বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়; প্রথমটি বায়ু, দ্বিতীয়টি বাত্যা বা ঝড়ের বাতাস। মৃ-ধাতু নিষ্পন্ন মরুৎ শব্দের মধ্যে রয়েছে ভয়ংকরের দ্যোতনা। মৃত আত্মার সঙ্গে মরুৎগণ সম্পর্কিত; বজ্র ও বিদ্যুৎ এঁদের অস্ত্র হওয়াতে এঁরা ঝড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সিংহের ন্যায় গর্জনশীল মরুৎগণ উত্তরদেশের অধিবাসী, পৃষতী মৃগ তাঁদের বাহন এবং তীক্ষ্ণ ও বর্ষণোন্মুখ ধারা যেন তাঁদের লৌহনির্মিত দণ্ডরাজি। অরণ্যের বৃক্ষশ্রেণি যখন তাঁদের প্রবল আঘাতে উন্মুলিত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, মনে হয় যেন পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে শক্রপক্ষ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। রুদ্র ও পৃশ্নি মরুদগণের পিতা ও মাতা এবং ইন্দ্র তাঁদের ভ্রাতা। যজুর্বেদের পর্যায় থেকে মরুৎদের ভীতিপ্রদ বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তুলনামূলক ভাবে বায়ুদেবরূপে পর্জন্যের ভাবমূর্তি কতকটা অস্পষ্ট; মৌসুমি বায়ুজনিত বৃষ্টিপাতের অগ্রদূতরূপে তাঁর সামান্য কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপঃ দেবতার ভাবমূর্তির পশ্চাতে রয়েছে আকাশে প্রচ্ছন্ন একটি কাল্পনিক জলাধার। আপঃ বা জলরাশিকে কখনও কখনও উচ্চতম স্বর্গে নিবদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও বা অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন বলা হয়েছে। এই সব উৎস থেকে জীবন ও পরিপুষ্টিদায়ক সজীব বৃষ্টিধারারূপে অবতরণ করে তা শস্যে পুষ্টিসঞ্চার করে।
ঋগ্বেদে রুদ্র একজন গৌণ দেবতা; তাঁর উদ্দেশে তিনটি মাত্র সূক্ত নিবেদিত। যদিও রুদ্রের ক্ষতিকর বাণবর্ষণের কথা বলা হয়েছে, তবু সাধারণ ভাবে তিনি অন্যান্য ঋগ্বেদীয় দেবতার মতোই কল্যাণপ্রদ— আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অন্যদের থেকে কিছুমাত্র পৃথক নন। রথে আরূঢ় এই দেবতাটির গলায় সোনার হার এবং হাতে তির-ধনুক। কিন্তু তাঁর মধ্যে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই যজমানের সন্তান, আত্মীয় ও গোসম্পদের ক্ষতি না করার জন্য প্রায়ই তাঁর নিকট আর্ত, করুণ, মিনতি ও প্রার্থনা জানানো হয় এবং সেই সঙ্গে যজমানের শত্রুদের ধ্বংস করারও অনুরোধ জানানো হয়। তাঁর ভাবমূর্তির মধ্যে কৌমজীবনের পৃষ্ঠপোষক দেবতার রূপ প্রচ্ছন্ন — প্রতিবেশীদের অকল্যাণের বিনিময়ে, প্রয়োজনবোধে অনৈতিক ভাবে যিনি নিজ কৌম ও গোষ্ঠীর কল্যাণসাধনে প্রয়াসী হচ্ছেন। তাঁর কল্পনার মধ্যে যে দ্বৈধতা রয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এবং মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে রুদ্র-শিব দেবভাবনার উৎপত্তি; প্রাচীনতার দেবকল্পনায় যে বৈশিষ্ট্য ও সেই সঙ্গে অপূর্ণতা রয়েছে, পরবর্তী প্রত্নকথাগুলিতে তা ক্রমে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রাচীনতম রুদ্র ও পৃশ্নির সন্তানরূপে পরবর্তী রুদ্রগণের জন্ম। এঁরা নির্মম ও শক্তিশালী। যে মৌসুমিবায়ুজনিত বৃষ্টিপাতের সঙ্গে আর্যরা ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার পরেই প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন, এই রুদ্রদের গোষ্ঠী তারই প্রতিভূ। ঝড়ের মেঘের মতো রক্তবর্ণ রুদ্র ও চর্মনির্মিত জলাধার বা পৃশ্নি প্রকৃতপক্ষে মৌসুমিমেঘাবৃত বর্ষাকালীন আকাশের দ্যোতনা নিয়ে আসে। এটা স্পষ্ট যে, বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত দেবতাই মৌসুমি-বায়ু সৃষ্ট ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ আকাশের রক্তাভ দ্যুতি এবং বৃক্ষ উৎপাটনকারী ভয়ংকর ঝড়ে আন্দোলিত মেঘপুঞ্জের প্রতিনিধি। রুদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও রক্তিমাভার পরিচয় মেলে। সন্দেহ নেই, এই সব দেবকল্পনায় প্রকৃতি একটি অবয়বগত ভিত্তি নির্মাণ করেছিল আর আক্রমণকারী আর্য সৈন্যবাহিনীর পরাক্রম প্রত্নপৌরাণিক ভাবমূর্তি নির্মাণে সাহায্য করেছিল। তাই মৌসুমিবায়ুর বিভিন্ন রূপকে বায়ুবাতাঃ, পর্জন্য, রুদ্র, মাতরিশ্বা কিংবা মরুদণরূপে শক্তিশালী, অস্ত্রযুক্ত ও বিজয়ীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্নকথার প্রয়োজনে সৈন্যবাহিনীর জন্যে যে সেনাপতি প্রয়োজন, ইন্দ্র-কল্পনায় তারই অভিব্যক্তি।
ঋগ্বেদের এক-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি সূক্ত ইন্দ্রের প্রতি নিবেদিত; বৈদিক দেবসঙ্ঘে তাঁর অসামান্য গুরত্বই এতে প্রমাণিত হচ্ছে। অবয়ব সংস্থানের দিক দিয়ে ইন্দ্র উজ্জ্বল, তারুণ্যদীপ্ত, সুদর্শন, সুগঠিত হনু-যুক্ত; তিনি ‘সহসঃ সুনুঃ’ অর্থাৎ স্বয়ং শৌর্যের সন্তান; হরি নামক সুন্দর অশ্বসমূহ দ্বারা বাহিত রথে তিনি অরোহণ করেন। তাঁর অসংখ্য ও বিচিত্র বীরত্বপূর্ণ কার্যপলাপের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত। অন্য যে কোনও প্রধান বৈদিক দেবতার মতো ইন্দ্রকেও বিশ্বস্রষ্টা রূপে প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি গোসম্পদ দান করেন; পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেন খাদ্যসম্ভারে। ভারতের আদিম অধিবাসী অর্থাৎ ‘অসুর’ নামে পরিচিত সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগার্য জনতার সঙ্গে বহু সংগ্রামে বিজয়ী হয়েই ইন্দ্র তাঁর বিক্রমের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্ভব করে তোলেন। ইন্দ্রের যুদ্ধ জয়ের কাহিনি অস্পষ্ট বা নির্বিশেষ নয়; যে সমস্ত শত্রুর সঙ্গে ইন্দ্র যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তাদের সুনির্দিষ্ট ইতিহাসসম্মত নাম পাওয়া যায়। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রের প্রাচীনতম ভাবমূর্তির পশ্চাতে প্রকৃত একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল; আক্রমণকারী আর্যবাহিনীর সেনাপতিরূপে প্রাগার্যদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী অসংখ্য যুদ্ধে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ইন্দ্র শত্রুদের সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে ও তাদের শক্তির কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করেও ওই সব জনগোষ্ঠীর প্রধানদের বন্দি করেন, তাদের গোধন ও সম্পদ লুঠ করে নিয়ে নিজের অনুচরদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। সেই কৃষ্টিনেতারূপে ইন্দ্র আর্য জনগোষ্ঠীর আনুগত্য অর্জন করেন, পশুপালক যাযাবর আর্যদের কৃষিজীবীরূপে বিজিতের বাসভূমিতে বসতি স্থাপন করতে সাহায্য করে।
ইন্দ্ৰ যে বজ্র নামক অস্ত্র ব্যবহার করতেন, তা লৌহনির্মিত কোনও অস্ত্র বলেই মনে হয় এবং সেই কারণেই তা সেই ব্রোঞ্জের যুগে অপ্রতিরোধ্য ছিল। ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের পতনের পরে লোহা ব্যবহারের গোপন বিদ্যা ব্যাবিলনবাসীদের কাছ থেকে প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর্যদের মধ্যে ইন্দ্ৰই কেবলমাত্র বজ্রাস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং ব্রোঞ্জ ব্যবহারকারী সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের কাছে সেই অস্ত্রকে প্রতিরোধ করার মতো কোনও উপায় ছিল না। দীর্ঘকাল ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অগ্নি, বায়ু, মরুদণ, বিষ্ণু ও বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। গ্রিক প্রত্নকথার জেউস ও হেরার সঙ্গে ঋগ্বেদের ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী তুলনীয়। ইন্দ্রের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুরূপে উপস্থাপিত বৃত্র; অবশ্য বিজয়লব্ধ সম্পত্তি অর্থাৎ বৃষ্টি, আলোক, সম্পদ বা গোধন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে তাকে অনাবৃষ্টি বা অন্ধকারের অসুর কিংবা মানবদেহধারী শত্রুর নিধনকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবিক ভাবে ইন্দ্র সম্ভবত পরাজিত গোষ্ঠীপতির গোধন ও সম্পত্তি অধিকার করেছিলেন; হয়তো বা কখনও কখনও তিনি শত্রুদের জলাধার ও বাঁধ ধ্বংস করে সঞ্চিত জলরাশিকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের অন্যান্য শত্রুদের মধ্যে রয়েছে অহি (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী সম্ভবত বৃত্রেরই নামান্তর কিংবা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ব্যুৎপত্তি থেকে গ্রিক ‘অফিস’ অর্থাৎ সর্পের নাম), পিপ্রু উরণ, শুষ্ণ, প্রভৃতি। এরা সম্ভবত ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীগুলির নেতা, প্রত্যেকেই ইন্দ্রের দ্বারা পরাভূত বা নিহত। বহু যুদ্ধের বিজয়ী বীর রূপে ইন্দ্র ‘শতক্রতু’ বিশেষণে অভিনন্দিত হলেও তাঁর সর্বাধিক গৌরব নিহিত রয়েছে ‘বৃত্রহন’ পরিচয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অবেস্তায় ইন্দ্র ও বেরেথ্রগ্ন শব্দ দুটি পৃথক ব্যক্তির পরিচয় বহন করছে। অন্য দিকে ‘মঘবা’ শব্দের মধ্যে এই তথ্য প্রচ্ছন্ন যে, ইন্দ্ৰই প্ৰধান সম্পদদাতা।
ইন্দ্রের সঙ্গে প্রীতিপদ, উত্তেজক ও রমণীয় মাদকতা-উৎপাদক পানীয় সোমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই পানীয় ও তার উৎসকে কেন্দ্র করে যে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল এবং সোমপানের ফলশ্রুতিতে শত্রুজয়ের যে ঐতিহ্য পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছিল তারই প্রভাবে পরবর্তী যুগে সোমযাগ বিকশিত হয়; অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে পানীয় গ্রহণের রীতিও প্রচলিত হয়ে যায়। ঋগ্বেদীয় যুগের সঙ্গে ইন্দ্রের প্রাধান্য ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পরবর্তী সাহিত্যে ইন্দ্রের গৌরব ম্লান হওয়ার কারণ, ভারতভূমিতে আর্যদের চূড়ান্ত বিজয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে আর্য জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ, ভূমি ও গোধন অর্জন করার ঐতিহাসিক ভূমিকাও শেষ হয়ে গিয়েছিল।
প্রাচীনতর পারিবারিক মণ্ডলগুলিতে ইন্দ্ৰসূক্তসমূহের সুস্পষ্ট কাব্যিক সৌরভ রয়েছে; অধিকাংশই সাধারণ ভাবে যুদ্ধগীতি এবং এদের মধ্যে আমরা যেন অস্ত্রের ঝনৎকার ও বিজয়ীর সিংহনাদ ধ্বনিত হতে শুনি। প্রাগার্য গোষ্ঠীপতির ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা বা ‘মায়া’ অধিগত বলে তারা আর্যদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, কিন্তু ইন্দ্র ও তাঁর অনুচরদের নিকট এরা অসহায়। বহিরাগত আর্যদের শ্রেষ্ঠতর অস্ত্র ও বীরত্বের নিকট প্রাগার্য জনগোষ্ঠী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ সূক্তেই ইন্দ্রের বীরত্বের গৌরবজনক কাহিনিগুলোকে সামূহিক প্রত্নস্মৃতি থেকে তুলে এনে দেবতার আহ্বানসূচক স্তোত্র রূপে যুক্ত করা হয়, যাতে দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে জনগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রয়োজন অর্থাৎ সময় মতো বর্ষণ, প্রভূত পরিমাণ উত্তম শস্য, গোধন ও মানুষের উর্বরতা, বিজয়, ঐশ্বর্য ও দীর্ঘজীবন দান করতে পারেন। ঋগ্বেদের ইন্দ্র সর্বদা ন্যায় পথে চলেননি, যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজনে বহুবার তিনি ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু নীতিবোধ কখনওই কৃষ্টি-নেতার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য নয়, বিজয় অর্জনই তাঁর লক্ষ্য এবং সেখানেই তাঁর যথার্থ গৌরব। কেননা আর্য জনগোষ্ঠীর পক্ষে তখনকার সংগ্রাম জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই জনগোষ্ঠী তাঁদের ইন্দো-ইয়োরোপীয় আদি বাসভূমি থেকে দীর্ঘকালব্যাপী ভ্রমণের পথে বহু দূরে উপনীত হয়েছিলেন এবং দৃঢ় ও নিরাপদ বসতি স্থাপন তাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রের জয় তাঁদের শান্তি ও ঐশ্বর্যকে সুনিশ্চিত করেছিল বলে বৈদিকে দেবগোষ্ঠীতে তাঁর প্রাধান্য তর্কাতীত।
ঋগ্বেদের সূচনা ও সমাপ্তি হয়েছে অগ্নিবিষয়ক সূক্ত দিয়ে— গুরুত্বের দিক দিয়ে তিনি ইন্দ্রের ঠিক পরেই। প্রধানত তিনি দূতের ভূমিকা পালন করেন; তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবতাদের আহ্বান করে আনেন এবং তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য ও আহুতি বহন করে নিয়ে যান। অগ্নি উজ্জ্বল, পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ, সক্রিয় ও চিরতরুণ। তিনি পুরোহিত এবং সম্পদদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রত্নধাতম), এবং খাদ্য ও ধনের অধিকারী (বাজস্বৎ, অন্নবৎ, বসুমৎ)। তিনি ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ মিত্র। ‘দাতা শ্রেষ্ঠ’ বিশেষণটিতে সম্ভবত তাঁর দহনকর্ম, যুদ্ধনীতি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সূচিত হচ্ছে। অর্থাৎ বহিরাগত আর্যরা যখন প্রাগার্য ভূমি আত্মসাৎ করেন তখন তাঁরা অগ্নিসংযোগের দ্বারা শুধু যে জমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন তা-ই নয়, অগ্নিদহনে আরণ্যভূমি এবং ঊষর ক্ষেত্রকে কৃষির উপযোগীও করে তোলেন। অতএব অগ্নিই প্রকারান্তরে আর্যদের ধনদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। শতপথ ব্রাহ্মণের একটা বিবৃতি অনুযায়ী আর্যবসতি স্থাপয়িতাদের প্রথম প্রজন্ম অগ্নিকে অ-কর্ষিত ভূমিতে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন; অনার্যদের ভূমির অধিকার করার পূর্বে আক্রমণকারী আর্যরা বনভূমিতে অগ্নিসংযোগ করতেন। এ ভাবে নূতন ভূমি অধিকার করে তারা গোসম্পদ ও ধন লাভ করতেন। এই জন্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সর্বত্র অর্থাৎ আর্য জনগোষ্ঠীর বিজয় ও বিস্তারের প্রথম পর্বে অগ্নি তাঁদের প্রধান ধনদাতা দেবতা। আবার অগ্নি যেহেতু রাত্রে জ্বলন্ত প্রাচীর রূপে গোধনের নিরাপত্তা বিধান করতেন, সেহেতু এই উজ্জ্বল ও তারুণ্যদীপ্ত দেবতা আর্যদের যাযাবর জীবনে পশুসম্পদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবেই সম্পর্কিত ছিলেন, কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর অগ্নির সঙ্গে আর্যগোষ্ঠীর এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল, তাই অগ্নি সুদীর্ঘকাল ধরে মুখ্য দেবতা থেকেছেন।
আপ্রীসূক্তগুলি সম্ভবত অত্যন্ত প্রাচীন মন্ত্রসংগ্রহ, তবে এদের মৌলিক তাৎপর্যের বহুলাংশই আমাদের নিকট অজ্ঞাত। পশুযাগে আবৃত্ত এবং গীত এই আপ্রীসূক্তগুলিতে প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার সময় অগ্নিকে সুমিদ্ধ, পাবক, তনুনপাৎ, নরাশাংস, ইলা, বর্হিঃ, দ্বারো দেব্যাঃ, ঊষাসানক্তা, দৈব্যৌ হোতারৌ, ইত্যাদি নাম দিয়ে স্তব করা হয়েছে। এই সব বিশেষণের সূত্রাকারে প্রয়োগ সম্ভবত অতি প্রাচীনকালেই আরম্ভ হয়েছিল; অগ্নি তখন মানুষের রক্ষাকর্তা ও শুভার্থীদের অগ্রগণ্য ছিলেন। এই অগ্নি মানুষকে প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতাদের সন্নিকটে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দিবারাত্র তিনি সকল মানুষের সঙ্গে থাকতেন। ‘দৈব্যৌ হোতারৌ’ বা দৈব পুরোহিত রূপে অগ্নির বর্ণনা সম্ভবত অগ্নিচর্যার দুজন প্রাচীনতম পুরোহিত অর্থাৎ অথবা ও অঙ্গিরার দিকে ইঙ্গিত করছে। স্পষ্টতই অথবা ও অঙ্গিরাকে পরবর্তী ব্যাখ্যায় যথাক্রমে মঙ্গল ও অমঙ্গলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। এঁদের যে দু’ রকমের (শুভ ও অশুভ) ইন্দ্রজালের পুরোহিতরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তার সূত্রপাত হয়েছিল সুপ্রাচীনকালে। জাদু পুরোহিতরা পশুচারী জনগোষ্ঠীর মাংসের অর্ঘ্যযুক্ত প্রাথমিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। যজ্ঞীয় পশু বলিদানের অব্যবহিত পূর্বে অগ্নির দ্ব্যর্থবোধক বিশেষণগুলি সহ যে আপ্রীসূক্তগুলি প্রযুক্ত হত, তাতে সম্ভবত প্রাচীনতম পর্যায়ের মাংসাহূতি দানের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। পরবর্তী যুগে কৃষিজীবী সভ্যতার প্রবর্তনের পর নিরামিষ হব্যের প্রচলন হয়।
অগ্নি যেহেতু রাত্রিতে সূর্যের প্রতীকী বিকল্প, তাই অনিবার্য ভাবেই তিনি আলোক ও অশুভ প্রতিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। মমতার পুত্র অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমাকে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রাত্রিকালে প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে তিনি দানব বিনাশকারী বা রক্ষোহা। তবে অগ্নির স্বভাবে ভয়ংকর দিকও যথেষ্ট ছিল; তাই তাঁকে ক্রব্যাৎ বা শব-ভুক রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ শবদাহে অগ্নি শবকে গ্রাস করেন এমন মনে হয়। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অগ্নির প্রসন্ন ও ক্রুর এই দুটি আপাতবিরোধী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্পষ্ট একটি ভেদরেখা টানা হয়েছে। মৃত্যুর বা মৃতদেহ দহনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের ফলে তিনি পিতৃলোকে আহুতি বহন করে নিয়ে যান; তখন ‘স্বাহা” শব্দের পরিবর্তে ‘স্বধা’ শব্দটি তাঁর উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়। উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত দেবতারূপে অগ্নিকে বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতির সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়; এঁরা তাঁর সঙ্গে পুরোহিতের দায়িত্ব ভাগ করে নেন। অগ্নি যখন উচ্চতম স্বর্গে বিরাজ করেন তখন তাঁকে মাতরিশ্বা বলে বর্ণনা করা হয়; আকাশে তিনি বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে সমিধ সমূহে তিনি তনুনপাৎ এবং জলমধ্যে তিনি বাড়বাগ্নি। পরবর্তী সাহিত্যে অগ্নি ধীরে ধীরে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে ফেলেন এবং ক্রমশ রুদ্রের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা এসে যায়। বস্তুত, ঋগ্বেদের পর্যায়েই তাঁর সর্বাধিক সক্রিয় অবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রত্নপৌরাণিক স্তরের পূর্ববর্তী নৈসর্গিক উপাদানের অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। আর্যগণ যখন নিশ্চিত নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রাচীর-বেষ্টিত নগরী নির্মাণে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন, মানুষের প্রথম মিত্র ও রক্ষকরূপে অগ্নির মৌলিক মর্যাদা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল। অবশ্য প্রত্নকথাগুলির মধ্যে অগ্নির আবিষ্কারজনিত প্রাথমিক ভীতি ও বিস্ময়ও অমরত্ব পেয়ে গেছে। প্রতিদিন নতুন ভাবে জন্ম নেওয়ার ফলে রক্তিম অগ্নি দেবতাদের মধ্যে তরুণতম ও সবচেয়ে সুদর্শন রূপে পরিচিত।
অগ্নির পরেই পৃথিবীবাসী দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সোমদেব। সম্পূর্ণ নবম মণ্ডলে শুধুমাত্র একজনই দেবতা— সোম। এক ধরনের বিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ নিষ্কাশন করে তার রস সংগ্রহ করা হত। বৈদিক আর্যদের সবচেয়ে প্রিয় উত্তেজক পানীয় ছিল এই সোমরস। এই রসপানের তৃপ্তি ও উন্মাদনাতেই ক্রমে ক্রমে তার উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছিল। সোমসূক্তগুলি প্রাথমিক অবস্থায় প্রথম আটটি মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু সোমচর্যার গুরুত্ব ও জটিলতা ক্রমশ বর্ধিত হওয়ার ফলে পুরোহিতরা সোমযাগে প্রয়োগের সুবিধার্থে সমস্ত সোমসূক্ত একত্রে পৃথক ভাবে সংকলন করে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে প্রযোজ্য স্তব ও প্রার্থনার একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। নিঃসন্দেহে এই সম্পাদকীয় প্রচেষ্টাটি ঋগ্বেদ-সংহিতার শেষ পর্যায়ে হয়েছিল; দশম মণ্ডলে যেহেতু কোনও সোমসূক্ত নেই, আমরা স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, দশম মণ্ডল রচিত হওয়ার সময় কিংবা তার পরবর্তিকালে সোমমণ্ডলটি সংকলিত হয়েছিল। অবেস্তায় যে ‘হওম’-এর উল্লেখ আছে তাকে সোমযাগের ইন্দো-ইরানীয় প্রতিরূপ বলেই গ্রহণ করা হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতার শেষ পর্যায়ে বহু নতুন যজ্ঞ আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সোমযোগও ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত এবং গ্রন্থিল হয়ে উঠল— অনেক পুরোহিত এর সঙ্গে যুক্ত হলেন, অসংখ্য অনুপুঙ্খ দেখা দিল এবং তা দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রে পরিণতি লাভ করল। বস্তুত সংহিতা ও ব্রাহ্মণ যুগের মধ্যবর্তীকালে সোমদেবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সোম ইন্দ্রের মিত্র এবং অন্যান্য দেবতাদের মতোই তাঁর নামের সঙ্গে অস্পষ্ট কিছু বীরত্বপূর্ণ কাহিনি সংযোজিত হয়েছে, তবে সোমসুক্তের সর্বাধিক কাব্যগুণমণ্ডিত অংশে পানোন্মত্ত পুরোহিতদের অবস্থা বিশদ বর্ণনায় বিবৃত। ইন্দ্রের এই মাদক পানীয়ের প্রতি আসক্তি যেহেতু কিংবদন্তীতে পরিণত সেহেতু সোমের স্বাভাবিক মিত্ররূপে তিনি সেই সেনাপতির ভাবমূর্তিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন, জয়লাভ করার উপযোগী শক্তি অর্জন করার জন্য যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করার পূর্বে উত্তেজক পানীয় আকণ্ঠ পান করে নিতেন। অনুরূপ ভাবে অগ্নি সোমের সঙ্গে দু’ভাবে অন্বিত হয়েছেন; প্রসন্ন মূর্তিতে তিনি ইন্দ্রের মাধ্যমে এবং ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তিনি পিতৃগণের মাধ্যমে সোমের সঙ্গে যুক্ত। তাই সোমকে পিতৃমৎ এবং পিতৃগণকে সোমবৎ বলা হয়ে থাকে। সোমদেবের সঙ্গে অশ্বীদের কৌতূহলজনক দ্বৈত সম্পর্ক রয়েছে। দশম মণ্ডলের অন্তর্গত সূর্যাসূক্তে যে কাহিনির আভাস রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সূর্যার পিতা সবিতা প্রথম সোমদেবকেই কন্যাদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশ্বীরাই সূর্যাকে সঙ্গে করে রথে পতিগৃহে নিয়ে যান অথবা হয়তো সূর্যাকে তাঁরাই লাভ করেন। একদা সোমপানে বঞ্চিত হয়েছিলেন বলেই তাঁরা যেন সোমের জন্য নির্দিষ্ট বধূকে গ্রহণ করে প্রতিশোধ নিলেন। এই প্রত্নপৌরাণিক বিবাহ-কাহিনিতে সোম যেন পার্থিব উদ্ভিদ ও আকাশবিহারী চন্দ্রের রূপে তাঁর অবস্থানের মধ্যবিন্দুতে বিরাজ করছেন। বস্তুত সূর্য ও চন্দ্রের বিবাহ-বিষয়ক সুপ্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় প্রত্নকথার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাগুক্ত কাহিনির তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
যজ্ঞের অনুষ্ঠানচর্যার ইতিহাসের পরবর্তী স্তরে আমরা এক ধরনের যান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করি; স্তোত্রে আহুত যে কোনও বস্তুই সেই সূক্তে দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সংহিতা সংকলনের সম্পাদকীয় প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়েই এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় যখন প্রত্যেকটি সূক্ত— এমনকী প্রত্যেকটি মন্ত্রের জন্য— নির্দিষ্ট ঋষি, ছন্দ ও দেবতা নির্দেশিত হত। যে সমস্ত ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে কোনও দেবতা নির্দেশিত হয়নি, সম্পাদকরা যান্ত্রিক ভাবে ঋকে উল্লিখিত প্রাণহীন বস্তুর উপরও দেবত্ব আরোপ করতেন। এই চূড়ান্ত কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতার যুগে দেবতার বিশেষণগুলিও মধ্যে মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অর্জন করে দেবতারূপে পরিগণিত হয়েছিল। যজ্ঞে বলি-প্রদত্ত অশ্ব, বৃষ এবং অন্যান্য জন্তুতে যেমন দেবত্ব আরোপিত হয়েছিল, তেমনই নতুন প্রবণতার বিচিত্র অভিব্যক্তি ‘অজ একপাদ’ বা ‘অহিবুধ্ন্য’ রূপ কল্পনার মধ্যে দেখা গেল।
ঋগ্বেদের সময়কার দেবগোষ্ঠী যখন সাংসারিক দিক দিয়ে প্রায় নিয়ন্ত্রণাতীত হয়ে উঠল তখন ‘বিশ্বে দেবাঃ’ নামে নতুন একটি ধারণার জন্ম হল; এদের উদ্দেশে বহু সূক্তও গ্রথিত হল। প্রাথমিক স্তরে প্রাগুক্ত শব্দবন্ধটি যদিও সমগ্র দেবসঙ্ঘকেই সামূহিক ভাবে নির্দেশ করেছে, পরবর্তিকালে তা নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একটি নতুন ও অস্পষ্ট সাংকেতিক রূপ পরিগ্রহ করে— তার মধ্যে নতুন এক অস্পষ্ট আধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাও অনুভূত হয়। অন্যান্য ভূস্থানেও দেবতাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। অবশ্য পৃথিবী এবং সিন্ধু, বিপাশ, শুদ্রী, ইলা, ভারতী ও সরস্বতীর মতো নদীদের পরিচয়ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। দেবতাদের দ্বারা গৃহীত হওয়ার পর আহুতির অবস্থাকে ইলা বলে অভিহিত করা হয়েছে; তবে সরস্বতী নদী হলেও ভারতী নিশ্চিত ভাবে বিমূর্ত। ভারতী সম্ভবত ভারতের আর্যবসতিসমূহের কিংবা ভারতকৌমের নাম; তেমনই যে সরস্বতী নদীর তীরে প্রথম আর্যবসতিগুলি গড়ে উঠেছিল, তারই সমুন্নত নাম সরস্বতী। যখন যজ্ঞানুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের প্রাধান্যই আত্মসাৎ করে নিচ্ছিল, সেই সময় যজ্ঞের গৌণ উপকরণ ও অংশসমূহে দেবত্ব আরোপিত হচ্ছিল। ফলে যূপ, ক্ষুর কিংবা গ্রাবাণৌ (শিলনোড়া) যে দেবত্ব মণ্ডিত হয়ে উঠল তাদের মধ্যে যথার্থ দেবতার পরিচয় না থাকলেও নিশ্চিত ভাবে যজ্ঞচর্যার গৌরবের লক্ষণটুকুই ফুটে উঠেছিল। বিশঃ, প্রজা, অর্থাৎ জনসাধারণ ও কৃষকগণ তখন এক নামহীন জনগোষ্ঠীরূপে বিদ্যমান ছিল; ফলে তাদের আদর্শায়িত উপস্থাপনা যে-সব পৃথিবী-নিবাসী দেবতাদের মধ্যে ঘটেছিল তার কোনও স্পষ্ট অবয়ব ফুটে ওঠেনি।
ঋগ্বেদে রচনা ও সংকলনের অন্তিম পর্যায়ে অর্ধবিমূর্ত দেবতাদের একটি নতুন গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। এদের মধ্যে প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বকর্মার নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ; সাধারণ ভাবে এঁরা তখন যজ্ঞ এবং পুরোহিতদের কার্যাবলির বিমূর্ত সৃজনশীল ক্ষমতার প্রতীক। লক্ষণীয় এই যে, এই সব দেবতাদের প্রতি নিবেদিত অধিকাংশ সূক্তে মানুষের উপর দেবত্ব অরোপের কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই বা যজ্ঞে বিনিয়োগের জন্য কোনও নির্দেশও নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদিও বিনিয়োগের উল্লেখ রয়েছে, নিশ্চিত ভাবেই সেইগুলি সংহিতা-যুগের শেষ পর্যায়ে আবিষ্কৃত যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির সঙ্গেই সম্পৃক্ত। যেহেতু বিমূর্ত দেবতাদের প্রতি সূক্তসমূহ মূলত সংহিতা যুগের অন্তিম পর্যায়েই পাওয়া যায়, এতে সম্ভবত এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে এই সব সূক্তের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একেশ্বরবাদী প্রবণতা আর্য ও প্রাগার্য গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সংমিশ্রণেরই বিলম্বিত ফল।
আর্যরা প্রকৃতপক্ষে অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত শত্রুদের অমরতা দান করেছেন। দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে অতিজাগতিক তাৎপর্যে উত্তীর্ণ করে কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে সংঘর্ষ রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। প্রাগার্য গোষ্ঠীপতিদের প্রথম প্রজন্মকে সম্ভবত আর্যদের বিজয় লাভের এক শতাব্দী বা আরও কিছুকাল পরে মায়া শক্তিধারী অশুভ বাহিনীরূপে চিহ্নিত করা হয়, পরবর্তিকালেও আর্যদের যে কোনও ধরনের বিপদের জন্য তাদেরই দায়ী করা হত। কালক্রমে এই সব শত্রু অন্তরীক্ষচারী বা পাতালনিবাসী অদৃশ্য শক্তিরূপে চিহ্নিত হল। আঞ্চলিক বা পারিবারিক প্রত্নকথা ও আখ্যান অনুযায়ী এদের নাম, চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ হল ভিন্ন ভিন্ন। এই সব আর্য শত্রুগণ যথাসময়ে অসুর, রক্ষঃ (পরবর্তিকালে এরাই রাক্ষস), যক্ষ ও পিশাচ রূপে পরিচিত হল; উল্লেখ্য যে, এরা সর্বদাই যূথবদ্ধ (গণ), তবে প্রত্নপৌরাণিক বিশ্বকল্পনায় ভাল ও মন্দের মধ্যে দ্বিমেরু কোনও বিষম বিভাজন নেই; বহু দেবতার চরিত্র ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ করেও আমরা তাই দেখি। প্রেত ও পিশাচশক্তি সমন্বিত হয়ে যেমন রুদ্র ও মরুদ্গণে পরিণত হয়েছে, তেমনই বিপরীত ক্রমে এরাই অসুর, রক্ষ, প্রভৃতিতে বিবর্তিত হয়েছে। বস্তুত মূলগত ভাবে এরা পরস্পর ভিন্ন নয়, শুভশক্তির প্রবণতা থাকলে একই শক্তি দেবতা হয়ে ওঠে, কিন্তু ভারসাম্য বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়লেই জন্ম নেয় অসুরেরা। প্রকৃতপক্ষে অসুর কল্পনার মধ্যেই ঐতিহাসিক সত্য অধিক মাত্রায় প্রচ্ছন্ন।
