শ্রী বৈজ্ঞানিক সমগ্র – সুধীন্দ্রনাথ রাহা
সায়েন্স ফিকশন ও ভৌতিক কাহিনি সংকলন
সম্পাদনা – ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : মে ২০২০
প্রচ্ছদ : সুমিত বড়ুয়া
অলংকরণ : নারায়ণ দেবনাথ
বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত
.
প্রকাশকের কথা
সুধীন্দ্রনাথ রাহা যেমন বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত লেখকদের গল্প উপন্যাসের ভাবানুবাদ করেছেন তার সঙ্গে ‘শুকতারা’ পত্রিকায় ‘শ্রীবৈজ্ঞানিক’ ছদ্মনামে প্রথমদিকে লিখেছিলেন বিজ্ঞানভিত্তিক ছোটো ছোটো টীকা যেমন, হেলিকপ্টারের কথা, জেট বিমানের কথা, রকেটের কথা, ক্ষেপণাস্ত্র ও কৃত্রিম উপগ্রহ, কপিকলের কথা ইত্যাদি (প্রকাশকাল ১৯৬৮-১৯৭২)। পরবর্তীকালে ওই একই ছদ্মনামে তিরিশটি সায়েন্স ফিকশন ভাবানুবাদ করেছিলেন। দুই ডজনের অধিক বিদেশি সায়েন্স ফিকশন লেখকের কাহিনিকে ‘শ্রীবৈজ্ঞানিক’ ছদ্মনামে সুধীন্দ্রনাথ রাহা ভাবানুবাদ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের পৌত্র বৈজয়ন্ত রাহার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ও অনুবাদগুলিতে সুধীন্দ্রনাথের লেখনী শৈলীর স্পষ্ট ছাপ দেখে এইকথা নিশ্চিন্তভাবে বলা যায় যে ‘শ্রীবৈজ্ঞানিক’ ছদ্মনামের আড়ালের অনুবাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ রাহা।
প্রশ্ন উঠতে পারে বইটির নাম ‘শ্রীবৈজ্ঞানিক সমগ্র’ কেন হল? প্রসঙ্গত, বইটির আশি শতাংশ জুড়ে রয়েছে ‘শ্রীবৈজ্ঞানিক’ ছদ্মনামে অনূদিত সায়েন্স ফিকশন সংকলন। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে ও হারিয়ে যাওয়া ‘শ্রীবৈজ্ঞানিক’ ছদ্মনামটির পেছনের মানুষটিকে দৃষ্টিগোচর করার জন্য বইটির এই নামকরণ করা হল।
সায়েন্স ফিকশন সাহিত্য কি আদৌ বিজ্ঞান? নাকি বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে লেখা এক ‘সোনার পাথরবাটি’? সেই বিচারের ভার পাঠকের হাতে রইল। কিন্তু এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ভৌতিক তথা অলৌকিক সাহিত্য মানেই বিজ্ঞান থেকে শতহস্ত দূরের অলীক জগৎ। এই সংকলনে স্থান পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া তিরিশটি সায়েন্স ফিকশন অনুবাদ কাহিনি ও পাঁচটি ‘মৌলিক’ ভৌতিক কাহিনি। বাংলা ভাষায় এই প্রথমবার সায়েন্স ফিকশন এবং ভৌতিক কাহিনি দুই মলাটে প্রকাশিত হল কি না সেই তথ্য বাংলা সাহিত্য গবেষকের পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব। তবে সাহিত্যের দুই পৃথক ঘরানাকে দুই মলাটে নিয়ে আসার পরিকল্পনার পেছনে এক সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। বুক ফার্মের কাছ থেকে পাঠকেরা গতানুগতিকতার বাইরে নতুন স্বাদের পরিবেশনা আশা করেন। সেই কথা মাথায় রেখে তথাকথিত ‘অবৈজ্ঞানিক’ বিষয়ক এই সংকলন প্রকাশ করার চেষ্টা করা হল। আশা করি, পাঠকেরা দুই ভিন্ন স্বাদের গল্প সমানভাবে উপভোগ করবেন।
‘শ্রীবৈজ্ঞানিক’ ছদ্মনামে লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭২-১৯৭৮ সময়কালের মধ্যে। সংকলনের চারটি ভৌতিক কাহিনি প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৬৯ সালে। অর্থাৎ, আজ থেকে কম-বেশি প্রায় ৫০ বছর আগের হারিয়ে যাওয়া দুষ্প্রাপ্য ‘অগ্রন্থিত’ লেখাগুলি প্রথমবার বই আকারে পাঠকের দরবারে হাজির করতে পেরে ‘বুক ফার্ম’ গর্বিত।
সুধীন্দ্রনাথ রাহার পৌত্র বৈজয়ন্ত রাহার অনুমতিতে এই সংকলনটি প্রকাশিত হল। লেখাগুলি সংগ্রহ ও সম্পাদনার জন্য গবেষক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরলস পরিশ্রমকে কুর্নিশ। সংকলনের অন্তর্গত ‘অশরীরী ঈগল’ বইটি সংগ্রহ করা হয়েছে সোমনাথ দাশগুপ্তের মাধ্যমে সব্যসাচী দেবের কাছ থেকে। বইটির অন্যতম সম্পদ নারায়ণ দেবনাথের দুষ্প্রাপ্য অলংকরণ। তাঁদের সকলকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।
.
ভাবানুবাদ মূল বিদেশি কাহিনি ও লেখক
১ আলফা সেন্টৌরির পথে জেমস ক্লিশের ‘কমন টাইম’
২ লতার নাম হাঁউ-মাঁউ-খাঁ আয়ান উইলিয়ামসনের ‘কেমিক্যাল প্ল্যান্ট’
৩ দশ লাইট-ইয়ার দূরত্বে ফ্রান্সিস জি বেয়ারের ‘স্যান্ডস আওয়ার এ্যাবোড’
৪ মহাকাশের পালকওয়ালা মানুষ ম্যরে লেইনস্টারের ‘দ্য এলিয়েনস’
৫ নক্ষত্র? না, ক্ষেপণাস্ত্র এইচ জি ওয়েলসের ‘দ্য স্টার’
৬ মঙ্গলের প্লেগ উইলিয়াম টেইনের ‘দ্য সিকনেস’
৭ জীবন-মৃত্যুর লটারি আর্থার সি ক্লার্কের ‘ব্রেকিং স্ট্রেইন’
৮ পৃথিবী যখন ধ্বংস হল জন উইন্ডহ্যামের ‘নো প্লেস লাইক আর্থ’
৯ জীবন-মৃতের জাদুঘর আর্থার পোর্জেসের ‘দ্য রুম’
১০ এগিয়ে চলো অসম্ভবের মুখে ভ্যালেনটিন জুরভলিওভার ‘এ্যাসট্রোনট’
১১ এম-১ ই এফ রাসেল-এর ‘বিটার এন্ড’
১২ কালচক্রের সওয়ার এইচ জি ওয়েলসের ‘দ্য টাইম-মেশিন’
১৩ পাগলা গ্রহ ফ্রেডারিক ব্রাউনের ‘প্লাসেৎ ইজ এ ক্রেজি প্লেস’
১৪ রোবট বন্ধুর মৃত্যু জন কিপ্যাক্সের ‘ফ্রাইডে’
১৫ অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে হেলেন ম্যাক-ক্লয় রচিত ‘নাম্বার টেন কিউ স্ট্রিট’
১৬ ক্লোরোফাগ ম্যরে লেইনস্টারের ‘ডক্টর’
১৭ সন্ত্রাসবাদী বৈমানিক ডগলাস ফসেটের ‘ডুম অব দ্য গ্রেট সিটি’
১৮ কত রহস্য ওই অসীমে! জি গুরেভিচের ‘ইনফ্রা ড্র্যাকোনিচ’
১৯ মহাবিমানের উল্লম্ফন জে ব্লিশের ‘নর আয়রন বারস’
২০ জীবন কোথায় নেই? আর্থার সি ক্লার্কের ‘বিফোর ইডেন’
২১ আঙুল যাদের ছ-টা ই আর জেমসের ‘সিক্স-ফিঙ্গার্ড-জ্যাকস’
২২ আজি হতে শতবর্ষ পরে অজ্ঞাত
২৩ ফিরে চলো গুহামানবের যুগে এলিস গুইন জোনসের ‘হোয়েন দ্য এঞ্জিনস হ্যাড টু স্টপ’
২৪ ধূমকেতুর উদরে অজ্ঞাত
২৫ হাসপাতালের ‘টি’ ওয়ার্ড অ্যালফ্রেড বেস্টারের ‘ডিস অ্যাপিয়ারিং অ্যাক্ট’
২৬ দেহান্তরী ই এফ রাসেলের ‘দিস ওয়ান’স অন মি’
২৭ অ্যাপিনের গবেষণা সাফি (এইচ মনরো) রচিত ‘টোবার মোরি’
২৮ মঙ্গলের পথে সেকেলে কাপ্তেন (উদ্বোধন) জেমস হোয়াইট-এর ‘ফাস্ট ট্রিপ’
২৯ ত্রিমূর্তি (মনিদীপা) জে ব্লিশ-এর ‘বীপ’
৩০ এক ঘুমে এক-শো বছর ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর ‘দ্য ফ্যানটম আইল্যান্ড’
____
২৮ ও ২৯ : দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত।
অন্যান্য ‘শুকতারা’ পত্রিকায় প্রকাশিত।
.
সব্যসাচী সুধীন্দ্রনাথ রাহা
কৈশোর থেকে যৌবন যাঁর লেখা পড়ে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তিনি হলেন সুধীন্দ্রনাথ রাহা।
শেক্সপিয়র থেকে চার্লস ডিকেন্স, টমাস মান, ভিক্টোর হুগো, লিও টলস্টয়, পার্ল বাক, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, ম্যাক্সিম গোর্কি— কে নেই সেই তালিকায়? বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য মুক্তারাশিকে ভাষার ব্যবধানের ঝিনুকের মধ্য থেকে উদ্ধার করে এনেছেন তিনি। সহজ ভাষায় বিদেশি সাহিত্যের অজস্র মূল্যবান গল্প উপন্যাসকে সহজ ভাষায় ভাবানুবাদ করে গল্পটা তিনি শুনিয়ে দিয়েছেন বাংলার অগণিত কিশোর কিশোরীকে। যাঁরা আজ কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রবীণত্বের সীমানায় প্রবেশ করেছেন তাঁদের মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত আছে সুধীন রাহার নাম। তিনি প্রয়াত হন ১৯৮৬ সালে। নিঃশব্দে পেরিয়ে গেছে আরও ৩২টি বছর। কালের অবচেতন মনে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে তাঁর লেখককীর্তির অমূল্য স্মৃতি।
১৮৯৬ সালের ১৭ জুলাই (১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৩ শ্রাবণ) অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার নলধা গ্রামে সুধীন্দ্রনাথ রাহার জন্ম হয়। পিতা যদুনাথ রাহা ও মাতা মৃন্ময়ী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুধীন্দ্রনাথের সহোদর দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন নাট্যকার ও সাহিত্যপ্রেমী মানুষ।
সুধীন্দ্রনাথের বিদ্যার্জনের প্রসঙ্গে কুচবিহারের রাজপরিবারের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ওই রাজ্যের দেবীগঞ্জ অঞ্চলে ‘দেবীগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাই ইংলিশ স্কুল’ নামে শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীগঞ্জেই সুধীন্দ্রর পিতা যদুনাথ আদালতে মোক্তারি করতেন ও কর্মসূত্রে সেখানে সপরিবার থাকতেন। উল্লিখিত স্কুলেই সুধীন্দ্রর শিক্ষার্জন শুরু হয়। এখান থেকেই তিনি ১৯১২ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯১৪ সালে কুচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজ (বর্তমানে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ) থেকে তিনি আইএ উত্তীর্ণ হন প্রথম বিভাগেই। ১৯১৬ সালে এখান থেকে তিনি ইংরেজিতে অনার্স সহ স্নাতক হন, কিন্তু বৃত্তি না পাওয়ায় অর্থাভাবে এমএ পড়া হল না। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে দেশের পরিস্থিতি ছিল অস্থির। ইতিমধ্যে ১৯১৪তেই মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৩ বছরের কিশোরী প্রীতিলতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। কালক্রমে তাঁরা দশটি পুত্র-কন্যার জনক-জননী হন।
স্নাতক হওয়ার পর ১৯১৮ সালের মধ্যভাগ থেকে সুধীন্দ্রনাথ শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুলে প্রধানশিক্ষকের পদে ১৯২৫ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। তখন শিক্ষকতার বেতন ছিল সামান্য, তাই পরিবার প্রতিপালনের জন্য শিক্ষকতার পাশাপাশি তাঁকে সাহিত্য রচনাসহ আরও অনেক কিছুই করতে হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় এসে তাঁরা ওঠেন হেদুয়ার কাছে ঈশ্বর ঠাকুর লেনে। ১৯২৪ সালে সুধীন্দ্রনাথ প্রথম নাটক লেখেন, পরবর্তী সময়েও বহু মঞ্চসফল নাটক লিখেছেন। প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। ১৯২৪ থেকে তাঁর নাটক কলকাতার মঞ্চে অভিনীত হয়। এ সময় তিনি একটি ছাপাখানায় ম্যানেজারি এবং সাহিত্যচর্চা একত্রে করতে থাকেন। সমসময়ে তিনি ব্যক্তিগত পড়াশুনা ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছেন ন্যাশনাল ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির (জাতীয় গ্রন্থাগার) মাধ্যমে। সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সুধীন্দ্রনাথ সপরিবার বসবাস শুরু করেন কোন্নগরের দেবপাড়া অঞ্চলে গঙ্গাতীরবর্তী একটি ভাড়াবাড়িতে। ১৯৪২-এ আবার আবাস পরিবর্তন, পরিবারসহ তিনি চলে আসেন কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে। ১৯৪২-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতায় বোমা পড়ায় বহু লোক শহর ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের বড়োছেলে সুখেন্দ্রনাথের কর্মস্থল লখনৌতে পাঠিয়ে দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ নিজে বেলেঘাটা অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নিয়ে একা থাকতে শুরু করেন। ১৯৪৫-এ তাঁর পরিবার কলকাতায় ফিরে এলে সিঁথিতে একটি ভাড়াবাড়িতে তাঁরা বসবাস শুরু করেন। সুধীন্দ্র নিজে নিকটস্থ একটি ল্যাবরেটরিতে চাকরি নেন। ১৯৫৩ থেকে আবার জীবিকা বদল। হুগলির দ্বারহাটায় রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে সুধীন্দ্র সহকারী প্রধানশিক্ষকের পদে যোগ দেন। এখানেই স্কুলের লাগোয়া একটি জমি কিনে তিনি নিজস্ব একটি মাটির বাড়ি বানিয়ে নেন, এই বাড়িতেই তিনি নিজের হাতে বাগান তৈরি করেন। এই সময়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না। তবে তিনি একখানি অভিধান লেখেন ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। ১৯৫৬তে প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে তিনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন ও পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। সংসারও অভাব ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। বাড়িতে ইংরেজি পড়াতেন তিনি, কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতেন সামান্যই। ১৯৫৮তে পারিবারিক সমস্যার দরুন আবার কলকাতায় ফিরে আসেন তাঁরা, এবার কাশীপুরে সৎচাষিপাড়া রোডে ভাড়াবাড়িতে বসবাস। ইতিমধ্যেই হুগলির ভিটে বিক্রি করে দেন সুধীন্দ্রনাথ। এবার কাশীপুরে থাকাকালীন শুরু হয় তাঁর অবিচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনা। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৯, এই ২৫ বছর ধরে কলকাতার বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে তাঁর রচিত নানা নাটক অভিনীত হয়েছে। তখন ছিল বাংলার মঞ্চনাটকের সুবর্ণযুগ। তাঁর নাটকে অভিনয় করেছেন কিংবদন্তিসম অভিনেতা অভিনেত্রীরা; যথা শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সরজুবালা, আঙুরবালা, কানন দেবী প্রমুখ। সুধীন্দ্রনাথের নাটকের গীতিকার ও সুরকার কখনো স্বয়ং নজরুল, কখনো গীতিকার হেমেন রায়, সুরকার কৃষ্ণচন্দ্র দে; নাট্যপরিচালক নরেশ মিত্র।
তাঁর প্রথম নাটক ‘মহারাষ্ট্র প্রকাশ’-এর প্রকাশক ছিলেন তিনি নিজেই। পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবোধে সেসময় বাংলা ছিল অগ্রগণ্য। এরই পটভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকেও স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহার কথা প্রচ্ছন্ন ছিল। কিছু দুষ্কৃতকারী যে বিপ্লবীদের ভেক ধরে প্রতারণা ও অর্থোপার্জন চালিয়ে যাচ্ছে তারই মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা ছিল ‘বাংলার বোমা’ নাটকে। আবার ‘মারাঠা মোগল’ নাটকে ছিল মারাঠা অভ্যুত্থানের আড়ালে স্বদেশ মাতৃকার বন্দনা। তাঁর ‘বিপ্লব’ নাটকটি ব্রিটিশ প্রশাসন নিষিদ্ধ করে দেয়। বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ গ্রন্থসূত্রে জানা যায় ‘মারাঠা মোগল’ নাটকটিও নিষিদ্ধ হয়েছিল।
১৯৪২-এর দেশজুড়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, একই সময়ে ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩-৪৪-এ পঞ্চাশের মন্বন্তরে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়ে যায় বাঙালির রঙ্গমঞ্চ নাট্যচর্চা। ফ্যাসিস্ত বিরোধী তথা বাম রাজনীতির অভ্যুত্থান বদলে দিতে থাকে সাংস্কৃতিক বিনোদনের খোলনলচে। ‘নবান্ন’ নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা নাটকের যুগ বদল ঘটে যায়। ১৯৪৯-এ তাঁর রচিত ‘বিক্রমাদিত্য’ নাটকের অভিনয়ের পরেই সুধীন্দ্রনাথ নাট্যগজৎ থেকে অবসর নেন। পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির মঞ্চনাটক তিনি পছন্দ করতে পারেননি।
তাঁর লেখা অন্তত ৫০টি নাটকের কথা জানা গিয়েছে যার মধ্যে প্রায় ১৯টি বঙ্গরঙ্গালয়ে বাণিজ্যিকভাবে অভিনীত হয়। তাঁর ভাই দেবেন্দ্রনাথের নাটক ‘অর্জুন বিজয়’ কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। এই নাটকটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-র প্রযোজনায় ১৯৪০-এর ৭ ডিসেম্বর অভিনীত হয়। এ ছাড়া তাঁর রচিত ‘শাহজাহান’, ‘আওরঙ্গজেব’, ‘হাম্বির’, ‘বিশ্বামিত্র’, ‘শিবসূর্য’ প্রভৃতি নাটকের নাম পাওয়া গিয়েছে। নানা সূত্র থেকে জানা যায় তাঁর লেখা নাটক আকাশবাণীতে ও যাত্রা হিসেবেও অভিনীত হয়েছে।
পেশাদারি নাট্যমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ ১৯৫০ থেকে শুধুমাত্র ছোটোদের জন্য কলম ধরেন। তখন থেকে বলতে গেলে ‘নবকল্লোল’ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিদেশি কাহিনির অনুবাদগুলি ছাড়া বাকি যা লিখেছেন তা সবই ছোটোদের জন্য। ছোটোদের জন্য রচিত তাঁর সাহিত্যসম্ভারের সিংহভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ‘দেব সাহিত্য কুটীর’ প্রকাশনা সংস্থা থেকে। এ ছাড়া শরৎ সাহিত্য ভবন, সুনির্মল সাহিত্য মন্দির এই দুটি অধুনালুপ্ত ছোটোদের প্রকাশনা থেকেও অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনাসম্ভার থেকে তাঁকে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রূপে অনায়াসেই চিহ্নিত করা যায়। নাটক, রহস্য, সামাজিক, অ্যাডভেঞ্চার বা যুদ্ধের গল্প— একদিকে বিদেশি সাহিত্যের অতিখ্যাত/খ্যাত/অল্পখ্যাত লেখকদের অজস্র অনুবাদ, আবার একেবারেই বিশুদ্ধ মৌলিক সামাজিক উপন্যাস যার চরিত্রগুলি যেন আমাদের ঘরের আঙিনা থেকে চয়ন করে নেওয়া। বিশেষভাবে স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধের ফল্গুধারা তাঁর মৌলিক গল্প উপন্যাসের মধ্যে বহমান। আজও পরিণত বয়স্ক ও মনস্ক পাঠক সুধীন্দ্রনাথের এই লেখাগুলি পড়ে শৈশবের মতোই আকর্ষণ বোধ করবেন।
শিশু-সাহিত্যিক রূপে তাঁর কলমের বহুমুখিতা অল্প বয়সে আমার পাঠকসত্তাকে অভিভূত করেছিল। গোয়েন্দা, অ্যাডভেঞ্চার, বিদেশের রোমাঞ্চকর সত্যঘটনা, মনীষীদের জীবন, সামাজিক গল্প সব ধরনের লেখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সামাজিক গল্পগুলিতে জীবনযন্ত্রণা, সামাজিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলার বেদনাবোধের ধারা বহমান। বিপরীতে স্বদেশের হারানো গৌরব ফিরে পাবার অতৃপ্ত বাসনা তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনিগুলিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। একইসঙ্গে লেখক বিশ্বাস করতেন, কিশোর পাঠক বয়সে ছোটো হলেও মানসিকতায় ছোটো নয়, তাই সমকালীন বাস্তবতা, ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান, মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষের দুঃখ, বেদনার বাস্তব চিত্রকেও সে-বয়সের পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন তিনি। ‘শুকতারা’য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ‘তাসের প্রাসাদ’ কিংবা ‘সেদিন যারা আপন ছিল’ উপন্যাস তার সাক্ষ্য দেয়।
অথচ জীবিকার তাগিদে তাঁকে লেখা শুরু করতে হয়েছিল মনসামঙ্গল, সত্যনারায়ণের পাঁচালি কিংবা গোপাল ভাঁড়ের গল্প লিখে, তার থেকে তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বিশেষ করে ভাবানুবাদের দক্ষতা তাঁকে এক উচ্চাসনে নিয়ে যায়।
১৩৫৪ (১৯৪৮) সালে ‘দেব সাহিত্য কুটীর’ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে ছোটোদের মাসিক পত্রিকা ‘শুকতারা’।
‘শুকতারা’র জন্মলগ্ন থেকেই সুধীন রাহা-র নানা লেখা প্রকাশ হতে থাকে। ‘শুকতারা’র অন্যতম আকর্ষণ ছিল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত টারজানের গল্প। টারজানের প্রথম দুটি পর্ব লিখেছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ‘দাদুমণি’ নাম নিয়ে দীর্ঘদিন ‘শুকতারা’য় সম্পাদকীয় লিখেছেন। ১৩৫৯ থেকে সুধীন রাহা শুরু করেন টারজানের ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার। ওঁর মৃত্যুর পরও ১৩৯৯ সাল পর্যন্ত টারজানের অভিযান চলেছিল তাঁর কলমে। এডগার রাইস বারোজের মূল টারজানের অ্যাডভেঞ্চারের থেকে এ কাহিনির বেশ কিছুটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। মূলত প্রাপ্তবয়স্ক প্রসঙ্গ থেকে কাহিনির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য এই অনুবাদের পরিবর্তন। অথচ তা কাহিনির রোমাঞ্চকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না। টারজানের কাহিনিকার বা অনুবাদক হিসাবে সুধীন রাহা ‘সব্যসাচী’ ছদ্মনামটি ব্যবহার করেছেন।
‘সব্যসাচী’ ছদ্মনামটি ব্যবহার করার প্রশ্নে একটি বিতর্কিত প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। ‘শুকতারা’য় প্রকাশিত ‘অমর বীর কাহিনী’ সিরিজের লেখাগুলি একাধিকবার পড়ে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল এগুলি সুধীন রাহারই লেখা অখচ লেখকের নাম থাকত মধুসূদন মজুমদারের, যিনি ‘দৃষ্টিহীন’ ছদ্মনামে লিখতেন। আজাদ হিন্দ-ফৌজের অভিযানের পটভূমিকায় তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি গল্প ‘শুকতারা’য় প্রকাশিত হয়েছিল। আরও কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছিল সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নামে, একই বিষয়ে গল্প, নায়কের নাম এক, ভাষা এক, লেখার মধ্যে লেখকের স্বদেশপ্রেমের সুরটিও স্পষ্ট, অথচ লেখক রূপে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজে স্বর্গের সিঁড়ি, নীল আলো প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর লেখা। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র ‘হিমাংশু’ বিপরীতে সুধীন রাহার গোয়েন্দা চরিত্র ‘শৈলেশ’। ‘শুকতারা’য় ধারাবাহিক রহস্যোপন্যাস ‘ইস্কাবনের টেক্কা’ প্রকাশকালে এই চরিত্রের আবির্ভাব। দেখেছি ‘শুকতারা’য় প্রকাশিত শৈলেশকে গোয়েন্দা রেখে লেখা গোয়েন্দা গল্পের লেখিকা হিসেবে শৈলবালা ঘোষজায়া-র নাম; কারণ শৈলবালার ‘আন্দু’ উপন্যাস সেকালের প্রায় বৈপ্লবিক লেখা। সেই লেখিকার নামে সুধীন রাহার গোয়েন্দা চরিত্রের ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ রহস্যের সৃষ্টি করে। সৌরীন্দ্রমোহন ও শৈলবালার লেখার ধরনধারণ সম্বন্ধে যেসব পাঠক অবহিত আছেন, উপরোক্ত গল্পগুলি পড়লে তার সঙ্গে সেসব গল্প যে মিলবে না, আমি নিশ্চিত। ‘শ্রীবৈজ্ঞানিক’ ছদ্মনামে সুধীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা লিখতেন আবার ‘দশকুমার চরিতম’ শীর্ষক সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ খোদ নাট্যকার ‘আচার্য দণ্ডি’ নামটিই নিজের নামের বদলে বসিয়ে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে লেখক সুধীন্দ্রনাথ রাহাকে আমার বহুরূপী লেখক বলে মনে হয়েছে।
এ ছাড়াও নানা কারণে তিনি নানান বিচিত্র ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন এবং মূলত সেই ছদ্মনামগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল ‘শুকতারা’য় নানা ধরনের লেখার সঙ্গে। ওই পত্রিকায় প্রথম দিকে বিজ্ঞান নিবন্ধ লেখার সময় শ্রীবৈজ্ঞানিক ও শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত এই দুটি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। সেই থেকে ছদ্মনামের নামাবলি দীর্ঘ হতে থাকে— শ্রীদীপক, রসরাজ, বাণীকুমার, প্রবাল, যশোধর মিশ্র ইত্যাদি। ‘অলক ঘোষ’ নামে অজ্ঞাত লেখকের ধারাবাহিক উপন্যাস ‘দস্তার আংটি’ কিংবা ‘পাতালের পথে’ পড়ে পাঠক সুনিশ্চিতভাবেই সুধীন রাহার কলমের গন্ধ পাবেন। এ ছাড়া তাঁর রচনার স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায় দীনকর শর্মা, দোলগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু গুপ্ত, পরাশর রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকদের লেখায়। অনুমিত হয় বহুরূপী লেখকের ছদ্মনামের আড়ালে আছেন সেই একই ব্যক্তি।
এত অজস্র ছোটোদের লেখা সৃষ্টি করে যাওয়ার মূলে ছোটোদের ভালোবাসার একটা ভূমিকা অবশ্যই ছিল। বৈষয়িক ব্যাপারে অনেকটাই উদাসীন, রচনার স্বত্ব, নাম-যশ সম্বন্ধে একইরকম নির্বিকার একজন সাহিত্যকার রূপে তিনি আমাদের চেতনায় থেকে যান।
৮৯ বছর বয়সে জীবনের শেষদিকে তিনি ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হন, শেষ সাতদিন ছিলেন নার্সিং হোমে, এরপর জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যু। পরিতাপ ও লজ্জার বিষয় মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিরূপে ‘কালিদাস’ পুরস্কার পান। অসুস্থতার জন্য তা গ্রহণ করতেও যেতে পারেননি, পরিজনরা নিয়ে আসে। বেশিমাত্রায় আত্মসমালোচক ও আত্মবিস্মৃত বাঙালির কাছে সেটাই একমাত্র সান্ত্বনা।
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
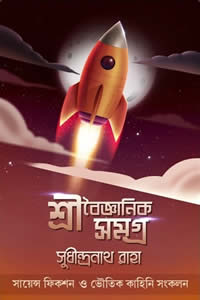
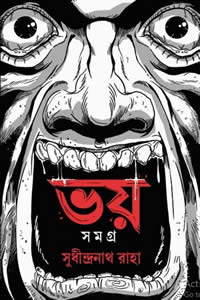

Leave a Reply