ঘনাদা সমগ্র ১ – প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রথম সংস্করণ – জানুয়ারি ২০০০
প্রচ্ছদ – সমীর সরকার
.
ঘনাদা ১ম খণ্ডের ভূমিকা – সুরজিৎ দাশগুপ্ত
অ্যাটম বোমায় বিধ্বস্ত জাপানের আত্মসমর্পণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান। পরদিন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগস্ট থেকে বাংলায় আনন্দোৎসব। আকাশ থেকে ও বর্ষার কালো মেঘ কেটে শরতের নীলিমা ফুটে উঠল, নীচের মাটিতে জাগল কাশ ফুলের ঢেউ। এসে গেল পুজো, সেই সঙ্গে দেব সাহিত্য কুটিরের ১৩৫২ বঙ্গাব্দের পূজাবার্ষিকী ‘আলপনা’ আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ঘনশ্যামদা, সংক্ষেপে ঘনাদা। সেই পূজা বার্ষিকীতে প্রকাশিত ‘মশা’ গল্পটি থেকেই ঘনাদা গল্পমালার শুরু। কিশোর-কিশোরীর জন্য লেখা হলেও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সববয়েসি পাঠকের সমাজে সাড়া পড়ে যায়। তারপর থেকে প্রতি বছরেই দেব সাহিত্য কুটিরের কর্তৃপক্ষ তাঁদের পূজাবার্ষিকীর জন্য ঘনাদার একটি গল্প দাবি করতে থাকেন। আর প্রেমেন্দ্র মিত্র বছরে বছরে লিখে যেতে থাকেন ‘পোকা’, ‘নুড়ি’, ‘কাঁচ’ প্রভৃতি এক-একটি গল্প।
‘মশা’ গল্পে প্রথম প্রবেশে ঘনাদার চরিত্র নির্মীয়মাণ বলে একটুখানি অনিশ্চিত। তখন মেসের কোন তলায় থাকেন তিনি, জানানো হয়নি। তখন তিনি এক-এক সময় মেসের এক-এক বাসিন্দার কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নেন, কিন্তু ‘নুড়ি’ গল্প থেকে দেখি যে তিনি সিগারেট ধার করেন শুধু শিশিরের কাছ থেকেই এবং ‘মাছ’ গল্প শুরু করার মধ্যে তাঁর ২৩৫৭টা সিগারেট শিশিরের কাছ থেকে ধার করা হয়ে গেছে। ঘনাদার সিগারেট ধার করার অভ্যাস প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন পাঁচটি গল্প নিয়েছেন তেমনই ঘনাদার মেসের ঠিকানা বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন জানাবার জন্যও তিনি ষষ্ঠ গল্প ‘টুপি’ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। এইভাবে এক-এক বছরে এক-একটি গল্পে তিনি গড়ে তুলেছেন ঘনাদার বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত ঐতিহ্য। লক্ষ্যণীয় যে ঘনাদার গল্পসমগ্রের প্রথম খণ্ডে সংকলিত গল্পগুলির লেখক-চরিত্রের নাম জানানো হয়নি। পাঠক হিসেবে আমরা শুধু এইটুকুই জেনেছি যে উত্তমপুরুষে যিনি উপস্থিত তিনিও শিশির, গৌর, শিবুর মতো এই মেসেরই একজন বাসিন্দা। এই উত্তমপুরুষ প্রথম মুখ খুলেছেন ‘ছুঁচ’ গল্পটিতে। এর আগে পর্যন্ত মেসের এই বাসিন্দাটির উপস্থিতি আমরা টেরই পাইনি।
প্রেমেন্দ্র যখন ঘনাদার গল্পগুলি লেখা শুরু করেন তখন তিনি সিনেমার জগতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তাঁর পরিচালিত বাংলায় ‘পথ বেঁধে দিল’ ও হিন্দিতে ‘রাজলক্ষ্মী’ মুক্তি পায় ১৯৪৫-এই; সেই বছরেই মুক্তিপ্রাপ্ত নীরেন লাহিড়ীর ‘ভাবীকাল’ ছবিটির তিনি ছিলেন উপদেষ্টা, কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার—চিন্তায়, গীতিহীনতায় ও সংলাপবিরলতায় ‘ভাবীকাল’ নতুন বাংলাছবির প্রথম ইঙ্গিত; আবার ১৯৪৭-এই তাঁর পরিচালিত ‘নতুন খবর’ ও ‘কালোছায়া’ মুক্তি পায়—দুটি ছবিতেই বিগত দশকের রোমান্টিক চরিত্রাভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অভিনয়ে তিনি প্রয়োগ করেন; এবং একই সঙ্গে পরিচালক সুশীল মুজমদারের জন্য লেখেন ‘অভিযোগ’-এর কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গীতি; আবার ১৯৫০-এ মুক্তি পায় তাঁর রচিত ও পরিচালিত ‘কুয়াশা’; তা ছাড়া আবার সুশীল মজুমদারের ফরমাশে লিখে দেন ‘দিগভ্রান্ত’র কাহিনী ও চিত্রনাট্য। এত সব কথা ঘনাদার গল্পের প্রসঙ্গে আনলাম এটা বলার জন্য যে চলচ্চিত্র জগতের প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র নিয়ম করে নিষ্ঠার সঙ্গে বছরে বছরে ঘনাদার গল্প লিখে গেছেন।
ফিল্মি ফরমাশে জর্জরিত ওই পর্বে প্রেমেন্দ্র, কী দারুণ পরিশ্রম করে ঘনাদার গল্পগুলি লিখেছিলেন ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। গল্পগুলি মোটেই উদ্দাম কল্পনার উধাও পক্ষবিস্তার নয়, বরং মেধা ও শ্রমের আনন্দঘন মিলনের রোমাঞ্চকর পরিণাম। পড়লেই বোঝা যায় যে এক-একটি গল্প লেখার জন্য প্রত্যেক বছর তাঁকে নতুন নতুন কত ব্যাপক প্রস্তুতির ও কত গভীর গবেষণার আয়োজন করতে হত। এক পক্ষে তাঁকে চিন্তা করতে হত যে এবারে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় বা সূত্র অবলম্বন করে লিখবেন, সেই চিন্তার মধ্যে এটাও খেয়াল রাখতে হত যে বিষয়টির সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এবং একবার মনঃস্থির করার পরে শুরু হত সেই বিষয়টির সঙ্গে জড়িত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের পালা। অপর পক্ষে চলত বিষয়টি নিয়ে গল্প নির্মাণের জন্য কোনও উপযুক্ত স্থান বা দ্বীপ বা দেশের অনুসন্ধান এবং কাহিনী সংঘটনের জন্য পছন্দমতো ক্ষেত্র চিহ্নিত করার পর শুরু হত সেই অঞ্চলের বিশদ প্রাকৃতিক তথা ভৌগোলিক বিবরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি এবং সেইসঙ্গে সেখানকার ভাষা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-মেলা, সংস্কৃতি, জনজীবন ইত্যাদি, এমন কী জীবজন্তুর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ। কিন্তু গল্প লেখার সময় শুধু সেটুকু তথ্য ও জ্ঞানই বেছে নিতেন যেটুকু গল্পটিকে বিপুল অবিশ্বাস্যতা সত্ত্বেও সত্যপ্রতিম করে তোলার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। সেই বাছাইয়ের পরে বিভিন্ন চরিত্রকে ব্যবহার করে প্রেমেন্দ্র মিত্র যেভাবে ঘটনাগুলি কল্পনা ও বিন্যস্ত করে এক-একটি নাটকীয় কাহিনী গড়ে তুলতেন সেটাই তাঁর প্রতিভার পরিচয়।
ঘনাদার প্রতি প্রেমেন্দ্রর বিশেষ পক্ষপাত ছিল বলেই শত অসুবিধের মধ্যেও প্রত্যেক বছর তিনি ঘনাদাকে নিয়ে গল্প লিখে গেছেন। পক্ষপাতের একটি কারণ এই যে যেমন পাঠকেরা ঘনাদাকে ভীষণ ভাল না-বেসে পারেনি তেমনই লেখকও।
তা ছাড়া প্রেমেন্দ্র সারা জীবনই অন্তরে ছিলেন তাদের দলের দলী ‘অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম’ এবং ঘনাদার কাহিনী লেখার উপলক্ষ্যে তিনি উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু, দুর্গম অরণ্যপথ, দুরারোহ আগ্নেয়গিরি, এমন কী এভারেস্টেরও শিখরে, পৃথিবীর দুয়ে বা দুরধিগম্য নানা প্রান্তে প্রান্তে অভিযান করে বেড়িয়েছেন এবং কল্পনা-সাধিত সেসব অভিযানে নিজেই পেয়েছেন গভীর আনন্দ। মানসিকতায় তিনি বৈজ্ঞানিক, বস্তুর স্বরূপসন্ধানী ও যুক্তিবাদী এবং স্বভাবে জ্ঞানপিপাসু ও তথ্যজিজ্ঞাসু আর প্রতিভায় ছিলেন উদ্ভাবনে উর্বর ও সংস্থাপনে কুশলী। চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্ত বাস্তব ভিড়-ব্যস্ততা ও হিসেব-কেতাবের দাবি-দাওয়ার জটাজালের মধ্যে বাঁধা পড়েও তাই সেই মানসিকতা, স্বভাব ও প্রতিভাকে চরিতার্থ করার সুযোগ তিনি খুঁজে নিতেন ঘনাদার কাহিনী রচনার মাধ্যমে।
অপর একটি কারণ হল ছোটদের বিকাশশীল চরিত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগ্রত করার দায়। তাঁর মুখে শুনেছি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, তখন তিনি চলে যান তাঁর জন্মস্থান বারাণসীতে এবং সেখানে কলকাতা থেকে আসেন মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য দু-ভাই। বিজ্ঞানে আগ্রহ-উদ্দীপক বাংলা শিশুসাহিত্য গড়ে তোলার জন্য তখন তিনজনে মিলে নানা পরিকল্পনা করেন। প্রেমেন্দ্র উৎসাহের চোটে লিখে ফেললেন ছোট একটি উপন্যাস এবং বছর তিনেক পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ‘রামধনু’ নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করলেন আর তাতেই বেরোয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই উপন্যাস, যা পরে ‘পিঁপড়ে পুরাণ’ নামে ডি. এম. লাইব্রেরি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। প্রেমেন্দ্র অচিরে হয়ে ওঠেন সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘মৌচাক’ পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক। একে একে ‘কুহকের দেশে’ ‘ময়দানবের দ্বীপ’, ‘পৃথিবী ছাড়িয়ে’, (পরে ‘শুক্রে যারা গিয়েছিল’ নামে প্রকাশিত) ‘আকাশের আতঙ্ক’, ‘শমনের রং সাদা’ প্রভৃতি কাহিনী লিখে তিনি বাংলায় বিজ্ঞানভিত্তিক মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির পথ খুলে দেন আর পাশাপাশি লেখেন বিজ্ঞান-বিষয়ক নানা নিবন্ধ, এমনকী বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানির জন্য বিজ্ঞাপনের কপি লেখাতেও তিনি অভিনবত্ব আনেন বিজ্ঞানের জ্ঞান সহজ করে পরিবেশনে। বিজ্ঞানচেতনা সঞ্চার করা ছিল প্রেমেন্দ্রর জীবনের একটা ব্রত। ঘনাদার গল্পে আছে সাহিত্যের মাধ্যমে সেই ব্রত পালনের তন্নিষ্ঠা ও বিস্তার।
আরও একটি কারণ স্পষ্ট— সাহিত্যিকের দায়। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে ১৯৪৪ সালে ‘কেন লিখি’ নামে যে-সংকলনটি প্রকাশিত হয় তাতে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, ‘লেখাটা শুধু অবসর বিনোদন নয়, মানসিক বিলাস নয়। সামনে ও পেছনের এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দুজ্ঞেয় পণ্যময় জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল এক দায়।’ লেখাটা তাঁর জীবিকা ছিল না, ছিল জীবন। তাই তিনি লেখার কারণকে এক কথায় প্রকাশ করেছিলেন, ‘আমি লেখার একটিমাত্র কারণই বুঝি—বুঝি যে সত্যিকার লেখা শুধু প্রাণের দায়েই লেখা যায়—জীবনের বিরাট বিপুল দায়।’ একটি বাক্যের এই মন্তব্যটির গভীরতর তাৎপর্যকে বোঝা প্রয়োজন। কারণ উল্লিখিত দায়টা ঘনাদার গল্পগুলো লেখার পেছনেও সমান সক্রিয়। ঘনাদার বানিয়ে বানিয়ে নিজের বাহাদুরির গল্পগুলির অবলম্বন যেসব তথ্য বা তত্ত্ব রয়েছে তার কোনওটাই বানানো বা লেখকের উদ্ভাবিত নয়, সবগুলোই সম্পূর্ণ সত্য, শুধু ঘটনাবলির বিন্যাসটাই যেটুকু উদ্ভাবিত, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমস্ত গুলগল্পই ছদ্মবেশী শিক্ষামূলক সাহিত্য। ঘনাদার মজাদার গল্পের মোড়কে জ্ঞান বিতরণকেও প্রেমেন্দ্র মিত্র মনে করতেন তাঁর সাহিত্যিক কর্তব্য বলে। বিনোদন আর জ্ঞানদান একই সাহিত্যিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে ঘনাদার গল্পগুলিতে।
দুই
অর্থাৎ ঘনাদার সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনীর ঘটনাজালে আমরা যেসব অজানা বা অচেনা বা নতুন শব্দ কি নাম পাই সেসবকে প্রথমে লেখকের বা কথকের কল্পিত বা বিরচিত মনে হলেও আসলে সেগুলি সত্যই। তেমনই সত্য বিজ্ঞানের কি ভূগোলের কি ইতিহাসের যেসব তত্ত্ব বা তথ্যের উল্লেখ রয়েছে সেসবও। আশ্চর্য কল্পনার জটিল স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া অজস্ৰ জ্ঞাতব্য বিষয়—এটাই লেখকের গল্পগুলো বলার জন্য ভেবে ঠিক করা কায়দা বা ধরন। তাঁর গল্প বলার এই বিশেষ-ধরনটাকে তিনি প্রথম গল্পেই অভীষ্ট পাঠককুলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।
‘মশা’ গল্পটির ঘটনাস্থল সাখালীন দ্বীপ। যখন প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পটি লিখেছিলেন তখন এই দ্বীপটি হঠাৎ সংবাদ-জগতে গুরুত্ব পেয়ে যায়, কারণ তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ আর বিজিত পক্ষের মধ্যে সন্ধির ব্যবস্থাগুলোর সময় সামনে এসে পড়ে সাখালীনের ভাগ্য নির্ণয়ের প্রশ্ন। তাই ঘনাদার মুখে শুনি, ‘সাখালীন দ্বীপের নাম শুনেছ, কিন্তু কিছুই জানো না-কেমন?’ সাখালীন আগে ছিল একা রাশিয়ার, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়ী হয়ে জাপান লাভ করে দ্বীপটির দক্ষিণ ভাগের উপর কর্তৃত্ব, আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিজয়ী পক্ষের শরিক সোভিয়েত রাশিয়া সে-কর্তৃত্ব ফিরে পায়। যে-সময়কার গল্প ঘনাদা এখানে বলেছেন সে-সময় সাখালীন বিভক্তই ছিল। আবার ‘নুড়ি’ গল্পে প্রেমেন্দ্র ঘনাদাকে নিয়ে গেছেন দক্ষিণ গোলার্ধে নিউ হেব্রাইডিজের অন্তর্গত এফাটার কাছে যেখানে ২০° অক্ষরেখা ও ১৭০° দ্রাঘিমা কাটাকুটি করেছে সেখানে আনিওয়া দ্বীপের সংলগ্ন এমন একটা ছোট্ট দ্বীপে যেটার মিকিউ নাম গল্পের প্রথম দিকে ঘনাদা একবারই মাত্র বলেছিলেন আলতোভাবে, কিন্তু পরে যখন অন্যতম শ্রোতা মনে রাখার জন্য দ্বীপটার নাম আবার জানতে চেয়েছেন তখন ঘনাদা বললেন, ‘যা ডুবে গেছে তার নামে কী দরকার?’ এই উত্তর থেকে বুঝতে পারি যে ঘনাদার কল্পনা থেকে মিকিউ দ্বীপটি গল্পের খাতিরে একবার মাথা তুলে উঠে আবার সেই কল্পনার মধ্যেই তলিয়ে গেছে। কিন্তু অস্তিত্বহীন নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত এরকম স্থানের বা বস্তুর উল্লেখ ঘনাদার গল্পে খুবই কম। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ‘লাট্টু’ গল্পটির উল্লেখ করতে পারি। পঞ্চাশের দশকে ভিন্ন গ্রহ থেকে আসা ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত চাকির বিষয়টা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে প্রচুর উত্তেজনা দেখা দেয়, তার অস্তিত্ব বা উদ্ভব নিয়ে তর্ক থেকেই গেছে, তবু সেই আছে-কি-নেই-কে-জানে জিনিসটি নিয়ে ‘লাট্ট’ গল্পটি লেখা।
বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের দিক থেকে ‘মশা’ ও ‘পোকা’র মধ্যে মিল রয়েছে—দুটি গল্পই নির্মিত হয়েছে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—প্রথমটিতে মশার শরীরে এবং পরেরটিতে সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া তথা পঙ্গপালের শরীরে এমন রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে যা জীববিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের একাংশের গবেষণার বিষয়। পার্থক্য শুধু এই যে ওই গবেষকগণের উদ্দেশ্য মানবের হিতসাধন আর গল্পদুটির বৈজ্ঞানিক দুজনের লক্ষ্য মানবের অনিষ্টসাধন। কিন্তু অনিষ্টের চক্রান্তকে বানচাল করতে না পারলে ঘনাদার মান-মর্যাদা কীসের? আবার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরমাণু শক্তির জন্য পৃথিবীর অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে যে-প্রতিযোগিতা শুরু হয় তার প্রতিফলন হয়েছে ‘কাঁচ’ ও ‘হাঁস’ গল্পদুটিতে–এর মধ্যে ‘কাঁচ’ গল্পটি থেকে জানতে পারি যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর সময় থেকেই জার্মানি পরমাণু বিজ্ঞানের চর্চায় বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পরমাণু বোমা তৈরি করলেও পরমাণু বিজ্ঞানে জার্মানিই অধিক অগ্রসর ছিল এ সত্য আজ স্বীকৃত। ভারত যখন পরমাণু বিজ্ঞানের চর্চায় নেহাত অপরিণত তখন প্রেমেন্দ্র ‘কাঁচ’ গল্পে মৌল উপাদান ইউরেনিয়াম আর ‘হাঁস’ গল্পে হাইড্রোজেনের বদলে ডিউটেরিয়ামওয়ালা ভারী জল খোঁজ করার কাহিনী দিয়ে বাংলার কিশোরদের তথা সব বয়েসি পাঠকের মনে পরমাণু বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাতে চেয়েছেন। তেমনই ‘ফুটো’ গল্পে মহাশূন্যের ফোর্থ ডাইমেনশন বা চতুর্থ মাপের জটিল গণিতকে ঘটনার রূপে উদাহরণ দিয়ে যেভাবে সরল করে তিনি বুঝিয়েছেন তা নবীন মনকে মহাজাগতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী করবে, আবার একই সঙ্গে ওই গল্প নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে মঙ্গলগ্রহে যাবার যে-সাধনায় এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক নিমগ্ন তার সামিল হতে।
অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, ‘ঘনাদার জন্য তাঁর স্রষ্টার নাম চিরস্থায়ী হবে।’ এই ঘোষণার তাৎপর্য আমাদের বিশেষ বিবেচনা দাবি করে। ঘনাদার গল্প, যা এক অর্থে লম্বা লম্বা বাততালা, সেগুলোকে আজগুবি গুলগল্পের পর্যায়ে ফেলা কোনওমতেই উচিত হবে না, যদিও ‘সুতো’ গল্পটির প্রস্তাবনায় হাঁসের পেট থেকে পাওয়া কৌটোর চিরকুটে ‘ঘনাদার গুল’ কথাটাই লেখা দেখা গেছে। স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৭৪-এ SPAN পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘Ghana-da is a teller of tall tales, but the tales always have a scientific basis. I try to keep them as fac- tually correct and as authentic as possible. ‘ ঘনাদার গল্প রচনায় প্রেমেন্দ্র-প্রতিভা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যেসব গল্পে সেসবের মধ্যে এই খণ্ডের অন্তর্গত ‘ছুঁচ’ গল্পটি স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবিদার। ঘনাদার বয়ানে মূল গল্পাংশে ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণী-বিদ্যা ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের বিস্তর বিষয়কে অসাধারণ কৌশলে ও দক্ষতার সঙ্গে মিশ্রণ করে ঘনাদার বাহাদুরির বৃত্তান্তকে যেমন জ্ঞানগর্ভ তেমনই রোমাঞ্চকর রূপ দিয়েছেন। আর সেসবের বিপরীতে কৌতুকের বিষয় হিসেবে দেখিয়েছেন মেসের অন্যান্য বাসিন্দাদের বিদ্যের বহর—জর্জ ওয়াশিংটনের কুড়ুল দিয়ে চেরি গাছ কাটার বিখ্যাত ঘটনাটিকে একজন যখন চালিয়েছে লিঙ্কনের নামে তখন আরেকজন শুধরে দেবার নামে নিউটনের নাম করেছে এবং প্রথমজন সেই ভুলটাকে মেনে নিয়েছে ‘উদারভাবে’। এই গল্পের আরবীয় প্রসঙ্গের জের টেনেছেন ‘মাছি’ গল্পটিতে।
ঘনাদার গল্পগুলিতে উপস্থাপিত তথ্য ও সত্যের যে-রহস্যজাল প্রেমেন্দ্ৰ মিত্ৰ সৃষ্টি করে গেছেন তা গল্পগুলি সংকলনের সময় সম্পাদকের কাজকে কঠিন করে তুলেছে। সে-কাজ আরও কঠিন হয় এজন্য যে মুদ্রিত মূল কপিতেই অনেক ভুল থেকেছে। তীব্র একাগ্রতার সঙ্গে একবার গল্প লিখে ফেলার পরে তার প্রুফ দেখার মতো আগ্রহ প্রেমেন্দ্রর ছিল না। দু-একটি উদাহরণ দিই। প্রথম গল্প ‘মশা’ প্রকাশিত হয় ‘আলপনা’-তে, তারপর মুদ্রিত হয় ‘ঘনাদার গল্প’, ‘ঘনাদা চতুর্মুখ’, ‘অফুরন্ত ঘনাদা’ প্রভৃতি একাধিক সংকলনে, সবগুলোতেই একই ছাপার ভুল থেকে যায়—অ্যাম্বার চুরির পরে ঘনাদা ঠিক করেন যে স্টিমার-ঘাটার ওপর কড়া নজর রাখলে চোর সাখালীন থেকে বেরুতে পারতে পারবে না’। বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ‘পারতে’ কথাটা কেটে দিয়েছি। উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থেই ‘ছড়ি’ গল্পে শিশিরের কাছে ঘনাদার ধার-করা সিগারেটের সংখ্যা ‘২৩৯৮টা’ মুদ্রিত হয়েছে। এটাকে করেছি ‘৩২৯৮টা’। আবার ‘টুপি’ গল্পের শুরুতে এভারেস্ট শিখরের তিব্বতি নাম বলা হয়েছে “চো মো লঙ মা’, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঘনাদা যখন সেই নামটি পুনরাবৃত্তি করেছেন তখন হয়ে গেছে ‘চো সো লঙ মা’। সাধারণ পাঠকের কাছে ‘মো’ আর ‘সো’র যথার্থতা নিয়ে তর্ক অবান্তর এবং এই ধাঁধা একাধিক বইয়ে রয়ে গেছে। খোঁজ করে জানলাম, ‘মো’-ই হবে। একাধিক গ্রন্থে সংকলিত ‘ঢিল’ গল্পটিতে মেসের ঠিকানা ‘বারো নম্বর বনমালি নস্কর লেন’ চলে এসেছে। ‘ছুঁচ’ গল্পে গ্যাবোঁতে যখন ঘনাদার সন্দেহ নিরসনের জন্য সোলোমাস বলছেন যে কীভাবে লাভালের সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রিসে যাবার নাম করে তিনি গ্যাঁবোতে হাজির হলেন সেখানে মূল গ্রন্থ ‘আবার ঘনাদা’ থেকে কয়েকটি শব্দের ছাড় গ্রন্থানুক্রমে বহাল থেকেছে। এখানে, ‘আমি গ্যাঁবোতে হাজির হব’–এই অংশটি বর্তমান সম্পাদক-কৃত খোদার ওপর নয়, ছাপাখানার উপর খোদকারি।
আমার লক্ষ্য ছিল সম্পাদনার সময় প্রেমেন্দ্রর প্রতি অনুগত থাকার। তাই ‘সুতো’ গল্পে তিনি যা লিখেছিলেন তার রদবদল করিনি, যদিও তিনি নিজেই ঘনাদারই আর এক মহান কাহিনী ‘সূর্য কাঁদলে সোনা’তে কিছু কিছু অন্যরকম লিখেছেন। কাহিনী দুটির ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্প্রসারিত হয়েছে ‘ঘনাদাকে ভোট দিন’ গল্পটিতেও। অনুমান করা যায় যে ‘সুতো’ লেখার পরে প্রেমেন্দ্র ইংকাদের হত্যা ও পেরু লুণ্ঠনের ইতিহাস অন্তত ছ-সাত বছর ধরে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেই সূর্য কাঁদলে সোনা’ উপন্যাসটি লিখেছিলেন এবং সেদিক থেকে সূর্য কাঁদলে সোনা’র নাম ও তথ্যগুলি স্বাভাবিক ভাবেই বেশি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আমি প্রেমেন্দ্রর লেখার ওপর কলম চালাতে সাহস করিনি, বিশেষত তিনি নিজেই যেখানে আরও যাচাই করে সূর্য কাঁদলে সোনা’তে (বর্তমানে ‘ঘনাদা তস্য তস্য’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) সেই বর্বরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী লিখে গেছেন, বরং এখানে আমি যদ্দুষ্টং তৎ রক্ষিতং নীতিই অবলম্বন করেছি। তিনি যদি আগে কিছু ভুল লিখে পরে তা না শুধরে থাকেন তা হলে আমি কে যে তাঁর ভুল শুধরে দেব! আমার দৌড় ছাপার ভুল শুধরে দেওয়া পর্যন্ত। ‘ভাষা’ গল্পে ম্যালে ও চিনে ভাষায় অনেক কথাবার্তা আছে–আমি নিশ্চিত যে এখানেও প্রেমেন্দ্র তাঁর স্বভাব অনুসারে যথেষ্ট খোঁজখবর করে ম্যালে ও চিনে ভাষার সংলাপগুলি লিখেছিলেন, কিন্তু ওগুলি যথাযথ ছাপা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি এবং পাঠকদের অনুরোধ করব যে ও-দুটি ভাষা জানা থাকলে নিজেই ঠিক-বেঠিক যেন নিজগুণে যাচাই করে নেন ও আমাদেরও ভুলগুলো জানান আর জানা না থাকলে যেন বিশ্বাস করেন যে প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে নির্ভুল থাকতেই সচেষ্ট ছিলেন, কোনও স্তরে মুদ্রণ-প্রমাদ না হয়ে থাকলে সমস্ত নির্ভুলই আছে। এখানে এই খণ্ডের শেষ গল্প ‘মাটি’তে ব্যবহৃত একটি শব্দের ওপর টীকা দেওয়া উচিত—শব্দটি হল ‘নেফা’ (NEFA), যা North East Frontier Agencyর সংক্ষিপ্ত রূপ, এর এখন অস্তিত্ব নেই—নেফা ১৯৭২ থেকে অরুণাচল প্রদেশ নামে পরিচিত।
জাতের বিচারে ঘনাদার গল্পগুলিকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়—কল্পবিজ্ঞানের গল্প আর ইতিহাসের গল্প। কল্পবিজ্ঞানের গল্পকে আধুনিক যুগের রূপকথা বলতে পারি। আধুনিক মানুষ চারপাশের বস্তুবিশ্বের চরিত্র ও স্বরূপ সন্ধান করে, সেই বিশ্বকে নিজের প্রয়োজন মতো উন্নত বা পরিবর্তন করার সাধনা করে—মানুষের এই সন্ধান ও সাধনাকে অবলম্বন করেই আধুনিক রূপকথা বা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের উন্মেষ। এই কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলি ঘনাদাকে ঘিরেই রচিত। সবগুলোই ঘনাদার নিজের কীর্তি-কাহিনী। আর ঘনাদার পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে ইতিহাসের গল্পগুলি। এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গল্পই বিশ্বসাহিত্যে দ্রুত বিকাশশীল কল্পবিজ্ঞান জাতের। বাংলা সাহিত্যেও কল্পবিজ্ঞান শাখার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ঐতিহ্যের সূচনা ঘনাদার এই গল্পগুলি—যে-ঐতিহ্যের প্রথম সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল ‘পিঁপড়ে পুরাণ’ নামের ছোট একটি উপন্যাসে। কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনীর শুরু ‘কুহকের দেশে’ থেকে যাতে রেডিয়মের তেজস্ক্রিয় শক্তিকে ঘিরে ঘটনাচক্র গড়ে উঠেছে।
তবে বিশুদ্ধ কল্পবিজ্ঞান থেকে ঘনাদার গল্প স্বতন্ত্র। প্রেমেন্দ্র নিজেই এগুলোকে tall tales-এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এই পর্যায়ের সাহিত্যরচনায় সবচেয়ে বিখ্যাত নাম কল্পনার সঙ্গে ব্যঙ্গের সমাহারে লেখা ‘The Gods of Pegana’, ‘A Night at an Inn’ প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক লর্ড ডানসেনি, যাঁর পুরো নাম Edward Morten Drax Plankett Dunsany এবং মার্ক টোয়েন, আন্তন শেখভ, এইচ জি ওয়েলস, জি কে চেস্টারটন, আর্থার কোনান ডয়েল, রে ব্র্যাডবুরি প্রভৃতি বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের tall tales লিখেছেন। প্রেমেন্দ্রর নিজস্ব ধরন হল সত্যের বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপরে অবিশ্বাস্যতার মনোহর প্রলেপ প্রয়োগ। ডাহা মিথ্যেকে সহনীয় বা বিশ্বাস্য করে তোলার কোনও চেষ্টা না করে অবিশ্বাস্যতাকেই উপভোগ্য করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক ও পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে চেতনা জাগানো। স্বভাবতই অভিনবত্বের জন্য ঘনাদার গল্প জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে প্রচুর। ঘনাদার বহুগল্পের অনুবাদ শুধু যে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা নয় ইংরেজি অনুবাদে বই হয়ে বেরিয়েছে ‘The Adventures of Ghana-da’ আর হিন্দি অনুবাদে দুখানি বই: ‘ঘনশ্যামদা’ ও ‘ঘনশ্যামদা-কা অউর কিসসা’।
তিন
গল্পের রসগ্রহণের জন্য জরুরি না হলেও তথ্যের দিক থেকে এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে ঘনাদার দৌলতে বিখ্যাত মেসটা একেবারে কাল্পনিক নয়, তার একটা বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। প্রথম যৌবনের অস্থিরতায় প্রেমেন্দ্র যখন একবার শ্রীনিকেতনে যাচ্ছেন কৃষিবিজ্ঞান পড়তে, একবার ঢাকা যাচ্ছেন দাদামশায়ের মতো ডাক্তার হবার জন্য বিজ্ঞান পড়তে, যখন কলকাতায় হরিশ চাটুজ্যে স্ট্রিটে দিদিমার বাড়িটা বিবিধ কারণে ভাড়া দেওয়া রয়েছে তখন কলকাতায় এসে একাধিকবার তিনি ভবানীপুরে গোবিন্দ ঘোষাল লেনের এক মেসে ছিলেন। সেই মেসেরই ছায়া পড়েছে বনমালি নস্কর লেনের মেসের উপর, হয়তো সেই মেসের এক বাসিন্দা বিমল ঘোষেরও ছায়া পড়েছে ঘনাদার উপর-প্রেমেন্দ্র তাঁকে ডাকতেন টেনদা বলে— তবে টেনদা ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও হৃদয়বান। আর প্রেমেন্দ্র ছিলেন তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ। এই গল্পগুলি পড়ে বোঝাই যায় যে ঘনাদার মেসে থাকার খরচ মেসের গুণমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দই পরম উৎসাহে বহন করে তাঁর বিপুল চিত্তাকর্ষক আত্মনেপদী অবিশ্বাস্য গল্পগুলি শোনার লোভে, যদিও প্রথম গল্পটিতে জানানো হয়েছে যে ঘনাদার বড় বড় কথার জ্বালায় মেসের বাসিন্দারা জ্বালাতন, কিন্তু দ্বিতীয় গল্পটিতেই দেখি যে মেসের সদস্যরা ঘনাদার গল্পে আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে।
প্রথম গল্পে বিপিন নামে এক মেসবাসীর দেখা পেয়েছি, কিন্তু পরে তাকে দেখা যায় না। ঘনাদার আসরে প্রধান কুশীলব শিশির, শিবু ও গৌর এবং এই তিনজন ছাড়াও একজন রয়েছে যে সাধারণত নেপথ্যে থেকে গল্পগুলি পাঠকসমাজের জন্য আনন্দের সঙ্গে লিখে গেছে অর্থাৎ গল্পগুলির ‘আমি’। এই ‘আমি’ আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং যথাসময়ে নিজের নামটিও জানাবে—কিন্তু সেটা জানাবে পরবর্তী খণ্ডে। নামগুলির আড়ালে রয়েছেন এক-একজন বাস্তব চরিত্র। শিবু মানে রসসাহিত্যের স্রষ্টারূপে স্বনামখ্যাত শিবরাম চক্রবর্তী যাঁর মতে প্রেমেন্দ্রই বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, গৌর মানে গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু যিনি চলচ্চিত্রের পরিচালক ও একই সঙ্গে একাধিক গল্প-সংকলনের সম্পাদক, আর শিশির মানে চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও অভিনেতা শিশির মিত্র, যিনি গৌরাঙ্গপ্রসাদের সঙ্গে মিলে বসুমিত্র চিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন এবং বসুমিত্রের ব্যানারেই প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ‘কালোছায়া’ ছবিটি তৈরি করেছিলেন।
লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আত্মপ্রকাশ আকস্মিক ও নাটকীয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে গোবিন্দ ঘোষাল লেনের ওই মেসে থাকার সময় আবিষ্কার করেন ঘরের একটা জানলার খাঁজে গোঁজা কার লেখা পুরনো একটি পোস্টকার্ড, কৌতূহলের বশে চিঠিটি পড়তে পড়তে তাঁর মনে বিদ্যুতের উদ্ভাসে এল দুটি গল্প, সেই রাত্রেই গল্পদুটি লিখে পরদিন সকালে পাঠিয়ে দিলেন সেকালের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পত্রিকা ‘প্রবাসী’তে। ফিরে গেলেন ঢাকাতে। মাস তিনেক পরে কলকাতা থেকে সম্পর্কে মামা বীরেন সেনের এক ছত্রের পোস্টকার্ড: সুধীর, তোর প্রবাসী এলে পড়ে পাঠিয়ে দেব। প্রেমেন্দ্ররই ডাকনাম সুধীর। প্রেমেন্দ্র ওরফে সুধীর তো অবাক। পরের চিঠিতে মামা খুলে জানালেন যে ‘প্রবাসী’ জানিয়েছে, দুটি গল্পই মনোনীত ও অচিরে প্রকাশিত হবে। ‘প্রবাসী’তে ১৯২৪-এর মার্চে ‘শুধু কেরানি’ আর এপ্রিলে ‘গোপনচারিণী’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যিক মহলে সাড়া পড়ে গেল। সেই বছরেই ‘কল্লোল’ পত্রিকায় লেখেন ‘সংক্রান্তি’, তার পরে আরও গল্প, আরও কবিতা ও ‘মিছিল’ নামে উপন্যাসটি। পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রাবস্থায় লেখা ‘পাঁক’ উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে বেরোয় প্রথমে ‘সংহতি’ পত্রিকায়, তারপর ‘বিজলী’তে ও শেষাংশ কালি-কলমে’।
রবীন্দ্রনাথ ‘পুনশ্চ’র গদ্যকবিতাগুলি লেখার পাঁচ বছর আগেই প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯২৫-এ ‘বিজলী’, ‘কালি-কলম’ প্রভৃতি পত্রিকায় লেখেন ‘আজ এই রাস্তার গান গাইব—এই নগরের শিরা-উপশিরার’, ‘মানুষের মানে চাই’, দেশবন্ধুর শবযাত্রা দেখে লেখেন ‘পায়ের শব্দ শুনতে পাও? নিযুত নগ্ন পায়ের মহাসংগীত’ ইত্যাদি কবিতাগুলি। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এই কবিতাগুলিই বাংলা গদ্যকবিতার শুরু। সেজন্য বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, ‘He is one of our earliest practitioners-one might say pioneers of the prose poem’ এবং এরও আগে প্রেমেন্দ্রর এসব কবিতার ছন্দ ও ভঙ্গি কীভাবে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘এই ফ্রি ভর্সকে পালিশ করে নিজের মনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আমি আমার জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা “শাপভ্রষ্ট” লিখলুম’ আর প্রেমেন্দ্রকে বর্ণনা করেছেন ‘কবির মধ্যে কবি’ বলে।
প্রেমেন্দ্র মিত্রর প্রথম কবিতার বই ‘প্রথমা’ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। ততদিনে তাঁর ছোটগল্পের তিনটে বই বেরিয়ে গেছে—’পঞ্চশর’, ‘বেনামী বন্দর’ আর ‘পুতুল ও প্রতিমা’। এই ছোটগল্পগুলির বৈশিষ্ট্য হল এক-একটি বাস্তব পরিস্থিতির ভাবার্দ্রতা-বর্জিত গভীর বিশ্লেষণ ও তার সূত্র ধরে মানুষের চরিত্রে নিহিত অতল রহস্যের অমোঘ উদ্ভাসন। পরে পরে প্রকাশিত ‘মৃত্তিকা’, ‘অফুরন্ত’, ‘মহানগর’, ‘নিশীথনগরী’, ‘ধূলিধূসর’ প্রভৃতি ছোটগল্পের সংকলনগুলি এক-একটি চরিত্রশালা— সে-চরিত্রশালায় দেখি যে মানুষের মনের ভেতরে জালের মতো ছড়ানো অন্ধকার বা স্বপ্নালোকিত অলিগলিতে যেসব অভিরুচি ও আবেগ, যেসব ভালবাসা ও দ্বেষহিংসা, যেসব প্রবণতা ও প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকে, সেসব অনুকূল বা দুর্বল মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ বা আক্রমণ করে আশ্রয়দাতাকে এবং তখন অপ্রত্যাশিতভাবে ভেঙে পড়ে মানুষের বাইরের চেহারা, তার প্রতিজ্ঞা, তার ব্যক্তিত্ব, তার সংস্কার। খ্যাতির শিখরে পৌঁছে তারাশঙ্কর বন্দ্যেপাধ্যায় স্বীকার করেছেন যে প্রেমেন্দ্রর ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’ গল্পটি পড়ে তিনি নিজের মতো করে গল্প লেখার প্রেরণা ও সাহস পেয়েছিলেন। বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীকে সম্পূর্ণ এক করে ফেলার কৌশলে সিদ্ধ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বাংলা ছোটগল্পের সর্বাগ্রগণ্য শিল্পী বলা যায়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘ছোটগল্পের টেকনিকের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে শাশ্বত স্বাক্ষর রেখে গেলেন, সে টেকনিক আসলে তাঁর বিষয়বস্তুই।’
প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা সমগ্র সাহিত্য পরিমাণে স্বল্প হলেও বৈচিত্র্যে বিপুল। তিনি কত রসের কত স্বাদের গল্প যে লিখেছেন তার হিসেব দেওয়ার স্থান এখানে নেই। তবু খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি যে নিছক কল্পনার পাখা মেলে দেওয়ার আনন্দেই তিনি এমন অনেক গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি লিখেছেন—যেমন ‘পরীদের গল্প,’ ‘কোয়াই’, ‘চড়ুই পাখিরা কোথায় যায়,’ ‘ল্যাজ-নাড়া ছড়া’ ইত্যাদি—যেগুলিতে পাওয়া যায় রূপকথার অথবা লোককথার অনাবিল রস। আবার মাহুরি কুঠিতে এক রাত,’ ‘বাঘটা! ও বাঘ! বাঘ!’ প্রভৃতি কৌতুক রসের গল্প ও ছড়া। অপ্রাকৃত রসের রহস্যঘন গল্প লিখতে তিনি ভালবাসেন-এ-জাতের গল্পগুলির মধ্যে ভানুমতীর বাঘ’, ‘জঙ্গলবাড়ির বৌরাণী’, ‘তেনা-রা’, ‘নিশুতিপুর’, ‘মাঝরাতের কল’, ‘কলকাতার গলিতে’, ‘জোড়াকুঠির ভাঙাপোল’ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘হয়তো’, ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ প্রভৃতি গল্পেও তাঁর অপ্রাকৃত আবহ সৃষ্টির প্রতিভা প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার ভূতের গল্পের সঙ্গে অদ্ভুত রসের অপূর্ব মিলন হয়েছে মেজোকর্তার গল্পগুলিতে। ঘনাদার মতো মেজোকর্তাও এক বিচিত্র চরিত্র। এঁরা যে-অর্থে বিচিত্র সে অর্থে না হলেও পরাশর বর্মাও কম বিচিত্র নন, কারণ তিনি পেশায় গোয়েন্দা হলেও স্বভাবে কবি এবং এক-এক গল্পে তাঁর এক-এক সাংস্কৃতিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনই আর এক চরিত্র মামাবাবু। প্রেমেন্দ্রর সৃষ্ট এ ধরনের চরিত্রগুলির মধ্যে মামাবাবুই সবচেয়ে প্রবীণ, কারণ তাঁর প্রথম আবির্ভাব ‘মৌচাক’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘কুহকের দেশে’ নামের কিশোর-উপন্যাসে এবং পুনরাবির্ভাব ‘ড্রাগনের নিশ্বাসে’, তারপরে আরও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তদন্তের গল্পে।
কেমন মানুষ ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র? এক কথায় এর উত্তর—অন্তরঙ্গতায় ও আন্তরিকতায় ভরপুর এক মানুষ। যেমন চেনা-অচেনা সমস্ত মানুষকে ভালবাসার তেমনই সমস্ত মানুষের ভালবাসা কেড়ে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁর বাড়িতে সারাক্ষণ সাহিত্য ও সিনেমা জগতের, সাধারণভাবে সংস্কৃতি জগতের, মানুষের আসাযাওয়া এবং বার্ট্রান্ড রাসেল-এর সাম্প্রতিকতম রচনার চুলচেরা বিচার থেকে পরদিনের ঘোড়দৌড়ে সম্ভাব্য বিজেতা ঘোড়ার ঠিকুজিকুষ্টি, জে বি এস হলডেন-এর ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ থেকে কমপিউটার ব্যবস্থার বিপুল সম্ভাবনা পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় নিয়েই আলোচনা চলত। অতিথি-অভ্যাগতদের প্রতি তাঁর স্ত্রী বীণা মিত্রর ছিল অপার প্রশ্রয় ও উদার আপ্যায়ন। তাঁর কথা প্রসঙ্গে লীলা মজুমদার লিখেছেন, ‘প্রত্যেকটি কৃতী পুরুষের পিছনে একজন করে অসামান্যা নারীর প্রভাব থাকে…অনেক পরে প্রেমেন্দ্র নিজেও বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না বীণা তাঁর যে-কোনও নতুন লেখাকে অনুমোদন করছে ততক্ষণ তাঁরও শান্তি থাকত না।’ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ শিক্ষা প্রেমেন্দ্রর ছিল না, কিন্তু নিজেকে তিনি খুবই উচ্চ শিক্ষিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন ইহবাদী ও যুক্তিবাদী, জীবনজিজ্ঞাসু ও জীবনপ্রেমিক এক জীবন্ত বিশ্বকোষ এবং মানবিক সহৃদয়তার এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত।
১৯৭৫ সালে যখন ‘প্রেমেন্দ্র রচনাবলী’ প্রকাশে তিনি সম্মতি দেন তখন স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদক রূপে আমাকে মনোনয়ন করেছিলেন, কিন্তু সেই প্রকাশকের পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। এবার ‘ঘনাদা সমগ্র’ সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে আমি তাঁর পরিবারবর্গ ও বর্তমান প্রকাশকের উদ্দেশে আমার ধন্যতা জানাই।
সুরজিৎ দাশগুপ্ত
১ ডিসেম্বর ১৯৯৯
কলকাতা
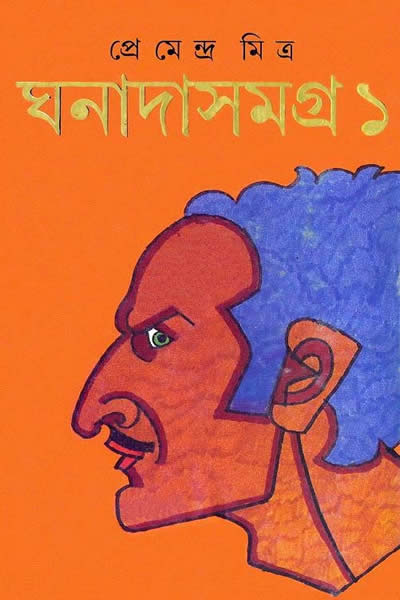
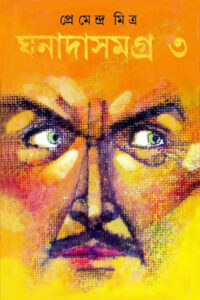
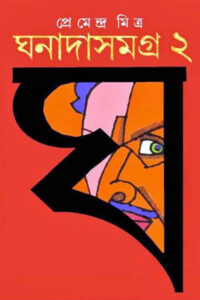

Leave a Reply