কিশোর সাহিত্য সম্ভার – হেমেন্দ্রকুমার রায়
সম্পাদনা – শোককুমার মিত্র
শিশু সাহিত্য সংসদ
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৭
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : গৌতম চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক – দেবজ্যোতি দত্ত
প্রকাশকের কথা
শিশু-কিশোরদের মনের খবর রাখতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়৷ এত যুগ পরেও তাই তাদের জন্য তাঁর লেখাগুলো স্বাদে-গুণে অতুলনীয়৷ ভূত-গোয়েন্দা-রহস্য-রোমাঞ্চ তখনও যেমন ভালো লাগত, এখনও তেমনই লাগে৷ শিশু-কিশোরদের মনের সর্বজনীন ও সর্বকালীন ধর্মটাই এমন৷ হেমেন্দ্রকুমার রায় তাই তাঁর লেখায় উপজীব্য করেছিলেন ওই বিষয়গুলোকেই৷ গল্পের চরিত্র নির্বাচন ও প্লট সাজানোয় তাঁর মুনশিয়ানা এবং লেখায় সাহিত্যগুণ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল্যবান বৈশিষ্ট্য৷ এতে কিশোর মনের প্রকৃত পুষ্টির সহায়ক হয়৷ হেমেন্দ্রকুমার রায় তাই আজও যথেষ্ট জনপ্রিয়৷
তাঁর সুনির্বাচিত ১৮টি গল্প ও ৫টি উপন্যাস নিয়েই প্রধানত এই সংগ্রহ৷ এর সঙ্গে একটি নাটিকা ও কয়েকটি ছড়া যুক্ত হয়েছে৷ হেমেন্দ্রকুমার রায় অনেক গুণের গুণী ছিলেন৷ ছড়াগুলি ও নাটিকাটি তাঁর সেই স্বাভাবিক গুণেরই পরিচয় বহন করে৷ বিমল-কুমার-জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবুদের বাইরে এই হেমেন্দ্রকুমারকেও জানুক আমাদের সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকারা এই অভিপ্রায়ে এদের অন্তর্ভুক্ত করা গেল৷ জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে এগুলিও তাদের ভালো লাগবে এমন আশা রইল৷
সংকলনভুক্ত লেখাগুলি প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য হেমেন্দ্রকুমারের পুত্রবধূ শ্রীমতী শেফালী রায় ও এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স-এর শ্রীশমিত সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ৷
দেবজ্যোতি দত্ত
.
ভূমিকা
বুদ্ধদেব বসু একবার মন্তব্য করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আজীবন ছোটোদের জন্য বড়োদের কবিতা লিখে গেছেন এবং সুকুমার রায় বড়োদের জন্য ছোটোদের লেখা লিখে গেছেন৷ কোনটা বড়োদের জন্য লেখা এবং কোনটাই-বা ছোটোদের মনে করে লেখা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ বেশি নয়৷ তবু একটু অসুবিধে হয় বই কী! রবীন্দ্রনাথের সে কি ছোটোদের জন্য লেখা? যদিও তা প্রকাশিত হয়েছিল ছোটোদের পত্রিকায়৷ অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালাগুলো কি ছোটোদের?
একটা সময় ছিল যখন বাংলা সাহিত্যে বড়োদের লেখার পাশাপাশি ছোটোদের লেখা নিয়ে একটি আন্দোলনের আয়োজন হয়েছিল৷ উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকেই এ বাবদ বেশ কিছু লেখক আবির্ভুত হয়েছিলেন৷ অবশ্য প্রধান প্রেরণা ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি৷ এ বাড়িকে কেন্দ্রে রেখে পরপর বেশ কিছু লেখক কিশোরদের জন্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন৷ প্রমদাচরণ সেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং আরও অনেকের কথাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়৷ এ ধারা অনুসরণ করে চলে আসেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রভৃতি যাঁদের মধ্যমণি ছিলেন সুকুমার রায়৷ বেরোয় প্রচুর কিশোর পত্রিকা৷ সখা, বালক, মুকুল, সাথী, সন্দেশ-কত নাম আর করা যায়৷
যাঁদের কথা উপরে বলা হল তাঁরা অধুনা কিশোর সাহিত্যের এক-একজন দিকপাল বলে স্বীকৃত৷ এসব লেখকের বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা আজীবন শিশু বা কিশোরদের জন্য সাহিত্য রচনাতে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন৷ রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্বতন্ত্র৷ রবীন্দ্রনাথকে তো আর কোনো বিশেষ শ্রেণিতে আটকে রাখা যায় না৷ বাকি যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁদের সকলেই ছোটোদের জন্য ছোটোদের লেখাই লিখে গেছেন৷ তাঁরা সচরাচর তাঁদের নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন৷
কিন্তু ব্যতিক্রম কি থাকে না? এ ব্যাপারেও ছিল৷ কিছু লেখককে পাওয়া যায় যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন বড়োদের উপযোগী লেখা, তারপর অকস্মাৎ কালের সাগর পাড়ি দিয়ে চলে এসেছিলেন ছোটোদের প্রাঙ্গণে এবং আর কখনোই সে প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করার বাসনা দেখাননি৷ এ শ্রেণির লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শিবরাম চক্রবর্তী৷
হেমেন্দ্রকুমার ‘ভারতী’ গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন৷ তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধু৷ রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর বিশেষ স্নেহভাজন৷
বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার একজন বরিষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার৷ রেনেসাঁস-মানুষের বড়ো বৈশিষ্ট্য হল জীবনের সর্বদিকে তাঁদের মনোসঞ্চার৷ হেমেন্দ্রকুমারের মধ্যে এ সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশ সকলেই লক্ষ করবেন৷
হেমেন্দ্রকুমার গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, লিখেছেন প্রবন্ধ৷ নাচ গান চিত্রকলার প্রতি ছিল তাঁর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ৷ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ঘনিষ্ঠজন ছিলেন তিনি৷ তাঁর নাটকের জন্য গান লিখে দিয়েছেন, নৃত্য পরিচালনা করেছেন৷ নাচঘর পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে বাংলা থিয়েটার ও নবজাত বাংলা ফিল্মের একজন গভীর অনুরাগী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন৷ তাঁর থিয়েটার, ফিল্ম ও অন্যান্য আর্টবিষয়ক নিবন্ধ একালের পাঠকদেরও ভাবিয়ে তুলতে সক্ষম৷ বড়োদের উপযোগী তাঁর লেখা কিছু গল্প এমনকী সেকালে বিদেশি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল৷ কিন্তু কলরবমুখরিত খ্যাতির এ অঙ্গন তিনি অগ্রাহ্য করে চলে এলেন কিশোরদের আঙিনায়৷ এবং আর ফিরে গেলেন না৷ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে মৌচাক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ পেতে লাগল তাঁর লেখা যকের ধন৷ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জনপ্রিয় হল৷ শিশুদের মনস্তত্ত্ব যথাযথ অনুধাবন করে তারপর থেকে তাঁর কলম দিয়ে বেরোতে লাগল কিশোর পাঠকদের জন্য প্রীতিসিক্ত রচনা৷ যকের ধন প্রকাশের পর কেটে গেল প্রায় তিরাশি বছর৷ এখনও তার জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি৷ জনপ্রিয়তার জোরে সেকালে এ বইখানি চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছিল৷
যকের ধন বইতে বিমলকুমার রামহরি ও বাঘাকে সঙ্গী করে চলে গিয়েছিল দুর্গম কাছাড় অঞ্চলে অভিযানের টানে৷ আবার যকের ধন তাদের এনে ফেলেছিল তখনকার প্রায় অপরিচিত আফ্রিকা মহাদেশের দুর্গমতর মরু কান্তারে৷
আফ্রিকা পরিচিত ছিল অন্ধকারময় দেশ হিসেবে৷ বহু মানুষের ধারণা ছিল আফ্রিকায় আছে শুধু ভয়াবহ মরুভূমি, বিপজ্জনক নদী, অসংখ্য হিংস্র জন্তু এবং নরখাদক আদিম মানুষ৷ আর আছে গরিলা যাদের জীবতাত্ত্বিক অবস্থান বানর ও মানুষের অন্তর্বর্তী পর্যায়ে৷ তাই বড়ো মাপের অভিযানের জন্য আফ্রিকা হয়ে উঠেছিল তখনকার বহু বাঙালির সাহিত্যচর্চার বিষয়৷ বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের আফ্রিকার জঙ্গলে-র সঙ্গে উচ্চারিত হতে লাগল যকের ধন৷ সিংহদমন গাটুলার সাহায্য নিয়ে গুপ্তধনের সন্ধানে ডাকাবুকো বিমল ও কুমারের ভয়াবহ অভিযান৷ বাঙালি কিশোরদের অকুতোভয় ‘আইকন’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল তারা৷
অধুনা কোনো কোনো মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে, ভূতপ্রেতের গল্প কিশোরমনের উপযোগী নয়৷ এসব কাহিনি নাকি কিশোর মনে ভুল বার্তা পাঠায়৷ রূপকথার গল্পও বাতিল কেননা তা অবাস্তবতাকে প্রশ্রয় দেয়, গোয়েন্দা গল্পও পরিত্যজ্য কারণ খুন-জখম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা কিশোরদের একেবারেই উচিত নয়৷
এ ধরনের অভিমত আসলে এক ধরনের অপপ্রচার৷ বেশ কয়েক বছর আগে সারা বিশ্বে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল যে, কিশোর পাঠকরা কোন শ্রেণির রচনা সব থেকে বেশি পছন্দ করে৷ কিশোর দল জানিয়েছিল তাদের পছন্দের তালিকায় অগ্রবর্তী হিসেবে অবস্থান করছে ভূতের গল্প, গোয়েন্দা কাহিনি, লোককথা, রূপকথা, অভিযানের গল্প ইত্যাদি৷ তাই অপপ্রচারের বাধা কাটিয়ে সাহিত্যের সত্যের দিকে চোখ ফেরাতে হয়৷ সাংস্কৃতিক মহলে শিশু-কিশোর সাহিত্য যখন এভাবে আক্রান্ত হতে থাকে তখন কিশোর সত্যের সন্ধানের জন্য যাঁদের দিকে একাগ্রতা নিয়ে তাকাতে হয়, হেমেন্দ্রকুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম৷
শিশু-কিশোর সাহিত্যের শিল্পী হিসেবে যাঁদের নাম কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা অনেকেই নিজেদের নিবদ্ধ রেখেছেন উল্লেখিত দু-চারটি বিষয়ের মধ্যে৷ উপেন্দ্রকিশোর মূলত লোককথার শিল্পী, দক্ষিণারঞ্জন রূপকথার, যোগীন্দ্রনাথ মজার ছড়া ও গল্পে৷ সুকুমার রায়কেও অবশ্য মজার ছড়া ও গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা চলে বটে কিন্তু তাঁর রচনার অভ্যন্তরীণ চাপ সব কিছু সংজ্ঞাকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসে এবং তা শেষ পর্যন্ত আর শিশু-কিশোরদের জন্য নির্দেশিত থাকে না৷
হেমেন্দ্রকুমার কিন্তু উল্লেখিত কোনো একটি বা দুটি বিশেষ ধারার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেননি৷ তুলনামূলকভাবে একটু বেশি বয়সে শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেও তাঁর রচনার পরিমাণ কিন্তু কম নয়৷ একাধিক মুদ্রণ ও সংস্করণ তাঁর রচনাকে এখনও পূর্ণমাত্রায় জীবিত বলে প্রমাণ করছে৷
হেমেন্দ্রকুমারের বিস্তীর্ণ সাহিত্যশস্যক্ষেত্রের দিকে নজর করলে দেখা যাবে শিশু-কিশোরদের উপযোগী এমন কোনো ফসল নেই যা তাঁর দ্বারা ফলন করা হয়নি৷ উপন্যাস লিখেছেন অনেক, তাদের ধরনও আলাদা৷ গোয়েন্দা, অভিযান, ভূত, ইতিহাস, কল্পবিজ্ঞান-কী নেই তাঁর উপন্যাসসমূহে৷ শিশু-কিশোরের পছন্দসই বেশ কিছু চরিত্র বাঙালি লেখকরা সৃষ্টি করেছেন৷ মনে পড়বে ঘনাদা, টেনিদা, ফেলুদা, পিণ্ডিদা, হর্ষবর্ধন গোবর্ধন প্রভৃতির কথা৷ কিন্তু দু-জোড়া স্মরণীয় চরিত্র সম্ভবত আর কেউ সৃষ্টি করেননি হেমেন্দ্রকুমার ছাড়া৷ তাঁর বিমল ও কুমার এবং জয়ন্ত ও মানিককে চেনে না এমন বাঙালি কিশোর নেই৷ সঙ্গে জয়ন্ত মানিকের সঙ্গী সুন্দরবাবু ও তাঁর ‘হুম’৷ বিমল-কুমারের রামহরি ও বাঘাকে এ তালিকায় যোগ করা যায়৷ বিমল ও কুমার অ্যাডভেঞ্চারের রাজা, জয়ন্ত ও মানিক হল গোয়েন্দা শিরোমণি৷ কেউ কি ভুলতে পারে বিমল ও কুমারের যকের ধন-এর অভিযান অথবা হিমালয়ের ভয়ংকর? তাদের বিচরণভূমিকে হেমেন্দ্রকুমার শুধুমাত্র মর্তেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, পাঠিয়েছেন মহাকাশে৷ গ্রহান্তরে৷ এবং তখনকার বাঙালিদের কাছে প্রায় মহাকাশের মতোই অপরিচিত আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায়৷ তাদের সঙ্গী হয়েছে শুধু বিনয়বাবু ও বাঘাই নয়, একটি কিশোরী পর্যন্ত৷ কিশোরীদেরও তিনি অবহেলা করেননি অভিযানের কাহিনিতে৷ বিমল ও কুমার ডাকাবুকো৷ সেই সঙ্গে বুদ্ধিমান৷ জয়ন্ত ও মানিক বুদ্ধিমান৷ সেই সঙ্গে ডাকাবুকো৷ আসলে কিশোরদের কল্পনাকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য৷ তা করতে গিয়ে তিনি এমনকী বিজ্ঞানকেও দরকারে অগ্রাহ্য করেছেন৷ নইলে বানরের খুলিতে মানুষের মগজ ভরে দিলেই যে তারা কথা বলতে পারবে এমন অসম্ভব কথাও তিনি লিখে গেছেন অক্লেশে৷ ইতিহাসকে আশ্রয় করে লিখেছেন পঞ্চনদের তীরে৷ হর্ষবর্ধন রাজশ্রীকে নিয়ে অনুভবী গল্প, কাশ্মীর অভিযানে ব্যাপৃত বাঙালিদের বীরত্বগাথা৷ আলো দিয়ে গেল যারা বইটির মধ্যে প্রতিটি কাহিনিতে রয়েছে হেমেন্দ্রকুমারের ইতিহাসপ্রীতি৷ যেসব কাহিনি পাঠ্যবইয়ের সীমার মধ্যে পড়ে না তাদের প্রাণ দিয়েছেন তিনি৷ কিশোরদের মন যাতে নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি প্রীতিপূর্ণ থাকে তার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন হেমেন্দ্রকুমার৷
কবিতা ও ছড়া লিখতে ভালোবাসতেন হেমেন্দ্রকুমার৷ পেশাদার মঞ্চের নাটকে তিনি বেশ কিছু গান লিখে দিয়েছিলেন৷ যেন তারই রেশ ধরে বেশ মজাদার ছড়া ও কবিতা লিখেছেন বিবিধ গল্প ও উপন্যাসে৷ সোনার আনারস উপন্যাসটির কথাই ধরা যাক৷ এ কাহিনিতে একটি ধাঁধা আছে ছড়ায় লেখা৷ এ ধাঁধার বৈশিষ্ট্য হল এটি খুব একটা দুরূহ নয়৷ কিশোররাই যাতে বুদ্ধি খাটিয়ে এ ধাঁধার অর্থ বার করতে পারে লেখার সময় একথাটি ভোলেননি হেমেন্দ্রকুমার৷ কবির মগজ বানরের মাথায় প্রোথিত করার ফলে যে কবিতা উৎপন্ন হয় সেগুলোও কিশোরদের ভালো লাগার জন্যই লেখা৷
বিদেশি সাহিত্য থেকে অকাতরে নিয়েছেন হেমেন্দ্রকুমার৷ যেমন নিয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর ও শিবরাম৷ কিন্তু এসব সাহিত্যসৃজনকে কখনোই বিদেশি বলে মনে হয় না৷ জার্মান লেখক এরিখ কাস্টনারের কাহিনি থেকে নিয়েছেন দেড়শো খোকার কাণ্ড৷ পরিবেশনের মুনশিয়ানায় কখনো তাদের বিদেশি বলে মনে হয় না৷ নিয়েছেন এডগার এলান পোর ভীতিপূর্ণ গল্প থেকে৷ সার আর্থার কোনান ডয়েলের গল্প থেকে৷ এবং আরো এধার-ওধার থেকে৷ সব লেখাই বিশেষভাবে যেন হেমেন্দ্রবৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ৷ সিনেমার গল্প থেকে নেওয়া তাঁর কিং কং পড়ে কৈশোরে কে-না শিহরিত হয়েছেন৷ কে-না হন৷ আমাদের কৈশোরে তো চেতনায় ধ্বনিত হত ‘কং কং কং-টাস্কো টাস্কো’৷
আসলে হেমেন্দ্রকুমারের সব ধরনের লেখার মধ্যেই প্রকাশ পেত এক আশ্চর্য ও অন্তরঙ্গ প্রসন্নতা৷ তাঁর জীবনযাপনের মধ্যে তিনি নিরন্তর চর্চা করে অর্জন করেছিলেন সুগভীর প্রসন্নতা-তাকে তিনি প্রবাহিত করে দিতে পেরেছিলেন তাঁর সাহিত্যে৷ বাগবাজারের গঙ্গার তীরের বাড়িতে বসবাস করে তিনি লিখতেন৷ সামনে দিয়ে বয়ে যেত গঙ্গা৷ এখনকার মতো কলুষিত ও চর-পড়া গঙ্গা নয়৷ প্রশস্ত মালিন্যহীন দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে৷ গঙ্গার কলুষতাহীন নির্মল বাতাস, আকাশের ভাববৈচিত্র্য তাঁর কল্পনায় প্রাণ ও শক্তিসঞ্চার করত৷ হেমেন্দ্রকুমারের লেখায় পাওয়া যায় প্রকৃতির এ প্রাণশক্তি ও ঔদার্য৷
কিশোর মনের পক্ষে এ প্রাণশক্তি ও ঔদার্য গভীরভাবে দরকারি৷
কালিন্দী বিষ্ণু বসু
কলকাতা-৭০০০৮৯
১.১.২০০৭
.
হেমেন্দ্রকুমার রায়
(হেমেন্দ্রকুমার রায় – জন্ম : ২.৯.১৮৮৮ মৃত্যু : ১৮.৪.১৯৬৩)
১৩৩০-এ ছোটোদের প্রায়-নতুন মাসিক পত্র মৌচাক-এ এক ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু হল, নাম যকের ধন৷ লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়৷ প্রথম সংখ্যা থেকেই সে লেখা পাঠকদের মুগ্ধ করে এক অনতিক্রম্য আকর্ষণে বেঁধে ফেলল৷ এমন অভিনব গল্প এর আগে বাংলার কিশোর পাঠক পড়েনি, কখনো ভাবেনি যে, এমন লেখা কোনো লেখক তাদের হাতে তুলে দিতে পারেন৷ রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি-যার প্রতি পদে বিপদ আর বিপদজয়ের দুঃসাহসিক প্রয়াস৷ পত্রিকার একটি সংখ্যা পাঠের পর পরবর্তী সংখ্যার জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষার এমন রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা এর আগে আর কখনো হয়নি৷ সেদিনের কিশোর পাঠক এবং পরবর্তীকালের বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক বিমল দত্তের জবানবন্দিতে সেদিনের ছবি বড়ো স্পষ্ট হয়েছে-‘হেমেন্দ্রকুমারের যকের ধন যখন মৌচাক-এ মাস মাস বেরোচ্ছে তখন আমি স্কুলের ছাত্র৷ আমি তখন একটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক৷ যেসব কিশোর এই গ্রন্থাগার থেকে বই নিত তারা একযোগে মৌচাক পড়তে চাওয়ার ফলে মৌচাক ইস্যু করা হত না৷ তারা সকলে গোল হয়ে বসে মৌচাক একসঙ্গে পড়ত৷ আমাকে নিয়মিতভাবে তখনকার হ্যারিসন রোডে এম. সি. সরকারের দোকান থেকে খোদ সুধীরচন্দ্র সরকারের কাছ থেকে মৌচাক নিয়ে আসতে হত৷’ অর্থাৎ ডাকে আসার দেরিটুকুও কিশোর পাঠকেরা নষ্ট করতে চাইত না৷ বলা যেতেই পারে যকের ধন প্রকাশের ফলে বাংলা ছোটোদের সাহিত্যে নতুন যুগের শুরু হয়ে গেল৷
সত্যিকথা বলতে কী, বাংলায় ছোটোদের রসসাহিত্যে নানা রসের জোগান থাকলেও অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের কোনো অস্তিত্ব ছিল না৷ এক আলাপচারিতায় শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এই অভাবের দিকটি নির্দেশও করেছিলেন৷ এমন কাহিনি চাই যেখানে অজানার আকর্ষণে আর দুঃসাধ্য সাধনের উৎসাহে ছোটোদের মনে বিপদ বাধার সঙ্গে লড়াই করার দুঃসাহস জোগাবে৷ জোগাবে অজানাকে করতলগত করতে আপনার দেহ ও মনের বল বীর্য বুদ্ধি ও কৌশল দিয়ে মৃত্যুকে উপেক্ষা করার শক্তি৷ এই সোজা শিরদাঁড়াযুক্ত নির্লোভ সাহসী তরুণের ছবি সেদিনের বাঙালি কিশোরের সামনে তুলে ধরা একটি জাতীয় কর্তব্যও ছিল৷ কারণ তখন বাংলায় ছোটোদের জন্য গল্প লেখার একটি নির্দিষ্ট ছক ছিল৷ সেই ছক ভেঙে হেমেন্দ্রকুমার প্রথমে তাঁর পাঠককে নিয়ে গেলেন আসামের দুর্গম খাসিয়া পাহাড়ে৷ সাধারণ বাঙালির তখন দৌড় বড়োজোর হাওয়া বদলের দেশ মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা কি গিরিডি৷ অথচ যকের ধন উদ্ধারে বিমল-কুমার চলেছে নির্জন দুর্গম পাহাড়ি পথে সঙ্গী যাদের রামহরি আর বাঘাকুকুর৷ লুকোচুরি চলেছে শয়তান করালী মুখুজ্যে আর তার দলবলের সঙ্গে৷ এ কাহিনির ছত্রে ছত্রে শিহরণ-যা হেমেন্দ্রকুমারকে একটি লেখাতেই কিশোর সাহিত্যের সম্রাটের আসনে বসিয়ে দিল৷
অথচ এতকাল হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন বয়স্যপাঠ্য সাহিত্যকার, কবি, প্রাবন্ধিক৷ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা ভারতী গোষ্ঠীর একজন৷ রবীন্দ্রনাথের দিদি, ভারতী সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর স্নেহধন্য৷ রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি৷ ছোটোবেলা থেকেই শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ৷ মাত্র ১১ বছর বয়সে ছাপার হরফে তাঁর সাহিত্যকীর্তি প্রকাশিত হয়েছিল৷
রেখা ও তুলির প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল ছোটোবেলা থেকে৷ স্কুলের পড়া চুকিয়ে তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে ভরতি হন৷ অবনীন্দ্রনাথের অনুরাগী হেমেন্দ্রকুমার শুনেছিলেন শিল্পাচার্য শীঘ্রই শিক্ষক হিসাবে ওই বিদ্যালয়ে যোগ দেবেন৷ সেই সম্ভাবনা হেমেন্দ্রকুমারকে আর্ট স্কুলে ভরতি হতে প্রেরণা জুগিয়েছিল৷ কিন্তু সেসময় অবনীন্দ্রনাথ আসেননি৷ পরে, হেমেন্দ্রকুমার ওই বিদ্যালয় ছেড়ে আসার কিছুদিন পরে তিনি ভাইস প্রিন্সিপল হিসাবে আর্ট স্কুলের কাজে যোগ দিয়েছিলেন৷
হেমেন্দ্রকুমার জন্মেছিলেন ১৮৮৮-র ২ সেপ্টেম্বর, উত্তর কলকাতায় তাঁদের ২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই লেনের বাড়িতে৷ তাঁর প্রকৃত নাম ছিল প্রসাদ রায়৷ এই নামে ভারতী এবং মৌচাক-এও কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল৷ বাবা রাধিকানাথ রায় মিলিটারি অ্যাকাউন্টস-এ কাজ করতেন৷ সাহিত্য ও সংগীতে তাঁর ছিল গভীর টান৷ স্কুলের পাঠ্যসূচির বাইরে কিশোর হেমেন্দ্রকুমার পিতৃদেবের ইচ্ছানুসারে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁকে পড়ে শোনাতেন শেকসপিয়র, শেলি, কিটস, মিলটন প্রভৃতি সাহিত্যিকদের রচনা৷ ফলে কৈশোরেই যেমন তাঁর মনে সাহিত্যপ্রীতি বাসা বাঁধে, তেমনি সাহিত্য রচনার প্রাথমিক পাঠও নেওয়া হয়ে যায়৷ বাবার সঙ্গে নিত্য সাহিত্য পাঠ ও নানা বিদ্যা বিষয়ক চর্চার ফলে তাঁর মন যথেষ্ট শিক্ষিত হয়ে ওঠে৷ প্রথাগত শিক্ষায় তিনি বেশিদূর না এগোলেও তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার কখনো অপূর্ণ থাকেনি৷ একসময়ে তিনি বাবার অফিসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন, তবে খুব বেশিদিন সেকাজ করেননি৷ তারপরে সাহিত্যসেবাকেই তাঁর জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন৷ তখনই ভারতী পত্রিকা ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণির পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস-কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে৷ শিল্পবিষয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষ গুরুত্ব ছিল৷ যমুনা পত্রিকার মালিক-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল তাঁকে বলেছিলেন, ভালো না লাগলে সামান্য কটি টাকার জন্য পরের চাকরি করার দরকার নেই; অফিসের কাজে সময় নষ্ট না করে লিখলেই ওই টাকা যমুনা থেকে দেওয়া হবে৷ এবং চাকরি ছাড়ার পর যমুনা থেকে নিয়মিত তিনি প্রতিশ্রুত টাকা পেতেন৷ তা ছাড়া অন্য পত্রিকায় লিখেও তাঁর আয় যথেষ্ট হত৷ ততদিনে তাঁর দুটি গল্পের বই পশরা এবং সিঁদুর চুপড়ি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে৷ অনুবাদ করেছিলেন বিখ্যাত ড. ভগনার৷ অনুবাদকের বিশ্বাস ছিল বইদুটির যেকোনো গল্প বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য৷ তাঁর উপন্যাস জলের আলপনা এবং কালবৈশাখী ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যেমন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পত্রিকা বিজলীতে বেরিয়েছিল ঝড়ের যাত্রী৷ এগুলি ছাড়া বড়োদের জন্য তিনি যে বইগুলি লিখেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-মধুপর্ক, সুচরিতা, ভোরের পূরবী, শূন্যতার প্রেম, রসকলি, মালাচন্দন, ফুলশয্যা, পরীর প্রেম, পায়ের ধুলো, আলেয়া, পদ্মকাটা, পাঁকের ফুল, মণিকাঞ্চন ইত্যাদি৷ তাঁর অনূদিত ওমর খৈয়াম গুণীজনের প্রশংসা পেয়েছিল৷
বাংলা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ির যোগ৷ সেই সুবাদে দানীবাবু অমৃতলাল, অপরেশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়৷ আর তাঁর বন্ধু ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি৷ যোগেন চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ীদের সঙ্গেও গভীর যোগ৷ নৃত্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল৷ তিনি সীতা নাটকের নৃত্য পরিচালনা করেছিলেন৷ এই নাটকের জন্য গানও লিখেছিলেন৷ তাঁর রচিত সংগীতের সংখ্যা এক হাজারের বেশি৷ তার মধ্যে সীতা নাটকের ‘মঞ্জুল মঞ্জুলি নবসাজে’ এবং ‘অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে’ ছাড়াও রেকর্ডের গান ‘মন কুসুমের রঙ ভরা’, ‘ও শেফালি তোমার আঁচলখানি’ বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল৷ হেমেন্দ্রকুমার নিজেও সুকন্ঠের অধিকারী ছিলেন এবং রেকর্ড কোম্পানির শুরুর দিকে তাঁর কন্ঠের গান ডিসকে ধরা ছিল৷ নাট্য প্রসঙ্গে তিনি দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন-রঙ্গালয়ে শিশিরকুমার এবং শৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ৷
হেমেন্দ্রকুমার লোকসংস্কৃতির একজন যোগ্য রসিকও ছিলেন৷ ওড়িশার সেরাইকেল্লার রাজপরিবারের নিজস্ব ছৌ নৃত্যের শিল্প মাধুর্য আস্বাদন করে হেমেন্দ্রকুমার এই শিল্পসম্পদকে শিক্ষিত আধুনিক মানুষের কাছে উপস্থাপিত করে তার প্রভূত প্রচার ও মূল্যায়নের সুযোগ করে দেন৷ তাঁকে ওই নৃত্যের আবিষ্কারকের কৃতিত্ব দিলেও অত্যুক্তি হয় না৷ মোহনবাগান ক্লাবের অন্ধ সমর্থক হেমেন্দ্রকুমার একসময়ে খেলাধুলাতেও যথেষ্ট পটুত্ব অর্জন করেছিলেন৷ যৌবনে নিয়মিত খেলেছেন সেকালের প্রতিষ্ঠিত টিম হেয়ার স্পোর্টিং দলে৷
১৩৩১ সালে হেমেন্দ্রকুমার ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সেযুগের চলচ্চিত্র-রঙ্গমঞ্চ ও শিল্পকলা বিষয়ক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা নাচঘর৷ হেমেন্দ্রকুমার ওই পত্রিকার প্রাণস্বরূপ ছিলেন৷ দীর্ঘদিন এই পত্রিকাটি তাঁরই পরিচালনায় একই সঙ্গে জনপ্রিয়তা ও গুণীজনের সমীহ আদায় করেছিল৷
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হেমেন্দ্রকুমার ছোটোদের জন্য যকের ধন লেখার পর ক্রমে কলম বদলে ফেললেন৷ বড়োদের আসর ছেড়ে এসে ধীরে ধীরে ছোটোদের আসরে জাঁকিয়ে বসলেন৷ মৌচাক সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর পত্রিকার জন্য প্রতিষ্ঠিত শিশুসাহিত্যিকদের সঙ্গে বয়স্কপাঠ্য লেখকগোষ্ঠীকেও লিখতে আমন্ত্রণ জানাতেন৷ ভারতী, কল্লোল, কালিকলম, বিচিত্রা গোষ্ঠীভুক্ত লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই মৌচাকে লিখেছেন কিন্তু তাঁদের প্রায় সকলেই দু-নৌকো সামলেছেন৷ শিবরাম চক্রবর্তী আর হেমেন্দ্রকুমার রায় বাকি জীবন মূলত শিশুসাহিত্যেরই সেবা করে গেছেন৷ হেমেন্দ্রকুমারের সৃষ্ট সাহিত্যের পরিধি বিশাল ও ব্যাপক৷ তিনি যেমন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সার্থক পথিকৃৎ, তেমনি রহস্য ও গোয়েন্দা গল্পেরও অন্যতম প্রধান লেখক৷ বিমল-কুমার যেমন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির মানিকজোড় ঠিক তেমনি জয়ন্ত-মানিক হচ্ছে গোয়েন্দা গল্পের দুরন্ত জুটি৷ যকের ধন পাঠক সমাজে এমন আলোড়ন তুলেছিল যে, যেমন কনান ডয়েলকে পাঠকের চাপে শার্লক হোমসকে ফের ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল, হেমেন্দ্রকুমারকেও তেমনি আবার যকের ধন লিখে সে দাবি মেটাতে হয়েছিল৷ অবশ্য বিমল-কুমারের অভিযানে ভাটা পড়েনি কখনো, মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন, ময়নামতীর তীর, মায়াকানন-লেখা তো চলছিলই৷ অ্যাডভেঞ্চারের লেখায় তিনি এমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে, আবার যকের ধনের সন্ধানে বিমল-কুমার আফ্রিকা পাড়ি দিতে ভয় পায়নি, সূর্যনগরীর গুপ্তধনে বিমল-কুমারের সঙ্গী কিশোরী মৃণু ইনকাদের দেশে চলে গেল শুধুমাত্র দুঃসাহসের নেশায় ভর করে, যেমন সে ওদের সঙ্গী হয়েছিল হিমালয়ের ভয়ংকর দিনগুলোয়৷ নীল সায়রের অচিনপুরে-লস্ট আটলান্টিসের গল্পে প্রথম সভ্যতার শেষ আর্তনাদ শুনিয়েছেন তিনি৷ অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় তিনি যেমন দেশে-বিদেশে, পাহাড়ে-পাতালে, এমনকী গ্রহান্তরেও পাড়ি জমিয়েছেন, কিশোর পাঠককে হাজির করেছেন নানা বিপজ্জনক মুহূর্তের সামনে, আবার তা জয় করবার দুঃসাহস দেখিয়ে তার স্নায়ুকে শক্ত করে দিয়েছেন যাতে জীবন যুদ্ধে যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলার মানসিকতা তার গড়ে ওঠে৷ সাহসে ভর করে গড়ে ওঠে কিশোর পাঠকের চরিত্রের ভিত৷ ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের নানা তথ্যে ভরা লেখায় পাঠকের জ্ঞানের ভাণ্ডারও পূর্ণ করে দিতে চেয়েছেন তিনি৷ ইতিহাসের যে কাহিনি পুরোনো ধুলোভরা পাতা থেকে উদ্ধার করে আমাদের উপহার দিয়েছেন সেগুলো বীরত্ব, ন্যায়, সংগ্রাম, দেশপ্রেম ও ভালোবাসায় সমুজ্জ্বল৷ অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি একাজ করেছেন-দায়িত্বশীল শিশুসাহিত্যিকের ভূমিকা স্মরণে রেখে৷
আগেই বলেছি জয়ন্ত-মানিকের গোয়েন্দা জুটি অসংখ্য রহস্যের সমাধান করেছে তাদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, উপস্থিত বুদ্ধি ও অনুমান শক্তির সাহায্যে৷ তাদের কাহিনিতে একটি ভন্ডুলরাম চরিত্র আছে-পুলিশ ইনসপেক্টর সুন্দরবাবু৷ তিনি বিমল-কুমারেরও অনেক অভিযানের সঙ্গী হয়েছেন৷ সুন্দরবাবুর হাস্যকর উপস্থিতি কিছুটা রিলিফের কাজও করে৷ অবশ্য অনেক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সুন্দরবাবু কার্যকরী ভূমিকাও নিয়ে থাকেন৷ বাংলা ছোটোদের সাহিত্যের এই বিভাগটিতে তিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী৷
ভৌতিক এবং অলৌকিক কাহিনি রচনায় হেমেন্দ্রকুমারের লেখনী অতি সচল৷ মৌলিক গল্প, বিদেশি গল্পের আত্তীকৃত গল্প বা অনূদিত গল্প-সকল ক্ষেত্রেই তাঁর লেখায় আশ্চর্য টান৷ মানুষ পিশাচ, বিশালগড়ের দুঃশাসন, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ, মোহনপুরের শ্মশান-এর কাহিনি এমনকী কঙ্কাল সারথি-র মতো ছোটো গল্প পড়তেও ভয়ে শরীরের রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে৷ কল্পবিজ্ঞানের গল্পও তাঁর হাতে বেশ খুলত৷ রংমশাল-এ ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলেন অসম্ভবের দেশে৷
অনুবাদের কাজেও তাঁর মুন্সিয়ানা স্বীকার করতেই হয়৷ জার্মান লেখক এরিক কাস্তনারের এমিল অ্যান্ড হিজ ডিটেকটিভস-এর বাংলা করলেন দেড়শো খোকার কাণ্ড-সে তো বাংলার ঘরের গল্প হয়ে গেল৷ তেমনি কিং কং, আজব দেশে অমলা (অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড), অদৃশ্য মানুষ (ইনভিজিবল ম্যান) ইত্যাদি অনেক কাহিনির ভাষান্তর করেছেন তিনি৷
তাঁর সময়ে আর কোনো সাহিত্যসেবী একই সঙ্গে এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে সাহিত্যচর্চা করতে সাহসী হননি৷ একথা সত্য যে, তাঁর সবকটি লেখাই মাস্টারপিস হয়ে ওঠেনি বটে, তবে সুখপাঠ্যতা ও সাধারণ বিচারে কোনো লেখাই ন্যুন নয়৷ হেমেন্দ্রকুমার কবি ছিলেন-ছোটোদের উপযোগী অনেক কবিতা-ছড়া লিখেছেন৷ নাটিকাও লিখেছেন৷ তাঁর বেশ কিছু নাটিকা বেতারে সম্প্রচারিত হয়েছিল৷ মৌচাক পত্রিকায় ত্রিশের দশকে বাসন্তিকা নামে হেমেন্দ্রকুমার রচিত একখানি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়৷ এটিই ছোটোদের সাহিত্যে একমাত্র গীতিনাট্য৷ শোনা যায়, ‘বাসন্তিকা’ সেকালে মঞ্চস্থও হয়েছিল৷ ছোটোদের জন্য তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা দেড়শো ছাড়িয়েছে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়৷ এরই মাঝে ছোটোদের ভিন্ন মেজাজের সাড়া জাগানো পত্রিকা রংমশাল কৃতিত্বের সঙ্গে দু-দফায় প্রায় পাঁচ-বছর (১৩৪৫-৪৬, ১৩৪৭-৫১) সম্পাদনা করেছেন৷ রবীন্দ্রনাথের একাশিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রংমশাল-এর যে রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন-সেটি তাঁর পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি৷ শরৎসাহিত্য ভবন থেকেও বেশ কয়েকবছর ধরে তাঁর সম্পাদনায় পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হত৷
তাঁর স্মৃতিকথাধর্মী লেখা যাঁদের দেখেছি, এখন যাঁদের দেখছি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল৷ এই গ্রন্থদুটিতে দেখা যায় যে, সারা জীবন তিনি যত বিখ্যাত মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তার খণ্ড চিত্র৷
ভুবনেশ্বরী পদক এবং মৌচাক পুরস্কার ছাড়া আর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার তাঁর জোটেনি বটে, কিন্তু হাজার হাজার পাঠক তাঁর রচনা পাঠে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁকে নিয়ত পুরস্কৃত করছে সেকথা কখনো বিস্মৃত হওয়া যায় না৷
পরবর্তীকালে বাগবাজারে একেবারে গঙ্গার ধারে তিনি একটি ত্রিতল গৃহ নির্মাণ করে বাস করতেন৷ এই বাড়ির তিনতলার বারান্দা থেকে জাহাজে চড়ার রোমাঞ্চ অনুভব করা যেত৷ তিনি ছিলেন শিল্পী, শিল্পরসিক৷ বহু ছবি, মূর্তি ও ভাস্কর্য তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল৷ এ সংগ্রহশালার প্রশংসা বন্ধুদের মুখে মুখে ফিরত৷
১৯৬৩-র ১৮ এপ্রিল কলকাতায় ৫৬১ রবীন্দ্র সরণীর বাড়িতে পরিণত বয়সে বিচিত্রকর্মা মানুষটির জীবনাবসান হয়৷
অশোককুমার মিত্র
বিধাননগর
কলকাতা-৭০০১০৬
১.১.২০০৭
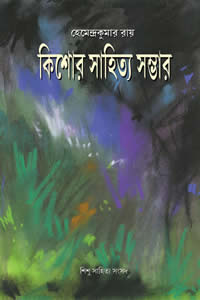

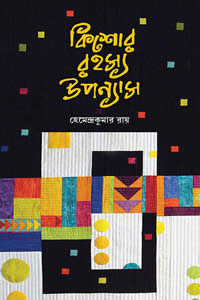


Leave a Reply