কবিতার বাজার মন্দা
ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যজগতে স্বর্ণযুগের সূচনা হল বটে, কিন্তু তাই বলে তার সবটুকুই শোনা নয়। তা হয়ও না। অবিমিশ্র ভালো বা অবিমিশ্র মন্দ কোনো যুগই নয় ইতিহাসে। ভালো—মন্দ মিশিয়ে ইতিহাস। সাহিত্যিক ও প্রকাশকের স্বর্ণযুগের বা উনিশ শতকের ইতিহাসও তাই। প্রথমার্ধের ‘রোমান্টিক পুনর্জীবনের’ যুগ মোটামুটি ভালো বলা চলে। দ্বিতীয়ার্ধে মন্দের ভাগ বেশি। মারি ও লংম্যানের মতন প্রকাশকরাও তখন তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।
প্রকাশকদের যথেষ্ট ত্রুটি—বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতককে নিঃসন্দেহে সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই সময় আদর্শ প্রকাশকরা সাহিত্য ব্যবসায় অবতীর্ণ হন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ের চেয়ে প্রকাশনের ব্যবসা যে ভিন্ন জাতের, একথা তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়ী নীতির দ্বারা প্রমাণ করে দেন। তাহলেও সব পুস্তক ব্যবসায়ীই জন মারি বা লংম্যান, কনস্টেবলের মতন ছিলেন না। সাধারণ ব্যবসায়ীর মতন মুনাফালোভী গ্রন্থব্যবসায়ীও অনেকে ছিলেন। অনেক সাহিত্যিককে তাঁরা বাজারের কাস্টমারের মতন শোষণ করেছিলেন। এই ধরনের প্রকাশকদের লক্ষ্য করেই চার্লস ল্যাম্ব (Charles Lamb) তাঁর বিখ্যাত কটূক্তি করেছিলেন মনে হয়। এক বন্ধুকে চার্লস ল্যাম্ব লিখেছিলেন :
“Throw yourself rather, my dear sir, from the steep Tarpeian rock, slap-dash head-long upon iron spikes. If you had but five consolatory minutes between the desk and the bed, make much of them, and live a century in them, rather than turn slave to the booksellers. They are Turks and Tartars when they have poor authors at their beck… You know not what a rapacious, dishonest set these booksellers are.”
ল্যাম্বের এই স্বীকারোক্তি প্রকাশনের ইতিহাসে একটা দলিলের মতন রয়ে গেছে। এ রকম বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ, এত তীব্র ভাষায়, প্রকাশকদের বিরুদ্ধে আর কোনো গ্রন্থকার বোধহয় প্রকাশ করেননি। তুর্কী ও তাতারদের মতন প্রকাশকরা সর্বগ্রাসী ও অত্যাচারী, একথা জন মারি ও লংম্যানের যুগে ল্যাম্বের মতন লেখকের পক্ষে বলা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। ল্যাম্বের এই ঐতিহাসিক উক্তি থেকে এইটুকু অন্তত বোঝা যায় যে, উনিশ শতকে প্রকাশন জগতে স্বর্ণযুগের সূচনা হলেও, তার সবটাই সোনা ছিল না এবং সকলেই জন মারি বা লংম্যান ছিলেন না।
সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুনর্জীবনের যে জোয়ার এসেছিল, উনিশ শতকের মাঝামাঝি তাতে ভাটা পড়ল। কাব্যেরও যে আদর ছিল গোড়াতে তা আর রইল না। “Poetry was out of fashion”। কাব্যের বাজারে এই সময় সবচেয়ে বেশি মন্দা দেখা দিল। কবিরা প্রথম জখম হলেন। এমনকী জন মারির মতন সৎসাহসী বিচক্ষণ সাহিত্যরুচিসম্পন্ন প্রকাশকও কবিতার বই প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতেন। কাব্যের পাঠক ও প্রকাশক আমাদের দেশে নেই বলে আমরা অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করে থাকি এবং মন্তব্য করি যে, এটা আমাদের দেশেরই বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বৈশিষ্ট্যটা শুধু আমাদের দেশের পাঠকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ বৈশিষ্ট্য ইংরেজি সাহিত্যের, ইংরেজ পাঠক ও প্রকাশকদেরও ছিল একসময়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Wordsworth) বা টেনিসনের (Tennyson) মতন কবিকেও একসময় কাব্যের পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। জন মারির মতন প্রকাশকও কাব্য ও উপন্যাসের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছিলেন। জর্জ প্যাস্টনের ভাষায়, “to look with rather a jaundiced eye on poetry and fiction”। এই সময় মারির মতন প্রকাশকও শুধু কাব্যের নয়, উপন্যাসেরও সমস্ত পাণ্ডুলিপি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন, জেন অস্টেনের উপন্যাস পর্যন্ত নিজে প্রকাশ করার সাহস পাননি।
লংম্যান প্রকাশিত ওয়ার্ডসওয়ার্থের একখানি কাব্য—সংকলন (৫০০ কপির সংস্করণ) বিক্রি হতে চার বছর সময় লেগেছিল। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতা লিখে মোট একহাজার পাউন্ড রোজগার করেছিলেন। টেনিসনের কবিতার পাঠকের সংখ্যাও এত অল্প ছিল এবং এত কম অর্থ তিনি উপার্জন করেছিলেন যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেইজন্য তিনি বিবাহ করতে পারেননি। রবার্ট ব্রাউনিঙের (Robert Browning) অবস্থাও তদ্রূপ। মক্সন (Moxon) ছিলেন ব্রাউনিঙের অন্যতম প্রকাশক। কবিতার চাহিদা তখন এত কম ছিল যে, প্রকাশক মক্সন বাধ্য হয়ে ব্রাউনিঙকে অনুরোধ করেছিলেন, পুস্তিকাকারে (Pamphlets) তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য, যাতে প্রত্যেক পুস্তিকা প্রকাশের খরচ দশ বারো পাউন্ডের বেশি না হয়। ব্রাউনিঙ তাতেই রাজি হন এবং ১৮৪১ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁর অনেক কবিতা পুস্তিকাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এডমন্ড গস (Edmund Gosse) তাঁর “Dictionary of National Biography”—র মধ্যে ব্রাউনিঙের একখানি চিঠি প্রকাশ করেন এই পুস্তিকা প্রকাশের ব্যাপার সম্বন্ধে। তার মধ্যে ব্রাউনিঙ যা লিখেছেন তা সত্যিই মর্মান্তিক। ব্রাউনিঙ লিখেছেন :
“He (Maxon) printed, on nine occasions, nine poems of mine, wholly at my expense; that is, he printed them and subtracting the very moderate returns, sent me in duly, the bill of the remainder of expense…”
প্রকাশক খরচ করে কবিতার বই প্রকাশ করতেন। বই বিক্রি হলে যা পাওয়া যেত তাতে প্রকাশকের খরচ না উঠলে, বাকিটা তিনি কবি ব্রাউনিঙের নামে বিল করে পাঠিয়ে দিতেন। তবু মক্সন অন্যান্য অনেক প্রকাশকের তুলনায় তখন অনেক বেশি উদার ও সাধু ছিলেন।
শুধু মারি বা মক্সন নন, লংম্যান সম্বন্ধেও এই সময়ের অনেক কাহিনি শোনা যায়। তার মধ্যে একটি বিশেষ উপভোগ্য কাহিনির উল্লেখ এখানে করছি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জনৈকা মহিলা লেখিকা প্রকাশক লংম্যানের কাছে তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য সোজাসুজি আবেদন করেন। লংম্যান তার উত্তরে তাঁকে জানান :
“My dear Madam, it is no good bringing me poetry; nobody wants poetry now. Bring me a cookery book, and we might come to terms.”
মর্মার্থ এই ”মহাশয়া, কবিতার বই প্রকাশের জন্য এখন আমাদের কাছে আসবেন না। কবিতা আজকাল আর কেউ পড়তে চান না। তার চেয়ে গৃহস্থালী রান্নাবান্না সম্বন্ধে যদি কোনো বই লেখেন নিয়ে আসবেন, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।” চিঠিখানা পড়লেই বোঝা যায়, প্রকাশক লংম্যান দুঃখ করে বিদ্রুপ করেছিলেন, সত্যিই লেখিকাকে রন্ধনের বই লিখতে বলেননি। কিন্তু লংম্যানের মতন খ্যাতনামা প্রকাশকের কাছ থেকে এইরকম একখানা চিঠি পেয়ে লেখিকা লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, সত্যিই যখন একখানা বই লেখার প্রস্তাব করেছেন লংম্যানের মতন প্রকাশক, তখন এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়। সুতরাং তিনি কবিতা লেখা কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রেখে, রন্ধন সম্বন্ধে বই লিখতে আরম্ভ করলেন। বই লেখা শেষ হলে একদিন লংম্যানের কাছে পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হলেন। লংম্যান তো অপ্রস্তুত। অথচ ওই রকম চিঠি লিখে ফেলেছেন যখন এবং ভদ্রমহিলা যখন সেই চিঠির ওই রকম ব্যাখ্যা করেছেন, তখন কথার খাতিরে বই প্রকাশ না করেও উপায় নেই। মহিলার নাম এলিজা অ্যাকটন (Eliza Acton)। ১৮৪৫ সালে লংম্যান এই মহিলার রন্ধনকলার এই “Modern Cookery” প্রকাশ করেন। একটার পর একটা সংস্করণ হয় বইখানার অল্পদিনের মধ্যে। কিন্তু মহিলার মনে পাছে কোনো ক্ষোভ থাকে, সেইজন্য লংম্যান পরে তাঁকে কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দিতে বলেন প্রকাশের জন্য। এলিজার কাব্যগ্রন্থও লংম্যান প্রকাশ করেন। মহিলা—কবির বাসনা অতৃপ্ত রাখেননি তাঁরা। কবিতার বইখানি একেবারেই বিক্রি হল না, দেখা গেল। অথচ রন্ধনকলার বইখানির সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। তখন লংম্যান একদিন মহিলাকে ডেকে বললেন : ”দেখলেন তো?” পাঠকের রুচি সম্বন্ধে যা বলেছিলাম আপনাকে, তা সত্যি কিনা?”
লংম্যানের জীবনে নতুন যুগের সূচনা হল এই সময়—অবশ্য গৃহস্থালী রান্নাবান্নার বই প্রকাশ করে নয়, মেকলির (Macaulay) ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে। তখন চতুর্থ টমাস লংম্যান প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে ”লংম্যান, ব্রাউন, গ্রীন” (Longman, Brown, Green)। এই পর্বে লংম্যানরা প্রথম প্রকাশ করেন মেকলির “Lays of ancient Rome”, ১৮৪২ সালে। মেকলি এই গ্রন্থখানি লংম্যানদের উপহার দিয়েছিলেন, অর্থাৎ দান করে দিয়েছিলেন সমস্ত স্বত্ব। কিন্তু বইখানি যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন লংম্যান পাণ্ডুলিপিখানি সমস্ত স্বত্বসহ গ্রন্থকার মেকলিকে প্রত্যর্পণ করেন। প্রকাশনের ইতিহাসে এতখানি মহত্ব ও উদারতার পরিচয় আর কেউ দিয়েছেন কি—না সন্দেহ। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকাশক লংম্যানের এই উদারতার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল, কেবল আমাদের দেশে নয়, ওদেশেও। গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব গ্রন্থকারের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় পেয়ে, সেই গ্রন্থ যখন মুনাফা যোগাতে লাগল তখন তা গ্রন্থকারকে সানন্দে প্রত্যর্পণ করা যে কতখানি মহত্বের পরিচয় দেওয়া, তা এদেশের প্রকাশকরা বোধ হয় আজও কল্পনা করতে পারেন না। মেকলে ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই বই যে কত টাকা পেয়েছেন তার হিসেবে নেই।
মেকলির কয়েক খণ্ড ‘ইতিহাস’ ও লংম্যান সাহস করে প্রকাশ করেছিলেন তখন। যে সময়ে পাঠকদের রুচি সম্বন্ধে প্রকাশক লংম্যান পূর্বোক্ত কঠোর মন্তব্য করেছিলেন, সেই সময় মেকলির ইতিহাসের মতন বিরাট নীরস গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করা যে একাধারে কতখানি দুঃসাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া, তাও বোধহয় আমাদের দেশের প্রকাশকরা কল্পনা করতে পারবেন না। শুধু প্রকাশ করা নয়, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতিহাস প্রকাশিত হবার পর, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের জন্য লংম্যান অগ্রিম বিশ হাজার পাউন্ড দিয়েছিলেন মেকলিকে। ১৮৫৬ সালের ১৩ মার্চ লংম্যান চেকে এই টাকা দিয়েছিলেন লেখককে। বই প্রকাশের ইতিহাসে এই তারিখটি তাই স্মরণীয় হয়ে আছে। উপন্যাস বা গৃহস্থালীর বই নয়—ইতিহাসের বইয়ের জন্য লেখককে এত টাকা অগ্রিম দেওয়ার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল। লংম্যানদের সৎসাহস, সাধুতা ও উদারতা সাহিত্য—জগতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় জুড়ে আছে—শুধু ইংলন্ডের নয়, সারা পৃথিবীর।
লংম্যানদের মতন মারেদেরও পরিবর্তন হচ্ছিল এর মধ্যে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে তৃতীয় জন মারের যুগ আরম্ভ হয়। কবিতার বাজার মন্দা বলে যা—তা যে—কোনো বই প্রকাশ করাও সমীচীন নয়—একথা মারেরা বুঝতেন। তাই এই সময় তৃতীয় জন মারে ইউরোপের প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধে একটি ক’রে ”হ্যান্ডবুক” প্রকাশের এক অভিনব পরিকল্পনা করেন। ১৮৩৬ সালে প্রকাশক মারি নিজে হল্যান্ডের হ্যান্ডবুক লিখে প্রকাশ করেন, যাচাই করে দেখার জন্য। বই ভালো বিক্রি হল যখন, তখন যোগ্য লেখকদের দিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের উপর এই ধরনের হ্যান্ডবুক প্রকাশ করলেন। মারের এই প্রচেষ্টার বিস্ময়কর সাফল্য হল। সাহিত্যের মন্দা বাজারের দিনেও প্রচুর টাকা তিনি মুনাফা করলেন। এত টাকা মুনাফা করলেন যে, তাই দিয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করলেন এবং তার নাম দিলেন ”হ্যান্ডবুক হল” (Handbook Hall)। আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে মারেদের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় প্রত্যেক দেশের সচিত্র বিবরণগ্রন্থও তাঁরা প্রকাশ করলেন, প্রধানত পর্যটকদের জন্য। অবশেষে ডারুইনের (Darwin) যুগান্তকারী গ্রন্থ “Origin of Species” ও “Descent of Man” প্রকাশ করে মারে সারা পৃথিবীর পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। বইয়ের বাজার যখন মন্দা, তখন ডারুইনের বই প্রথম ছাপার পরিকল্পনা করা যে কতটা দুঃসাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া, একশো বছর পর আজ আমরা তা কল্পনা করতে পারব না।
প্রাজ্ঞ সমালোচকরা, বিজ্ঞ সাহিত্যরসিকরা এবং অভিজ্ঞ প্রকাশকরা প্রায়ই বলে থাকেন, বইয়ের মন্দা এবং তার জন্য পাঠকদের রুচিবিকারকে দায়ী করেন। কিন্তু সাহিত্যের এই ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে পাঠকরা কখন কি চান না—চান, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞদের বিচার সব সময় নির্ভুল নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই ইতিহাস থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয়। কবিতার বাজার যখন মন্দা, ব্রাউনিঙের মতন কবিকে যখন নিজে খরচ দিয়ে পুস্তিকাকারে কাব্যগ্রন্থ ছাপতে হচ্ছে, কবিতার বদলে কুকারির বই যখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তখন মেকলির ‘ইতিহাস’ বা ডারুইনের ‘অরিজিন অফ স্পেশিজের’ মতন বই—এর চাহিদা হল কী করে? আরও বিস্ময়কর হল, যে প্রকাশকরা অনেক কম খরচেও কবিতার বই ছাপতে রাজি হননি, তাঁরা বহুগুণ বেশি খরচ দিয়ে, মেকলে ও ডারুইনের সুবৃহৎ গ্রন্থ সাগ্রহে প্রকাশ করলেন কার ভরসায়?
কেবল সাহিত্যরসের দিক থেকে বিচার করে এ—প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই গতানুগতিক সাহিত্যেতিহাসে এর উত্তর খোঁজা বৃথা। বাইরের সমাজ, সেই সমাজের পাঠকগোষ্ঠীর রুচি ও মানসিক ক্ষুধা ইত্যাদির বিচার না করে, যাঁরা সাহিত্যের গুণাগুণের তত্ত্বকথা নিয়ে ইতিহাস রচনা করেন, তাঁদের রচিত ইতিহাস হিসেবে তার মূল্য নগণ্য। যখন কুকারির বই বিক্রি হয়, কবিতার বই বিক্রি হয় না, ঠিক সেই সময় ডারুইন ও মেকলির বই কী করে পাঠকচিত্ত জয় করল, এ—প্রশ্নের উত্তর সাহিত্যের যে ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না, সে—ইতিহাস কিসের ইতিহাস জানি না।
সমাজবিজ্ঞানী এ—প্রশ্নের উত্তর দেবেন এই বলে যে, পাঠকদের মনের যুগোপযোগী খোরাকের কথা কোনোদিনই একাডেমিক সমালোচকরা বিচার করে দেখেননি। শেয়ারমার্কেটের তেজিমন্দার মতন তাঁরা পাঠকদের সাহিত্যপাঠের সাময়িক রুচির উত্থান—পতনের বিচার করেছেন। যদি আরও গভীরে তাঁদের দৃষ্টি পৌঁছত তাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন, পাঠকদের বাইরের মানসিক তরঙ্গের তলায় আর—একটি অন্তঃস্রোত আছে এবং সেখানে অনেক অজানা অতৃপ্ত চাহিদা জমা হয়ে রয়েছে। সেখানে তাঁরা যে—যুগের পাঠক, সেই যুগের উপযোগী পাঠ্যবস্তু চান। তা পান না বলেই, ঘোলা জলে তৃষ্ণা মেটান। তাই বলে, ঘোলা জলের চাহিদাটা সত্য নয়। সাহিত্যের ইতিহাসে তাই সবদেশেই দেখা যায়, চটকদারি সাহিত্যের বেসাতি ক’রে যাঁরা পাঠকদের সাময়িক রুচি পরিতৃপ্ত করেন এবং হাউইয়ের মতন সাহিত্যাকাশে খ্যাতির আলোকে ঝলমল করে ওঠেন, তাঁরা হঠাৎ নিভে গিয়ে নিরেট পাথরখণ্ডের মতন আবার ধপ করে মাটিতে পড়েন। তারপর আর তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। যথাসময়ে যথাস্থানে তাঁরা বিলুপ্ত হয়ে যান। ‘মডার্ন’ কুকারির’ লেখিকার যুগ ছিল আসলে ডারুইন ও মেকলির যুগ। তবু মডার্ন কুকারি প্রচুর বিক্রি হয়েছিল, কারণ মেকলির ‘ইংলন্ডের ইতিহাস’ এবং ডারুইনের ‘জীবের ক্রমবিকাশের’ ইতিহাস, তখনও প্রকাশিত হয়নি। যখন প্রকাশিত হল, তখন বোঝা গেল, যুগের চাহিদা কী এবং পাঠকরা সে—সম্বন্ধে সচেতন কি না? দেখা গেল, যুগের অন্তঃসলিলা চিন্তাপ্রবাহ থেকে পাঠকরা পিছিয়ে ছিলেন না। যুগোপযোগী পাঠ্য তাঁরা পাননি বলে, অপাঠ্য কুকারি ও প্রেমকাহিনি তাঁরা পড়েছেন। রোমান্টিক কবিতাও তাঁদের আর ভালো লাগছিল না। কেবল কল্পনার মুক্ত ডানায় ভর দিয়ে শূন্যে বিচরণ করতে তাঁদের মন চাইছিল না। তাঁরা আরও বাস্তব, আরও জীবন্ত কিছু চাইছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ প্রধানত নির্মাণের যুগ, প্রসারের যুগ, গঠনের যুগ। ধনতন্ত্রের অবাধ অগ্রগতির যুগ, বাষ্পীয় রেলগাড়ির যুগ। সাহিত্যে তার জন্য উপন্যাস চাই, ইতিহাস চাই। বিভিন্ন দেশের হ্যান্ডবুক প্রকাশ করে মারি তাই এত মুনাফা করেছিলেন যে তাই দিয়ে গৃহনির্মাণ করে তার নাম দিয়েছিলেন—হ্যান্ডবুক হল। সাহিত্যের ইতিহাসে এই হ্যান্ডবুক হল একটি অবিস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ। প্রকাশকের যুগ থেকে সাহিত্য যে ধীরে ধীরে পাঠকের যুগে উত্তীর্ণ হচ্ছে, এই কীর্তি হল তারই সাক্ষী।
উপন্যাসের যুগ
“If the great Victorian poets had long to wait before receiveing their due reward, Dickens proved that dazzling prizes were to be won in the realm of fiction in the middle of the nineteenth century.”–– Mumby.
কাব্যের বাজার মন্দা হলেও, উপন্যাসের বাজার গোড়া থেকেই তেজি ছিল। যুগটিই হল উপন্যাসের। কাব্যের যুগ প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কাব্য বা ছন্দোবদ্ধ ভাষাই হল মানুষের আদি অকৃত্রিম ভাষা। নৃত্যের মতন কাব্যই তাই মানুষের আদি শিল্পকলার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু উপন্যাস তা নয়। সমাজে মানুষ যতদিন না মানুষ বলে গণ্য হয়েছে, মানুষের ব্যক্তিসত্তা স্বীকৃত হয়েছে, স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগেছে, ততদিন উপন্যাসের নায়ক—নায়িকার জন্ম হয়নি এবং উপন্যাসের সাহিত্যিক রূপায়ণও সম্ভব হয়নি। তাই উপন্যাসের জন্মের জন্য আমাদের ফিউডাল যুগের অবসান ও বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফিউডাল যুগের সাহিত্যিক অবদান হ’ল গাথা ও মহাকাব্য; বুর্জোয়াযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অবদান হল উপন্যাস। উপন্যাস সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক সত্যটি র্যালফ্ ফক্স (Rahph Fox) তাঁর ‘The Novel and the People’ গ্রন্থে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। র্যালফ্ ফক্স বলেছেন :
“The novel is the epic art form of our modern bourgeois society… We can even say that not only is the novel the most typical creation of bourgeois literature, it is also its greatest creation. It is new art form. It did not exist, except in very rudimentary form, before that modern civilisation which began with the Renaissance…”
যুগে যুগে, ইতিহাসের যাত্রাপথে, নতুন নতুন শিল্পকলার সৃষ্টি হয়। বহির্জগতের পরিবর্তনের ফলে মানুষের মনোজগতে যে নতুন ভাবধারার, যে নতুন চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাকে সাহিত্যে ও শিল্পে রূপায়িত করার জন্য মানুষ নতুন নতুন ‘মাধ্যম’ সন্ধান করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহির্জগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের মন প্রথম অর্গলমুক্ত হয়ে যখন বিচিত্র ভাবরাজ্যে পক্ষবিস্তার করল, যুক্তি ও বুদ্ধির আলোয় যখন দীপ্ত হয়ে উঠল তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জীবন, তখন কাব্যের পরিমিত প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সে তৃপ্তি পেল না। নতুন ‘form’ বা রূপের সন্ধান করতে লাগলেন নবযুগের শিল্পী। উপন্যাস হল এই নবযুগের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান রূপ এবং তার ভাষা হল বন্ধনহীন গদ্যভাষা। আধুনিক ছাপাখানার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অবদান—উপন্যাস ও গদ্যভাষা। উপন্যাস—প্রসঙ্গে র্যালফ্ ফকস তাই বলেছেন১—
“…the novel as an art in its own right, with its own rules, with its universal acceptance and appreciction, is a creature of our own civilization, above all, of the printing press.”
উপন্যাস হল আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের মহান শিল্পরূপ। এই সমাজের যৌবনকালে উপন্যাসের চরম বিকাশ হয়েছিল যেমন, তেমনি তার প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে চরম অবনতি হতেও বাধ্য। আজ সেই অবনতি ও চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে উপন্যাস। উপন্যাস শুধু খাঁটি ধনতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি নয়, তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই নতুন শিল্প—মাধ্যম ধনতান্ত্রিক যুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অবদান বলে ইতিহাসে স্বীকৃত। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীকে এই ধনতান্ত্রিক যুগের যৌবনকাল বলা যায়। উপন্যাসের চরম বিকাশও তাই এই সময় হয়। ফিল্ডিং (Fielding), স্কট (Scot), ডিকেন্স (Dickens), ব্রন্তে (Bronte), অস্টেন, ধনতান্ত্রিক যুগের এই যৌবনকালের দান। যে যুগের চোখেমুখে নবযৌবনের উদ্দাম প্রাণচঞ্চল্য, বিশ্বাস ও আদর্শ প্রবণতার উজ্জ্বল প্রকাশ হয়েছিল, সেই যুগে এই সব ঔপন্যাসিকের জন্ম হয়েছিল ইংলন্ডে। তার মধ্যে ডিকেন্স ছিলেন মধ্যমণি। ডিকেন্স সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা—গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে চেস্টারটনের লেখা ‘চার্লস ডিকেন্স’ উল্লেখযোগ্য। চেস্টারটন (G. K. Chesterton) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে (The Dickens Period) চমৎকার ভাষায়, নিজস্ব অননূকরণীয় ভঙ্গিতে, ডিকেন্সের ঐতিহাসিক পটভূমিকার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন২—
“It was a world that expected everything of everybody. It was a world that encouraged anybody to be anything. And in England and literature its living expression was Dickens… He was the voice in England of this humane intoxication and expansion, this encouraging of anybody to be anything. His best books are a carnival of liberty…”
সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীকে নিঃসন্দেহে উপন্যাসের মধ্যাহ্নকাল বলা যায়। সেই মধ্যাহ্নে মধ্যগগনের সূর্যরূপে ডিকেন্সের আবির্ভাব হল। প্রকাশনক্ষেত্রেও একটা নতুন যুগের বিকাশ হল, কেবল ডিকেন্সকে কেন্দ্র করে নয়, আরও অন্যান্য ঔপন্যাসিককে কেন্দ্র করে। দেখা গেল, কাব্যের বাজার যেমন মন্দা, উপন্যাসের বাজার আদৌ তা নয়। নতুন যুগের এই নতুন মাধ্যম ও আঙ্গিকের জন্য যেন পাঠকরাও উন্মুখ হয়েছিলেন। তাঁরা কাব্যের মূল্য না বুঝলেও, উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মানবচরিত্রের যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ, সমাজ—জীবনের যে বৃহত্তর পরিচয় তাঁরা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন, একমাত্র উপন্যাসেই তা সম্ভব হল। নতুন সমাজের নায়ক—নায়িকারা বিচিত্ররূপে, বিচিত্র ভঙ্গিতে উপন্যাসের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর সুখ—দুঃখ—বেদনা, আশা—আকাঙ্ক্ষা, চারিত্রিক সংগতি—অসংগতি সব যখন উপন্যাসের দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠল পাঠকের সামনে, তখন পাঠকরাও অসীম আগ্রহে নতুন নতুন উপন্যাসের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যুগের তাগিদেই উপন্যাসের চাহিদা বাড়ল।
ডিকেন্স যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করলেন, তখন অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতন খুব সন্তর্পণে, সসংকোচেই করলেন। তিনিই যে যুগশিল্পী, একথা বুঝতে প্রকাশক ও পাঠকদের খুব দেরি হয়নি। পাঠকরা যেন ডিকেন্সের অভাবই বোধ করছিলেন এতদিন এবং তাঁদের সঙ্গে প্রকাশকরাও। প্রথমে একদিন ডিকেন্স তাঁর প্রথম রচনাটি চুপিসাড়ে এক মাসিক পত্রিকার অফিসে ‘চিঠির বাক্সে’ ফেলে দিয়ে আসেন। সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করতেও তাঁর ভরসা হয়নি। লেখাটি যখন সেই পত্রিকায় একদিন প্রকাশিত হল, তখন ডিকেন্সই সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ অন্য কেউ তখনও তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। উইলিয়াম হল (William Hall) নামে জনৈক পুস্তকবিক্রেতা এই পত্রিকাখানি ডিকেন্সের কাছে বিক্রি করেছিলেন। বিক্রেতা ও ক্রেতা কেউ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। তার দুবছর পরের কথা। এই হল সাহেব (ইয়ং হল বা লিটল হল বলে পরিচিত) একদিন এক সরাইখানায় গিয়ে উপস্থিত হলেন, এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্য। ব্যক্তিটির নাম চার্লস ডিকেন্স। আর যিনি খুঁজে খুঁজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন সরাইখানায়, ইয়ং হল সাহেব, তিনি হলেন বিখ্যাত প্রকাশন—প্রতিষ্ঠান ”চ্যাপমান অ্যান্ড হল”—এর (Chapman & Hall) অংশীদার হল সাহেব। চ্যাপমান ও হল দুজন তরুণ বন্ধু উদযোগী হয়ে একটি পাবলিশিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক মাম্বি এঁদের সম্বন্ধে বলেছেন : “Chapman and Hall two young men whose names are as closely allied to Dickens and his works as is that of John Murry to Lord Byron.” প্রকাশক জন মারির নামের সঙ্গে যেমন বাইরনের নাম জড়িত, তেমনি প্রকাশক চ্যাপমান ও হলের সঙ্গে চার্লস ডিকেন্সের নামও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।
সরাইখানায় গ্রন্থকার ডিকেন্স ও প্রকাশক হলের সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হল, সেদিন কেউ কারও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানতেন না। চার্লস ডিকেন্স জানতেন না যে তিনি ইংলন্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সম্মান পাবেন একদিন এবং হল সাহেবও জানতেন না যে, ডিকেন্সের বই প্রকাশ করে তিনি লাভবান হবেন বা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দুজনের যখন কার্নিভালের সরাইখানায় প্রথম দেখা হল, তখন হল সাহেব ”দি পিকউইক পেপার্স” (The Pickwick Papers) লেখার প্রস্তাব করেন। ধারাবাহিকভাবে রচনাগুলি প্রকাশিত হবে এবং সেমুর (Seymour) সেগুলি চিত্রিত করবেন, এই প্রস্তাব হয়। ডিকেন্স প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রকাশক প্রত্যেক মাসের রচনার জন্য ১৪ পাউন্ড করে পারিশ্রমিক দিতে রাজি হন। ডিকেন্স লেখেন : “The work will be no joke, my dearest Kate, but the emolument is too tempting to resist.” পিকউইকের প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন ডিকেন্স বিবাহ করে সংসার পাতার ভরসা পান এবং বিবাহ করেন। খণ্ড—খণ্ডভাবে পিকউইক পেপার্স প্রকাশিত হয় এবং চার—পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হবার আগে পাঠকরাও তার মূল্য বুঝতে পারেননি। প্রকাশকরাও প্রথম দিকে যে খুব লাভবান হয়েছিলেন, তা নয়। চার—পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পরে পাঠকমহলে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। প্রকাশক বই ছেপে সরবরাহ করতে হিমসিম খেয়ে গেলেন। আশাতীত মুনাফা হল তাঁদের। অপ্রত্যাশিত মুনাফা পেয়ে প্রকাশকরা ডিকেন্সকে তাঁর প্রাপ্য ছাড়াও আরও অনেক বেশি টাকা স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে দিলেন। ডিকেন্স ও চ্যাপমান হলের সম্পর্কের বন্ধন আরও দৃঢ় হল।
ডিকেন্সের যুগ আসছে, এইরকম একটা চাপা গুঞ্জন যখন পাঠকমহলে শুরু হল, তখন অন্যান্য প্রকাশকরাও ডিকেন্সের বইয়ের জন্য লালায়িত হয়ে উঠলেন। রিচার্ড বেন্টলে (Richard Bentley) নামে একজন প্রকাশক তাঁর “Bentley’s Miscellany” পত্রিকার সম্পাদকের পদে ডিকেন্সকে নিযুক্ত করে ফেললেন, কারণ “Bentley was one of the shrewdest men in the trade.” ধুরন্ধর প্রকাশক বেন্টলে বুঝেছিলেন যে, ডিকেন্সকে এইভাবে সম্পাদকের কাজ নিযুক্ত করতে পারলে তিনি তাঁকে দিয়ে নিয়মিত লেখাতে পারবেন পত্রিকার জন্য এবং সেই লেখা পরে প্রকাশ করতেও (গ্রন্থাকারে) তাঁর বাধা হবে না। তাই হল। ‘অলিভার টুইস্ট’ ধারাবাহিকভাবে ডিকেন্স লিখতে আরম্ভ করলেন বেন্টলের জন্য। যুগপৎ অনেক লেখার চাপ পড়ল তাঁর উপর। ‘পিকউইক’ তখনও লেখা শেষ হয়নি, ‘অলিভার টুইস্ট’ (Oliver Twist) নিয়মিত লিখতে হচ্ছে এবং ‘বার্ণাবি রুজও’ লিখতে হবে। ক্রমে এই কাজের বোঝা বহন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ’য়ে উঠল, কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে তিনি এমনভাবে বাঁধা পড়েন যে, মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পান না। তখন তাঁর প্রথম প্রকাশক চ্যাপমান হলই তাঁকে আড়াই হাজার পাউন্ড দিয়ে বেন্টলের সমস্ত দায় থেকে মুক্ত করেন, অলিভার টুইস্ট ও বার্নাবির চুক্তিপত্র বাতিল করিয়ে দেন। তা ছাড়া ম্যাক্রোন (Macrone) নামে যে প্রকাশকের কাছে ডিকেন্স প্রথম তাঁর ‘Sketches by Boz’ বিক্রি করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকেও টাকা দিয়ে চ্যাপমান কপিরাইট ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রন্থকারকেই প্রত্যর্পণ করেন। ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁর প্রকাশকের সম্পর্ক যে কত আপনার, এই সব ঘটনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়।
চ্যাপমান ও হলের এই উদারতা যে নিছক বদান্যতা নয়, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা প্রকাশক ও ব্যবসাদার। মুনাফাই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য, অন্যান্য ব্যবসাদারদের মতন। কিন্তু জন মারি, লংম্যান, চ্যাপমান ও হল প্রভৃতি প্রকাশকদের বিশেষত্ব এই যে, বইয়ের ব্যবসাকে তাঁরা বাজারের অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ব্যবসার মতন মনে করতেন না। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে, সেই হাঁসকেই যে সবার আগে মানুষের মতন মর্যাদা দেওয়ার দরকার এবং বাঁচিয়ে রাখার দরকার, একথা তাঁরা উপলব্ধি করতেন। লেখকদের মূল্য ও মর্যাদা তাঁরা বুঝতেন ও দিতেন। মুনাফাটাকে অন্ধের মতন আঁকড়ে থাকতেন না। সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রকাশকদেরও যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, একথা তাঁরা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। অতিরিক্ত মুনাফা অনেক সময় স্বেচ্ছায় তাঁরা গ্রন্থকারের সঙ্গে বণ্টন করে নিয়েছেন, নিজেরা ভোগ করেননি। ইংলন্ডের মতন দেশে তাই সাহিত্যের যেমন সমৃদ্ধি হয়েছে, সাহিত্যিকেরও তেমনি মর্যাদা বেড়েছে। সংস্কৃতিবান, রুচিবান, উদার প্রকাশকদের দান তাতে কম নেই। যুগোপযোগী দূরদৃষ্টি নিয়ে, উদীয়মান ধনতান্ত্রিক যুগে, ইংলন্ডে যে সব প্রকাশকের আবির্ভাব হয়েছিল সাহিত্যক্ষেত্রে, তাঁদের মধ্যে জন মারি, লংম্যানস, চ্যাপমান হল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বহু বিচক্ষণ সমালোচকের তুলনায় এঁদের সাহিত্যপ্রতিভা যাচাই করার ক্ষমতা যে অনেক বেশি ছিল, তার প্রমাণ একাধিকবার এঁরা দিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্য তাই দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে।
……..
১. Ralph Fox : The Novel and the People : (Moscow, 1954) : Introduction : p. 61-68.
২. G. K. Chesterton : Charles Dickens (London, 15th edition, 1925) : p. 10.
প্রতিভা ও সমাজ
প্রথম প্রস্তাব
সাহিত্যের বিকাশে এবং সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশে পেট্রন ও প্রকাশকের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ধনিক পেট্রন ও প্রতিপত্তিশালী প্রকাশকের সুনজর ও সহযোগিতা সাহিত্যিকের জীবনে যে এককালে একান্ত প্রয়োজন ছিল, সাহিত্যের ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। অস্বীকার করে লাভ নেই। পেট্রন ও প্রকাশকের পোষকতার ছায়াতলে সাহিত্যিকের প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে এবং অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা শিলাবৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই বীজ মহীরূহে পরিণত হয়। পৌরাণিক অবতারদের মতন প্রতিভাবানেরা সমাজপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়ে হঠাৎ যুগান্তকারী দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন না। প্রতিভার বিকাশের ও প্রতিভার স্বীকৃতির ইতিহাস, বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসেরই একটি অধ্যায় মাত্র।
সাহিত্যের ইতিহাস—লেখকরা অনেকে একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন। স্বীকার করলে প্রতিভার যথাযোগ্য মর্যাদা ও মূল্য দেওয়া হয় না, খাটো করা হয়—হয়তো এই রকম সজাগ মনোভাব তাঁদের এই কুন্ঠার কারণ। তা যদি না হয়, তাহলে বলতে হয় যে তাঁরা মনে করেন, ‘প্রতিভা’ এমন কোনো অলৌকিক বস্তু, যা সমাজের জল—হাওয়া ছাড়াও শূন্যতার মধ্যে আপন শক্তিতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে। ওঠে যদি উঠুক, কিন্তু ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ নেই। ”বিশ্বাস” প্রমাণসাপেক্ষ নয়, তর্কসাপেক্ষও নয়। কারও আত্মোপলব্ধি নিয়ে কোনোদিন তর্ক করা চলে না। ইতিহাস তা নয়। সমাজের ইতিহাসও নয়, সাহিত্যের ইতিহাসও নয়। সাহিত্যের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেন : “Science and the fine arts may require a rich economic soil. But imaginative writing is a flower that flourishers merrily among rocks and ice, in frost and storms.’’ (Vossler) —”বিজ্ঞান ও চারুকলার সমৃদ্ধির জন্য স্বচ্ছল আর্থিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়তো হতে পারে। কিন্তু কল্পনা—সাহিত্য হল এমনই এক জাতীয় ফুল, যা হেসে—খেলে পাহাড়ে—পর্বতে তুষার—ঝঞ্ঝায় ও বরফের মধ্যেও ফুটে উঠতে পারে।” হিরের টুকরোর মতন কথা, আলোর ঝলকানি আছে, কিন্তু কথার মধ্যে কোনো বস্তু নেই, ওজন নেই। ফাঁকা কথার ঝলমলানি। বিখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশকিং এই উক্তির সুন্দর উত্তর দিয়েছেন১ : “But the history of literature regarded in its sociological aspect, teaches us to view generalisations of this sort with a certain mistrust.” অরিস্ততল যেমন ভাবতেন যে, কাদা হলেই কেঁচো হবে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কাদা হলেই যে কেঁচো হবে, এমন কোনো কথা নেই। নাও হতে পারে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, মোজায়েক মেজেতে কেঁচো হবে। তা হতে পারে না। কেঁচো হতে হলে কাদা চাই—ই চাই, যদিও কাদা হলেই কেঁচো হয় না। তুষারপৃষ্ঠে রজনিগন্ধা ফুল ফোটে না। বরফের উপরেও কল্পনা—সাহিত্যের রঙিন ফুল ফুটে ওঠে, একথা নিছক কাব্যিক কল্পনা হিসেবে উপভোগ্য, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সমাজের সঙ্গে প্রতিভার কোনো যান্ত্রিক সম্পর্ক নেই, অর্থনীতির সঙ্গেও না। প্রাচুর্যের মধ্যেই প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর, একথাও সত্য নয়। তা যদি হ’ত, তাহলে পৃথিবীর রাজা, মহারাজা, লর্ড বেরনরা বড় বড় প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও শিল্পী হতেন। কথাটা একেবারেই তা নয়। ওই কাদা ও কেঁচোর সম্পর্কের কথা এসে পড়ে। সুস্থ সামাজিক পরিবেশ হলেই যে সুসমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার মানে এই নয় যে, সমৃদ্ধ সাহিত্য রিক্ত সমাজের ঘুঘুডাঙায় গজিয়ে উঠবে। পাথরের উপর কাব্যের গোলাপ ফুল ফুটে সুগন্ধে মাতিয়ে দেবে চারিদিক—এমন আজগুবি কাণ্ড সাহিত্যের ইতিহাসে ঘটা সম্ভবপর নয়। কথাটার মানে হল, সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য অনুকূল সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন। প্রতিভার প্রকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য রসাল ও সারাল মাটি চাই। নিরেট পাথরের বুকের উপর সাহিত্যের ফুল ফোটে না। ভসলারের কথা সত্য নয়।
প্রতিভা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক যাঁরা মানেন এবং মানেন না, তাদের দুই দলের মধ্যেই গোঁড়া উগ্রপন্থীরা আছেন। একদল মনে করেন, সমাজই সর্বেসর্বা, প্রতিভা বা ব্যক্তিত্ব কিছু নয়। বিশেষ সমাজে বিশেষ প্রতিভার বিকাশ হয়, সমাজই প্রতিভানিয়ন্তা। লেখার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা ভালো খেতে—পরতে পেলেই বড় সাহিত্যিক হতে পারেন, এই মত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের ও প্রতিভার সম্পর্ক ”যান্ত্রিক” মনে করেন। সমাজ যেমনভাবে চালায়, তেমনিভাবে সাহিত্য এগিয়ে চলে, প্রতিভা এগিয়ে চলে। এ ধারণা মারাত্মক ভুল এবং ঠিক এর বিপরীত ধারণার মতনই অর্থহীন ও অবান্তর। দ্বিতীয় দল যাঁরা মনে করেন সাহিত্য, প্রতিভা, তার সঙ্গে সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁদের ধারণাও ভুল। একই ভুলের এপিঠ আর ওপিঠ। সমাজের সঙ্গে প্রতিভার সম্পর্ক আছে, কিন্তু সেটা সব সময় প্রত্যক্ষ নয় এবং কোনো সময় যান্ত্রিক নয়। পরিবেশশূন্য প্রতিভাও আজগুবি কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। প্রতিভার স্ফূরণের জন্য অনুকূল পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু পরিবেশ অনুকূল হলেই যে প্রতিভার স্ফুরণ হতে থাকবে, তা নয়। সমাজ ও প্রতিভা, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে এইটাই বড় কথা। প্রতিভার স্ফুরণ অনুকূল পরিবেশ ছাড়া সম্ভবপর নয়। সাহিত্যের বিকাশের জন্যও চাই সুস্থ সরস পরিবেশ। মধ্যযুগে এই অনুকূল পরিবেশ বলতে বোঝাত, ধনিকদের পৃষ্ঠপোষকতা। পরবর্তীকালে এই পরিবেশ বলতে বোঝাত, প্রতিপত্তিশালী প্রকাশকদের সাহায্য ও সহানুভূতি। ভবিষ্যতে হয়তো বোঝাবে, সাধারণ শিক্ষিত সাহিত্য—রসিক পাঠকগোষ্ঠীর সুবিচারবোধ। পাঠকগোষ্ঠী চিরকালই প্রতিভার স্ফুরণে ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে, পাঠকগোষ্ঠীর কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত হবার পর। উপস্থিত হবার সমস্ত পথই বন্ধ ছিল মধ্যযুগে। প্রতিভা ও লোকসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের যে পথ, সে—পথের পাহারাদার ছিলেন ধনিক পৃষ্ঠপোষকরা। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন বিচারের জন্য পাঠকদের বা রসিকদের সামনে উপস্থিত হওয়াই সম্ভব হত না। মধ্যযুগে বা সামন্তযুগে তাই প্রতিভা সম্পূর্ণ ধনিক পেট্রনের মুখাপেক্ষী ছিল। সাহিত্যিক বা শিল্পীর কোনো স্বাধীন আদর্শ ছিল না, কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল না। পেট্রনের আদর্শই ছিল তাঁর আদর্শ, তাঁর নীতিই ছিল পোষ্য কবি ও শিল্পীর নীতি। কথাটা পেট্রার্ক (Petrarch) ও চসার (Chaucer) প্রসঙ্গে ড. শুশকিং অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন১ —
“Thiny of Petrarch, who yet, as the most celebrated poet of his day, enjoyed an entirely exceptional position, into what difficult situation he was brought by the simple fact that the poet could not support himself by the sale of his works to the public! For twenty years he was supported by the Colonna family; then, when Riezi achieved his dream of the revival of the Roman Republic, Petrarch carried on in his support a bitter polemic against the tyrants of Rome–– those same Colonnas. Latter he lived for a considerable time with the terrible Visconti family, at Milan.’’
এই হল পেট্রার্কের মতন প্রতিভাবানের জীবনকাহিনি। কুখ্যাত অন্নদাতা কলোন্না পরিবারের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে। প্রতিভাকে বন্ধক দিতে বাধা হয়েছেন তিনি। কবি চসারকেও তাই করতে হয়েছিল১ :
“Chaucer had his Visconti–– the unscrupulous John of Gaunt. He ate the bread of a court at which French taste and the rather state theories of love of past centuries were still accepted; and a good part of his literary activity ran on these lines.”
কেবল সামন্তযুগে নয়, ধনতান্ত্রিক যুগেও দেখা যায়, বড় বড় ধনিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা প্রথম দিকে ঠিক সেকালের রাজামহারাজাদের মতন শিল্পী—সাহিত্যিকদের পোষকতা করেছেন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরাও যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করেছেন। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannheim) এই প্রসঙ্গে বলেছেন২:
“We need not go into the importance which the Court of Weimer had for Goethe, Schiller, and Wieland, and Munich had for Wagner. But it is essential to note how with the rise of modern capitalism the wealthy merchant and banking families play their part in cultural life.”
আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আগে সেই ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। পালযুগের কবি ”রামচরিত” রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী, সেনযুগের ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য, জয়দেব থেকে আরম্ভ করে মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র কলকাতা শহরের কবিয়ালরা পর্যন্ত সকলেই রাজা, মহারাজা ও ধনিকদের প্রসাদজীবী ছিলেন। লক্ষ্মণসেন থেকে আরম্ভ করে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ, কি হাটখোলার জমিদার—সকলকেই তাঁরা তোষণ করেছেন এবং সকলেরই প্রচুর প্রশংসা ও গুণগান করেছেন। তা যদি না করতেন, তাহলে ঠিক বলা যায় না তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হত কিনা। মুকুন্দরামের পেট্রন—দর্শনের আগে চণ্ডী—দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি। পেট্রনের বরাভয় পাবার পর তিনি চণ্ডীদেবীর বরাভয় লাভ করেছিলেন। ঘনরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যশক্তির বিকাশের ইতিবৃত্তও তাই। এমনকী ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিয়ালদের পর্যন্ত।
সুতরাং গোবরগাদায় পদ্মফুলের মতন প্রতিভা যে—কোনো পরিবেশে ফুটে উঠতে পারে, একথা ভুল। এই ধরনের উক্তির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। পদ্মফুল যেমন যত্রতত্র ফোটে না, এমনকী ঘাসও যেমন যেখানে—সেখানে গজিয়ে ওঠে না, প্রতিভাও তেমনি যে—কোনো সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিকাশের বা বৃদ্ধির সুযোগ পায় না। শুধু তাই নয়। প্রতিভার স্বরূপও অনেকটা নির্ধারিত হয় সামাজিক পরিবেশের দ্বারা। রামপালের কি লক্ষ্মণসেনের, বর্ধমানের মহারাজার কি কৃষ্ণনগরের মহারাজার রাজসভায় যে—কবি তাঁর কবিত্বশক্তি প্রকাশের সুযোগ পান, তাঁর কাব্যাদর্শও সেই রাজসভার পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ বা কাব্যনীতিকে তিনি তাঁর কাব্যে। রূপায়িত করতে পারেন না। তাঁর কাব্যরুচিও তাঁর পেট্রন তৈরি করেন। আদর্শ, নীতি, ও রুচি সবই রাজসভার পরিবেশে বা ধনিক পৃষ্ঠপোষকের বৈঠকখানায় পেট্রনদের খেয়াল—খুশি মাফিক তৈরি হয়। কবি সেই আদর্শই অনুসরণ করেন, সেই নীতিই মেনে চলেন এবং সেই রুচিরই পরিচয় দেন তাঁর কাব্যে। অর্থাৎ তাঁর কবি—প্রতিভার অনেকটাই পেট্রনের মনোরঞ্জনের জন্য অপব্যয় হয়ে যায়। জয়দেব বা ভারতচন্দ্রের কাব্যরুচি ও নীতির মধ্যে যে—পরিচয় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, তা তাঁদের প্রতিভার যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁদের পেট্রন রাজা লক্ষ্মণসেন ও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার পরিবেশের, রাজরুচির ও রাজনীতির। রাজসভার শুধু নয়, সেই রাজার রাজত্বকালীন সমাজের রুচি ও নীতিরও সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায় তাঁদের কাব্য। প্রতিভা তাঁদের স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠার অবকাশ যতটা না পায়, তার চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ পায় টবের শৌখিন পরগাছা হয়ে বেড়ে উঠতে। প্রতিভার পদ্মফুল নিশ্চয়ই, কিন্তু কাচের জলপাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। বাহার আছে, মর্যাদার মহত্ত্ব নেই। কবি জয়দেবের প্রতিভা যেমন, ধোয়ীর বা গোবর্ধনের বা ভারতচন্দ্রেরও তেমনি। শক্তির জৌলুস আছে, কিন্তু তা দেখলেই বোঝা যায় যে, সেটা খেলোয়াড় কবি রাজার সামনে বাহাদুরি নেবার জন্য যথাসাধ্য কৃতিত্বের সঙ্গে দেখাচ্ছেন। রাজা—বাদশাহরা যেমন হাতির লড়াই বা ময়ূরের লড়াই দেখতেন এবং সেদিনের কলকাতার হঠাৎ নবাবরা যেমন বুলবুলির লড়াই বা মেড়ার লড়াই উপভোগ করতেন, ঠিক তেমনি রাজা ও তাঁর সভাসদরা কবির কবিত্বশক্তির জৌলুস দেখতেন এবং কবিরাও তা দেখিয়ে ধন্য হতেন। মধ্যযুগের সামন্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এইভাবে প্রতিভার বিকাশ হত।
দ্বিতীয় প্রস্তাব
“What happens in this intellectual field does not differ greatly from what happens in the realm of natural science; an endless variability of creation is influenced in definite directions by a certain selection. For this selection we find of importance in the past the circumstance that it proceeds from the literary interest of groups in possesssion of economic and social sources of power, on which the creative artists are dependent.”–Schucking.
সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে বাইরের সমাজের সম্পর্ক যে কতকটা জীববিজ্ঞানের সূত্রের মতন নির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা, জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশকিং সেই কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন১। কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাহিত্যিকদের আত্মম্ভরিতায় বাধলে হয়তো তাঁরা স্বীকার করতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিকরা স্বীকার করতে বাধ্য। সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের ইতিহাস পড়েও যাঁরা একথা স্বীকার করতে চান না, বুঝতে হবে তাঁরা ইতিহাসের কোনো শিক্ষা ও নীতিকে মূল্যবান মনে করেন না। মতামত যেখানে তর্কাতীত বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং সেই বিশ্বাস যখন ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে, তখন তা খণ্ডন করার জন্য কোনো যুক্তিতর্কের অবতারণা করা অর্থহীন। ইতিহাসের ধারা থেকে যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাঁদের জন্যই এই বক্তব্য।
ডাঃ শুশকিং—এর প্রতিপাদ্য হল : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা ঘটে, সাহিত্য শিল্প ও মনীষার ক্ষেত্রে তার চেয়ে পৃথক কিছু ঘটে বলে মনে হয় না। কথাটার তাৎপর্য হল এই যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন কার্য—কারণের সম্বন্ধ সূত্র দিয়ে বাঁধা থাকে, কোনো ব্যতিক্রম হবার উপায় থাকে না, মনীষা ও প্রতিভার ক্ষেত্রেও কতকটা তাই থাকে। বিশেষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে বিশেষ প্রতিভা ও মনীষার বিকাশ হয়। প্রতিভার স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য বলতে যা বোঝায়, তা ওই সামাজিক কারণের বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। মনীষার ও প্রতিভার বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে সাহিত্য—সৃষ্টির মধ্যে, কিন্তু সেই বৈচিত্র্যটা কোনো অলৌকিক শক্তির প্রকাশ—বৈচিত্র্য নয়, সামাজিক শক্তির বৈচিত্র্য। সাধারণত আমরা প্রতিভার এই স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্যকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করি যে, ‘প্রতিভা’ বা ‘মনীষা’ অলৌকিক শক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু সেরকম বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই, থাকতে পারেও না। প্রতিভাবান যিনি, মনীষী যিনি, তিনি ভগবান নন, মানুষ এবং রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয় একটা পথ ধরে এবং সেই পথ বাইরের সামাজিক শক্তির নির্দিষ্ট পথ। তার মানে, সমাজ যন্ত্রী, আর তিনি যন্ত্র তা নয়। ছককাটা সড়ক ধরে প্রতিভার বিকাশ হয় না, একথা খুব সত্য। আঁকাবাঁকা পথে, বাঁধা পথের বেড়া লঙ্ঘন করে, মনীষার প্রকাশ হয়। ঠিক কথা। কিন্তু একথা ঠিক বলে সমাজের নিয়ন্ত্রণশক্তি নেই, একথা একেবারেই ঠিক নয়।
যুগে যুগে প্রতিভা ও মনীষার বিকাশের ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণি ও গোষ্ঠীরাই তাঁদের বিকাশের ধারা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিপ্লবী প্রতিভার বিকাশ হয়েছে তখন, যখন সমাজে কোনো বিপ্লবী গোষ্ঠীর বা শ্রেণির প্রতিপত্তি বেড়েছে এবং সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে সেই মনীষার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম বড় একটা হয়নি দেখা যায়। মহাকবি সেক্সপিয়রের অন্যতম পেট্রন ছিলেন সাউদাম্পটনের আর্ল। “Rape of Lucrece”—র উৎসর্গ—পত্রে সেক্সপিয়র তাঁকে লিখেছিলেন : “What I have done is yours; what I have to do is yours.” এটা শুধু উৎসর্গপত্রের কথার কথা নয়। কথার মধ্যে যে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, তার তাৎপর্য গভীর। ”যা আমি করেছি তা আপনার, বা আপনারই অনুগ্রহে”—একথা তেমন বিস্ময়কর নয়, বেদনাদায়কও নয়। কিন্তু পরবর্তী কথা : ”যা আমি করব, বা যা আমাকে করতে হবে, তাও আপনারই অনুগ্রহে”—রীতিমতো বেদনাদায়ক। ”সেন্টিমেন্টের” দিক থেকে বেদনাদায়ক, কিন্তু ‘ইতিহাসের’ দিক থেকে নয়। এই হল সত্যকার ইতিহাস। এই উৎসর্গপত্রের উক্তি সম্বন্ধে শুশকিং মন্তব্য করেছেন১ :
“This might be interpreted as polite phrase-making, but that would be quite mistaken. We know how powerfully the aesthetic taste of a small aristocratic class was able at that time to impose itself in the field of true literature…”
কেউ যদি মনে করেন যে, উৎসর্গ—পত্রে সেক্সপিয়র ভদ্রতা করেছেন শুধু, তাহলে তিনি ভুল করবেন। শিষ্টতা ও ভদ্রতা প্রকাশের ক্ষেত্র ও পাত্র আরও অনেক ছিলেন, কিন্তু সাউদাম্পটনের জমিদার ভদ্রলোককে পাত্র নির্বাচন করা হল কেন? “Rape of Lucrece” রচনার সঙ্গে এই পেট্রনের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত রুচি চরিতার্থের কি কোনো সম্পর্ক নেই। ভক্তরা হয়তো বলবেন, নেই, কারণ ভক্তের ভাব—গদগদ মনে সেকথা ভাবতেও ব্যথা লাগবে। কিন্তু ভক্তি ও তথ্যনিষ্ঠা এক নয়। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, ভক্তরা ভাবান্ধ, ইতিহাস বা তথ্যের চেয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি তাঁদের কাছে অনেক বড়। দুঃখের বিষয়, ব্যক্তিগত উপলব্ধির মানদণ্ডে ইতিহাসের ধারা বিচার করা যায় না। সেক্সপিয়রের মতন প্রতিভা সর্বকালের ও সর্বজনের শ্রদ্ধেয়। কিন্তু যদি বলা যায় যে, তাঁর প্রতিভা ও মনীষার বিকাশের সঙ্গে তদানীন্তন সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণির ও গোষ্ঠীর রুচিনীতির সম্পর্ক ছিল এবং সেই রুচি ও নীতির দ্বারা তাঁর মনীষা অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তাহলে কি তাঁর প্রতিভাকে খর্ব করা হয়? কখনোই হয় না। অন্তত সাধারণত হয় না, বা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ‘ভক্তের’ কাছে হয়, কারণ ভক্তের সঙ্গে মনীষার সম্পর্ক ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের মতনই অন্ধ। বৈষ্ণব ভক্তরা শ্রীচৈতন্য যে ‘মানুষ’ হয়ে জন্মেছিলেন, একথা ভাবতেও কষ্ট পান। সত্যদ্রষ্টা, শক্তিশালী বিরাট পুরুষের মতন তিনি যে যুগান্তকারী কোনো সামাজিক আন্দোলন করেছিলেন, একথা বলতে তাঁরা কুন্ঠিত হন। সবই শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক লীলাখেলা না বললে তাঁরা প্রীত হন না। ইতিহাসের পটভূমিকা থেকে তাঁরা শ্রীচৈতন্যকে সরিয়ে দিয়ে একটা অলৌকিক পটভূমিকায় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এই হল ভক্ত মাত্রেরই নিয়ম, কেবল বৈষ্ণব ভক্তদের নয়, সকল শ্রেণির ভক্তদের। প্রতিভা ও মনীষার ভক্তরাও এর ‘ব্যতিক্রম’ নন। প্রতিভা স্বয়ম্ভু বা সমাজ ও বস্তুজগৎ—নিরপেক্ষ, একথা না বললে তাঁরা মনে করেন প্রতিভাকে খর্ব করা হয়। তাঁদের সান্ত্বনা দেবার কোনো উপায় নেই, কেউ দিতে পারবেন না, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা তো একেবারেই পারবেন না।
যা বলছিলাম। কতকটা প্রাণীজগতের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতন (Natural selection), সাহিত্য—শিল্পজগতেও সামাজিক নির্বাচন চলতে থাকে। নির্বাচন বৈজ্ঞানিক নিয়মের মতনই নির্মম। নির্বাচনের ফলে যোগ্যতমের উর্দ্ধতন যেমন সম্ভব হয় জীবজগতে, তেমনি সাহিত্যজগতেও যোগ্য প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে। নির্বাচনে ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁরা, যাঁদের প্রভাব—প্রতিপত্তি আছে সমাজে। সামাজিক প্রভাব—প্রতিপত্তি সাধারণত দেখা যায় অর্থগৌরব ও বংশগৌরবের সঙ্গে জড়িত। যাঁদের আর্থিক প্রতিপত্তি আছে, বংশগত আভিজাত্য আছে, তাঁরাই সাহিত্যিক রুচি, নীতি, ভালো—মন্দের মাপকাঠি, আদর্শ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁরা খুশি হলেই সাহিত্য ও শিল্প অনেকটা সার্থক হয়, অখুশি হলে হবার সম্ভাবনা থাকে না এবং সাধারণতঃ হয় না। তার কারণ সাহিত্য বা শিল্পানুরাগী সাধারণের সংখ্যা যতদিন সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন সেই স্তরের উপর প্রতিপত্তিশালী শ্রেণির প্রভাবও থাকে যথেষ্ট। সুতরাং প্রতিভার ও মনীষার জীবনমরণ কাঠিটিও থাকে তাঁদের হাতে। এ—ক্ষেত্রে তাঁদের মুখাপেক্ষী না হয়ে কারও উপায় নেই, তা তিনি যত বড় প্রতিভাবানই হন না কেন।
মুখাপেক্ষিতার আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ইতিহাসের পাতা থেকে। সাধারণত গতানুগতিক ”সাহিত্যের ইতিহাসে” এ সব দৃষ্টান্ত স্থান পায় না। তার মধ্যে এ সবের কোনো মূল্য নেই, অতি নগণ্য। প্রতিভাটাই বড়, তার বিকাশের ইতিহাসটা সেখানে খুব ছোট ব্যাপার। কিন্তু সমাজ—বিজ্ঞানীর কাছে এই জাতীয় দৃষ্টান্তের মূল্য খুব বেশি এবং বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যখন প্রতিভা ও সমাজের সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করছি, ভক্তের ঠুলিবাঁধা বলদের দৃষ্টিতে নয়, তখন দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখযোগ্য।
আলেকজান্ডার পোপ (Alexander Pope) বড় কবি ছিলেন। এখন হয়তো অনেকে তা বলবেন না, কিন্তু তাঁর যুগে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে তিনি একজন প্রথম শ্রেণির কবি বলেই ইংলন্ডে গণ্য হতেন। তা হলেও পোপ যখন হোমারের কাব্য অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন এবং যে অনুবাদের জন্য তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতিও অর্জন করেন—তখন মধ্যে মধ্যে ছোট—খাট একটি বৈঠক ডেকে তিনি তাঁর পেট্রন লর্ড *হালিফাক্সকে (Lord Halifax) অনুবাদ পাঠ করে শোনাতেন। স্যামুয়েল জনসন বলেছেন যে, লর্ড হালিফাক্স প্রায়ই তাঁর অনুবাদ সংশোধন করে দিতেন এবং কী করলে আরও ভালো হয় বলে দিতেন। এমনিতে যে ব্যাপারটা অন্যায় কিছু তা নয়। হালিফাক্স গুণী ব্যক্তি, সংশোধন তিনি করে দিতে পারেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, গুণীদের কাছে কবি পোপ তাঁর অনুবাদ সমালোচনার্থে পাঠ করে শোনাতেন না। সেরকম কোনো সাধু অভিপ্রায়ই তাঁর ছিল না। শোনাতে তিনি বাধ্য হতেন এবং এমন একটি গোষ্ঠীর কাছে, যাঁরা প্রথমত তাঁর পেট্রনগোষ্ঠী, দ্বিতীয়ত হয়তো বা গুণী। কবি চসার তাই করতেন, তাঁর শিষ্য লিডগেটও (Lydgate) তাই করতেন। লিডগেটের পেট্রন ছিলেন পঞ্চম হেনরির ভাই গ্লুসেস্টারের ডিউক। ডিউক নিজে কবির কবিতা সংশোধন করে দিতেন পর্যন্ত। স্পেন্সারও (Spenser) তাই করেছেন। ফ্রান্সে ভলতেয়ারের (Voltaire) মতন প্রতিভাবানকেও তাই করতে হয়েছে। সকলকেই তাই করতে হয়েছে। কেউ ব্যতিক্রম ছিলেন কি না সন্দেহ।
যতদিন না সাহিত্যক্ষেত্রে বাইরের ”প্রকাশকরা” অবতীর্ণ হয়েছেন এবং অভিজাতগোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত পাঠকশ্রেণি তৈরি হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এই অপমান অনেকটা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। বিদ্রোহ করার ইচ্ছা হলেও অনেকেই বিদ্রোহ করতে পারেননি। কারণ বিদ্রোহ করা মানেই সমাজে প্রতিষ্ঠার সুযোগ হারানো এবং প্রতিষ্ঠা না পাওয়া বা স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হওয়া মানেই প্রতিভার অপমৃত্যু। প্রকাশকদের যুগেও যে প্রতিভা এই বিশেষ গোষ্ঠীর কবল থেকে একেবারে মুক্ত হয়েছে তা নয়। তা হতে পারে না। প্রকাশকদের যে ইতিহাস আলোচনা করেছি আগে, তাতে দেখা যায় যে, প্রথমযুগের প্রকাশকরাও অনেকটা পেট্রন—মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং পেট্রন ও লেখকের মধ্যে থেকে তাঁরা যোগাযোগ করে দিতেন। পরবর্তীকালে প্রকাশকরাই যখন পেট্রন হন, তখন পেট্রনযুগের মনোভাব তাঁদের মধ্যেও নতুন রূপে প্রকট হয়ে ওঠে। সাহিত্যের রুচি—নীতির প্রবর্তন তাঁরাই অনেকটা করতে থাকেন। তবু পেট্রনযুগের চেয়ে প্রকাশক—যুগের পরিবেশ অনেক বেশি স্বাধীন ও মুক্ত। বিভিন্ন প্রকাশকের স্বার্থের সুযোগ নিয়ে ইতিহাসে প্রথম প্রতিভাবান শিল্পী—সাহিত্যিকরা আত্মপ্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ পান। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির যুগের সমাজের কথা।
………..
১. L. L. Schucking : Sociology of Literary Taste : p. 8.
১. শুশকিং : ঐ, ১০
১. শুশকিং : ঐ, ১০
২. Karl Mannheim : Man and Society–– In an Age of Reconstruction (London 1940) : Part II, P. 84 fn.
১. শুশকিং : ঐ, ১৫
১. শুশকিং : ঐ, ১১
* লর্ড হালিফাক্স ১এর প্রকৃত নাম এডওয়ার্ড ফ্রেডরিক লিন্ডলে উড (১৮৮১—১৯৫৯) একসময়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল (১৯২৬—১৯৩১) ছিলেন। আলেকজান্ডার পোপ এর জীবনকাল (১৬৮৮—১৭৪৪), এই হিসেবে হালিফাক্স তখন জন্মাননি। হেনরি সেন্ট জন ১ম ভিসকাউন্ট বোলিংব্রেক (১৬৭৮—১৭৫১) পোপ—এর বন্ধু ও পেট্রন ছিলেন। তাঁর লেখা ‘এসে অব ম্যান (১৭৩৪)’ এবং ‘ডানসিআড (১৭২৮)’ বোলিংব্রক এর প্রেরণায় লেখা হয়েছিল। আবার স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯—১৭৮৪)—এর পেট্রন জর্জ ৩ (১৭৩৮—১৮২০)। জনসন—এর আর্থিক দুরবস্থার জন্য ১৭৬২ সাল থেকে আমৃত্যু বছরে ৩০০ পাউন্ড সরকারী ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন।
সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদা
প্রথম প্রস্তাব
সভ্য—সমাজে অন্যান্য সকল শ্রেণির সঙ্গে সাহিত্যিকেরও আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু সকল শ্রেণি যেমন সমাজে সমান মর্যাদা পাননি, তেমনি সাহিত্যিকরাও পাননি। একেবারে আদিম সমাজে হয়তো অন্যান্য লোকশিল্পীদের মতন তাঁরাও মর্যাদা পেতেন, কারণ তখন অর্থের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক ততটা প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ হয়নি। পরে যখন তা হয়েছে, সমাজ যখন নানা শ্রেণিতে ভাগ হয়ে গেছে এবং এক শ্রেণির সঙ্গে অন্য শ্রেণির প্রভু—ভৃত্য, শাসক—শাসিত ও শোষক—শোষিতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তখন সাহিত্যিকরাও বৃহত্তর লোকসমুদ্রের বুকে নগণ্য ভৃত্যরূপে বুদবুদের মতন মিলিয়ে গেছেন—‘Unwept, unhonoured, unsung.’
বর্তমান যুগে সাহিত্যিকদের যে মর্যাদা বেড়েছে, একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। সভা—সমিতিতে, মৃত সাহিত্যিকদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে জীবিত সাহিত্যিকদের যে—রকম ডাক পড়ে, তাতে এইটুকু অন্তত পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সাহিত্যের মূল্য বাড়ুক না বাড়ুক, সাহিত্যিকের মর্যাদা বেড়েছে। কিন্তু তারপরেও কথা আছে। সভাপতিত্ব করতে সাহিত্যিকদের যদি ‘ফি’ দিয়ে ডাকতে হত, তাহলে সভা—সমিতির উদ্যোক্তাদের উত্তেজনা অনেকটা কমে যেত এবং যাঁদের নিতান্তই থাকত তাঁদের আর সাহিত্যিকদের কাছে ধরনা দিতে হত না। বরং তখন হয়তো উলটো ব্যাপারই ঘটত। সাহিত্যিকরা নিজেরাই সভা—সমিতির উদ্যোক্তাদের কাছে ধর্ণা দিতেন, যেমন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছে দেন। সুতরাং এ—যুগের সাহিত্যিকদের মর্যাদা যথেষ্ট বাড়লেও, ভেবে দেখা উচিত, সেই মর্যাদাটা কী বস্তু, কেনই বা বেড়েছে এবং কতটুকু বেড়েছে।
সত্যিই কি সাহিত্যিকদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে? সোজাসুজি উত্তর দেবার মতন সহজ প্রশ্ন নয়। কলকাতা শহরে দেখা যায়, বাড়িওয়ালারা আজও অনেকে সাহিত্যিক ও উকিলের নাম শুনলে বাড়ি ভাড়া দিতে চান না। বাইরে হয়তো “To Let”—এর সঙ্গে “Writers & Pleaders not allowed” কথাটা লেখা থাকে না, কিন্তু অনেক বাড়িওয়ালাকে দেখেছি সাহিত্যিক ও উকিলের নাম শুনে জবাব দিতে : ”ভাড়া দেব না।” এটা কি সাহিত্যিকদের সামাজিক মর্যাদার পরিচয়? এর ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়। স্বনামধন্য কোনো সাহিত্যিক (বিশেষ করে ফিল্ম বই লিখে যিনি স্বনামধন্য হয়েছেন) হয়তো কড়া বাড়িওয়ালার কাছেও খাতির পাবেন, কিন্তু সেটা তিনি ‘সাহিত্যিক’ বলে নয়, নিজেও বাড়িওয়ালা হতে পারেন, এরকম টাকার মালিক বলে বা সঙ্গতি আছে বলে। যে কোনো প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের তুলনায় একজন গভর্ণমেন্ট আফিসের সাধারণ কেরানীর মর্যাদা অনেক বেশি বাড়িওয়ালার কাছে, দোকানদারের কাছে এবং হাটবাজারে। যে—সমাজে বাড়িওয়ালার মর্যাদা বেশি, সে—সমাজে বাড়ি করাটাই বড় কথা, বই লেখা নয়। যে কোনো সামাজিক সভায় বাড়িওয়ালা ও গাড়িওয়ালারা যে—রকম মর্যাদা পান, সাহিত্যিকরা তার কিছুই পান না, এখনও না। যে দু—একজন পান তাঁর সাহিত্যিক হয়েও বাড়ি ও গাড়িওয়ালা হতে পেরেছেন বলে পান, কেবল সাহিত্যিক বলে পান না। কেবল সাহিত্যিকদের মর্যাদা দু—চারজন সাহিত্য—ক্ষ্যাপার সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাও সেটা ভুয়ো মর্যাদা, তার কোনো ‘মেটিরিয়াল’ বা বাস্তব ভিত্তি নেই। যেমন কোনো সাহিত্যিক যদি তাঁর অনুরাগীদের কাছে টাকা ধার চান তো পাবেন না, কারণ অনুরাগীরা জানেন যে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না। এরকম আরও অনেক ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। লাভ নেই দিয়ে। আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।
সাহিত্যিক স্বামীর গর্বিতা স্ত্রী হতে চান, এরকম দু—একজন ক্ষণজন্মা কন্যা হয়তো বর্তমান সমাজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক জামাইয়ের শ্বশুর হতে চান, এরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সাহিত্যিকরাও যখন বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দেন সংবাদপত্রে তখন তাঁর পেশা ও চাকরির কথা উল্লেখ করেন, সাহিত্যনেশার কথা বলেন না। ”কী করেন?” ”কবিতা লিখি বা শুধু লিখি”, একথা রবীন্দ্রনাথেরই বলা শোভা পায় এবং বলেও কিছু আসে যায়নি তাঁর। কিন্তু কবিতা লিখি, গল্প লিখি বা প্রবন্ধ লিখি, কেবল এই কথা বললে কোনো উদীয়মান সাহিত্যিকের চাকরি জুটবে না, স্ত্রী জুটবে না এবং জীবনে কোনোদিন সংসারধর্ম করাই হয়তো তাঁর সম্ভব হবে না। ভাবী জামাই হিসেবে শ্বশুরের কাছে সাহিত্যিক বা শিল্পীর মর্যাদা যে কতটুকু, তার সুন্দর পরিচয় দিয়ে গেছেন থ্যাকারে (Thackeray) । থ্যাকারের বিখ্যাত “The Newcomes” গ্রন্থ যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লেডি কিউ ও তাঁর নাতনি ইথেলকে চেনেন। একজন চিত্র—শিল্পী তাঁর নাতনি ইথেলকে বিবাহ করতে চেয়েছেন শুনে লেডি কিউ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন :
“An artist propose for Ethel! One of her footmen might propose next… The father come and proposed for this young painter, and you didn’t order him out of the room!”
থ্যাকারের যুগের মনোভাব অনেক বদলে গেছে। লেডি কিউদের যুগও আর নেই। কিন্তু এখনও অনেক লেডি কিউ আছেন যাঁরা তাঁদের কন্যা বা নাতনির পাণিপ্রার্থী কোনো সাহিত্যিকদের স্বচ্ছন্দে এই ধরনের কথা বলে বিদায় করতে পারেন। এদিক দিয়ে মনে হয় না যে, থ্যাকারের যুগ পার হয়ে আমরা খুব বেশি দূর এগিয়ে এসেছি। আগের চেয়ে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির কাছে সাহিত্যের মর্যাদা বেড়েছে, সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত মর্যাদা বেড়েছে, কিন্তু তাঁর সামাজিক মর্যাদা বিশেষ বেড়েছে বলে মনে হয় না। এ—যুগের কোনো বড় কন্যা দরিদ্র শিল্পী বা সাহিত্যিকের প্রেমে পড়ে হয়তো তাঁকে বিয়ে করতে চান, কিন্তু সেটা সাধারণত চলচ্চিত্রের নায়িকাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সাহিত্যিক তাঁর নিজের দিবাস্বপ্ন বা অচরিতার্থ বাসনাকে এইভাবে চলচ্চিত্রের মধ্যে চরিতার্থ করতে চান বলেই ধনীর কন্যা দরিদ্র শিল্পীর প্রেমে পড়েন এবং তাঁকে বিয়ে করে সুখীও হন। আসলে বাস্তব জীবনে তা কখনো ঘটে না বলেই চলচ্চিত্রে দেখতে তা ভালো লাগে। এ রকম ব্যাপার মনোমৈথুনের ট্রাজিক দৃষ্টান্ত হলেও, এর মধ্যে সামাজিক সত্য (Social reality) বলে কিছু নেই। সামাজিক সত্যটা ঠিক তার বিপরীত। সেই ট্রাজিক রিয়ালিটিকে কমেডিতে পরিণত করে সাহিত্যিক নিজে তাঁর ব্যর্থ মনস্কামনা পূরণ করেন মাত্র। লোকের ভালো লাগে এ রকম উপন্যাস পড়তে বা ফিল্ম দেখতে, তার কারণ বিশাল মধ্যবিত্তশ্রেণির হতভাগ্য কোটালপুত্র ও কোটালকন্যাদের প্রায় সকলেরই প্রাণের বাসনা তাই। তাঁদের বাসনা সমাজে চরিতার্থ হয় না যখন, তখন উপন্যাসের পৃষ্ঠায় অথবা চলচ্চিত্রের পর্দায় যদি তা ক্ষণিকের জন্যও পরিপূর্ণ হয়, তাহলে সেইটুকুই লাভ। এইজন্য আমাদের এই সমাজে এই জাতীয় সাহিত্যের হঠাৎ—জনপ্রিয়তা এত বেশি। ধনীর পুত্র ও দরিদ্রের কন্যা অথবা দরিদ্রের পুত্র ও ধনীর মধ্যে প্রেম—এ যেন দুর্ভাগা মধ্যবিত্তের প্রাণের কথা ও ব্যথা দুই—ই। তাই যে সাহিত্যিক তাকে মধ্যযুগের রোমান্সের মতন রূপায়িত করতে পারেন সাহিত্যে, তিনি হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই ধরনের দরিদ্র শিল্পী সাহিত্যিক ও ধনিকের কন্যার প্রেম সিনেমার পর্দায় দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, এটাই ”সোশ্যাল রিয়ালিটি”, তাহলে তিনিও যে দিবাস্বপ্নবিলাসী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। থ্যাকারের যুগ শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। অর্থাৎ মর্যাদার মক্কা অনেক দূর।
জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ডাঃ শুশকিং বলেছেন : “In past centuries the position of the artist in society was never particularly good. Those, of course, who had reached the peaks of Parnassus always found ready and honoured acceptance in the highest circles of society.” যাঁরা পার্নাসাসের চূড়ায় পৌঁছেচেন তাঁরা যে উচ্চসমাজে সাদর মর্যাদা ও সমাদর পাবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কথা হচ্ছে চূড়ায় কজন পৌঁছতে পারেন? তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, চূড়ান্ত সার্থকতার কাছে, যে ক্ষেত্রেই হোক, সকলেই মাথা হেঁট করেন। সেখানে বিশিষ্ট পেশার কোনো প্রশ্ন আসে কি? কথাটা তলিয়ে ভেবে দেখবার মতন। সাধারণ দরজি থেকে যিনি বিরাট ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সের লক্ষপতি মালিক হয়েছেন, সাধারণ গামছা—বিক্রেতা থেকে যিনি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তাঁকে মর্যাদা দেয় না কে? সকলেই মর্যাদা দেন, কিন্তু কাকে দেন? তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা ও ক্ষমতাকে দেন এবং সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন তাঁর সাফল্যকে, সার্থকতাকে। “Nothing succeeds like success.” —কথাটা সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাতে একথা বোঝায় না যে সেই পেশাকে বা পেশাদারকে তাঁরা মর্যাদা দেন। দরজি থেকে যিনি ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সের মালিক হন, তাঁকে মর্যাদা দেওয়ার অর্থ দরজিকে মর্যাদা দেওয়া নয়। তেমনি যে সাহিত্যিক সার্থকতার পর্বতশৃঙ্গে উঠেছেন, তাঁকে মর্যাদা দেওয়ার অর্থ সাহিত্যিক বা সাহিত্যকে মর্যাদা দেওয়া নয়। কথাটা বিশেষভাবে বোঝা প্রয়োজন। লর্ড চেস্টারফিল্ড যে পোপ (Pope) বা এ্যাডিসনের (Addison) সাহচর্যে নিজেকে ধন্য মনে করতেন এবং তাঁদের বন্ধুত্ব কামনা করতেন, তা থেকে একথা বোঝায় না যে তিনি সাহিত্যিক পেশাকে শ্রদ্ধা করতেন। সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী, জয়দেব ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালারা পর্যন্ত রাজসভায় বা বড়লোকের বৈঠকখানায় যে মর্যাদা পেতেন, তাকে আধুনিক অর্থে কোনোমতেই ”সামাজিক মর্যাদা” বলা যায় না। সামাজিক মর্যাদা সেটা নয়। সেটা হল মধ্যযুগীয় বদান্যতা ও উদারতা, আধুনিক যুগের ব্যক্তিগত বা সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই।
মোগলযুগের শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে (সপ্তদশ শতাব্দীর কথা) ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের যা বলে গেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন :
“If the artists… were encouraged, the useful and fine arts would flourish; but these unhappy men are contemned, treated with harshness, and inadequately remunerated for their labour… The artists, therefore, who arrive at any eminence in their art are those only who are in the service of the king or of some powerful Omrah, and who work exlusively for their patron.” (Letter to Vayer, July 1663)
বার্নিয়েরের শেষ কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিল্পীদের যে—কোনো মর্যাদা ছিল না, একথা তিনি পরিষ্কার বলেছেন। শিল্পীদের ক্ষমতা থাকলেও সেই ক্ষমতাপ্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। তাঁদের মধ্যে দু—একজন যাঁরা খ্যাতি অর্জন করতেন, তাঁরা হয় কোনো রাজসভায়, না হয় কোনো ওমরাহের পোষকতায় থেকে তাঁর মনোরঞ্জন করার জন্য শিল্প রচনা করতেন। রাজা বা ওমরাহ তাঁদের সুনজরে দেখতেন, পোষকতা করতেন বলে সাধারণ লোকও তাঁদের মর্যাদা দিত। সেটা শিল্পীর মর্যাদা নয়, রাজা বা ওমরাহের মোসাহেবের মর্যাদা।
বার্নিয়ের আমাদের দেশের সপ্তদশ শতকের কথা বলে গেছেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিল্পীর বা সাহিত্যিকের বিশেষ কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। দু—একজন ভাগ্যবান যাঁরা রাজসভায় প্রবেশাধিকার পেতেন, তাঁরাই যা সামান্য মর্যাদা পেয়ে গেছেন সমাজে। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। ইংলন্ডেও সাহিত্য—প্রতিভার চেয়ে অর্থের মর্যাদা ছিল বেশি, এই সেদিন পর্যন্ত। খুব বিসদৃশভাবে ছিল। ডাঃ শুশকিং তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন :
“It strikes us today, however, as odd when we hear that in 1723 a comedy of Steele’s enjoyed great popularity because the author was reputed to have an income of a thousand a year. Clearly there was nothing much in being an artist.” বাস্তবিকই তাই।
দ্বিতীয় প্রস্তাব
ডাঃ শুশকিং বলেছেন : “For a long time the son of a ‘good family’ was considered in some way to have lost caste if he became a professional writer or painter, and still more if he became an actor. To live by the pen was not very respectable.”
সাহিত্যের ইতিহাস বা সমালোচনা যাঁরা আরামকেদারায় বসে লেখেন তাঁরা হয়তো কথাটা ঠিক জানেন না, বা জেনেও স্বীকার করতে চান না। কিন্তু সাহিত্যিকদের ইতিহাস যাঁরা বাস্তব সমাজের পটভূমি থেকে বিচার করেন, তাঁরা একথাটা বিশেষভাবে জানেন ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।
অভিজাত বংশের সন্তান যাঁরা, তাঁদের পক্ষে এককালে সাহিত্য বা শিল্পচর্চাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা রীতিমতো মানহানিকর ব্যাপার ছিল। তাতে তাঁদের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা দুয়েরই হানি হত। এককথায় বলা যায়, কালি—কলম, রং—তুলি বা বাটালির পেশা কোনোদিনই সমাজে বিশেষ মর্যাদা পায়নি। দু—একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন ডাঃ শুশকিং। সমাজের ইতিহাস বাদ দিয়ে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেন, তাঁদের কাছে এই দৃষ্টান্তগুলি খুব ‘শকিং’ মনে হবে নিশ্চয়।
ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্ররা কংগ্রিভের (Congreve) কথা নিশ্চয় জানেন। নাট্যকার হিসেবে কংগ্রিভ যখন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন তখন তিনি একবার ফ্রান্সে বেড়াতে যান। ভল্টেয়ার (Voltaire) তখন বেঁচে ছিলেন। কংগ্রিভ ফ্রান্সে এসেছেন শুনে ভলতেয়ার তাঁকে সাহিত্যিক শ্রদ্ধাভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন। আলাপের সময় কথাটা ভলতেয়ার বলে ফেলেছিলেন কংগ্রিভকে। বেশ উৎসাহিত হয়ে ভলতেয়ার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন : ”আপনার মতন একজন বিখ্যাত লেখককে চোখে দেখলাম এবং আপনার সঙ্গে আলাপ হল, এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।” কথাটা শুনে কংগ্রিভ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন : ”মার্জনা করবেন, আমি লেখক নই, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মাত্র। ভদ্রলোক বলেই আমার পরিচয় দেবেন, লেখক বলে নয়। ও পরিচয়টা আমি দিতে চাই না।” ভলতেয়ার শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি কল্পনাও করেননি, এরকম একটা উত্তর কংগ্রিভের মুখ থেকে তাঁকে শুনতে হবে। ভলতেয়ার অত্যন্ত মেজাজি ও তেজি ছিলেন। অপ্রস্তুত হয়ে ভলতেয়ার ফিরে এলেন না। তিনিও বেশ কড়া জবাব দিলেন কংগ্রিভের মুখের উপর। বললেন : ”আমি কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করতে আসিনি। লেখক কংগ্রিভের সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছিলাম।” কল্পনা করা যায় না। কংগ্রিভের মতন খ্যাতনামা লেখকের কাছেও ‘ভদ্রলোকে’র মর্যাদা অনেক বেশি ‘লেখকের’ চেয়ে। লেখক বলে পরিচয় দিতে তিনি সংকোচবোধ করতেন।
আরও একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বিখ্যাত সাহিত্যিক স্যামুয়েল রিচার্ডসনের (Samuel Richardson) বিশেষ অনুরাগী ছিলেন লেডি ব্রাডসহাউ (Lady Bardshaugh)। ল্যাঙ্কাশায়ার মহলের অভিজাতবংশের মহিলা লেডি ব্রাডসহাউ। একে অভিজাত, তার উপর লেডি। রিচার্ডসনের সঙ্গে লেডি ব্রাডসহাউ নিয়মিত পত্রালাপ করতেন একান্ত গোপনে। রিচার্ডসনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা তিনি কারও কাছে কোনোদিন প্রকাশ করেননি। পাছে কেউ জেনে ফেলে এই ভয়ে সব সময় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। যদি তাঁর ল্যাঙ্কাশায়ারের বন্ধুরা কোনোরকমে জানতে পারতেন যে তিনি একজন লেখকের সঙ্গে পত্রালাপ করেন, তাহলে হয়তো তাঁরা তাঁকে সমাজচ্যুত করতেন। লেডি ব্রাডসহাউ মুশকিলে পড়ে গেলেন, যখন স্যামুয়েল রিচার্ডসন তাঁকে তাঁর স্বাক্ষরসহ একখানি নিজের ফটোগ্রাফ উপহার দিলেন। কোথায় ফটোগ্রাফখানি তিনি রাখবেন তাই নিয়ে ভেবে আকুল হলেন লেডি। অবশেষে তিনি ঠিক করলেন যে, রিচার্ডসনের স্বাক্ষর বদলে ফেলে, তার বদলে ‘ডিকেনসন’ লিখে তিনি ছবিটা রেখে দেবেন। “When he sent her his portrait she altered his signature to Dickenson, to prevent the acquaintance from coming to light.”১ সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদা যে কি রকম ছিল, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে, আমার মনে হয়, লেখকরা মর্মে মর্মে বুঝতে পারবেন। এর আগে থ্যাকারের লেডি কিউ—এর কথা বলেছি। লেডি ব্রাডসহাউ সাহিত্যিকের অনুরাগী হয়েও লেডি কিউ—এর মনোভাব কাটাতে পারেননি।
‘জেন্টলম্যানের মনোভাব মধ্যযুগের অন্তিমকাল পর্যন্ত এমনভাবে প্রকট হয়ে উঠত সর্বক্ষেত্রে যে অনেক সময় তা দেখে চমকে উঠতে হত। আধুনিক ব্যক্তি—স্বাধীনতার যুগেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত মধ্যযুগীয় মনোভাবের রেশ ছিল। একটা যুগের দৃষ্টিভঙ্গি যান্ত্রিক নিয়মে যুগান্তরের সময় অথবা নতুন যুগের অভ্যুদয়কালে হঠাৎ অন্তর্ধান করে যায় না, যেতে পারে না। যেতে অনেক সময় লাগে। সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন শ্রেণির ও স্তরের মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে বদলায়। নতুন সামাজিক সম্পর্ক মানুষকে নতুন ভঙ্গিতে দেখতে ও বিচার করতে শেখায়। সেটা আরও বেশি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তার অনেক পরে ধীরে ধীরে মানুষের মানসিক গড়নটা বদলাতে থাকে। মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগে পৌঁছলেই মানুষের মানসিক গড়ন আধুনিক হয় না বা রাতারাতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় না। সাহিত্যিকদের সামাজিক মর্যাদাও হঠাৎ রাতারাতি বদলায়নি। অন্যেরা সাহিত্যিকদের কী চোখে দেখতেন তা লেডি কিউ ও লেডি ব্রাডসহাউ—এর দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। তার চেয়েও বড় সত্য হল, সাহিত্যিকরা নিজেরাই ”সাহিত্যিক” বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পেতেন। কংগ্রীভ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। পেট্রনদের পরিবর্তে যখন প্রকাশকদের যুগ এল, তখনও সাহিত্যিকরা নিজেরাই এই মনোভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। মধ্যযুগের সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ড তখনও তাঁরা সগৌরবে বহন করে নিয়ে চললেন। প্রকাশকদের কাছ থেকে সাহিত্যিকরা তাঁদের বইয়ের জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা নিতে সংকোচবোধ করতেন। কারণ, লিখে টাকা নেন বা টাকা রোজগার করেন, একথা ভাবতেও তাঁদের লজ্জা হত। তাতে ‘ভদ্রলোক’ হিসেবে তাঁদের সামাজিক মর্যাদার হানি হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। সুতরাং বইয়ের টাকা প্রকাশকদের কাছেই জমা থাকত। অনেকে বোধহয় জানেন না (এবং জানলে দুঃখিত হবেন) যে করুণ ‘এলিজি’ (Elegy) কাব্যের কবি থমাস গ্রে পর্যন্ত তাঁর প্রকাশকের কাছ থেকে ওই কবিতার জন্য টাকা নিতে রাজী হননি, তাঁর ভদ্রলোকসুলভ মর্যাদার হানি হবে বলে। ভদ্রলোকের মর্যাদা সম্বন্ধে এরকম টনটনে জ্ঞান নিয়ে গ্রে’র মতো কবি ‘এলিজি’ কাব্য রচনা করেছিলেন, একথা ভাবতেও কী রকম লজ্জা হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক ওয়াল্টার স্কটের মনোভাবও তাই ছিল—“Scott always preferred to be known as a landed gentleman rather than as an author––”২ সাহিত্যিক বলে পরিচয় দেওয়ার চেয়ে জমিদার বলে পরিচয় দিতে স্কট অনেক বেশি গর্ববোধ করতেন। কবি বাইরন যদিও শেষকালে প্রকাশকদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব বেশি টাকা আদায় করার চেষ্টা করেছেন, তাহলেও প্রথম দিকে বই—এর জন্য টাকা নিতে তিনি সঙ্কোচবোধ করতেন, ওই একই কারণে।
প্রকাশকের যুগেও দেখা যায় যে সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে সাহিত্যিকরা লেখার জন্য টাকা নিতে সংকোচবোধ করতেন। সুতরাং সাহিত্যিক পেশার যে কি রকম সামাজিক মর্যাদা ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ ছাড়া, ‘ছদ্মনামে’ (Pen-name) লেখার রীতিও প্রধানত এই কারণে চালু হয় বলে মনে হয়। ভদ্রলোক ও অভিজাত বংশের সাহিত্যিকরা স্বনামে লিখতে চাইতেন না, সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে। পরিবারের আভিজাত্যের খ্যাতি যাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্যই তাঁরা ‘ছদ্মনামে’ লিখতে আরম্ভ করেন। জার্মানির কথা উল্লেখ করে ডাঃ শুশকিং এ সম্বন্ধে বলেছেন১ :
“In the matter of the social standing of the artist it is very significant, for example, that in Germany at the beginning of the century, and for a long time after it, many aristocrats who engaged in literary work felt it necessary to assume middle class pen-names–”
কাউন্ট বেরন, এডলার সকলে তাঁদের বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত ছদ্মনাম নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। শুধু জার্মানিতে নয়, অন্যান্য দেশেও এই রীতি চালু হতে থাকে। এই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে ধীরে ধীরে আধুনিক যুগে—“It was the natural consequence of the changed outlook on life associated with the rise of the middle class.” : ধনতান্ত্রিক যুগে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশের পর, সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদা বাড়তে থাকে। কিন্তু রাতারাতি বাড়েনি, খুব ধীরে ধীরে বেড়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত নতুন যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যেও মধ্যযুগের মনোভাব বেশ সজাগ ছিল দেখা যায়। বাইরনের মতো কবির মন থেকেও অতীত ধারণার মূল উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। ১৮১৩ সালের ১৪ নভেম্বরের ডাইরিতে বাইরন লেখকদের সামাজিক মর্যাদার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন১
“I do think the preference of writers to agents–– the mighty stir made about scribbling and scribes, by themselves and others–– a sign of effeminacy, degeneracy and weakness. Who would write, who had anything better to do?”
এখানে বাইরন লেখকদের সম্বন্ধে mighty stir—এর কথা উল্লেখ করেও বলছেন যে ওটা degeneracy—এর লক্ষণ। তিনি ১৮১৩ সালে এমন কথাও বলেছেন যে “Who would write, who had anything better to do?” প্রচলিত সংস্কার, প্রথা বা দৃষ্টিভঙ্গি রাতারাতি বর্জন করা যে কত কঠিন, তা বাইরনের এই ১৮১৩ সালের উক্তি থেকে বোঝা যায়। নতুন যুগের বিকাশ হলেও, মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়লেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও দেখা যায় যে, ইংলন্ডের মতন দেশে বাইরনের মতন কবিও, সাহিত্যিকদের নিয়ে মাতামাতি করাটাকে, চারিত্রিক অবনতি ও মেয়েলিপনার লক্ষণ বলে অভিযোগ করছেন। সাহিত্যিকরা নিজেরাই সকলে তখনও তাঁদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হননি দেখা যায়। তার অনেক পরে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং অন্যের কাছ থেকে যোগ্য মর্যাদা পেয়েছেন। তার ইতিহাস খুব বেশি হলে একশো বছরের বেশি নয়। কিন্তু সেই মর্যাদার স্বরূপ কী? সত্যিই কি সেটা খাঁটি সাহিত্যিক পেশা ও প্রতিভার মর্যাদা, না সাহিত্যিক ব্যবসায়ে সাফল্যের মর্যাদা?
…………
১. Schucking : The Sociology of Literary Taste : Chap. 3 pp. 16-25
১. Schucking : ঐ : “Shifting of the Sociological Position of the Artist” অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১. ডাঃ শুশকিং—এর গ্রন্থে পূর্বোক্ত অধ্যায়ে উদ্ধৃত।
বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত
বাংলা হাতে লেখা পুথির প্রচলন শেষ হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষদিকে। বাংলাদেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রায় একশো বছর পর পর্যন্ত হাতেলেখা পুথির কদর ও প্রচলন ছিল দেখা যায়। তার প্রধান কারণ দুটি। প্রথম কারণ হল, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর সবরকমের বই ছাপা হত না এবং ছাপা সম্ভবও ছিল না। মুদ্রিত বইয়ের প্রচার ধীরে ধীরে হয়েছে, রাতারাতি হয়নি। কোনোদেশেই হয়নি। মুদ্রণও তখন যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং বহু মূল্যবান বই পাণ্ডুলিপি আকারেই থাকত, ছাপা সম্ভব হত না। দু—চারজন পণ্ডিত ও অনুরাগী পাঠক প্রয়োজনবোধ লিপিকর নিযুক্ত করে পাণ্ডুলিপি ‘কপি’ করিয়ে নিতেন। রাধাকান্ত দেব ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদেরও তাই করতে হয়েছে। পাণ্ডুলিপি প্রচলিত থাকবার দ্বিতীয় কারণ হল, পাঠকগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী বই ছাপা হয়েছে, যেমন এখনও হয়। বইয়ের ‘মূল্য’ অনুযায়ী বই ছাপা হয়নি, আজও সবসময় হয় না। এমন অনেক পুথি ছিল, যা মূল্যবান হলেও, ব্যয়বহুল বলে মুদ্রিত করা সম্ভব ছিল না এবং মুদ্রিত হলেও তার পাঠক পাওয়া যেত না। প্রাচীন পুথি নয় শুধু, নতুন—লেখা বইও অধিকাংশ সময় পাঠকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে ছাপা হত। প্রাচীন পুথি আজও অনেক ছাপা হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুথিশালায় আজও বহু মূল্যবান পুথি অমুদ্রিত অবস্থায় রক্ষিত আছে।
হাতেলেখা পুথির যুগে সমাজে সাধারণ ‘পাঠকগোষ্ঠীর’ কোনো অস্তিত্ব ছিল না। রাজা—মহারাজা ও জমিদার—তালুকদাররা মধ্যে মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনে পুথি নকল করিয়ে নিতেন। অনেক সময় তাঁরা নিজেরাও লিখে নিতেন, তবে রাজা বা রাজকুমাররা ধৈর্য করে পুথি নকল করতে পারতেন না। মধ্যে মধ্যে রাজকন্যা ও রাজমহিষীরা করতেন। বনবিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী লিখিত ”প্রেমবিলাস” গ্রন্থের পুথি (২৬২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় আছে। মুক্তকেশী বসুজায়া—লিখিত ‘অন্নদামঙ্গল’ গ্রন্থের পুথিও (২৬৩৩) আছে। রাজামহারাজেরা যে পুথি সবসময় নিজেদের পাঠার্থে নকল করাতেন তা নয়। দেবালয়ে, ধর্মানুষ্ঠানে ও ব্রাহ্মপণ্ডিতদের দান করবার জন্যও পুথি নকল করা হত। সোনা দান, গো—দানের মতন পুথি দানও পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। ধর্মশাস্ত্রে তাই পুথিদানের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে দেখা যায়। লিপিকরেরা ও তার উল্লেখ করতে ভোলেননি। পুথি দান নয় শুধু, পুথি নকল করলেও যে পুণ্যলাভ করা যায়, লিপিকররা সেকথাও উল্লেখ করেছেন। মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের পরেও দেখা যায়, এই পুণ্যার্জনের লোভে অনেক ধনী ব্যক্তি প্রচুর অর্থব্যয় করে বই ছেপে বিতরণ করেছেন। তার মধ্যে বর্ধমানের রাজাদের প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।
পুথি নকল করা যে খুবই কষ্টকর ব্যাপার, তা বলে বোঝাবার দরকার নেই। সেকালের পেশাদার লিপিকাররা, একালের প্রেস—কম্পোজিটরদের মতন, একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠলেও, যথেষ্ট মেহনত করে তাঁদের অর্থ রোজগার করতে হত। ১১৫৯ সালে কৃষ্ণরাম দাসের ‘কালিকামঙ্গল’ গ্রন্থের পুথি নকল করে লিপিকর আত্মারাম ঘোষ ”দগিণা ১ জোড়া কাপড় আর ২ তঙ্কা” পেয়েছিলেন (সোসাইটির পুথি, ৯।৩২২)। তখনকার দিনে একজোড়া কাপড়ের দাম দু—টাকা ধরলেও, কালিকামঙ্গল পুথির মূল্য বা খরচ পড়ে চারটাকা। আজকালকার টাকার মূল্যহারে অন্তত বত্রিশ টাকা। পুথি কপি করানো যে কত ব্যয়সাধ্য ছিল, তা এই সামান্য হিসেব থেকেই অনুমান করা যায়। মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে লিপিকরদের ‘রেট’ কিছু যে কমেনি তা নয়। পেটের দায়ে ও প্রতিযোগিতার ফলে কিছুটা তাঁরা কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, দু—হাজার শ্লোক—সম্বলিত ‘কাব্যাদর্শ’ গ্রন্থের পুথি মাত্র পাঁচসিকা দিয়ে কিনেছিলেন। ১৮১২ সালে পূজারি গোস্বামীর গীতগোবিন্দটীকার একখণ্ড দশ আনায় বিক্রি হয়েছিল, একথা পুথিতেই লেখা আছে (সোসাইটির পুথি, ৭ খণ্ড, ১৩৪)। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলেই যে ক্রমে পুথির মূল্য কমে আসছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু রেভারেন্ড ওয়ার্ড সাহেব, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পুথি নকলের হার অত্যন্ত বেশি বলে অভিযোগ করেছেন। তখন ৩২,০০০ অক্ষর নকল করাতে বারো আনা থেকে একটাকা পর্যন্ত দিতে হত। মনে হয়, ওয়ার্ড সাহেব পুথিনকলের খরচের কথা ভেবে এই অভিযোগ করেছেন, লিপিকরের পরিশ্রমের কথা ভেবে বলেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেখা যায় এই হার বেড়ে প্রায় চতুর্গুণ হয়েছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৬৯ সালের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি থেকে জানা যায় যে, তখন পুথিনকলের হার ছিল একহাজার শ্লোক প্রতি চারটাকা। অনভিজ্ঞ লিপিকররা ছাপাখানার আতঙ্ক দ্বিতীয় যুগে কাটিয়ে উঠে, একথা বুঝেছিলেন যে, সব পুথি ছাপা সম্ভব নয় এবং ছাপার হারও এমন কিছু কম নয় যে তাঁদের পারিশ্রমিকের হার কমাতে হবে। পরবর্তীকালে, ছাপাখানার কাজ ভালোভাবে চালু হবার পরেও, পুথিনকলের হার বৃদ্ধির কারণ তাই বলে মনে হয়।
এত ব্যয় করে ও কষ্ট করে, সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে পুথি নকল করানো হত না, তা বলাই বাহুল্য। পুথির ধনিক মালিকই পুথি পাঠ করতেন, অথবা দান করতেন। পুথিগত বিদ্যার কোনো প্রচার হত না। বাইরের সমাজের সাধারণ লোক পুথি পাঠ করবার কোনো সুযোগও পেত না। এমনকী, সাধারণ লোকের মধ্যে দু—চারজন বিদ্যোৎসাহী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ধনির গৃহ থেকে পুথি চুরি করে যে পাঠ করবেন, তারও কোনো উপায় ছিল না। লিপিকররা, বোধহয় পুথির মালিকদের পরামর্শে, পুথির শেষে কড়া দিব্য দিয়ে রাখতেন, যাতে পুথি কেউ না চুরি করে। যেমন :
অর্জিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যচ্চ মেহনঘ।
কর্তুমিচ্ছতি যঃ পাপী তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ।।
আত্মনো হ্যুপকারায়োপকারায় পরস্য চ।
ইদং হরতি যো মূঢ়স্তস্য তাতঃ পশুধ্রুবম্।।
(সোসাইটি, ৭। ৪৯৭৫)
দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি
মাতা গাধিং পিতা সুকরং জর্ম্মে জর্ম্মে
(পরিষৎ—পুথি, ১৭২)
এই পুস্তক যে বেক্তি চুরি করিবে।
সে সাসুরে হইবেক য়ার পুত্রবধূকে হরণ করিবে।
(পরিষৎ—পুথি, ২৮৫)
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা পুথির বিবরণ, ৩।৫২২)
‘বংশোক্ষয় ভবেৎ’, ‘পশুধ্রুবম’, ‘মাতা গাধিং পিতা সুকরং’, ‘পুত্রবধূকে হরণ করিবে’, ‘গোব্রাহ্মণ বধ লাগিবেক’ ইত্যাদি কটূক্তি ও অভিশাপ উপেক্ষা করে, কেবল জ্ঞানার্জনের তাড়নায়, সাধারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে পুথি চুরি করা যে কত কঠিন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। পুথির যুগে জ্ঞানবিদ্যা তাই ধনিকের গৃহে ও রাজসভায় বন্দি হয়ে থাকত। সাধারণ মানুষের তার মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল না।
ছাপাখানা যখন স্থাপিত হল তখন এক নতুন যুগের সূচনা হল আমাদের দেশে। বহির্জগতে যুগে যুগে অনেক বিপ্লব হয়েছে এবং তার ফলে সমাজের ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের আগে জ্ঞানজগতের কোনো বিপ্লব হয়নি কোথাও। পৃথিবীর কোনো দেশেই হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে ইউরোপে যেমন বিদ্যাজগতে এক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, আমাদের ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল। ভারতবর্ষের বা বাংলাদেশের ছাপাখানার বিস্তারিত ইতিহাস এখানে আলোচনা করব না। যোগ্য ব্যক্তিরা সে—সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেছেন। তথ্যাকীর্ণ সেই নীরস ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন আপাতত নেই। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রসার সম্বন্ধে বাংলাদেশের ছাপাখানা ও মুদ্রকদের সম্বন্ধে যতটুকু বলা দরকার, তাই বলব।
ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ১৫৫৬ ও ১৫৫৭ সালে, ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায়, প্রথম বই ছাপা হয়। বাংলাভাষায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হল ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থ—ভেদ’। ১৭৪৩ সালে মুদ্রিত। বাংলাভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত নয়, রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলাদেশেও মুদ্রিত নয়, পর্তুগালের লিসবন শহরে মুদ্রিত। লেখকের নাম পাদ্রি মানোএল—দা—আসসুম্পসম। ১৭৩৪ সালে তিনি ভাওয়ালে বসে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ—ভেদের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। বইয়ের মধ্যে মোটামুটি রোমান—ক্যাথলিক ধর্মের ধর্মবীজ, মূল বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি বর্ণনা করা হয়েছে। রোমান থেকে বাংলায় অক্ষরান্তরিত করলে, বইয়ের গোড়ায় আবেদনটি এইভাবে পাঠ করা যায়১ :
বেঙ্গালীরে জানান
পড়হ
দোস্ত বেঙ্গলী, শোন : পুথি সকলের উত্তম পুথি, শাস্ত্রসকলের উত্তম শাস্ত্র : শাস্ত্রী—সকলের উত্তম শাস্ত্রী খ্রিস্তর শাস্ত্রী, কৃপার শাস্ত্র এবং কৃপার শাস্ত্রের পুথি।
এহি পুথিতে শোনো মন দিয়া পাইবা বুঝন, বুঝান, বুঝিবার বুঝাইবার উপায় তরিবার। আস্থার ভেদের অর্থ শোনো, শোনাও; পৃথকে জানিয়া বুঝো, বুঝাও, পরিণামে পন্থ ধরো ধরাও; শিষ্য গুরুর ন্যায়েতে ন্যায় করিতে শিখো, শিখাও, এহা জানিয়া, বুঝিয়া, মানিয়া মুক্তি হইবেক; দশ আজ্ঞা পালন করো যদি।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ—ভেদের বিশেষ স্থান আছে। কিঞ্চিদধিক দুশো বছর আগেকার বাংলা গদ্যভাষার নিদর্শন এই বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। ইউরোপীয়দের মধ্যে বাংলাভাষা চর্চার আদিযুগে বিদেশিদের দ্বারা রচিত বাংলা রচনার সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন এই বইটি। পূর্ববঙ্গের (ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের) প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে স্বল্পাধিক সাধুভাষার সংমিশ্রিত রূপের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবেও এর মূল্য আছে। তা ছাড়া, রোমান বর্ণমালায় হলেও, বাংলাভাষার এই প্রথম মুদ্রিত রূপ বলে, এ বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।১
ভারতীয় ভাষায় প্রথম বই ছাপা হয় কোচিনে। ১৫৭৭ সালে জন গোনসালভেস নামে একজন স্পেনীয় পাদ্রি মালায়ালাম—তামিল অক্ষর প্রস্তুত করে, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের ‘Doctrina Christao’ গ্রন্থের অনুবাদ মুদ্রিত করেন। অনূদিত গ্রন্থের নাম ”ক্রীস্ট্য বন্নকনম”। এই ‘ক্রীস্ট্য বন্নকনমই’ ভারতে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত ভারতীয় ভাষার সর্বপ্রথম বই। এবইয়ের একখানি কপি মাত্র প্যারিসের ‘বিবলিওথেক ন্যাশানেল’ লাইব্রেরিতে আছে, তাও ১৫৭৯ সালে পুনমুর্দ্রিত সংস্করণ, প্রথম সংস্করণ নয়।২ আজ পর্যন্ত অন্তত এর আগেকার ছাপা ভারতীয় অক্ষরে আর কোনো মুদ্রিত গ্রন্থের নিদর্শন অনুসন্ধান ক’রে পাওয়া যায়নি। উল্লেখযোগ্য হল, ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বই ‘ক্রীস্ট্য বন্নকনম’ এবং রোমান হরফে বাংলাভাষার প্রথম মুদ্রিত বই ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থ—ভেদ’, দু—খানিই খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত বই, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অনুবাদ ও রচনা করা। মধ্যযুগে, হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির আমলে, ধর্মই ছিল সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। আধুনিক মুদ্রণযুগের আদিপর্বে দেখা যায়, মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে মুদ্রিত গ্রন্থের চরিত্র রাতারাতি বদলায়নি। পাণ্ডুলিপির যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই ছাপাখানার প্রসার হয়েছে ধীরেসুস্থে। তার কারণ, ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে বা মুদ্রিত বই প্রচারিত হবার ফলে, কোনো দেশের পাঠকগোষ্ঠী নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হঠাৎ গড়ে ওঠেনি। ছাপাখানার প্রথম যুগে ইউরোপেও ধর্মগ্রন্থের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই প্রথম যুগের মুদ্রকরা ধর্মগ্রন্থই বেশি ছেপেছেন। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, হবার কোনো কারণও ছিল না। কেবল ইউরোপের সংস্পর্শে আসার ফলে এদেশে ছাপাখানার প্রবর্তন হয়েছিল বলে, ইউরোপবাসীর খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থই ছিল এদেশের সর্বাধিক মুদ্রিত গ্রন্থ। ছাপাখানার আদিপর্বে, মুসলমান আমলে ইসলামধর্মীরা যদি ছাপাখানার প্রবর্তন করতেন, তাহলে ইসলামধর্মই হত এদেশের প্রথম যুগের মুদ্রিত গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু।
বাংলা বর্ণমালার প্রথম মুদ্রিত রূপ দেখা যায় হলহেডের (Halhed) ‘A Grammar of the Bengal Language’ নামক গ্রন্থে। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড রচিত এই গ্রন্থ ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইংরেজিতে লেখা এই ব্যাকরণের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে অংশ—বিশেষ বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়। বাংলাদেশের হুগলি শহরে, ছেনিকাটা বাংলা হরফে (কাঠের অক্ষরে নয়), এ্যানড্রুজের ছাপাখানায় বইখানি ছাপা হয়। বাংলাদেশে মুদ্রণযুগের প্রবর্তন হয় ১৭৭৮ সাল থেকে। অবশ্য হলহেডের ব্যাকরণেই যদি সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হয়ে থাকে, তাহলে একথা সত্য। পরে যদি আরও প্রাচীন কোনো বই পাওয়া যায়, তাহলে এ সত্য মিথ্যা প্রমাণিত হবে।
হলহেডের ব্যাকরণ—মুদ্রণের একটু ইতিহাস আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলাদেশে ইংরেজ—শাসন কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হবার পর, বিদেশিরা এদেশের ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনবোধ করেন। ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগের জন্য নয়, শাসনকার্যের প্রয়োজনের জন্য। হলহেড সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষায় এই বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। রচনার পর মুদ্রণের সমস্যা দেখা দেয়। বাংলা সাহিত্য থেকে যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাই বা ছাপা হবে কোথায়? তখনও মুদ্রণোপযোগী বাংলা হরফ তৈরি হয়নি এবং তাতে কোনো বইও ছাপা হয়নি। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন গবর্নর—জেনারেল। এর আগে বিলেতে উইলিয়ম বোল্টস এক সেট বাংলা মুদ্রণহরফ তৈরি করাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং হলহেডের ব্যাকরণ ছাপানো এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তখন চার্লস উইলকিন্স নামে কোম্পানির একজন বিদ্যোৎসাহী সিভিলিয়ানকে ওয়ারেন হেস্টিংস অনুরোধ করেন, বাংলা হরফের ছেনি কেটে দিতে। উইলকিন্স এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বিদ্যাচর্চায় তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগও ছিল। আগেই তিনি নিজের চেষ্টায় বাংলা হরফের দু—একটি ছেনি তৈরি করেছিলেন। হলহেডের সঙ্গেও উইলকিন্সের বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং তিনি সাগ্রহে সম্মত হলেন। ছেনি কাটা, ঢালাই করা, ছাপা, সব তিনি নিজের হাতেই প্রথম করেন। বাংলা ছাপার হরফ প্রথমে এইভাবেই তৈরি হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে চার্লস উইলকিন্সকে বাংলাদেশের ক্যাক্সটন বলা যায়।
বাংলাদেশের এই ইংরেজ ক্যাক্সটনের সহকারী একজন বাঙালি ক্যাক্সটন ছিলেন, তাঁর নাম পঞ্চানন কর্মকার। প্রথম থেকেই বাংলা ছাপার হরফ তৈরির কাজে তিনি উইলকিন্সের সহযোগী ছিলেন। উইলকিন্স তাঁকে সযত্নে অক্ষরের ছেনিকাটা শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাংলার কর্মকারদের লৌহকর্মে আশ্চর্য কুশলতার কথা মনে করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, অক্ষরের ছেনিকাটা শিখতে পঞ্চাননকে খুব কষ্ট করতে হয়নি। তিনি বাংলা অক্ষরের ছেনিকাটায় অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করে, পরে নিজে একটা আলাদা সেট অক্ষর তৈরিও করেছিলেন। হলহেডের ব্যাকরণ যে বাংলা অক্ষরে ছাপা হয়েছিল, তার চেয়ে পঞ্চাননের হাতে তৈরি বাংলা অক্ষরগুলি আরও বেশি সুন্দর হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে এই অক্ষরে কর্ণওয়ালিসের কোড ছাপা হয়। প্রধানতঃ পঞ্চানন কর্মকারের চেষ্টাতেই মুদ্রণহরফ নির্মাণ একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী শিল্পে (টাইপ ফাউন্ড্রি) পরিণত হয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত পঞ্চাননের তৈরি অক্ষরের ছাঁদেই বাংলা মুদ্রণহরফ তৈরি হয়েছে।১
ব্যাকরণ ও আইনকানুনের অনুবাদগ্রন্থ ছাড়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দু—খানি অভিধান। প্রথমটি হল, আপজনকৃত ”ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলবি”। কলকাতার ”দি ক্রনিকেল প্রেস” থেকে ১৭৯৩ সালে এই অভিধান প্রকাশিত হয়।* দ্বিতীয়টি হল, হেনরি ফরস্টারের “A Vocabulary in two parts, English and Bangalee, and vice versa” নামক অভিধান। এই অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড—১৮০২ সালে।
ভারতীয় অক্ষরে প্রথম বই ছাপা হয় খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে, তার নাম ক্রীস্ট্য বন্নকনম। এ বই ভারতবর্ষেই ছাপা হয়। বাংলাভাষায় প্রথম বই ছাপা হয় রোমান হরফে, নাম কৃপার শাস্ত্রের অর্থ—ভেদ। পর্তুগালের লিসবন শহরে ছাপা হয়। বাংলাদেশে প্রথম বাংলা অক্ষর ছাপা হয় ইংরেজিতে লেখা বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থে। তারপর আইনকানুনের অনুবাদ ও অভিধান। তারপরে ছাপা হয় বাংলা খ্রিস্টধর্মেরই বই। বাংলা মুদ্রিত অক্ষর প্রথমে ব্যাকরণ, আইনকানুন ও অভিধানেই ব্যবহৃত হয়। স্বাধীনভাবে যদি বাংলা ছাপাখানার সূত্রপাত হত, তাহলে হয়তো ভগবদগীতা ও কোরআনের বাংলা অক্ষরে মুদ্রণ, অথবা বাংলা অনুবাদ মুদ্রণ থেকেই আরম্ভ হত, ইউরোপে যেমন বাইবেল মুদ্রণ থেকে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে তার ব্যতিক্রম হয়েছে পরাধীনতার জন্য। বিদেশি শাসকদের নিজেদের শাসনকার্যের স্বার্থে ব্যাকরণ, আইনকানুন ও অভিধানের প্রয়োজন হয়েছে বেশি। ইংরেজরা এদেশে পাদ্রির বেশে ধর্মপ্রচার করতে আসেননি। তাই খ্রিস্টধর্মের গ্রন্থের চেয়ে ব্যাকরণ, অভিধান ও আইনগ্রন্থের প্রয়োজন তাঁদের অনেক বেশি ছিল। এই প্রয়োজনের জন্যই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মুদ্রণযুগের সূত্রপাত হয়েছে ব্যাকরণ অভিধান ও আইনের বই দিয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই হ’ল মুদ্রণ যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ বা বাংলার কবিয়ালরা তখনও রাজসভায় বন্দি হয়ে আছেন, জনসভায় যাত্রাপথে ছাপাখানার প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি।
ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে বাংলাদেশে। ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় এবং ব্যাপটিস্ট মিশনারি উইলিয়ম কেরির শ্রীরামপুর পদার্পণে ব্যাপটিস্ট মিশনের পত্তন হয়। এই দুটি ঘটনাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেসব ইংরেজ সিবিলিয়ানকে এদেশে পাঠাতেন, কাজকর্মের সুবিধার জন্য তাঁদের যে সর্বাগ্রে এদেশীয় ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, তৎকালীন গভর্নর—জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁরই উদযোগে ১৮০০ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত—মৌলবি প্রভৃতি নিয়োগ করা হয় এবং এদেশি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা আরম্ভ হয়। মুদ্রণের প্রয়োজন বাড়ে এবং তার ফলে কলকাতায় ছাপাখানারও প্রসার হয়।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য, আধুনিক মুদ্রণযুগে, আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, বিদেশি ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে, তাঁদের মধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের নাম সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাংলার মুদ্রণশিল্প ও মুদ্রিত সাহিত্যের আদিপর্বের ইতিহাস প্রধানত ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের কীর্তিকাহিনির ইতিহাস। এই মিশনারীদের মধ্যে সবচেয়ে উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন উইলিয়ম কেরি। কেবল মিশনের পক্ষ থেকে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষার জন্য নয়, নতুন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের কর্তা হিসেবেও, উইলিয়ম কেরি মুদ্রণযুগের উদযোগপর্বে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালনও করেছিলেন।১
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যে ব্যাপটিস্ট মিশনারি আসেন। তাঁর নাম জন টমাস। ১৭৮৩ সালে প্রথম একবার বাংলাদেশে এসে, ১৭৮৪ সালেই তিনি ইংলন্ডে ফিরে যান এবং ১৭৮৬ সালে দ্বিতীয়বার বাংলায় ফিরে আসেন। টমাসের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা এবং তার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোধ করেছিলেন। শিক্ষার জন্য তিনি একজন যোগ্য শিক্ষক সন্ধান করতে লাগলেন। এই যোগ্য শিক্ষক হলেন রামরাম বসু। মুনশি রামরাম বসুর সঙ্গে টমাস মালদহ যান। পরে নবদ্বীপ এসে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৭৯২ সালে তিনি আবার ইংলন্ড ফিরে যান। ১৭৯৩ সালে আবার তিনি ফিরে আসেন। এইবার তাঁর সঙ্গী হয়ে আসেন উইলিয়ম কেরি। আসার পথে জাহাজেই কেরি বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন টমাসের কাছে। পরে রামরাম বসুই তাঁর মুনশি নিযুক্ত হন। কোম্পানির সাহেবদের হুকুম ছিল, এই মিশনারিদের যেন কলকাতায় কোনো মিশন প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়া হয়। আশ্রয়হীন অবস্থায় কেরি সপরিবারে মুনশিসহ, বাংলাদেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে—ঘুরে বেড়ান। কলকাতা থেকে ব্যান্ডেল, ব্যান্ডেল থেকে নদিয়া, নদিয়া থেকে ব্যবসায়ী নীলু দত্তের মানিকতলার বাগানবাড়ি, সুন্দরবন অঞ্চলের দেবহাট্টায় তিনি প্রায় সাত—আট মাস ধরে ভেসে বেড়ান। অবশেষে ১৭৯৪ সালে মালদহের মদনাবাটির নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের চাকরি নিয়ে তিনি চলে যান। ইতিমধ্যে বাংলাভাষায় কেরি বেশ দক্ষতা অর্জন করেন এবং তাঁর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ছাপার ইচ্ছা হয়। ১৭৯৬ সালের মধ্যেই নিউ টেস্টামেন্ট সম্পূর্ণ অনুবাদ করা শেষ হয়ে গেল। কলকাতার মুদ্রকদের কাছে হিসেবে নিয়ে তিনি জানলেন যে, ৬০০ পৃষ্ঠার অনুদিত গ্রন্থ, নতুন সেট বাংলা অক্ষর কাটিয়ে দশ হাজার কপি ছাপতে চল্লিশ হাজার টাকার (৪৩৭৫০ টাকা) বেশি খরচ পড়বে। অক্ষরের সেট ইংলন্ড থেকে কাটিয়ে আনতে হবে। এত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। ১৭৭৯ সালে তিনি খোঁজ পেলেন যে কলকাতায় দেশীয় ভাষার অক্ষরনির্মাণের একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। মনে হয়, এই হরফনির্মাণের কারখানা হুগলির পঞ্চানন কর্মকার, তাঁর সহকারীদের সঙ্গে, কলকাতা শহরে এসে স্থাপন করেছিলেন। বাংলা টাইপফাউন্ড্রির প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন কর্মকার। কেবল বাংলা ভাষার নয়, পঞ্চাননের সহযোগী ও জামাই মনোহর মিস্ত্রি, অন্যান্য আরও অনেক ভারতীয় ভাষার ছাপার অক্ষরের সেট তৈরি করেছিলেন। ১৭৯৯ সালে কেরির সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকারের পরিচয় হয়। এই সময় ইংলন্ড থেকে সদ্য—আগত একটি ছোটো কাঠের ছাপাখানা—কলকাতায় নিলামে বিক্রি হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়। নীলকর উডনি সাহেব বাইবেল প্রচারের উদ্দেশ্যে এই প্রেস ৪০কি ৪৬ পাউন্ড দিয়ে কিনে কেরীকে দান করেন। ১৭৯৮ সালে ছাপাখানাটি মদনাবাটির ঘাটে এসে পৌঁছায়। ১৭৯৯ সালের গোড়ার দিকে কেরি কলকাতায় আসেন টাইপের অর্ডার দেবার জন্য। এই সময় বাংলার মুদ্রণ অক্ষরের আদি—কারিগর পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এদিকে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রান্ট প্রভৃতি নতুন মিশনারিরা এইসময় কলকাতায় আশ্রয় না পেয়ে ড্যানিশ—এলাকা শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য তাঁরা (ফাউন্টেন ও ওয়ার্ড সাহেব) কেরির কাছে যাত্রা করেন নৌকাযোগে। তাঁদের পরামর্শে কেরী ১৭৯৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর, সমস্ত উপার্জিত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে, কেবল ছোটো কাঠের ছাপাখানাটি সঙ্গে নিয়ে, নৌকাপথে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কেরির আগমনের পর ব্যাপটিস্ট মিশনের পত্তন হয় ১৮০০ সালে।
ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, কেরির পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানার দায়িত্ব নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। ১৮ই মার্চ তারিখে (১৮০০ সাল) প্রথম শীট মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে, কলকাতা থেকে পঞ্চানন কর্মকার এসে শ্রীরামপুরের মিশন ছাপাখানায় যোগ দিয়েছিলেন। পরে রামরাম বসুও আসেন। পঞ্চাননকে পেয়ে অক্ষরনির্মাণের দুশ্চিন্তাও তাঁর দূর হয়েছিল। কাঠের ছাপাখানায় যেদিন বাইবেলের বাংলা অনুবাদের প্রথম শীট ছাপা হয়, সেদিন পাদ্রি সাহেবরা এক নতুন স্বপ্ন দেখে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। ছোট্ট একটি বিলেতি কাঠের ছাপাখানা, হ্যান্ডপ্রেস। সব কাজ হাতেই করতে হয়। তবু তাই দিয়ে কত কাজ যে করা যায়, তা পাণ্ডুলিপির যুগের লেখক ও লিপিকররা কল্পনা করতে পারছেন না। হাজার হাজার শীট ও পৃষ্ঠা ছাপা যায়, যা লিপিকররা মাসের পর মাস মেহনত করেও কপি করতে পারতেন না। হাজার হাজার পাঠকের কাছে মুদ্রিত বই পৌঁছে দেওয়া যায়, যা ছাপাখানার আগে কোনোমতেই সম্ভব হত না। ওয়ার্ডের জার্নালে ১৮ মার্চ তারিখে (১৮০০ সাল) লেখা আছে—“This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Mathew.” ম্যাথুর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম বাংলা মুদ্রিত পৃষ্ঠার সামনে দাঁড়িয়ে, পঞ্চানন কর্মকারের হাতে ছেনিকাটা বাংলা অক্ষরগুলির দিকে চেয়ে, কেরীর দৃষ্টিপথে সেদিন বাংলাভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গ্রন্থের হাজার হাজার মুদ্রিত পৃষ্ঠা ও তার পাঠকদের ছবি ভেসে উঠেছিল। অজ্ঞানতার তিমির ভেদ করে, রাজসভা থেকে জনসভার পথে মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যের নিশ্চিত ও দ্রুত অগ্রগতির স্বপ্ন দেখে, সেদিন তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না।
ছাপাখানায় পূর্ণোদ্যমে বইছাপার কাজ চলতে থাকে। ১৮১১ সালে লেখা ওয়ার্ডের একটি চিঠিতে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্ড লেখেন : ”ছোট্ট একটি ঘরে বসে আমরা লেখাপড়ার কাজ করি, আর সামনে চেয়ে দেখি মধ্যে মধ্যে প্রেসের দিকে। প্রেসের অফিসটি প্রায় ১৭০ ফুট লম্বা একটি হলঘর। ভারতীয় কর্মচারীরা সেখানে ব’সে নানাভাষায় বাইবেল অনুবাদ করছেন, অথবা প্রুফ সংশোধন করছেন। প্রেসের মধ্যে বিভিন্ন টাইপ—কেসে আরবী ফার্সী নাগরী তেলুগু পাঞ্জাবী বাঙলা মারাঠী চীনা ওড়িয়া বর্মী কানাড়ী গ্রীক হিব্রু ও ইংরেজী অক্ষর সাজানো আছে। হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান, সকল সম্প্রদায়ের কর্মচারী বসে কাজ করছেন—লেখা কম্পোজ করছেন, প্রুফ দেখছেন, অক্ষর ডিস্ট্রিবিউট করছেন। অফিসের বাইরে অক্ষরনির্মাণের জায়গা, সেখানে নানারকমের সব অক্ষর তৈরী হচ্ছে। তারই পাশে কয়েকজন লোক মিলে কালী তৈরী করছে, ছাপার কালী। কাছে বেশ বড় একটি ঘেরা খোলা জায়গায় কাগজীরা কাগজ তৈরী করছে হাতে। আমাদের নিজেদের ছাপার কাগজ আমরা নিজেরাই তৈরী করতাম।” এই বর্ণনা পড়েই মিশন প্রেসের দ্রুত অগ্রগতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়। ছাপাখানার সংলগ্ন ফাউন্ড্রিতে পঞ্চানন কর্মকার, তাঁর সহকারীদের নিয়ে সমস্ত ভারতীয় ভাষার ছাপার উপযোগী ছেনিকাটা হরফ তৈরি করছেন। তার পাশে কালি তৈরি হ’চ্ছে, ছাপার কালি। তারই কাছে, স্থানীয় কাগজিরা কাগজ তৈরি করছে হাতে। মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া কি? ভিতরে হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান, সকলে কম্পোজ করছেন, প্রুফ দেখছেন, অনুবাদ করছেন, কপি লিখছেন, ছাপছেন। হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি ও লিপিকরের যুগের অজ্ঞানতার অন্ধকারের বিরুদ্ধে, মধ্যযুগের রাজসভায় বন্দি বিদ্যার মুক্তির জন্য, এ যেন এক বৈপ্লবিক অভিযানের প্রস্তুতি।
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ধর্মপ্রচারের জন্য কেরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে মুদ্রণাভিযান আরম্ভ করেছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য হলেও, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কর্মক্ষেত্র হল ওয়েলেসলি—প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ১৮০১ সালে কেরি এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পসিত, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন মুখোপাধায়, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু প্রমুখ পণ্ডিতেরা প্রধানত তাঁরই সুপারিশে তাঁর অধীনে বাংলা বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কেরি নিজে এবং কলেজ—কর্তৃপক্ষও এই সময় বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ অভাব বোধ করতে লাগলেন। দেশীয় পণ্ডিতদের পুস্তক—রচনায় উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হল :
Resolved that Premiums shall be proposed to the learned Natives for encouraging literary works in the Native Languages. (Home Dept. Misc. 559,6)
তখন বই—ছাপাও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। ছাপার উপযুক্ত ছাপাখানাও বেশি ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের বিবিধ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য, বাংলা ছাপার হরফ ও ছাপাখানার উন্নতি ও দ্রুত প্রসার হতে থাকে কলকাতা শহরে। কলেজের কর্তৃপক্ষ মুদ্রণের ব্যয়—পূরণের জন্য প্রত্যেক মুদ্রিত বই কলেজ—লাইব্রেরির জন্য অনেকগুলি কপি কিনে নিতেন। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, প্রয়োজনে ও উৎসাহে, মুদ্রণযুগে বাংলাসাহিত্যের অগ্রগতি হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর বিখ্যাত A Dictionary in English and Bengalee (১৮৩৪) অভিধানের ভূমিকায় যা লেখেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :
“In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language was made imperative on young civilians. Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers. From this time forward writing Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta; a number of Books were supplied by the Serampore Press, which set the example of printing works in this and other eastern languages. The College Pundits following up the plan produced many excellent works.”
উইলিয়ম কেরি ১৮৩১ সাল পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, এবং সংস্কৃত মারাঠি ওড়িয়া অসমিয়া প্রভৃতি ভাষায় ব্যাকরণ অভিধানাদিও প্রকাশিত হয়েছিল।১
হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল—সোসাইটি, স্কুলবুক সোসাইটি ইত্যাদি শিক্ষা—সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিও ১৮১৭—১৮ সালের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষার এই প্রসারের তাগিদেই বাংলা ছাপাখানার এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছিল কলকাতায়। রামমোহন রায় এই সময় থেকেই তাঁর নবযুগের আদর্শসংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন, প্রধানত মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্যে। একথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেকালের সংবাদপত্রের এইসব সংবাদের তাৎপর্য তাই :
নূতন পুস্তক। —শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় অথর্ববেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন। (সমাচার দর্পণ, ২৭ মার্চ, ১৮১৯)
নূতন পুস্তক। —সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায় পুনর্বার সহমরণবিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক। (সমাচার দর্পণ, ৪ ডিসেম্বর, ১৮১৯)।
নবযুগের বাংলায় সামাজিক সংগ্রাম প্রধানত মুদ্রিত গ্রন্থের সংগ্রাম। হাতেলেখা পুথি—পাণ্ডুলিপির যুগের অশিক্ষার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রামমোহন—ইয়ং বেঙ্গল—বিদ্যাসাগরের যুগের প্রগতিশীল সংগ্রামের ইতিহাসকে এককথায় মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিবৃত্ত বলা যায়। Pen is mightier than the Sword—একথা পুথি—পাণ্ডুলিপির যুগের কথা নয়, প্রিন্টিং প্রেস বা ছাপাখানার যুগের কথা, মুদ্রিত গ্রন্থযুগের কথা। লিপিকরের হাতের কলম তার হাতের চেয়েও দুর্বল, কিন্তু মুদ্রণযুগের লেখকের কলম শাণিত তলোয়ারের চেয়েও ধারাল ও শক্তিশালী। মুদ্রিত গ্রন্থ গোলাবারুদের মতন মধ্যযুগের অজ্ঞানতার অন্ধকার দুর্গ ভেদ করে জ্ঞানের আলোকরাজ্যে অভিযান করেছে। বাংলাদেশে যখন এই অভিযান শুরু হয়েছে, তখন অর্ধস্ফুট বাংলাভাষায় সমসাময়িক সংবাদপত্রে সেই অভিযানকে এইভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছে :
যে দেশে ছাপার কর্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্বকালে কতক ২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য ২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে ২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।
গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক একস্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে। (সমাচার দর্পণ, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮১৯)।
এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যে হেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে ২ বৃদ্ধি পাইয়া সর্বদেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্বরা করে সেইমত ছাপার পুস্তক ক্রমে ২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহাদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্বকালে বধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তালপত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র ২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে। (সমাচার দর্পণ, ৩ এপ্রিল, ১৮১৯)।
মুদ্রণযুগের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা সবই প্রায় এর মধ্যে বলা হয়েছে। ভাষা অস্পষ্ট হলেও, বক্তব্য খুব স্পষ্ট। ”যেদেশের ছাপার কর্ম চলিত না হইয়াছে সেদেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না।” সভ্যতার ইতিহাসকে আজও ঐতিহাসিকরা মুদ্রণযুগ ও মুদ্রণপূর্ব যুগ, এই দুই পর্বে ভাগ করতে পারেন। মধ্যযুগ থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত ইতিহাস মুদ্রণপূর্বযুগের সভ্যতার ইতিহাস, আর মধ্যযুগের পরবর্তী আধুনিক যুগের ইতিহাস মুদ্রণযুগের ইতিহাস। ”পূর্বকালে কতক লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত।” পুথিপাণ্ডুলিপির যুগের একথা ঐতিহাসিক সত্য। তখন ”অন্য সকল লোক অন্ধকারে থাকিত।” কিন্তু ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর এদেশে যখন বই ছাপা আরম্ভ হয়েছে তখন ”ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।” ”এই যে ছোট বড় সকল ঘরে ”ব্যাপ্ত” হওয়া, এইটাই মুদ্রণযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হাজার হাজার বই ছাপা হচ্ছে। সব বই একস্থানে থাকছে না, ”নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে।” তার ফলে কি হচ্ছে? ”যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের” ইচ্ছা হচ্ছে এবং তারই ফলে ”এদেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।” ছাপা বইয়ের গতি ঠিক নদীর স্রোতের মতন—”ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায়”। নদী ক্ষুদ্র হলেও যেমন কূল—কূল করে প্রবাহিত হয়ে সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেইসব দেশের মাটিকে উর্বর করে, ছাপা বইও ঠিক তাই করে। সামান্য একটি ছোটো ছাপা বই হাজার মানুষের পাঠ্য হতে পারে এবং শত সহস্র মানুষের মনে জ্ঞানের বীজ ছড়িয়ে দিতে পারে। পতিত মানব—জমিনে আবাদ করলে যে কত সোনা ফলতে পারে, মুদ্রণযুগের আগে মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি।
১৮১৯ সালে, ‘সমাচার দর্পণে’র সংবাদে প্রকাশ, ”গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে।” আন্দাজের কিছুটা বাহুল্য হলেও, বাংলাদেশের ছাপাখানার আদিপর্বের এই কীর্তি সামান্য নয়। দশ বছরে দশ হাজার বই, অর্থাৎ প্রতি বছরে গড়ে একহাজার করে বই ছাপা হয়েছে। কত কপি করে প্রত্যেক বই ছাপা হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যায় না। কয়েকশো কপি করে ছাপা হলেও, ১৮১৯—২০ সালের মধ্যে কয়েক লক্ষ কপি মুদ্রিত বই বাংলাদেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজসভায় নয় বা পণ্ডিত—পুরোহিতদের মধ্যে নয়, সকল শ্রেণির সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজসভার বাংলা সাহিত্যের যুগ যে অস্তাচলে গেছে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্য জনসভামুখী হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মুদ্রিত গ্রন্থ বীর যোদ্ধার মতন মধ্যযুগের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলাদেশে নবযুগের প্রবর্তন করেছে। রিনেস্যান্স বা নবজাগরণের যুগ এসেছে মুদ্রিত গ্রন্থের অভিযানে। ১৮০১ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে কেবল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে দুলক্ষ বারো হাজার ভল্যুম বই ছাপা হয়েছে, চল্লিশটি ভাষায়। অধিকাংশ ভাষার মুদ্রণহরফ প্রথম তৈরি করে ছাপা হয়েছে। কেন ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ নবযুগের নবজাগরণের মহাকেন্দ্ররূপে গণ্য হয়ে থাকে, তা কেবল শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসের এই বিস্ময়কর কীর্তির কথা ভাবলেই বোঝা যায়।
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, ১৮২৫—২৬ সালের মধ্যে, কলকাতা শহরের যে সব ছাপাখানা, থেকে বইপত্র নিয়মিত ছাপা হচ্ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :
কলুটোলার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়
বহুবাজারের শ্রীলেবেন্ডর সাহেবের ছাপাখানা
আড়পুলির শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেস
মীরজাপুরের সম্বাদতিমিরনাশক প্রেস
মীরজাপুরের মুনশী হেদাতুল্লার ছাপাখানা
শাঁখারিটোলার মহেন্দ্রলালের ছাপাখানা
শাঁখারিটোলার বদন পালিতের প্রেস
শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেস
ইটালীর পিয়ার্স সাহেবের প্রেস
সমশুল আখবার প্রেস
কালেজ প্রেস
(১৮২৫—২৬ সালের ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকা থেকে সংকলিত)
কলকাতা শহরের (তখনকার) আশেপাশেও কয়েকটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন ”শুঁড়া লিথোগ্রাফিক প্রেস”। শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস ছাড়াও, নীলমণি হালদারের ছাপাখানা থেকে অনেক বই ছাপা হত। বাংলার নবজাগরণের অনুষ্ঠানপর্ব শেষ হয় এই সব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায়। একদিকে ধর্মসভার সংগঠকরা এবং আর একদিকে রামমোহন রায় ও হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ছাত্রবৃন্দ, ইয়ং ক্যালকাটা বা ইয়ং বেঙ্গল দল এই আন্দোলন শুরু করেন, প্রধানত এইসব ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত বইপত্র—পত্রিকা দিয়ে। উভয়দলের নেতারা মধ্যে মধ্যে বইপত্র ছেপে বিনামূল্যেও বিতরণ করেছেন।
মুদ্রণযুগের প্রথম পর্বে ইউরোপে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে বই ছাপা হত, কারণ মুদ্রণ তখন রীতিমতো ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। মুদ্রিত বইয়ের পাঠকগোষ্ঠী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণিরও তখন তেমন বিকাশ হয়নি। বাংলাদেশের মুদ্রকরাও তাই করেছেন। আগে বিজ্ঞাপন দিয়ে বই—ছাপার জন্য তাঁরা অগ্রিম টাকা সংগ্রহ করেছেন, তারপর বই ছেপে প্রকাশ করেছেন। মুদ্রণযুগের আদিপর্বে এইভাবে সীমাবদ্ধ সাবস্ক্রাইবারগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ আর্থিক পোষকতার প্রয়োজন হয়েছে। তার ফলেই মুদ্রণের প্রসার এবং মুদ্রিত বইয়ের প্রচার দুই—ই সম্ভব হয়েছে। এর দু—একটি দৃষ্টান্ত সেকালের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃত করছি১ :
”ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান। শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশী হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে থ্যাকার সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।” (সমাচার দর্পণ, ৩১ মার্চ ১৮২১)
”কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থে ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দূর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাষার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরুপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানোচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।
পুস্তকের পরিমাণ ছোটো আড়ার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক… উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবেক প্রতি পুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যায়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাঁচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদুক্তি হইতে পারি।… শ্রীকাশীনাথ শর্মণঃ। কলিকাতা শিমুল্যা।
এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতিজ্ঞানবান। (সমাচার দর্পণ, ২ জুন ১৮২১)
রামকমল সেনের অভিধানের জন্য অগ্রিম অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি খুব সহজ। কিন্তু দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনদাতা শ্রীকাশীনাথ শর্মণের পদ্ধতিটি অভিনব। তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মুদ্রক—প্রকাশক। পরিষ্কার ভাষায় তিনি ক্রেতা—পাঠকদের জানিয়েছেন যে ব্যাকরণ রচয়িতা যিনি তিনি—”তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকরার্থে ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন।” পুস্তকখানি মুদ্রণের জন্য গ্রহণ করেই তিনি নিশ্চিত হননি। ”বহু পরিশ্রমে” দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ ও রাম তর্কবাগীশের টীকানুসারে ”মূল ও ভাষার্থ” শুদ্ধ ও পরিবর্ধিত ক’রে তিনি অতিজ্ঞানবান” এবং তাঁর বই ছাপা হ’লে ”অনেকের উপকার হইবেক”—একথা জানিয়েও তিনি বলেছেন—”ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি।” ছাপাকর্ম যে সহজ কর্ম ছিল না, একথা কাশীনাথ শর্মার এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়। ১৮২৭ সালের ১৭ মার্চ কলকাতার আমড়াতলা গলির জনৈক বেণীমাধব দত্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাপার সংকল্প ক’রে ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রে জানাচ্ছেন যে—”গ্রন্থের পরিমাণ ৮৬৮ পৃষ্ঠা হইবেক একারণ মুদ্রাঙ্কিত করণে ব্যয়াধিক্য ভয়ে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া পূতচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে—”। বেণীমাধবের মতন তখন অনেকেই এইভাবে সাবস্ক্রাইবার সংগ্রহ করে বই প্রকাশ করতেন।
বাংলা বইয়ের প্রকাশক ও বিক্রেতা। মুদ্রিত বাংলা বইয়ের আদিপর্বের প্রকাশকরা অধিকাংশই মুদ্রকও ছিলেন। মুদ্রক ও প্রকাশকের মধ্যে ব্যবধান তখনও রচিত হয়নি। ইউরোপের ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। প্রথম যুগের বাঙালি মুদ্রক—প্রকাশকদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় গঙ্গাকিশোরের। একদিক দিয়ে বিচার করলে উইলকিন্সকে যেমন আমাদের দেশের ক্যাক্সটন বলা যায়, তেমনি অন্যদিক দিয়ে বিচার করে গঙ্গাকিশোরকেও বাংলার ক্যাক্সটন বললে ভুল হয় না। ইংলন্ডের আদি মুদ্রক—প্রকাশকরূপে (কেবল হরফ নির্মাতারূপে নয়) ক্যাক্সটন যেমন অমর হয়ে আছেন, বাংলাদেশের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তেমনি বাংলা বইয়ের আদি মুদ্রক—প্রকাশকরূপে ঐতিহাসিক সম্মান দাবী করতে পারেন। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের বিশাল বাঙালি পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে ক—জন পঞ্চানন কর্মকার ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের কথা জানেন?
মুদ্রণযুগের মহাতীর্থ শ্রীরামপুরের কাছে বহরা গ্রামে ছিল গঙ্গাকিশোরের বাড়ি। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় তিনি কম্পোজিটরের কাছে নিযুক্ত হন এবং সেই সুযোগে ছাপাখানার সমস্ত কাজকর্ম শেখেন। কিছুদিন পরে তাঁর স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার ইচ্ছা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তিনি কলকাতা শহরে এসে বই—প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। স্বাধীন ব্যবসা বইয়ের ব্যবসা যে করা যায়, তা বোধহয় গঙ্গাকিশোরের আগে আর কোনো বাঙালি ভাবেনি। বাংলা বই তার আগে ছাপা হয়েছে ধর্ম প্রচার ও স্কুলপাঠ্যরূপে। স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীরূপে কেউ তা ছেপে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেননি। প্রথম গঙ্গাকিশোরই এই ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শক। এদিক দিয়ে তাঁকে বাঙালি প্রকাশকদের ও পুস্তক—বিক্রেতাদের আদিগুরু বলা যায়। ১৮২০ সালে ত্রৈমাসিক ‘ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে লেখা হয় :
“…Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity. (On the effect of the Native Press in India, 134-35)
বই—প্রকাশ করে যে স্বাধীন বাণিজ্যের মতন অর্থ উপার্জন করা যায়, এবিষয়ে গঙ্গাকিশোরই প্রথম চিন্তা করেছিলেন। তিনি ইয়োরোপীয়দের ছাপাখানা থেকে বাংলা বই ছেপে বিক্রি করতেন। বিক্রির জন্য একটি ‘বুকশপও’ তিনি খুলেছিলেন। কলকাতা শহরে বাঙালি প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বইয়ের দোকান বলে মনে হয়। কেবল বইয়ের দোকান খুলেই তিনি নিশ্চিন্ত হননি। কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে তিনি এজেন্ট নিয়োগ করে পাঠাতেন বই বিক্রির জন্য। কলকাতা শহরে তখন বাংলা বই ছাপা হত প্রধানত ফেরিস এ্যান্ড কোম্পানির যন্ত্রালয়, লালবাজারের হিন্দুস্থানি প্রেস, লললুলালের সংস্কৃত যন্ত্র, বাঙ্গালি প্রেস বা বাঙ্গালা যন্ত্র, অথবা শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস থেকে। যতদূর জানা গেছে, তখন পর্যন্ত কোনো বাঙালি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় উদযোগী হননি। কিছুকাল অন্য প্রেস থেকে বই ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য উদযোগী ব্যবসায়ে লাভবান হয়ে, গঙ্গাকিশোর একটি বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য উদযোগী হন। তাঁর এই ছাপাখানাটির নাম বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস। এই প্রেসই বোধ হয় বাঙালির প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৮ সালের পরে নয়।
কেবল মুদ্রক—প্রকাশক নন, ক্যাক্সটনের মতন গঙ্গাকিশোরও নিজে লেখক ছিলেন। তিনি বাংলাভাষায় একখানি ইংরেজি ব্যাকরণ (১৮১৬), দায়ভাগ (১৮১৬—১৭), দ্রব্যগুণ (১৮২৪), চিকিৎসার্ণব (১৮২০?) প্রভৃতি গ্রন্থ নিজে রচনা করে প্রকাশ করেন। স্বরচিত গ্রন্থ ছাড়া, কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ তিনি ছেপে প্রকাশ করেন, তার মধ্যে কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৬ সালে তিনি ছ—খানি চিত্রসহ ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য ফেরিস এ্যান্ড কোম্পানির প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশ করেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণ এর আগে আর প্রকাশিত হয়নি বলে মনে হয়। গঙ্গাকিশোরই প্রথম অন্নদামঙ্গল ছেপে প্রকাশ করেন। সচিত্র মুদ্রিত বাংলা বইও এই প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী’, ‘লক্ষ্মীচরিত্র’, ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’, ‘চাণক্যশ্লোক’ এবং লললুলালের সহযোগে রামমোহন রায়ের কোনো কোনো বই ছেপে প্রকাশ করেন। হরচন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তির সহযোগে তিনি ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানিই বোধহয় বাঙালি প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।
ব্যবসায়ের জন্য স্বাধীনভাবে প্রথম বাংলা বই প্রকাশ করা, বই বিক্রির জন্য প্রথম বইয়ের দোকান করা, বাঙালি হয়ে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা, বাঙালির প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করা, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রথম বিক্রির জন্য ছাপা, প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই চিত্রিত করা—এতগুলি কাজ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম উদযোগী হয়ে করেছিলেন। বাংলার রিনেস্যান্স আন্দোলনে বাংলা ছাপাখানার ও বাংলা বইয়ের যদি কোনো ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকে, তাহলে গঙ্গাকিশোরই সে—সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সর্বপ্রথম তাকে সার্থক করার চেষ্টা করেন। গঙ্গাকিশোরের পরে এই পুস্তক—ব্যবসায়ের কাজে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন বাঙালিদের মধ্যে, তাঁদের মধ্যে বহুনিন্দিত বটতলার প্রকাশকরা উল্লেখযোগ্য।১ বাঙালি হিন্দু—মুসলমান মুদ্রক—প্রকাশক, যাঁরা বটতলার প্রকাশক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেকালে, তাঁরা পরবর্তীকালে যেকারণে যতই নিন্দিত ও উপেক্ষিত হন না কেন, বাংলা বইয়ের মুদ্রণ প্রকাশন ও প্রচারকার্যে তাঁরা যে সাহস ও শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাসে তা অবজ্ঞার বিষয় নয়।
বাংলা বইয়ের দোকান ও বিক্রয়ব্যবস্থা। গঙ্গাকিশোর একটি বইয়ের দোকান খুলেছিলেন বলে ‘ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া’ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বইয়ের দোকান বলতে আজকাল যা বোঝায়, সেরকম কোনো বইয়ের দোকান তিনি খুলেছিলেন কিনা, সঠিক বলা যায় না। মনে হয়, তাঁর ছাপাখানাই বইবিক্রয়ের কেন্দ্র ছিল এবং তাকেই বইয়ের দোকান বলা হত। ‘ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া’ একথাও বলেছেন যে তিনি এজেন্ট নিয়োগ করে বাইরে বই বিক্রির ব্যবস্থা করতেন। বটতলার প্রকাশকরাও তাই করতেন। মুদ্রণযুগের প্রথম পর্বে ইয়োরোপেও ভ্রাম্যমাণ ফিরিওয়ালারা বই নিয়ে মেলায়—মেলায় বিক্রির জন্য ঘুরে বেড়াতেন। বাংলা বইয়ের প্রথমযুগের মুদ্রক—প্রকাশরাও এইভাবে বই—প্রচারের ও বিক্রির ব্যবস্থা করতেন, এজেন্ট বা ফিরিওয়ালা নিয়োগ করে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন২ :
”তখন পুস্তকের ফেরিওয়ালা আমাদের এতৎ অঞ্চলের নগর পল্লীর অলিতে গলিতে সমস্ত দিন পুস্তক বিক্রয় করিত। কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, চরিতামৃত, প্রেমবিলাস, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থ, হিন্দু—মুসলমান পুরুষেরা কিনিত। মেয়েরাও জীবনতারা, কামিনীকুমার প্রভৃতি ক্রয় করিত। বটতলা ছাড়া অন্যত্র ছাপা দুই একখানি গ্রন্থও হকারদের কাছে মিলিত। ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে আমার বড় পোট ছিল। আমি প্রতি রবিবারে, তাহাদের পুস্তক ঘাঁটাঘাটি করিতাম। তাহারা আমায় কিছু বলিত না, আমি যে একজন বাঁধা খরিদ্দার। এমন খরিদ্দার চটাইবে কেন?”
(পিতা—পুত্রঃ অক্ষয়চন্দ্র সরকার : বোল্ড টাইপ লেখকের)।
অক্ষয়চন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কথা—বলেছেন। বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থই যে তখনও বেশি বিক্রি হত বাইরে, একথাও তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। প্রধানত তাঁরাই এজেন্ট পাঠিয়ে বাইরে বই বিক্রি করতেন। মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যের প্রসারে ও প্রচারে বটতলার প্রকাশকদের এই দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।
বাংলা বইয়ের দোকান বটতলার প্রকাশকরাই যে প্রথম খুলেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আসলে বাংলা বইয়ের দোকান তখন বিশেষ ছিলই না, কারণ দোকান সাজিয়ে বই বিক্রি করবার মতন মুদ্রিত বাংলা বই তখন খুব বেশি ছিল না। বই প্রথমে বিক্রি হত মুদ্রক—প্রকাশকদের ছাপাখানা থেকে, অথবা তাঁদের কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়ি বা সভাসমিতির আফিস থেকে, এবং যাঁর দরকার হত তিনি সেখান থেকে হদিশ করে কিনে আনতেন। বই ছাপিয়ে মুদ্রক—প্রকাশকরা এইভাবে বিজ্ঞাপনও দিতেন কাগজে। দু—একটি এই ধরনের বিজ্ঞাপন এখানে উদ্ধৃত করছি। ১৮১৮ সালে পীতাম্বর শর্মা ৪৯২ পৃষ্ঠার এক অভিধান ছাপিয়ে ‘সমাচার দর্পণ’ (২৫ জুলাই, ১৮১৮) পত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে—”চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা হয় তবে মোং উত্তরপাড়ায় শ্রীযুক্ত দূর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সোসায়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিতি।” এই বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়, বড় বইও তখন ৫০০ কপির সংস্করণ ছাপা হত। ১৮১৮ সালে ইংরেজি বর্ণমালা একখানি, অর্থ ও উচ্চারণসহ, বাংলায় তর্জমা করে ছাপা হয়—”কেতাব চামড়া বন্ধ জেলদ করা” এবং মূল্য ”ফি কেতাব ৩ টাকা”। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—”যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারী বাটীর নিকট শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।” এরকম বহু বইয়ের বিজ্ঞাপন তখনকার ইংরেজি—বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। দোকান খুলে বাংলা বই বিক্রির যে ব্যবসা করা যেতে পারে তা বাঙালিদের অন্তত তখনও খেয়াল হয়নি।
বিদেশি বা ইংরেজি বই বিক্রির দোকান কয়েকটি ছিল কলকাতা শহরে। এই সব বইয়ের দোকান প্রধানত চীনাবাজারেই ছিল। চীনাবাজারের বইয়ের দোকানের কথা শুনে অনেকেই হয়তো অবাক হবেন, কিন্তু এক শতাব্দী আগেকার কলকাতা শহরে বইবিক্রির প্রধান কেন্দ্র ছিল চীনাবাজার। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী এ—সম্বন্ধে চমৎকার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়—চতুর্থ দশকের কথা। তিনি চীনাবাজারের বইয়ের দোকান সম্বন্ধে লিখেছেন১ :
“Bookshops have attractions all there own, even in the China Bazar, this truth is very evident… The stock of books in some of these native shops is heavy… Shakespeare, Addision, Burns, Chalmers, Scott, Marryatt, indeed almost every author of note with general readers, has a place on the shelves of the bazaar bookseller.”
চীনাবাজারে অনেক দোকান এদেশি লোকের দোকান ছিল। নানারকমের পণ্যদ্রব্যের দোকানের মধ্যে বইয়ের দোকানও ছিল যথেষ্ট। বই কিনতে হলে চীনাবাজারেই যেতে হত। চীনাবাজারে বই—কেনা সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনের একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ”ভূদেব চরিতে” লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখানে সেটি উদ্ধৃত করছি২ :
অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন সময়ে ভূদেববাবুর একখানি ইংরাজী অভিধানের প্রয়োজন হয়। তিনি ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা হইতে সংগৃহীত দুই টাকা দশ আনা লইয়া চীনাবাজারে গমন করেন। তথায় মধুসূদন দে নামক এক ব্যক্তির পুস্তকের দোকান ছিল। সেই দোকানে একখানি জনসনের ডিক্সনারী’ দেখিয়া সেই খানিই ক্রয় করিতে মনন করিলেন; কিন্তু মূল্য জিজ্ঞাসা করায় মধু দে বলিলেন, ‘চারি টাকা’। ভূদেববাবু বলিলেন, ‘আমার কাছ দুই টাকা দশ আনা মাত্র আছে, উহা লইয়া পুস্তকখানি আমাকে দাও।’ মধু দে বলিলেন, ‘চারি টাকাতে বেচিলেও আমার লাভ অল্পই থাকে; এরূপ স্থলে দুই টাকা দশ আনাতে কেমন করিয়া দিব?’ ভূদেববাবু তখন অন্যান্য দোকানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ওই পুস্তক আর কোথাও পাইলেন না। রৌদ্রে হাঁটাহাঁটি করিয়া তাঁহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল। পুনরায় মধু দের দোকানের নিকট আসায় মধু দে বলিলেন, ‘কেন এত কষ্ট পাইতেছ, আমি উহা অপেক্ষা একখানি অল্প দামের অভিধান দিতেছি, লইয়া যাও।’
ভূদেববাবু বলিলেন, ‘ঐ খানিতে সকল কথার মানে পাওয়া যাইবে; ছোট অভিধান হইলে হইবে না। ঐ খানিই আমাকে দুই টাকা দশ আনাতে দাও।’ মধু দে বালকের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণের সন্তান জানিয়া বলিলেন, ‘তোমার পড়াশুনায় বড় আটা দেখিতেছি; আচ্ছা, বইখানি আমি তোমাকে অমনি দিতেছি, লইয়া যাও। ভূদেববাবু বলিলেন, ‘আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা আমি দিতেছি, বাকী আমি যাহা দিয়া উঠিতে পারিলাম না সেই অংশটাই তোমার দান হইবে।’ মধুসূদন দের মন প্রকৃত পক্ষেই উদার ছিল… তিনি স্বীকৃত হইয়া ভূদেববাবুর নিকট হইতে ঐ মূল্য লইয়া পুস্তকখানি তাঁহাকে দিলেন এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন, ‘তোমার যেরূপ পড়াশুনায় মন দেখিতেছি তাহাতে তোমার হাতে আমার বই নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার দোকানে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বই অনেক আছে; এক একবারে চারি পাঁচখানি করিয়া বই তোমাকে দিব, তুমি পড়িয়া আমায় ফেরত দিও…”
চীনাবাজারের এই মধুসূদন দের দোকান থেকে অনেকদিন ধরে অনেক বই নিয়ে ভূদেববাবু পড়েছেন। মহানুভবতা তখনও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিল এবং বই—ব্যবসায়ীদেরও ছিল, এমনকী চীনাবাজারেও। ভূদেববাবুর অভিজ্ঞতা থেকে আরও একটি কথা জানা যায়, বাঙালি বইবিক্রেতারা তখন নতুন ও পুরাতন বই, দুই—ই বিক্রি করতেন।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য অথবা সফিউদ্দিনের মতন বটতলার উদযোগী প্রকাশকরা ছাড়া, বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ে আর কেউ সে—সময় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন কি না জানা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছাপাখানা, বইপ্রকাশ ও বইবিক্রির স্বাধীন বাণিজ্যে বিশিষ্ট যুগনেতাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি দূরদৃষ্টি ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এই বাণিজ্য থেকে যথেষ্ট অর্থ ও উপার্জন করেছিলেন, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে বাংলার জীবিকার্জনের পন্থাস্বরূপ ছাপাখানা ও বই—ছাপার কাজ বেছে নিয়েছিলেন এবং তার জন্য প্রেস ও বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতেই বোঝা যায়, নবযুগের মুদ্রক—প্রকাশকদের কতখানি দায়িত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাসও দিনকতক ব্যবসা করেছিলেন, কিন্তু ছাপাখানার বা বইয়ের ব্যবসা নয়। স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর কর্মজীবনের গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন যে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে পরের অধীনে চাকুরি করা বর্তমান সমাজে কত কঠিন। তাই তিনি ব্যবসায়ের কথা ভেবেছিলেন এবং এমন এক ব্যবসায়ের কথা, যা তাঁর কর্মজীবনের বা মহান আদর্শের পরিপন্থী নয়। ১৮৪৭ সালে তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের চাকুরি ছেড়ে দেন, তখন কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত একজনকে বলেন : ”বিদ্যাসাগর খাবে কী করে?” বিদ্যাসাগর এই কথা শুনে বলেছিলেন : ”বোলো, বিদ্যাসাগর আলু—পটল বেচে খাবে।” আলু—পটল বেচে তিনি খাননি, প্রেসে বই ছেপে, তাই বেচে খেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে কাজ করার সময় তিনি ও তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকার সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেস কেনার মতন টাকা তাঁদের দুজনের কারও ছিল না। বিদ্যাসাগর তাঁর এক বন্ধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৬০০ টাকা ঋণ করে প্রেসটি কেনেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় তিনি যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন মার্শাল সাহেব সেই কথা জানতে পেরে তাঁকে বলেন যে ভারতচন্দ্রের ”অন্নদামঙ্গল” কাব্যের একটি ভালো সংস্করণ যদি তিনি উত্তম কাগজে সুন্দরভাবে ছেপে প্রকাশ করেন, তাহলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য তিনি ১০০ কপি কিনে নিয়ে প্রেসের ৬০০ টাকা ঋণ শোধ করে দেবেন। এই আশা পেয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্যের মূল পাণ্ডুলিপি আনিয়ে একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তার একশ’ কপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিক্রি করে বন্ধুর ঋণ পরিশোধ করেন।১ মুদ্রিত ও প্রকাশিত বইগুলি বিক্রির জন্য তিনি ‘সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী’ নামে একটি বইয়ের দোকান স্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙালি মুদ্রক—প্রকাশক ও পুস্তক—ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ছাপাখানা তিনি সখ করে স্থাপন করেননি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের কাজে, আধুনিক যুগে ছাপাখানার শক্তি যে কত বেশি তা বিদ্যাসাগর বুঝতেন। না বুঝলে, তাঁর অত কাজের মধ্যে তিনি ছাপাখানাটির দিকে মনোযোগ দিতে পারতেন না। তাঁকে আমি কেবল প্রকাশক বা পুস্তকব্যবসায়ী বলিনি, মুদ্রকও বলেছি। তিনি মুদ্রকও ছিলেন। কোনো মুদ্রকের চেয়ে ছাপাখানার টেকনিক্যাল বিদ্যা তিনি কম আয়ত্ত করেননি। ছাপাখানায় ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী অক্ষরের যতগুলি ঘর থাকে, বাংলায় তার ছয়—সাতগুণ বেশি ঘর থাকে, য—ফলা, র—ফলা, যুক্তাক্ষর ইত্যাদির বাহুল্যের জন্য। কোথায় কোন অক্ষরটি থাকলে কম্পোজিটারের সুবিধা হয়, সেরকম কোনো সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা তখনও বাংলা ছাপাখানায় প্রবর্তিত হয়নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বোধ হয় সর্বপ্রথম, বহু চিন্তা ও পরিশ্রম করে, কম্পোজিটারের অক্ষরের—কেসে, অক্ষর সাজানোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। বিদ্যাসাগর—প্রবর্তিত এই অক্ষরবিন্যাস পদ্ধতিই বাংলা ছাপাখানায় দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকে। তার নাম হ’ল ‘বিদ্যাসাগর সার্ট’।২
বাংলাদেশের ছাপাখানার ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও যে এতখানি দান আছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সমাজ শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য দান এত যুগান্তকারী ও মূল্যবান যে মুদ্রক—প্রকাশক—রূপে তাঁর দানের কথা আমরা প্রায় ভুলে গেছি বলা চলে। কিন্তু বিস্ময়ের বা বিস্মৃতির কোনো কারণ নেই। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যিনি আদর্শ—প্রতিমূর্তি ছিলেন, ছাপাখানা ও বইয়ের সঙ্গে তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ গভীর যোগাযোগ আকস্মিক ঘটনা নয়, ঐতিহাসিক যুক্তিসম্মত ঘটনা। নবযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি।
বিদ্যাসাগরের সহযোগী বন্ধুদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালংকার ছাড়াও, আরও অনেকে ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল) ও পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা যায়, বাংলার নবজাগরণের আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, ছাপাখানাও তাঁদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেউই ছাপাখানার সংস্রব ত্যাগ করে কিছুই করতে পারেননি। ছাপাখানাই ছিল তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার। বিরোধী পক্ষেরও তাই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগৃতি সংগ্রামকে তাই মুদ্রিত পত্রপত্রিকা ও পুস্তক—পুস্তিকার সংগ্রাম বলা যায়। ছাপাখানা ও ছাপা—বইয়ের সাহায্যেই আদর্শ—সংগ্রাম সম্ভব হয়। তার আগে, মধ্যযুগের কোনো ‘ইডিওলজি’র সংগ্রাম বলে কিছু ছিল না। ইডিওলজির সংগ্রাম বা আদর্শের সংগ্রাম ছাপাখানার দান, নবযুগের অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।
বাংলা সাহিত্যে প্রকাশকের দান। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যখন বাংলা সাহিত্যের একজন গণ্যমান্য প্রকাশক ছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্যে প্রকাশকের কোনো দান নেই, এমন কথা বলা যায় না। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকে, বই ছেপে যাঁরা প্রকাশ ও প্রচার করেছেন, তাঁদেরও প্রকাশক বলা উচিত এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁদের দানও উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও বটতলার হিন্দুমুসলমান প্রকাশকদের মতন উদযোগী পুস্তকব্যবসায়ীরা মধ্যযুগের রাজসভার অচলায়তন থেকে বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করে জনসভায় নিয়ে আসতে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বইয়ের দোকান থেকে, প্রকাশক ও মুদ্রকের গৃহ থেকে, অথবা ভ্রাম্যমাণ বই—ফিরিওয়ালাদের কাছ থেকে পাঠক—পাঠিকারা যে স্বাধীনভাবে বই কিনে পড়বার সুযোগ পেতেন, পুথি—পাণ্ডুলিপির যুগে সেরকম কোনো সুযোগ তাঁদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই সুযোগ প্রথম বাংলাদেশের প্রকাশকরাই করে দিয়েছিলেন? কিন্তু তাঁরা কারা? ইংলন্ড বা ইউরোপের প্রকাশকদের মতন তাঁরা কোনো ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন কি? ডডসলে বা টনসনের মতন প্রকাশক, অথবা পাইরেট ড্যান্টারের মতন প্রকাশক, বাংলাদেশে জন্মাননি কেন? বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে লংম্যান, কনস্টেবল, মারি, চ্যাপমান ও হল প্রভৃতির মতন নতুন পথপ্রদর্শক প্রকাশকের আবির্ভাব হল না কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীতে তো হয়ইনি, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশক পর্যন্ত, পুস্তক—ব্যবসায়ী ও প্রকাশক অনেক থাকলেও, ইউরোপের প্রকাশকদের সমতুল্য একজনও প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেননি। কেন করেননি? বাংলাদেশে প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অভাব ছিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতন যুগপ্রতিভা যে মারি বা লংম্যানের মতন প্রকাশকের অভাবে এদেশের পাঠকদের কাছে যথাকালে যোগ্য স্বীকৃতি পাননি, একথা বললে বোধহয় ভুল বলা হয় না। তার ফলে সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হয়নি, এমন কথা বলারও কোনো যুক্তি নেই। যুগোপযোগী যোগ্য প্রকাশকের অভাবে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে, বহু সাহিত্যিক প্রতিভার অকালমৃত্যু হয়েছে এবং সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য সাহিত্যক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে, সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়েনি। কাব্য—কথাসাহিত্যের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ চক্রে বাংলা সাহিত্য আবর্তিত হয়েছে। তার যা কিছু সমৃদ্ধির গৌরব, তাও এই সীমাবদ্ধ চক্রের গৌরব। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে এ—গৌরব স্বীকৃত হলেও, বাংলা সাহিত্যে যে সেখানে কতখানি উচ্চাসন দাবি করতে পারে তা বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসে আমরা বিচার করতে পারব না।
বাংলাদেশে প্রকাশকরা যখন যুগের তাগিদে আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁরা মধ্যযুগের পেট্রনের মতন পোষকতার ও দয়াদাক্ষিণ্যের মনোভাব নিয়ে এলেন, আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের ‘এন্টারপ্রেনোর’ বা উদযোগী ব্যবসায়ীরূপে এলেন না। ব্যবসায়ী রূপেও যখন এলেন, তখন ব্যবসাটা অস্তমিত যুগের দোকানদারি হয়েই রইল, নবযুগের ”এন্টারপ্রাইজ” হল না। এখানে তার দু—একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের জীবন থেকে। ১৮৩৯ সালে, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ ব্যয়ে রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন।১ বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁর গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁর ‘ক্যাপটিভ লেডি’ প্রথমে জে আর নেলার নামে একজন প্রবাসী বন্ধুকে উৎসর্গ করেন, কিন্তু গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট—জেনারেল জর্জ নর্টনের নামে উৎসর্গপত্র লিখে দেন। পোষক ও পোষকতার সঙ্গে সাহিত্যিকের জীবনের যোগাযোগ কিরকম, তা বুঝতে হলে বইয়ের উৎসর্গপত্র থেকে যেরকম সাহায্য পাওয়া যায়, এরকম আর কিছু থেকে পাওয়া যায় না। একথা সমাজবিজ্ঞানী শুশকিং সুন্দরভাবে তাঁর একখানি গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন।১ মধুসূদন বন্ধুর বদলে পেট্রন নর্টনকে বই উৎসর্গ করেছিলেন, কারণ নর্টন তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।২ মধুসূদনের সাহিত্যজীবনে পাইকপাড়ার রাজাদের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পোষকতার কথাও ভোলা যায় না। ‘রত্নাবলী’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ, ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক ও তার ইংরেজি অনুবাদ পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থেই অনূদিত, রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। পাইকপাড়ার ছোটরাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অনুরোধেই তিনি ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ ও ‘বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ নামে প্রহসন দু—খানি রচনা করেছিলেন এবং ১৮৬০ সালে রাজাদের ব্যয়ে বই দু—খানি প্রকাশিত হয়েছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে তিনি বইগুলি উৎসর্গও করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মধুসূদনের প্রথম ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’—গ্রন্থ ১৮৬০ সালে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন। এই পোষকতার জন্যই তিনি মহারাজাকে ‘তিলোত্তমা—সম্ভব কাব্যের’ নিজ হাতেলেখা পাণ্ডুলিপিখানি উপহার দেন এবং বইখানিও উৎসর্গ করেন।৩ বাংলাদেশে বইপ্রকাশের স্বাধীন ব্যবসার অবস্থা যে ১৮৬০—৭০ সাল পর্যন্ত কী ছিল, তা মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের এই রাজপোষকতা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়।
বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর সাহিত্যজীবনে কোনো ব্যবসায়ী প্রকাশকের সহযোগিতা লাভ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ ‘ললিতা’ ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং তার আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে ‘শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।’ শ্রীবৈকুন্ঠনাথ নিশ্চয় লংম্যান বা চ্যাপমানোর মতন কেউ ছিলেন না। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। আখ্যাপত্রে কেবল ‘মুজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮—৫, বিদ্যারত্ন যন্ত্র”—এই খবরটুকু পাওয়া যায়, আর কিছু জানা যায় না। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র—সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ কলকাতা ভবানীপুরের ১নং পিপুলপটী লেন থেকে সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরে নিজ বাসভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্র নামে প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখান থেকেই তার বইগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করতে থাকেন।১
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের ইতিহাসেও এই ধারার বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম হয়নি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ‘কবি কাহিনী’। তাঁর এক উৎসাহী বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এই বই ১৮৭৮ সালে প্রকাশ করেন। এ—সম্বন্ধে ”জীবনস্মৃতি”—তে তিনি লিখেছেন : ”এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ—আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু (প্রবোধচন্দ্র ঘোষ) এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন।” কবি কাহিনীর আখ্যাপত্রে লেখা আছে :
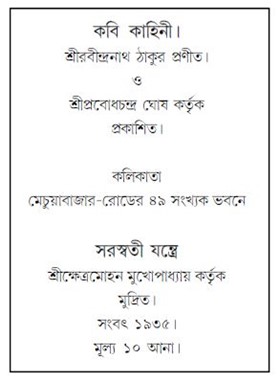
প্রথম গ্রন্থের মুদ্রিত রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথকেও বিস্মিত হতে হয়েছিল, ১৮৭৮ সালে। ১৯০৩—০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় (মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত)। প্রকাশক এস. সি. মজুমদার, ২০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী। ব্যবসায়ী—প্রকাশকদের মধ্যে এই ‘মজুমদার লাইব্রেরীরই’ নাম পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশকরূপে। এই কাব্যগ্রন্থ যখন ছাপা হয়, তখন সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকাশক শৈলেশ মজুমদার প্রসঙ্গে একখানি চিঠিতে লেখেন১ :
”গ্রন্থাবলী কি পর্যন্ত, হলো আমি তার কিছুই জানিনে। ফর্মাচারেক ফাইল পেয়েছিলাম—তারপরে আমার বরাদ্দ বন্ধ। আমার প্রতি নিতান্ত নিঃসম্পর্ক লোকের মতো ব্যবহার করা হচ্চে—শৈলেশের কাছ থেকে কোনো খবরও পাইনে, আশাও পাইনে, প্রুফও পাইনে। যা ছাপা হচ্ছে তাতে ভুলচুক আছে কিনা তাও বুঝতে পারচিনে। যে জননীর ছেলে যুদ্ধে গেছে, এবং যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেনাপতি মহাশয় বাড়িতে খবর পাঠান নিষেধ করেছেন, আমি সেই যুদ্ধক্ষেত্রগত সন্তানের (মাতার) মত বসে আছি—ছেলের গায়ে অস্ত্র লাগছে কিনা তাও জানিনে, সে জয়ী হচ্ছে কিনা সে খবরও পাইনে—এখন কোথায় কোন লড়াইটা হচ্চে সে জনশ্রুতিও আমার কাণে আসে না। কোনো দেশের কোন প্রকাশক গ্রন্থকারের প্রতি এরকম নিষ্ঠুর আইন চালায়নি। দূরে থাকি, সুতরাং নিরূপায় হয়ে বসে আছি। আপনি যদি শৈলেশকে ডেকে তার শৈলের মত অচল চিত্তকে আমার দুঃখে একটু বিচলিত করতে পারেন তাহ’লে আপনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। ইতি ১২ই চৈত্র ১৩০৯—
আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ—কালে, আজ থেকে ৫৩ বছর আগে, রবীন্দ্রনাথ যে মানসিক বেদনা বোধ করেছিলেন, দশ বছর আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের সব সাহিত্যিকই প্রায় সেই বেদনা বোধ করেছেন। মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের মতন প্রতিভা নিয়ে সকলে সাহিত্যক্ষেত্র অবতীর্ণ হননি। কোনো দেশেই তা হন না। বঙ্গদর্শন যন্ত্র, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র বা বিশ্বভারতীর মতন মুদ্রণ ও প্রকাশন—প্রতিষ্ঠান সকলের পক্ষে স্থাপন করাও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত প্রকাশকের পোষকতার অভাবে বাংলা সাহিত্যের যে কত ক্ষতি হয়েছে তা হিসেব করা যায় না।
পরবর্তীকালে বাংলাদেশে অনেক প্রকাশক বইয়ের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের দানও আছে। কিন্তু ইয়োরোপের প্রকাশকদের সঙ্গে এদেশের প্রকাশকদের যে মূলগত পার্থক্য রয়ে গেছে, তার কারণ কী? এ—প্রশ্ন মূলত সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্ন। এ—প্রশ্নের উত্তর, বাংলার নবজাগৃতি—আন্দোলনের উত্থান—পতনের ধারার মধ্যেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যে জাগৃতি—আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তা প্রধানত ইডিওলজির বা আদর্শের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, মাটিতে তার বনিয়াদ বা ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। এই বনিয়াদ হল অর্থনীতির বনিয়াদ। ইয়োরোপে (ইটালিতে) যে রিনেস্যান্সের সূত্রপাত হয়েছিল, তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ধনতন্ত্রের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠায়, অবাধ বাণিজ্যের জয়যাত্রায়। বাংলাদেশে শুধু ইডিওলজির ক্ষেত্রে এই জাগৃতির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল, নতুন শিক্ষার ফলে, কিন্তু তার কোনো ‘মেটিরিয়াল’ ভিত্তি বিশেষ ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামদুলাল দে’র মতন দু—চারজন বাঙালি ব্যবসায়ীর মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের (Free Enterprise) প্রেরণা জেগেছিল বটে, কিন্তু তা স্বাভাবিক বিকাশের কোনো ঐতিহাসিক পথ খুঁজে পায়নি। বেনিয়ানি ও মুচ্ছুদ্দিগিরি করে বাঙালিরা প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজ শাসকরা তা তাঁদের স্বাধীনভাবে ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে দেননি। ধনিক শিল্পপতির বদলে ইংরেজরা বাঙালিদের নতুন জমিদারশ্রেণি ও শিক্ষিত চাকুরিজীবী ভদ্রলোকশ্রেণিতে পরিণত করেছিলেন। বাংলার রিনেস্যান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলন তাই নানা ঘাত—প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষপর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পুনরায় চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়েছিল। নব্যসংস্কৃতির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ বা পরিণতি হয়নি। ইউরোপে ‘জ্ঞানের’ (Knowledge) সঙ্গে ‘বাণিজ্যের’ (Commerce), বুদ্ধির (Intellect) সঙ্গে ‘বিত্তের’ (Money) যে ঐতিহাসিক সমন্বয় হয়েছিল, বাংলাদেশে তার সূচনা হয়েছিল মাত্র, বিকাশ হয়নি।১ বিত্তবানরা তাই বিদ্যাবুদ্ধির বাণিজ্যের পথ বেছে নেননি। দরিদ্ররাও এই পথে দুঃসাহসীর মতন যাত্রা করে বিত্তসঞ্চয়ের চেষ্টা করেননি, ইউরোপের স্বল্পবিত্ত প্রকাশকদের মতন।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই যে দেশে অবাধ বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং উদ্যোগী শিল্পপতি বণিকের আবির্ভাব সম্ভব হয়নি, সে—দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উদযোগী বণিকের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞান—বিজ্ঞান ও সাহিত্যক্ষেত্রের উদযোগী বণিকরাই হলেন আধুনিক যুগের প্রকাশকরা। বাংলাদেশে যাঁরা বইয়ের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা নতুন বাঙালি জমিদার, পত্তনিদার ও গাতিদারদের মতন শোষণ ও পোষণের মনোভাব নিয়েই এসেছিলেন, উদ্যম সৎসাহস ও দূরদৃষ্টি নিয়ে আসেননি। সংকীর্ণক্ষেত্রে তাই বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের দৈন্য ঘোচেনি। বাংলাসাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠীও সেইজন্য প্রসারিত হয়নি, একশতাব্দী ধরে প্রায় একই ছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের দান তাই নগণ্য বলা চলে। যত সমৃদ্ধই হোক, কেবল কথাসাহিত্যের সম্ভার নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চাসন দাবি করা বা সমান মর্যাদা প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। সর্বভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাংলা সাহিত্যের আসন এইদিক দিয়ে টলে উঠবে কিনা, বলা যায় না। ১৮১৮ সালে পীতাম্বর শর্মা যখন ৪৯২ পৃষ্ঠার অভিধান প্রকাশ করেছিলেন, তখন তিনি ৫০০ কপি ছেপে, ৪০০ কপি বিক্রি হয়ে যাবার পর ১০০ কপির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। একশো বছর পরে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত যত শর্মা যত রকমের বই ছেপেছেন, ৫০০ কপির বেশি কেউ ছাপেননি। বাংলা বই, ছোটগল্প কাব্য ও প্রবন্ধ, পনেরো—কুড়ি বছর আগেও, ৫০০ কপির বেশি কোনো প্রকাশক ছাপতেন কি—না সন্দেহ। এর অর্থ এই যে একশো দেড়শো বছরেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির সংখ্যা ও পাঠকের সংখ্যা বাড়েনি। অর্থ তাই হলেও, কথাটা সত্য নয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জনসংখ্যা নিশ্চয় অনেক বেড়েছে, কিন্তু বইয়ের পাঠক তবু সেদিন পর্যন্ত বাড়েনি কেন? কারণ বাড়াবার চেষ্টা করা হয়নি, কোনো উদ্যোগী প্রকাশক তা করেননি। সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা তাই পীতাম্বর শর্মার যুগে সেদিন পর্যন্ত বাস করেছি।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, সম্প্রতি মনে হচ্ছে, আমরা পীতাম্বর শর্মার যুগ অতিক্রম করছি। বাংলা সাহিত্য এতদিন পরে রাজসভা থেকে বেরিয়ে, পাঁচশো—হাজার মধ্যবিত্ত পাঠকের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে, সবেমাত্র হাজার—হাজার পাঠকসাধারণের জনসভায় পৌঁছচ্ছে। শিক্ষিত রুচিবান উদযোগী বাঙালি প্রকাশকরাও সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। প্রকৃত নবযুগের সূচনা হচ্ছে সাহিত্যক্ষেত্রে, তাই বোধহয় বাংলার সাহিত্যিকরা নবযুগের অতীত ইতিহাস আজ আবার নতুন করে দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, শিক্ষা ও জাগৃতি—আন্দোলনের ইতিহাস, মনে হয় তাই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠছে। সাহিত্যের এই শুভযাত্রাকে ঠিকপথে পরিচালিত করার প্রধান দায়িত্ব যাঁদের, সেই বুদ্ধিমান বিচারশীল ও চিন্তাশীল পাঠকগোষ্ঠীর নিশ্চিন্ত সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে। এইটাই আশার কথা।
…….
১. কৃপার শাস্ত্রের অর্থ—ভেদ : সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ।
১. উক্ত গ্রন্থে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘প্রবেশক’ দ্রষ্টব্য।
২. “A Brief Note on Early Printing In India” (The Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing, National Library, Calcutta, 1955).
১. সজনীকান্ত দাস : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) : ২২—২৬ পৃষ্ঠা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড : সম্পাদকীয়— ”বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা”, ৭৩৬—৭৪৩ পৃষ্ঠা।
Early Bengali Printing on Paper : by S. C. Guha : Memoirs of the Madras Library Association, 1941, 44-47.
The three first type-printed Bengali books : H. Hosten : Bengal Past and Present, July-Dec. 1914.
* ৮নং লালবাজার আপজন সাহেবের ”দি ক্রনিকেল প্রেস” ছিল এবং এই প্রেস থেকে ”ক্যালকাটা ক্রনিকেল” পত্রিকা প্রকাশিত হ’ত। এই পত্রিকায় আপজন সাহেবের অভিধানের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। আপজন সাহেব প্রাচীন কলকাতার একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন।
১. উইলিয়ম কেরির অনেক ভালো ইংরেজি জীবনচরিত আছে। বাংলায় শ্রীসজনীকান্ত দাসের ”উইলিয়ম কেরী” (সাহিত্য—সাধক চরিতমালা—১৫) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
১. “The Life and Achievement of William Carey” (The Carey Exhibition etc. National Library).
১. সংবাদগুলি অধিকাংশই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ”সংবাদপত্রে সেকালের কথা” দুই খণ্ড থেকে সংকলিত।
১. হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের ”বঙ্গভাষার লেখক” গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত ”পিতাপুত্র” দ্রষ্টব্য।
২. বিনয় ঘোষ : কলকাতা কালচার (‘বটতলার সাহিত্য’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)
১. Sketches of Calcutta, or Notes of a Late Sojourn in the “City of Palaces” : By A Griffin (Glasgow 1843) : pp. 103-’4.
২. মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব—চরিত : ১ম ভাগ : ৫৬—৫৭ পৃষ্ঠা
১. বিদ্যাসাগর রচিত ”নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস” গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
২. বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর : ৩২ অধ্যায়।
১. “It affords us great pleasure to be able to announce that Baboo Annodaprasad Bonerjee, a distinguished Patron of native education has published at his own expense the whole of the Bengallee writings of the Late Raja Rammohun Roy, for the purpose of disseminating generally the enlightened views of that Indian philosopher in respect to theology and the Hindoo Shastras” ––The Calcutta Courier, January 6, 1840.
১. Schucking : The Sociology of Literary Taste : Ch. 2, 8-11
২. নগেন্দ্রনাথ সোম : মধুস্মৃতি (২য় সং) : ৬০—৬২ পৃষ্ঠা
৩./”মধুস্মৃতি” ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ”মধুসূদন দত্ত” (সাহিত্য—সাধক—চরিতমালা—২৩) দ্রষ্টব্য।
১. ”বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” (সাহিত্য—সাধক—চরিতমালা—২২) দ্রষ্টব্য।
১. বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ ১৩৪৯। এই তথ্য—নির্দেশের জন্য আমি পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।
১. Martin : Sociology of the Renaissance : 5-12, 27-46
পাঠ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৬)
বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত কলকাতা :
মর্ডান বুক এজেন্সি
নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮৬—১৯১৮)
বিশ্বকোষ, ২২ খ.
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৩৯ ব)
সংবাদপত্রে সেকালের কথা
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৬)
সাহিত্য সাধক চরিতমালা
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
সুকুমার সেন (১৯৪০)
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
কলিকাতা : মর্ডান বুক এজেন্সি
সুধীরচন্দ্র সরকার (১৯৬৬)
জীবনী অভিধান
কলিকাতা : এম সি সরকার
Bernier, Francois (1914)
Travel in the Mogul empire,
(A.D) 1656-1668
Edit ed by Vincent Arthur Smith
London, Oxford.
Binns, Norman E (1953)
Introduction to historical
biography
London : Association of
Assitant Librarians.
Burlinghame A E (1920)
Battle of the books in its
historical settings. N.Y: Huebsch
Carter, T F (1931)
Invention of Printing in China
Columbia: The University Press.
Chesterton, Gilbert Keith (1942)
Charles Dickens N.Y. Readers
Club.
Collins, A S (1927)
Authoriship in the days of
Johnson. London : Dutton.
Collins, A.S (1928)
Profession of letters, London :
Routledge.
De, Sushil kumar (1919)
History of Bengali literature in
the 19th century. Calcutta, The
University.
Duffus, Robert Luther (1930)
Books their place in a
democracy
Boston : Houghton Miffin.
Ellis, Havelock (1950)
The genius of Europe : N.Y :
Williams and Norgate.
Fox, Ralph Winston (1954)
Novel and the people, Moscow:
Foreign language Publishing.
Francke, K (1901)
History, of German Literature, as
determined by social forces.
N.Y. : H Holt.
Hunter, w.w. (1868)
Annals of rural Bengal, London:
Smith Elder
Kellett, E E (1931)
Fashion in literature, London,
Routledge
Kellett, E E (1929)
Whirligg of taste, London :
Harcourt Brace.
Mannheim, Karl (1940)
Man and society. London: Kegan
paul
McMurtrie, Douglas Crawford (1943)
The Book: the story of printing &
bookmaking N. Y: Oxford.
Muir, P.H (1947)
Book collecting as a hobby. New
York: A Knopf
Mumby, Frank Arthur (1949)
Publishing and bookselling,
London Jonathan cape.
Mumford, Lewis (1934)
Technics and civilization, N.Y :
Harcourt Brack
Myers, A.R (1961)
England in the late middle ages.
London : Pelican.
Needham, Joseph (1954-)
Science and civilisation in china
London : Allen & Unwin.
Peddie, Robert Alexander (1927)
Printing´ a short history of the art
London: Graffin
Schucking, Levin Ludwig (1966)
Sociology of literary taste.
London: Routledge
Sidhanta, Nirmal Kumar (1929)
Heroic age of india
London : Paul Trench
Trevelyan, George Macaulay (1942)
English social history, London :
Longman
Veblen, Thorstein (1918)
Theory of the Leisure
London : Macmillan
Woolf, Virginia (1929)
A Room Of One’s own. London
: Hog´arth Press
